ভূমিকা
যে জাতি তার গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করে না, সে জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি বাঙালী জাতি, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ক্ষেত্রে কথাটি হাড়ে হাড়ে সত্যি। তারা তাদের পূর্বসুরী গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা তো দূরের কথা খোঁজ খবরটুকুও রাখেন না। তাছাড়া বর্তমান প্রজন্মে এসে যতটুকু বা মূল্যায়ন করার চেষ্টা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও খন্ডিত। ঠুনকো স্বার্থের কারণে কাউকে বা অহেতুক বিরাট বিশাল করে দেখানো হচ্ছে আবার কাউকে খাটো করতে করতে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটিই সত্য নয়। ফলে জাতি বিভ্রান্ত হচ্ছে, প্রকৃত গুণীরা ক্রমে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছেন।
সেই দায়ভার থেকেই আমরা ‘মুসলিম মনীষীদের জীবনী’ ধারাবাহিকভাবে জাতির সামনে তুলে ধরার পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রথম খন্ডে দেশী-বিদেশী মোট ২০ জন মুসলিম মনীষীর সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল জীবনী তুলে ধরা হল। এদের মধ্যে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ইসলাম প্রচার, রাজনীতি নানা অঙ্গনের মনীষীরা রয়েছেন। আমরা বয়োক্রম অনুযায়ী শিরোনাম সাজিয়েছি।
এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুলোর ভিতর কয়েকটি লেখা কিশোর তরুণদের উদ্দেশ্য করে লেখা। তবে আমাদের বিশ্বাস তথ্যবহুল ঐ লেখাগুলো বড়দের উপকারে আসবে।
‘সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবনকথা’ প্রথম খন্ডে যে লেখাগুলো স্থান পেল-তাতে যদি কারো চোখে কোন ভুল তথ্য ধরা পড়ে তা আমাদের লিখে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।
বিনীত
নাসির হেলাল
১/জি/৯, মীরবাগ
ঢাকা ১২১৭।
\r\n\r\n
মহাকবি শেখ সাদী
প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন। ডাক নাম মসলেহউদ্দীন। আর উপাধি বা খেতাব হচ্ছে সাদী। আসল নাম নয়, তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন উপধি ‘সাদী’ নিয়ে। মানে শেখ সাদী নামে। জানা যায় কবির আব্বা তৎকালীন শিরাজের বাদশাহ আতাবক সাদ বেন জঙ্গীর সেক্রেটারী ছিলেন। কবি নিজে তুকলাবীন সাদ জঙ্গীর রাজত্বকালে কবিতা লিখতেন, এ কারণেই তিনি তার নামের সঙ্গে সাদী উপাধি যোগ করেন এবং পরবর্তীকালে শেখ সাদী নামেই পরিচিত হয়ে হন।
শেখ সাদীর জন্মসনের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবুও মোটামুটি বলা যায় তিনি ৫৮০ হিজরী মোতাবেক ১১৮৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু তারিখ সবার মতে৬৯১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২ খৃস্টাব্দ।
পরহেজগার পিতার সাহচর্যেই শেখ সাদী শিশুকাল অতিক্রম করেন। পিতার দেখাদেখি সাদীও নামায, রোযা ও রাত্রিকালীন ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। পিতার উৎসাহে কুরআন অধ্যয়নে তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। বলা যায় দরবেশ পিতার আদর্শেই আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠেন শেখ সাদী।
বাল্যকালেই সাদীর পিতা ইন্তিকাল করেন। পিতার ইন্তিকালের পর সাদী পুণ্যবতী ও গুণবতী মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকেন। এ সময়ে তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তির স্নেহধন্য হন। তিনি হলেন তাঁরই শ্রদ্ধাভাজন মামা আল্লামা কুতুবুদ্দীন শিরাজী। যিনি কিনা হালাকু খাঁর অন্যতম দরবারী বন্ধু ছিলেন।
তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সূত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁর নিজের লেখা হতে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন-তিনি যখন নিতান্ত ছোট তখন তাঁর আব্বা লেখার জন্য তাঁকে একটি ‘তখতি’ ও হাতের আঙ্গুলে পরার জন্য একটি সোনার আঙটি কিনে দেন্। কিন্তু এক মিষ্টি বিক্রেতা কবিকে মিষ্টি দিয়ে ভুলিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট দেয়। আংটি খোয়া গেলেও একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে কবি মিষ্টি খুব পছন্দ করতেন।
একবার ঈদের দিন ঈদের ভিড়ে শেখ সাদী পিতার জামার প্রান্ত ধরে হাঁটছিলেন, যেন পিতা হতে তিনি আলাদা না হয়ে যান। কিন্তু পথে খেলাধুলায় মত্ত ছেলেদের দেখে জামার প্রান্ত ছেড়ে তিনি তাদের দলে ভিড়ে যান। পরবর্তীতে শেখ সাদীর আব্বা যখন তাঁকে ফিরে পান তখন রেগে গিয়ে বলেন, “গাধা! তোকে না বলেছিলাম কাপড় ছাড়িস না।”
জানা যায়, একবার তিনি তাঁর আব্বার সাথে সারারাত ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিলেন। এ সময় ঘরের অন্যান্যরা ঘুমে অচেতন ছিল। এ অবস্থা দেখে সাদী তাঁর আব্বাকে বললেন, ‘দেখছেন, এসব লোক কেমন সংজ্ঞাহীন হয়ে ঘুমাচ্ছে। কারো এতটুকুও সৌভাগ্য হচ্ছেনা যে, উঠে দু’রাকাত নামায পড়ে।’ এ কথার উত্তরে সাদীর পিতা বললেন, ‘তুমি যদি শুয়ে থাকতে তবেই ভাল হতো; তাহলে পরচর্চা হতে বিরত থাকতে।’
শেখ সাদীর প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মহান পিতার নিকট হয়েছিল। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। এ সময়ে তিনি শিরাজের প্রখ্যাত আলেম উলামাদের সংস্পর্শে আসেন এবং জ্ঞান আহরণ করতেন।
প্রথম দিকে তিনি শিরাজের সুলতান গছদদৌলা প্রতিষ্ঠিত গছদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি আরো কয়েকটি মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণ করেন। এ সময়ে দেশের শাসক আতাবক জঙ্গী দেশ জয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে দেশ গঠনে উদাসীন ছিলেন। ফলে দেশের অস্থিতিশীল পরিবেশে সেখানে শিক্ষার কোন পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। এমতাবস্থায় শেখ সাদী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মানসে বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত মাদরাসা নিযামিয়ায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসার যাত্রকাল হতে মুতুওল্লী ছিলেন শিরাজের স্বনামখ্যাত আলেম শেখ আবু ইসহাক শিরাজী। শেখ সাদী অল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং বৃত্তি লাভ করেন।
মাদ্রাসা নিযামিয়ায় অধ্যয়নকালে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তৎকালীন সময়ের বিশ্ববিখ্যাত আলেম আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে জৌজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি ছিলেন তাফসীর ও হাদীসশাস্ত্রে তখনকার ইমাম। ইবনে জৌজীর আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। শেখ সাদী আল্লামা শাহবুদ্দীন সুহরাবদীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন।
শিশুকাল হতে যদিও শেখ সাদী ফকিরী ও দরবেশী জীবন বেশি পছন্দ করতেন তবুও তিনি জ্ঞান অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন, ‘দরবেশ শুধু নিজকে বাঁচানোর চেষ্টায়ই থাকে। অপরপক্ষে আলেমদের চেষ্টা থাকে নিজের সাথে অন্য ডুবন্ত লোকদের বাঁচিয়ে তোলার।’
শেখ সাদী বাগদাদের লেখাপড়া শেষ করে দেশভ্রমণে বের হন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন-
ত্রিশ বছর লেখাপড়ায়
ত্রিশ বছর দেশভ্রমণে
ত্রিশ বছর গ্রন্থ রচনায়
ত্রিশ বছর আধ্যাত্মিক চিন্তায়।
শোনা যায় তাঁর জীবনের উক্ত চারটি পর্যায় যেদিন পূর্ণ হয় সেদিনই নাকি তিনি ইন্তিকাল করেন। শেখ সাদী দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে এমন পান্ডিত্য অর্জন করেন যে তিনি আঠারটি ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হন। এর ভেতর অনেকগুলি ভাষা তার মাতৃভাষার মতই ছিল। আর তিনি এত অধিক দেশ ভ্রমণ করেন যে ইবনে বতুতা ছাড়া প্রাচ্য দেশীয় পর্যটকদের মধ্যে কেউই এত অধিক দেশ ভ্রমণ করেন নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি পায়ে হেঁটে চৌদ্দবার হজ্জ্ব পালন করেছিলেন। তিনি তার সফরকালে অসংখ্য নদী এমনকি পারস্যোপসাগর, ভারত মহাসাগর, ওমান সাগর, আরব সাগর প্রভৃতি পাড়ি জমিয়েছেন। আর সঞ্চয় করেছেন জ্ঞানের রাজ্যে অসংখ্য মনি মুক্তা, হিরা-জহরত।
দেশ ভ্রমণকালে শেখ সাদী এক সময়ে কোন কারণে দামেশকবাসীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে ফিলিস্তিনের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে তখনকার খৃস্টানদের হাতে বন্দী হন। খৃস্টানগণ বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হতে আনীত ইহুদী বন্দীদের সাথে কবিকে খন্দক খননের কাজে নিয়োজিত করে। একদিন সৌভাগ্যক্রতে তাঁর পিতার এক বন্ধু তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি দশ দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনেন এবং একশত আশরাফী দেনমোহর ধার্য করে নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু সাদীর এ স্ত্রী অতন্ত বাচাল ছিলেন বলে এই বিয়ে বেশিদিন টিকে নি। তিনি একদিন সাদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘তুমি কি পূর্ব জীবনের কথা ভুলে গেছ? তুমিতো সেই ব্যক্তি যাকে আমার পিতা দশটি রোপ্য দিনার দিয়ে মুক্ত করেছেন।’ উত্তরে কবি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, তিনি দশ দিনারে মুক্ত করে একশত আশরাফী দিয়ে পুনরায় বন্দী করেছেন।’
ভারত ভ্রমণকালের একটা ঘটনা তাঁর বুসতাঁ কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল সোমনাথ মন্দিরের। কবির মুখেই শুনি সেই ঘটনা, “আমি সোমনাথ এসে যখন দেখতে পেলাম হাজার হাজার লোক এসে মূতির নিকট নিজ নিজ মনস্কামনা হাসিলের জন্য পূজা দিচ্ছে তখন আমি বিস্মিত হলাম। হাজার হাজার জীবিত লোক এক প্রাণহীন মূর্তির নিকট মনষ্কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা জানাচ্ছে।”
একদিন আমি এক ব্রাহ্মণের নিকট যেয়ে এর রহস্য জানতে চাইলাম। ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনে মন্দিরের পূজারীদের ডেকে আনলো-তারা এসে ক্রোধ ভরে আমাকে চারিদিক হতে ঘিরে ফেললো, আমি তখন সমূহ বিপদ দেখে বললাম, তোমাদের দেবতার অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়…….তবে আমি এখানে নতুন এসেছি, এ মহান দেবতার পূজাদি কিভাবে দিতে হবে জানি না বলে জানতে চেয়েছি। আমাকে তা শিখিয়ে দাও যেন ঠিক পূজা করতে পারি।
তখন পূজারিগণ খুশি হয়ে আমাকে পূজার ধরন ধারণ শিখিয়ে দিয়ে মন্দিরে নিয়ে গেল। তারা আরও বলল, আজ রাতে তুমি মন্দিরে থাক তখন এ দেবতার শক্তি দেখতে পাবে।
আমি সারারাত মন্দিরে কাটালাম। ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তখন মূর্তি একখানা হাত উঠিয়ে পূজারীদের আশীর্বাদ করল। তখন সকলেই জয় জয় করে উঠল। এরপর নিশ্চিন্ত মনে সকলে চলে গেল। ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে হেসে বলল, কি বল, এখন বিশ্বাস হল তো!
আমি বাহ্যিকভাবে কেঁদে কেঁদে আপন মূর্খতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। তখন ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হয়ে মূর্তির নিকট নিয়ে গেলে আমি তার হাত চুম্বন করে সম্মান জানালাম। এরপর যেন সত্যিকার ব্রাহ্মণ হয়ে আমি নিশ্চিন্তে মন্দিরে আসা যাওয়া করতে লাগলাম।
আর এক রাত্রে সকলে চলে গেলে, আমি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মূর্তির নিকট গিয়ে এর ভেদ জানতে চাইলাম। আমার চোখে পড়ল মূর্তির পিছনে একখানি পর্দার আড়ালে রশি ধরে একজন পূজারী বসে আছে। রশির একদিক মূর্তির সাথে বাঁধা। সে পূজারী যখন রশি ধরে টানে তখনই মূর্তির হাত উপরে উঠে যায় আর সাধারণ লোক তাকেই মূর্তির শক্তি বলে নাচতে থাকে।
সে পূজারী পর্দার আড়াল হতে যখন দেখতে পেল আমি তাদের গোপন রহস্য জেনে ফেলেছি তখন সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি তখন প্রাণের ভয়ে তাকে ধরে এক কূপে ফেলে দিলাম।
এরপর সে রাতেই সোমনাথ ছাড়লাম। ভারতের পথে ইমনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হেযাজে এসে পৌছলাম।”
শেখ সাদী হলেন বিশ্ববিখ্যাত ক’জন কবির মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত গুঁলিস্তা ও বুঁসতা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অনেকে মনে করেন, এই গ্রন্থ দুটি অধ্যয়ন ব্যতীত ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন অপূর্ণ থেকে যায়। এ গ্রন্থ দুটি একত্রে ‘সাদী নামাহ’ নামে পরিচিত। নৈতিকতা বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ হল বুঁসতা। আর নৈতিকতা বিষয়ক গদ্যগ্রন্থ হল গুঁলিস্তা। গুলিস্তাঁয় লেখক অত্যন্ত সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নৈতিকতার বিষয় আশয় গল্পোচ্ছলে পরিবেশন করেছেন। এর ভেতর অবশ্য কবিতাও আছে। এমন কি কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতিও লেখক ব্যবহার করেছেন নিজের বক্তব্যকে সুন্দর ও জোরালো করার জন্য।
সাদী ছিলেন অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী। এ ব্যাপারে মাওলানা আবদুর রহমান জামী বলেছেন, ‘রুমীর মসনবী, আনোয়ারীর কাসিদা এবং সাদীর গযল সমপর্যায়ের।’ তিনি আরো মনে করতেন যে, শেখ সাদী বিশ্ব বিখ্যাত লেখক আমীর খসরুর চেয়েও বড় লেখক। অবশ্য আমীর খসরু নিজেও তার ‘সেপাহর মসনবী’ গ্রন্থে শেখ সাদীকে গযলের উস্তাদ হিসেবে স্বীকার করেছেন।
শেখ সাদীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে চমৎকার একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হল-‘শিরাজের এক ব্যক্তি সাদীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এক রাতে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পেলেন, েএকজন ফেরেশতা একখানি নূরের বরতন নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন। ঐ ব্যক্তি জানতে চাইলেন এ কি ব্যাপার? ফেরেশতা জবাবে বললেন, সাদীর একটি কবিতা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে-সে জন্য বেহেশতের এ উপহার। কবিতাটি হল-
জ্ঞানিদের চোখে
গাছের ঐ সবুজ পাতা
খোদা তত্ত্বের
এক একখানি গ্রন্থ।
ঐ ব্যক্তির যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন সেই রাতেই সাদীর গযলটির ব্যাপারে স্বপ্নে দেখা খোশ খবর জানতে গেলেন। আশ্চর্য! লোকটি দেখেন উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে শেখ সাদী সেই কবিতাটিই পড়ছেন।’
আরো একটি ঘটনা, শেখ সাদী তখন দেশ বিদেশে বেশ মশহুর হয়ে পড়েছেন। একদিন শিরাজ হতে ষোল শ মাইল দূরের কাশগড়ে বেড়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন ছোট বড় সবাই তাঁর নাম জানে ও তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ।
সাদী উঠেছিলেন কাশগড়ের জামে মসজিদে। সেখানে একজন ছাত্র আল্লামা যমখশীর একটি গ্রন্থ হাতে নিয়ে বলেছিল, ‘কোরবে যায়েদ মির’।
ছাত্রটির কথা শুনে শেখ সাদী বললেন, ‘খাওয়ারযমের ও তাঁর শত্রুর মাঝে সন্ধি হয়ে গেছে তবে যায়েদ ও মীরের ঝগড়া এখনো চলছে।’ ছাত্রটি একথা শুনে সাদীকে বললো, জনাবের দেশ কোথায়?
‘শিরাজ’।
তবে তো সাদীকে চিনেন। তাঁর দু/একটি কালাম শুনাবেন কি?
আরবীতে কিছু কালাম বললেন সাদী।
যদি দু’একটি ফারসী কালাম শুনাতেন। ছাত্রটি বলল।
একটি ফরাসী বয়াত পেশ করলেন সাদী।
পরে যখন ছাত্রটি জানলো ‘ইনিই সেই মহাকবি শেখ সাদী। তখন সে করজোড়ে কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, কাশগড়ে যদি কিছুকাল অবস্থান করেন তো খেদমত করতে পারতাম।’
কিন্তু সাদী কাশগড়ে আর থাকতে পারেন নি। তিনি সেখান হতে তিবরীজ চলে যান।
অনেক ইংরেজ লেখক শেখ সাদীকে প্রাচ্যের শেক্সপীয়র বলে আখ্যায়িত করেছেন।
শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল-
১. গুলিসতাঁ ২. বুস্তুাঁ ৩. করিমা ৪. সাহাবিয়া ৫. কাসায়েদে ফারসী ৬. কাসায়েদে আরাবীয়া ৭. গযলিয়াত ৮. কুল্লিয়াত ইত্যাদি।
বুস্তাঁ ও গুলিসতাঁ গ্রন্থ দুটি এশিয়ায় সব থেকে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই গ্রন্থ দুটির অনেক কথায় পারশ্য সাহিত্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে।
পন্ডিতদের মতে গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে ফারসি ভাষায় ৪ খানি গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। তা হল-
মহাকবি ফেরদাউসী’র-------শাহনামা
জালালুদ্দীন রুমি’র ------- মসনবী
শামসুদ্দীন হাফেযে’র------- দিওয়ান
এবং শেখ সাদীর-------------গুলিস্তাঁ
গুলিসতাঁ উপদেশমূলক চমৎকার সব গল্পে ভরপুর। যেমন-‘এক বাদশাহ এক অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেন। লোকটি বহু কাকুতি মিনতি করেও যখন কিছু হল না তখন বাদশাহকে গালি দিয়ে বসল। বাদশাহ তার কথা বুঝতে না পেরে উজিরের নিকট জানতে চাইলেন সে কি বলেছে।
সেই উজির ছিলেন নেক মেযাজের, তাই তিনি লোকটির উপকারার্থে বললেনঃ হুযুর লোকটি বলছে-যিনি রাগ দমন করে অপরাধ করেন, তিনি খোদার বন্ধু। একথা শুনে বাদশাহ খুশি হয়ে লোকটিকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। অন্য একজন হিংসুক স্বভাবের উজির ছিলেন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, হুযুর এ মিথ্যা কথা। লোকটি আপনাকে মন্দ বলেছে।
তা শুনে বাদশাহ বললেন, তোমার কথা সত্য হলেও অন্য উজিরের মিথ্যার চেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাতে ছিল পরোপকারের উদ্দেশ্য-আর তোমার কথায় অনিষ্ঠের অভিসন্ধি।’ বাদশাহ লোকটিকে ক্ষমাই করেছিলেন।
এমনি সব গল্প দিয়ে ভরা রয়েছে গুলিসতাঁ যার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। শেখ সাদী দৈহিকভাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন। কষ্টসহিষ্ঞু এ মানুষটি প্রচন্ড উদারও ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে দেশের পর দেশ ভ্রমণ করেছেন। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, নদী-নালা সবই তাঁর পায়ের তলায় হার মেনেছে। এমনকি তিনি ফকির দরবেশের ন্যায় এসব পথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খালি পায়ে পাড়ি জমিয়েছেন।
এ ধরনের ভ্রমণে যে নানা ধরনের দুঃখ কষ্ট আসে তা ভুক্তভোগীরা জানেন। শেখ সাদীর জীবনেও নানা বিপদ আপদ এসেছ এবং তিনি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একবার তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। এ ব্যাপারে গুলিস্তাঁ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘আমি কখনো কালের কঠোরতা ও আকাশের নির্মমতার ব্যাপারে অভিযোগ করিনি। তবে একবার আমি ধৈর্য্ ধরে রাখতে পারিনি। আমার পায়ে জুতা ছিলনা এবং জুতা কিনার মত অর্থও ছিল না। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কুফার মসজিদে গিয়ে উঠলাম। তথায় গিয়ে দেখি একটি লোক শুয়ে আছে যার একখানি পা-ই নেই। তখন খোদাকে শোকর জানিয়ে নিজের খালি পা থাকাও গনিমত মনে করলাম।’
শেখ সাদী তাঁর দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য বিচিত্র সব ঘটনা দেখেছেন। তিনি দেখেছেন-বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান পতন। তিনি উজিরের ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখেছেন। আবার ভিক্ষুককে দেখেছেন উজির বনে যেতে। তিনি এও দেখেছেন মুসলিম সাম্রাজ্যের শৌর্য্ বীর্য্, সাথে সাথে পতনের দৃশ্য। তাঁরই সামনে তাতারদের হাতে সাত লক্ষ মুসলমান খুন হয়েছে। খোরাসানের চারটি শহর, বলখ, মরদ, হেরাত এবং নিশাপুর ধ্বংস হতে দেখেছেন।
শেখ সাদী বড় বড় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন। এ সময়ে তিনি দেখেছেন ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে মানুষ মারা যায়। তিনি নিজেই আরবী একটি মর্সিয়ায় বলেছেন-
আব্বাসীয় খেলাফতের ধ্বংসের পর
যে সমাধান হয়েছে
খোদা তার সহায় হোক।
কেননা
যায়েদের বিপদ
উমরের চোখ খুলবে।
এই মহান মনীষী কবিকুল শিরোমণি শেখ সাদী ৬৯১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২ খৃস্টাব্দে আতাবকানের বংশের রাজত্বের শেষ সময়ে শিরাজ নগরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশত কুড়ি বৎসর। শিরাজ নগরীর দিলকুশার এক মাইল পূর্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে কবিকে সমাহিত করা হয়।
\r\n\r\n
মহাকবি হাফিজ সিরাজী
“হে হাফিজ তোমার বাণী চিরন্তনের মত মহান। কেননা, তার জন্য আদি ও অন্ত নেই। তোমার ভাষা আসমানের গম্বুজের মত একাকী নিজের ওপরই স্থিত। তোমার গজলের অর্ধেকটায় বা প্রথম কলিতে কিংবা অন্য কোন অংশের মধ্যে মোটেও পার্থক্য করা যায় না। কেননা এর সবটাই সৌন্দর্য্ ও পূর্ণতার নিদর্শন। একদিন যদি পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়, হে আসমানী হাফিজ! আমার প্রত্যাশা যে, একমাত্র তোমার সাথে ও তোমার পাশে থাকবো। তোমার সঙ্গে শরাব পান করব। তোমার মতই প্রেমে আত্মহারা হব। কেননা এটাই আমার জীবনের গৌরব ও বেঁচে থাকার পাথেয়।” (ওয়ালফ গঙ্গ গ্যেটে)
যার সম্বন্ধে মহাকবি গ্যেটে একথা বলেছেন তিনি হলেন বিশ্বের কবিকুল শিরোমনি হাফিজ শিরাজি। তাঁর পুরো নাম হলো খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী। বিশ্বের বিরল কবি ব্যক্তিত্ব হাফিজ শিরাজি। ৭১০ হতে ৭৩০ হিজরী সনের মধ্যে ইরানের শিরাজ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বাহাউদ্দীন সুলগারী। কবি শিরাজ ছিলেন পিতা সুলগারীর কনিষ্ঠ পুত্র। কবির দাদা ছিলেন ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের ‘কুপাই’ নামক স্থানের অধিবাসী। আতাবক শাসন আমলে তিনি সপরিবারে কুপাই ত্যাগ করে ফারছ এর রাজধানী শিরাজ নগরীর রুকনাবাদ নামক মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। কবির মায়ের জন্মস্থান ছিল ‘কাজেরুণ’ নামক স্থানে।
হাফিজ শিরাজী অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। যে কারণে পাঠশালায় গমনের পরিবর্তে রুটি রুজির তাগিদে তিনি একটি রুটির দোকানে কাজ নেন। এখানে তাঁকে শেষ রাত পর্যন্ত কঠোর শ্রম দিতে হত। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুলের জীবনের সাথে একান্ত মিল দেখতে পাই। কাজী নজরুল ইসলামও শিশুকালে ইয়াতিম হন এবং জীবিকার জন্য রুটির দোকানে কাজ নেন। কবি শিরাজী যে পথ দিয়ে রুটির দোকানে যেতেন ঐ পথেই ছিল একটি মক্তব। আসা-যাওয়ার পথে তাঁর মনে কোরআন শিক্ষার ইচ্ছা জাগে। তিনি মক্তবে ভর্তি হন এবং রুটির দোকানে কাজের পাশাপাশি লেখাপড়ার কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিরাজী সমস্ত কুরআন কন্ঠস্থ করেন ও লেখাপড়ায় অশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তোমরা শুনলে বিস্মিত হবে যে, তিনি চৌদ্দটি পদ্ধতিতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন,
‘হে হাফেজানে জাহান ছুবন্দে জাম না কারদ
লতায়েফে হুকমী বা নেকাতে কোরআনী।’
অর্থাৎ, ‘জগতের মাঝে এমন হাফেজ পাবে নাকো খুঁজে,
আমার মত যে কুরআনের তত্ত্বে দর্শন বুঝে’।
জানা যায় তিনি রুটির দোকানে কাজ করে যে কাজ করতেন তা চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে একভাগ তাঁর মায়ের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষকদের জন্য, তৃতীয় ভাগ ফকীর মিসকীনদের জন্য এবং চতুর্থভাগ রাখতেন নিজের হাত খরচের জন্য। কবির দিওয়ানে ই হাফিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিকহ), হাদীস, ন্যায়শাস্ত্র (কালাম), তাফসীর, ফার্সী সাহিত্য ইত্যাদিতে সুপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি তিনি জ্যোতিষ বিজ্ঞানের জ্ঞানও আয়ত্ব করেছিলেন।
কবি শিরাজী তাঁর যৌবনকালেই লেখালেখিতে হাত পাকিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যতদূর সম্ভব তিনি শাহ শেখ আবু ইছহাকের প্রশংসা কীর্তন আছে। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশাই তিনি মুজাফফর বংশীয়দের শাসনকালও অবলোকন করেন। যাই হোক কবি তাঁর জীবদ্দশাতেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জনে সক্ষম হন। যদিও তাঁর সময়টা ছিল সাহিত্য ও কাব্যচর্চার জন্য খুবই খারাপ সময়। কারণ এ সময়টাতে তাঁর দেশে নানা রকম হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ বিরাজমান ছিল।
কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্তবৃন্দ তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। বাগদাদের সর্বগুণান্বিত সুলতান আহমদ বিন আবেস কবি হাফিজকে বাগদাদে পাওয়ার জন্য বারবার আমন্ত্রণ পাঠাতে থাকেন কিন্তু কবি প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ঐ সময় কোথাও যেতে রাযী ছিলেন না। তাই সম্রাটের আহবানকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
ইস্পাহানের শাসনকর্তার মন্ত্রী উম্মাদ বিন মাহমুদ কবিকে দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু কবি এ দাওয়াতও কবুল করেন নি। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান শাহ মাহমুদ কবি সাহিত্যিকদের অসম্ভব সম্মান করতেন। দেশ বিদেশের কবি সাহিত্যিকদের তিনি নানা সম্মানে সম্মানিত করতেন। এ সময়ে কবি হাফিজ দাক্ষিণাত্যে আসার জন্য ইরাদা করেছিলেন কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।
বাঙালীদের জন্য গর্বের বিষয় হল, সে সময়কাল বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ কবি শিরাজীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি না আসতে পারলেও সে কথা তার কবিতায় লিখে গেছেন। কথিত আছে গিয়াসউদ্দীনের তিনজন প্রিয় দাসী ছিলেন – এদের নাম সরব, গুল ও লালা।
সুলতান একদিন এ চরণটি ফাঁদলেন—
‘সাকী হাদীসে সারবো গোলো লালা মিরওয়াদ’ কিন্তু আর পরবর্তী চরণটি পূরণ করতে পারলেন না। সভাকবিরাও সুলতানের মনপুত কিছু দিতে পারলেন না। তখন সুলতান উক্ত লাইনটি কবি হাফিজ শিরাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবি হাফিজ শিরাজী এর উত্তরে কবিতাটি পূর্ণ করে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবিতাটি এ রকম-
‘সাকী হাদীসে সারবো গোলো লালা মিরওয়াদ
ওইন বাহাস বা সালাসায় গোসালা মিরওয়াদ।
…………………………………………….
হাফিজ যে শওকে মজলেসে সুলতান গিয়াছোদ্দিন
খামুশ মালো কে কারে তু আজ লালা মিরওয়াদ।
কবিতাটির শেষ দু’লাইনের অর্থ হলো-‘হে হাফিজ সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মজলিসে চুপ করে থেকোনা, কেননা তাঁর কাজ কান্নার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।’
কবি শিরাজী সুলতান গিয়াসউদ্দীনের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর বাংলায় আসার জন্য মনস্থির করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু সাইক্লোন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে আসতে পারেন নি। আমাদের গর্ব হল কবিকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে বাংলা ও বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ইরানের সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।
কবি হাফিজ শিরাজী কাব্য প্রতিভা ও দর্শন সারা পৃথিবীর কাব্যা মোদী ও চিন্তাশীল মনকে যুগে যুগে নাড়া দিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার মহান কবি ও চিন্তাবিদ গ্যেটে(১৭৩৯-১৮৩২)বলেন, ‘হঠাৎ প্রাচ্যের আসমানী খুশবু এবং ইরানের পথ-প্রান্তর হতে প্রবাহিত চিরন্তন প্রাণ সঞ্জীবণী সমীরণের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন এক অলৌকিক ব্যক্তিকে চিনতে পারলাম, যার বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আমাকে আপাদমস্তক তার জন্য পাগল করেছে।’ মহাকবি গ্যেটে হাফিজের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে, ‘একটি সময়ের জন্য সবকিছুকে এবং সবাইকে ভুলে যান এবং নিজেকে ফার্সী ভাষার এই কবির ক্ষুদ্র ভক্ত বলে অনুভব করেন।’ এমন কি তিনি হাফিজের প্রেমানুভূতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকাব্য ফাউস্ট (FAUST) রচনা করেন। যেটাকে পাশ্চাত্য দিওয়ান বলা হয়।
বাংলা ভাষাভাষী কবি সাহিত্যিকদেরও তিনি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরতো নিজে ১৯৩২ সালে ইরানের শিরাজ নগরে কবির মাজারে উপস্থিত হয়ে ম্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন। এমনকি কবির পিতা মহর্ষি দেবন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এই ব্যাপারে লিখেছেন, ‘আমি জানি যে হাফিজের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতাকে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ঞবদের দর্শন ও সঙ্গীত ততখানি করতে পারত না। হাফিজ ছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক আনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিকতেন না। হাফিজের কবিতাই তাঁর সৃষ্টির আকাঙ্খাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তার ক্ষুধা নিবারণ করত এবং হাফিজ তাঁর তৃষ্ঞা মিটাত।’ জানা যায় মহর্ষি দেবন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরো দিওয়ান মুখস্ত ছিল।
গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ঞচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কান্তিচান্দ্র ঘোষ, হরেন্দ্র নাথ দেব প্রমুখ বিখ্যাত কবিরা কবি হাফিজের বহু রুবাইয়াৎ ও গযল অনুবাদ করেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজকে এত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন যে, তাঁর পুত্র বুলবুলের মৃত্যুশয্যায় বসেও তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন। তিনি ফার্সী থেকে মোট ৭৩ টি রুবাই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি যেদিন অনুবাদ শেষ করেন সেদিন কবি পুত্র বুলবুল ইন্তিকাল করেন। কবি তাই বেদনার সাথে লিখেছেন, ‘আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলাদশে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইরানের কবি সম্রাট হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। কিন্তু তিনি আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারতেন না।’
ফার্সী সাহিত্যের আলোচনা করে লেখা গ্রন্থটি হচ্ছে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ‘পারস্য প্রতিভা’। এ গ্রন্থে কবি হাফিজের ওপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন লিখেছেন, ‘ইরানের কবি’। অবশ্য এ গ্রন্থে ‘শামসুদ্দিন হাফিজ’ নামে যে নিবন্ধটি আছে তা তেমন তথ্যবহুল নয়।
বাংলা ভাষায় দিওয়ানে হাফিজের বহু অনুবাদ হয়েছে। এরমধ্যে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অনুবাদ কর্মটি বাংলা ভাষার এক অসামান্য প্রকাশনা। এ বইয়ের দীর্ঘ উপক্রমিনাতে তিনি হাফিজকে বাংলা ভাষাভাষির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে কাজী আকরাম হোসেনের অনুবাদটিও চমৎকার। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার দু’জন আধুনিক কবি যারা প্রগতিবাদী হিসেবেও পরিচিত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুবাশ মুখোপাধ্যায় কবি হাফিজের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছেন।
কবির ৬০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, ‘কবি হাফিজ আমাদের চিন্তায় ও মননে বহুকাল বিদ্যমান ছিলেন। বাংলা কবিতায় আবার তিনি নতুন করে জাগ্রত হচ্ছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষায় হাফিজ ছিলেন অনেক বড় প্রতিভা, অনেক বড় কবি এবং প্রেমিক। কবির কুরআনের ওপর দক্ষতা দেখে সমকালীন একজন পীর মুর্শিদ তাঁকে হাফিজ উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ব্যাপার কবি নিজেই লিখেছেন-
‘হাফিজ! তোমার চেয়ে সুন্দর গান আর দেখিনাই আর কারো
তোমার মুখের লুকানো কোরান সে তো সুন্দর আরো।’
কবি ছিলেন একজন সুন্দর প্রেমিক। তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে লিখেছেন-
‘প্রেয়সী মোর ছিল যে হায় পরীর মত অপসরী
পা থেকে তার কেশাগ্রতক নিটোল যেন ঠিক পরী।’
কবি তাঁর আদরের সন্তানের মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে লিখেছেন-
‘মোর নয়ন মণি দীলের মেওয়া তাহার তরে কাঁদে প্রাণ
হাসতে হাসতে চলে গেল, শোকে আমি ম্যূহমান।’
যদিও এখানে আপন সন্তানের জন্য কবি হাফিজ এ আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু এ শোক বাণী জগতের সব পুত্রহারা পিতৃ হৃদয়কে নাড়া না দিয়ে পারে না।
ও যাহ! একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি। দিগ্বিজয়ী মঙ্গল বীর তৈমুর লঙ কবির একটি কবিতা বুঝতে না পেরে কবিকে তলব করেন। কবিতাটি ছিল-
সেই শিরাজী প্রেমিক যদি জয় করে মোরে এই হিয়ারে
তার গালের তিলে বিলিয়ে দেব সমরকন্দ আর বুখারারে। (দিওয়ানে হাফিজ-গজল নং ৩)।
তৈমুর লঙ কবির কাজে জানতে চাইলেন, এ কবিতা কার? কবি যখন স্বীকার করলেন এ তারই কবিতা, তখন তৈমুর লং বললেন, ‘আমি হাজার হাজার সৈন্যের রক্তের বিনিময়ে হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে যা দখল করেছি, হাজারো লক্ষ ধন সম্পদ রত্নরাজির বিনিময়ে যা গড়ে তুলেছি, আর তুমি নারীর গালের কালো তিলের বিনিময়ে তা বিলিয়ে দিতে চাচ্ছ?
কবি বুঝলেন, যুদ্ধবাজ তৈমুরের মাথায় কাব্যের মহিমা ঢোকার কথা নয়। কবি তাই বিনীতভাবে বললেন, ‘মহামান্য বাদশাহ। এভাবে দান খয়রাত করতে গিয়েই তো আমার আজ এ দীন হীন অবস্থা। আপনি আমার মত করেন নি বলেই তো আপনি আজ জগদ্বিখ্যাত সম্রাট।’
কবি হাফিজের উপস্থিত চমৎকার উত্তরে তৈমুর লং খুশি হলেন। তিনি কবিকে সোনার আশরাফী উপহার দিয়ে বিদায় করলেন।
বিশ্বখ্যাত এই মহান কবি খাজা সামশুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী ৭৯১ হিজরী সালে শিরাজ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কবির মাজার শিরাজ নগরেই অবস্থিত। এখন এলাকাটি ‘হাফেজিয়া’ নামে প্রসিদ্ধ।
\r\n\r\n
হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)
ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সমস্ত ওলীয়ে কামেল ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছেন এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত উলূঘ খান জাহান(র.) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ মহান মনীষীর সাথে যে সমস্ত শিষ্যগণ ছিলেন তাঁরাও স্ব স্ব মহিমায় খ্যাতিমান হয়ে আছেন। কিন্তু এই বাংলার সন্তান একেবারে খাস বাঙালী কোন শিষ্য, হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.) এর মত যশস্বী হতে পারেন নি।
আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে মুহাম্মদ তাহির জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে নীলকান্ত বলেছেন-
‘পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইলো সর্বনাশ।’
তাঁর পূর্ব নাম ছিল গোবিন্দ ঠাকুর। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে খাট চোখে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘তাঁহার পূবে কি নাম ছিল জানিনা, জানিয়াও কোন কাজ নেই। এখন তাঁহার নাম তাহির।(যশোহর খুলনার ইতিহাস. ১ম খন্ড ৩৩৩ পৃষ্ঠা, শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র)। অবশ্য এ.এফ.এম. আবদুল জলীল সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, ‘বহুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিল গোবিন্দলাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি খান জাহানের বিশেষ প্রিয় পাত্র ও আমত্য ছিলেন।’(সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা-এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)। তিনি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী(র.) এর পরশে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রধান সহচরে পরিণত হন। হযরত উলুঘ খান জাহান আলীর এ দেশীয় শিষ্যদের মধ্যে হযরত পীর অলী মুহাম্মদ তাহিরই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জননন্দিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমারা পীরেলি নামে পরিচিত হন।
পীরেলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ. এফ. এম. আবদুল জলীল সাহেব লিখেছেন, ‘পয়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর অলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোহর অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ খান জাহানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করেন। তাঁহার নাম মুহাম্মদ তাহের। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। সতীশ বাবু তাহার সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়ো আত্মহিংসাই করিয়াছেন। কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ্য লাভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতি ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।’(সুন্দরবনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড ৩৩২, এ.এফ.এম আবদুল জলীল)। এ. এফ. এম. আবদুল জলীল অন্যত্র লিখেছেন-‘খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহি প্রাচীন হিন্দু প্রধান। সেনহাটি, মুলঘর কালিয়া প্রভৃতি স্থানের বহুপূর্বে এখানে উচ্চশ্রেণীর বসবাস ছিল। এই গ্রামের নাম ছিল পয়োগ্রাম, এখনও এ নাম আছে। এখানকার রায় চৌধুরী বংশের তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ তুর্ক আফগান আমলের প্রথম দিকে এ ব্রাহ্মণ বংশ রাজ সরকার হইতে সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহারা কনোজাগত ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ইহার গুড়ি বা গুড়গাঞী ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত। এই বংশের কৃতি সন্তান দক্ষিণা নারায়ণ ও নাগরা নাথ। কথিত আছে যে দক্ষিণা নারায়ণ দক্ষিণ ডিহি এবং নাগর উত্তর ডিহির সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।
দক্ষিণ ডিহি নামের সহিত দক্ষিণা নারায়ণের সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নাগর বেজের ডাঙ্গায় একটি হাট বসাইয়াছিলেন। উহার নাগরের হাট নামে পরিচিত ছিল। খান জাহানের আমলে চৌধুরীগণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন। নাগর নিঃসন্তান। ভ্রাতা দক্ষিণা নারায়ণের চারিপুত্র ছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব এই নবগত শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালিদের উৎপত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (সুন্দরবনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড ৩৩২, এ.এফ.এম আবদুল জলীল)।
এ সম্পর্কে মি. ওমালি বলেন, ‘খান জাহান একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ নিতে থাকেন। ইহাতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী মোহাম্মদ তাহের (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি) বলেন যে, ‘ঘ্রাণেন কার্ধ বোজনং’ অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধভোজন। খান জাহান পরে একদিন খানাপিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহার নাকে কাপড় দিলে খান জাহান বলেন, যখন ঘ্রাণে অর্ধভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তদনুসারে তাহের ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাহেরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি হিন্দু থাকিয়া যান। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দু পীরালি এবং তাহেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীরালি বলত। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এদেশে পীরালি গান এবং বহু কাহিনী রচিত হয়। ঐকান্তিক ধর্ম নিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহের পীরালি আখ্যা পান।”(সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৩/৩৩৪ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
অন্য এক বর্ণনা মতে “মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে জয়দেব ও কাবদেব এর অন্তরের মিল ছিল না। তাহের মনে মনে তাঁহাদিগকে মুসলমান করার চেষ্টা করিতেন। এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহা কতটুকু সত্য তাহা জানি না। গল্পটি বর্ণনা করিতেছি-একদিন রমজানের সময় তাহের রোজা রাখিয়াছেন। দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ বসিয়া আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার বাটি হইতে একটি সুগন্ধী নেবু আনিয়া তাহাকে উপহার দেন। পীরআলী নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময় কামদেব বলিলেন হুজুর, ঘ্রাণে অর্ধভোজন-আপনি গন্ধ শুকিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন? এ কথার পর পীরআলী ব্রাহ্মণের প্রতি চটিয়া যান। গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবেন। নির্ধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহের প্রাঙ্গনে গো-মাংসের সহিত নানারকম মশলা দিয়া রন্ধনকার্য্ ধুমধামের সহিত চলিল। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপুর। জয়দেব ও কামদেব নাকে কাপড় দিয়া প্রতিরোধ করিতেছিলেন। পীরআলী নাকে কাপড় কেন জিজ্ঞাসা করিলে কামদের মাংস রন্ধনের কথা উল্লেখ করেন। পীরআলী নেবুর গল্প উল্লেখ করিয়া বলেন-‘এখানে গো-মাংস রান্না হইতেছে। ইহাতে আপনার অর্ধেক ভোজন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি জাতিচ্যূত হইয়াছেন।’
অতঃপর জয়দেব ও কামদেব উক্ত মাংস খাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। পীরআলী তাঁহাদিগকে জামাল উদ্দীন, কামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়া আমত্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দু্ই ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীরালি ব্রাহ্মণ নামে সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহাই পীরালি সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিকথা।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৩/৩৩৪ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
এ প্রসঙ্গে জনৈক নীলকান্তের বরাত দিয়ে ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ গ্রন্থে ঘটকদিগের পুঁথি থেকে কিছু উল্লেখ করেছেন, তা হল-
খানজাহান মহামান পাতশা নফর।
যশোর সনন্দে লয়ে করিল সফর।।
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।।
পূর্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি।
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি।।
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ।।
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় হইল হাজির।।
এখানে লেখক খান জাহানকে কোন মুসলমান সুলতানের সনদ প্রাপ্ত প্রশাসক বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর মুহাম্মদ তাহিরের পরিচয় তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নয় বরং কোন নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলমান হয়েছে। প্রকারান্তরে লেখক(সম্ভবত) বলতে চেয়েছেন ইসলাম প্রচার এদেশে কৌশলে হয়েছে। পুঁথির অন্যত্র এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-
আঙ্গিনায় বসে আছে উজির তাহির।
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির।।
রোজার সে দিন পীর উপবাস ছিল।
হেনকালে একজন নেবু এনে দিল।।
গন্ধামোদে চারিদিক ভরপুর হইল।
বাহবা বাহবা বলে নাকেতে ধরিল।।
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন।
বসে ছিল সেইখানে বুদ্ধি বিচক্ষণ।।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।
ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে।।
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোহের মনে কৈলা স্থির।।
দিন পরে মজলিস করিল তাহির।
জয়দেব কামদেব হইল হাজির।।
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
শত শত বকরী আর গো-মাংস রন্ধন।।
পলান্ডু রশুন গন্ধে সভা ভরপুর।
সেই সভায় ছিল আরও ব্রাহ্মণ প্রচুর।।
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে বলে কত পালাইল।।
কামদেব জয়দেব করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন।।
জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।।
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি তো চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা।।
উপায় না ভাবিয়া দোহে প্রমাদ গণিল।
হিতে বিপরীত দেখি শরমে মরিল।।
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর।
থতমত খেয়ে দোহ হইল অস্থির।।
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
পীরালি হইল তাঁরা হইল জাতি ভ্রষ্ট।।
কামাল জামাল নাম হইল দোহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ে গেল হাহাকার।।
তখন ডাকিয়া দোহে আলী খানজাহান।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান।।
‘নবদীক্ষিত জামালউদ্দীন ও কামাল উদ্দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পাইয়া সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব খান জাহানের পয়গাম তৈরির পরেই হয়েছে। কথিত আছে খান জাহান তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বাগেরহাট অবস্থানকালে এই দুই ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে তথায় আসিতেন। বাগের হাটের পশ্চিমে সোনাতলা গ্রামে আজিও কামাল খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৬ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
ছল ছাতুরী বা কলা কৌশল নয় ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমানরা পীরেলি নামে পরিচিত হন। আর যে হিন্দু মুসলমান হতেন, তার হিন্দু আত্মীয়রা ঐ বংশের লোকদেরকে সমাজচ্যূত করত। তারা পীরেলি ব্রাহ্মণ বা পীরেলি কায়স্থ নামে পরিচিত হন। এই পীরেলিদেরকে কুলীণ ব্রাহ্মণরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতেন-
মোসলমানের গোস্ত ভাতে
জাত গেল তোর পথে পথে
ওরেও পীরেলী বামন।
জানা যায়, ‘পীরেলি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বহন করতো। তাই দেখতে পাই, কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিঙ্গিয়ার মুস্তফী পরিবার, দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী পরিবার, খুলনার পিঠাভোগের ঠাকুর পরিবার, এই পীরালিদের উত্তরাধিকার হিসাবে চিহ্নিত। কবি রবীন্দ্রনাথও এই পীরালি ঠাকুর পরিবারেই সন্তান।
সংশ্রব দোষে রায় চৌধুরী পরিবারের লোকেরা পুত্র কন্যার বিবাহ লইয়া বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা প্রতিপত্তি ও অর্থ বলে সমাজকে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে লাগিল। ইহাদের সহিত কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং আরও কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে পতিত হইয়াছিল। কলিকাতার ঠাকুরগণ ভট্টনারায়ণের সন্তান এবং কুশারী গাঁঞিভুক্ত ব্রাহ্মণ। খুলনা জেলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিল। পীঠাভোগের কুশারীগণ রায় চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পীরালি হন।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৭ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)। ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, ব্রাহ্মণ কান্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অংশের ১৭২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, ‘বর্তমান কালে খুলনা জেলার অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী মহাশয়েরা চেঙ্গুটিয়ার গুড় চৌধুরীগণের ন্যায় শক্তিশালী প্রবল শ্রোত্রিয় জমিদার ছিলেন। ইহারা শান্ডিল্য ভট্টনারায়ণ পুত্র দীন কুশারীর বংশধর। যে সময় শুকদেব রায় চৌধুরী বিশেষ বিখ্যাত জমিদার হইয়াছিলেন।ইনি পিঠাভোগের কুশারী বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত খানের কোন আত্মীয় হওয়াই সম্ভব।’(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কান্ড, তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ অংশের ১৭২ পৃ., নরেন্দ্রনাথ বসু)।
“কুশারী বংশের পঞ্চানন থেকেই পরবর্তীকালে কলকাতার বিখ্যাত জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।”(খুলনা জেলায় ইসলাম, মুহম্মদ আবু তালিব, পৃ. ৭১)।
অন্যদিকে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁকে অনেকেই পীরালী বংশোদ্ভুত মনে করেন। এ প্রসঙ্গে এ.এফ.এম. আবদুল জলীল বলেন, “মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এই পীরালী বংশের কৃতি সন্তান। তাঁহার আত্মীয় স্বজন পীরালি খাঁ বলিয়া পরিচিত। আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার বংশ পীরালি তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, গৌড়ের সুলতান যদু বা জালাল উদ্দীনের সময় হইতে তাঁহারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর। (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৭ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
এ বিষয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, “সমস্ত রায় চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিণত হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বংশ খান চৌধুরী নহে, শুধু খাঁ উপাধিধারী।”(সুন্দরবনের ইতিহাস, ৩৩৭ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
অন্যত্র এ.এফ.এম. আবদুল জলিল সাহেব লিখেছেন, ‘কলিকাতা এবং স্থানীয় সম্ভাব্য সমস্ত সূত্র হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিলাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর যেরূপ রক্তের সম্পর্ক, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সম্পর্ক ঠিক ততটুকু।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৮ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
“হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির পয়গ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। জানা যায়, পরে তিনি খলিফাতাবাদ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।”(হযরত খানজাহান আলী(র), পৃ. ৬-সেলিম আহমদ)।
প্রখ্যাত গবেষক জনাব অধ্যাপক আবূ তালিব বৈষ্ঞব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, “সত্যি বলতে কি, পীরালি আবু তাহিরই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বসূরী। আবূ তাহিরের আবির্ভাব যাদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, শ্রী চৈতন্য তাদেরকে বৈষ্ঞব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।(খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃ.-মুহাম্মদ আবূ তালিব)।
এরপরই তালিব সাহেব বলেছেন, “ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে পীরালী সাহেব শ্রীচৈতন্যের দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁরই পথের অনুসারী ছিলেন। আরও বলা যেতে পারে, নির্যাতিত হিন্দু পীরালী সমাজ একাধারে চৈতন্যের ধর্ম ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।(খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃ.-মুহাম্মদ আবূ তালিব)।
যা হোক পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় পয়গ্রাম কসবায়। “হযরত খানজাহান এই গ্রামটিকে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত রাজধানী শহর করার সুসংবাদ প্রদান করেন। এবং অবিলম্বে গ্রামটিকে একটি ‘কসবা’ বা শহরে পরিণত করেন। (খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৮ পৃ.-মুহাম্মদ আবূ তালিব)।
পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের জন্মস্থান হচ্ছে যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার(বর্তমানে জেলা) পেড়োলি গ্রামে। হযরত পীর আলী’র নামেই গ্রামটির নামকরণ হয় ‘পীরালী’। বর্তমানে নামটির বিকৃত রূপ হচ্ছে ‘পেড়োলি’।
হযরত পীর আলী’র নিকট এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ মুসলমান হন যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ আর ছিলনা বললেই চলে। এজন্য অন্যান্য হিন্দু ব্রাহ্মণগণ ভয় পেয়ে যান ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর স্বাক্ষ্য মেলে-
পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যবেত যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ জবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।।
কবি আরো বলেন-
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গায়েতে নবদ্বীপের হৈল সর্ববনাস।।
অথবা
“বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের আড়ে।
৮৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৪৫৯ সালে এ মহান কামেলে দ্বীন ও ইসলাম প্রচারক ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাজার বাগেরহাট হযরত উলূঘ খান জাহান আলীর(র) মাজারের পাশেই আছে। এ সম্বন্ধে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন, “মুহাম্মদ তাহির এখানে মারা যান নাই, এখানে মাত্র তাঁহার একটি শূন্যগর্ভ সমাধিবেদী গাঁথা রহিয়াছে।…..বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন রাখা কর্তব্য এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সেই একই জেলহ্জ্জ মাসে মুহাম্মদ তাহিরের জন্য এই স্মৃতি স্তম্ভ গঠিত করিয়া রাখিয়া যান। সমাধির উপরিভাগটি প্রায় খান জাহানে সমাধির ন্যায়, তবে ইহার ভিতরে কিছুই নাই, সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা যায়।” (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৮, সতীশ চন্দ্র মিত্র)। সতীশ বাবুর এই মন্তব্যের সহিত আমরা কোনভাবেই একমত হতে পারিনা। কবরের নীচে এ ধরনের সুড়ঙ্গের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রযেছে। তা’ছাড়া আমরা পূর্বেই তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেছি।
তাঁর শিলালিপিতে লেখা আছে, “হাজিহি রওজাতুন মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি ওয়া হাজিহি সাখরিয়া তুল লিহাবীবিহি এসমুহু মুহাম্মদ তাহির ছালাছা সিত্তিনা ওয়া সামানিয়াতা।” অর্থাৎ এই স্থান বেহেশতের বাগিচা সদৃশ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর মাযার, নাম-আবু তাহির, ওফাতকাল-৮৬৩ হি/১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। এই একই বৎসর হযরত খান জাহান (রঃ) এর ওফাত হয়।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি
\r\n\r\n
মহাকবি আলাওল
আমরা যাকে নিয়ে আজ আলোচনা করব তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি। আধুনিককালেও যাঁকে মহাকবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এইএই বহুভাষাবিদ পন্ডিত, অনুবাদক মহাকবি আলোচনার পূর্বে তাঁর যুগ সম্বন্ধে জেনে নিলে মনে হয় সবার জন্য সুবিধা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরাতন বলে মনে করা হয়। এই হাজার বছরকে পন্ডিতরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন-প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। ৬৫০ হতে ১২০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, ১২০১ হতে ১৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০১ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগ। অবশ্য হিন্দু পন্ডিতরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ১২০১ হতে ১৩৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ বলে থাকেন। কারণ এই দেড়শ বছর মুসলমানদের ভারত আগমন তথা বাংলাদেশ দখলের দরুণ কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে তারা মনে করে। অথচ সত্যি কথা হলো এই সময়েও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন শূন্য পূরাণ, কলিমা জালাল বা নিরঞ্জনের রুষ্মা, ডাক ও খনার বচন, সেক শুভোদয়া ইত্যাদি।
কবিগুরু মহাকবি আলাওল বা আলাউল এই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৫৯৭ খৃস্টাব্দে কারো কারো মতে ১৬০৫ বা ১৬০৭ খৃস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য দু’একজন পন্ডিত ব্যক্তি আলাওলের জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে বলে মনে করেন। কিন্তু কবির নিজের উক্তিকে সামনে রেখে প্রায় সকল পন্ডিতগণই ফরিদপুর জেলার জালালপুরের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কবির পিতা ছিলেন ফতেহাবাদের রাজ্যেশ্বর মজলিশ কুতুবের মন্ত্রী। কবি তাঁর পদ্মাবতী কাব্যে আত্মকথায় লিখেছেন—
মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তাহাতে জালাল পুর অতি পূণ্যস্থান।।
বহুগুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা।।
মজলিস কুতুব তখত অধিপতি।
মুই দীনহীন তান অমাত্য সন্তুতি।।
মহাকবি আলাওল ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত এক কবি। তিনি কৈশর বয়সে মন্ত্রী পিতার সাথে কার্যোপলক্ষে কোথাও যাত্রাকালে পথিমধ্যে দুর্ধর্ষ হার্মাদ জলদস্যূর কবলে পড়েন। কবির পিতা জলদস্যুদের হাতে শহীদ হন। কবি আহত হলেও প্রাণে রক্ষা পান। এরপর অনেক দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি আরাকানে এসে উপস্থিত হন। বেঁচে থাকার তাগিদে কবি মগরাজার সেনাবাহিনীতে রাজ-আসোয়ারের চাকরি গ্রহণ করেন। রাজ আসোয়ার মানে অশ্বারোহী সৈনিক। এ সময় আরাকান রাজসভায় একটি চমৎকার সাহিত্যিখ আবহাওয়া বিরাজ করছিল। গুণী ব্যক্তিদেরকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হত সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। কবি নিজেই লিখেছেন-
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পন্ডিত, গুণবন্ত।।
ফলে অচিরেই কবি আলাওলের গুণগরিমা, বিদ্যা বুদ্ধি ও সাহিত্য প্রতিভার কথা অভিজাত মহলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। কবি বলেন,
তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরেরে।
অন্নবস্ত্র দিয়ে সবে পোষন্ত আদরে।।
মূলত এখান থেকেই আলাওলের কাব্য সাধানার শুরু এবং এক আমত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ক্রমাগত ১৬৫১ খৃ. হতে ১৬৭৩ খৃ. পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মাঝে কবির উপর বয়ে যায় অনেক ঝড়ঝঞ্জা। কবিকে অনেক কষ্ট ক্লেশে নিপতিত হতে হয়। ১৬৫৯ খৃ. শাহসূজা বাংলাদেশ হতে বিতাড়িত হয়ে আরাকান রাজ্যে আশ্রয় লাভ করেন। যে কোন কারণেই হোক ১৬৯১ খৃ. তিনি আরাকান রাজ্যের বিরাগভাজন হয়ে নিহত হন। এ সময়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কবি আলাওল কারারুদ্ধ হন। পঞ্চাশ দিন কারাভোগের পর কবি মুক্তি পান। কিন্তু প্রতিকুল পরিবেশে সবাই কবির বিরুদ্ধে চলে যায়, ফলে তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ঠিক এ সময়ে কবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবির দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায়। এমনকি এ সময় তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রোসাঙ্গ রাজসভার আমত্য সৈয়দ মূসা, সমরসচিব সৈয়দ মুহাম্মদ খান, রাজমন্ত্রী নবরাজ মজলিশ, অন্যতম সচিব শ্রীমন্ত সোলেমান প্রমুখদের নজরে আসেন। ফলে পুনরায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।
তোমরা জানলে খুশি হবে যে, সেই যুগেও মহাকবি আলাওলের জানা ছিল অনেকগুলি ভাষা। তিনি মৈথিল, ব্রজভাখা, ঠেট, খাড়িবোলির মত উত্তর ভারতের উপভাষা ছাড়াও বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে সমান দখল রাখতেন। অপর দিকে তাসাউফ ও যোগতন্ত্রেও ছিল পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান। যার কারণে তিনি অনুবাদে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সত্যি কথা বলতে তাঁর মত অনুবাদক কদাচিৎ দু/একজন মিলে। তিনি কাব্য ক্ষেত্রে ছিলেন স্বচ্ছন্দ্য। কাব্যতত্ত্ব, অলংকার শাস্ত্র ও ছন্দবিজ্ঞান ছিল তাঁর আয়ত্ত্বে। এমনকি তিনি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলায় প্রয়োগ করেন। তার রোসাঙ্গে তিনি তো সঙ্গীত শিক্ষক রূপেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
আলাওল অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে-
১. পদ্মাবতীঃ প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিম মুহাম্মদ জায়সী ‘পদুমাবত’ কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ১৬৫১ খৃস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল ‘পদ্মাবতী’ অনুবাদ করেন। এ কাব্যটি আলাওলের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।
২. সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামানঃ আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের পরামর্শে ও উৎসাহে এ কাব্য লেখা শুরু করেন এবং পরে ১৬৬৯ খৃস্টাব্দে রোসাঙ্গ রাজের আমত্য সৈয়দ মূসার অনুরোধক্রমে তা সমাপ্ত করেন। এটি প্রেম মূলক কাহিনী কাব্য।
৩. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানীঃ দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য আমত্য সুলায়মানের অনুরোধে ও উৎসাহে ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি আলাওলের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।
৪. সপ্তপয়কারঃ পারস্য কবি নিজামীর সপ্তপয়কর নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। রোসাঙ্গরাজের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহাম্মদের আদেশে ১৬৬০ খৃস্টাব্দে আলাওল এটির অনুবাদ করেন।
৫. তোহফাঃ এ গ্রন্থটিও অনুবাদ। বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর ‘তোহফাতুন নেসায়েহ’ নামক ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে আলাওল এ কাব্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। এটি আলাওলের পঞ্চম রচনা।
৬. সেকান্দর নামাঃ এ ষষ্ঠ নম্বর কাব্যটি নিজামী গঞ্জভীর ফারসী সেকান্দর নামা গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল এ কাব্যটি সম্ভবত ১৬৭২ খৃস্টাব্দে রচনা করেন। আরাকান রাজ চন্দ্র সুর্ধমার নবরাজ উপাধীধারী মজলিস নামক জনৈক আমত্যের অনুরোধে আলাওল সেকান্দরনামা অনুবাদ করেন।
সঙ্গীতবিদ হিসেবেও আলাওলের প্রচুর খ্যাতি ছিল। তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বেশ কিছু গীতও রচনা করেছেন। অপরদিকে তিনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ঞবপদও রচনা করেছেন।
কবি ‘মুকীম’ তার সম্বন্ধে লিখেছেন-
গৌরবাসী রৈল আমি রোসাঙ্গের ধাম
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম।
যদিও কবি আলাওলের রচনা অনুবাদ প্রধান তবুও তার অনুবাদ মৌলিক রচনার সমপর্যায়ের। এই অসাধারণ প্রতিভাবান কবি, মহাকবি আলাওল আনুমানিক ৭৬ বছর বয়সে ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।
\r\n\r\n
শাহসূফী মুজাদ্দিদে যামান আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.)
চৌদ্দশতকে উপমহাদেশে যে সমস্ত পীরে কামেলের পরিচয় আমরা পাই, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সময়ে ভারত উপমহাদেশে এত ব্যাপকভাবে গৃহীত আর কোন ব্যক্তি হতে পারেন নি। যার কারণে তিনি উভয় বাংলায় মুসলমানতো বটেই হিন্দুদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। সত্যি কথা বলতে কি এখনো পর্যন্ত তাঁর মুরীদগণ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এই সূফী শ্রেষ্ঠ ও ইসলাম প্রচারক আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরায় ১২৫৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যেটা বর্তমানে ফুরফুরা শরীফ নামে পরিচিত। জন্মের মাত্র ৯ মাস পর তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোলাম মুকতাদীর। মাতা মুহব্বতুন্নিসা এতিম পুত্র আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) কে লালন পালন করেন এবং তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।
হযরত আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। প্রথমে সিতাপুর মাদরাসা, পরবর্তীতে হুগলী মুহসিনিয়া মাদরাসায় পড়ালেখা করেন। কৃতিত্বের সাথে তিনি মুহসিনিয়া মাদরাসা থেকে তদানীন্তন মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী জামাতে উলা পাশ করেন। পরে কলকাতা সিন্ধুরিয়া পট্টির মসজিদে হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ অধ্যয়ন করেন। মাওলনা বিলায়েত (রহ.) এর নিকট কলকাতা নাখোদা মসজিদে তিনি মানতিক হিকমা প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মদীনা শরীফে যান। সেখানে তিনি হাদীস ও হাদীস সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে তিনি একনাগাড়ে ১৮ বছর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। এমনকি নিরলস অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃত পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং কুতুবুল ইরশাদ হযরত ফতেহ আলী(রহ.) এর নিকট বয়’আত হয়ে ইলমে তাসাওফের সকল তরীকার পূর্ণ কামিলিয়াত হাসিল করেন এবং খিলাফত লাভ করেন।
তিনি শরীয়তের একান্ত পাবন্দ একজন পীরে কামিল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শরীয়ত ব্যতীত মারিফত হয় না। এজন্যই বাংলা, আসামে তাঁর অগণিত মুরীদও একই পন্থা অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, শুধু পীরের সন্তান হলেই পীর হওয়া যায় না। তিনি যে বংশের হউন না কেন যদি শরীয়ত মারিফত ইত্যাদিতে কামিল হন তবে তিনিই পীর হতে পারেন।
হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রহ.) ছিলেন একজন সুবক্তা। যার কারণে তিনি বাংলা আসামের গ্রামে গ্রামে প্রতিটি অলিগলিতে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতে পেরেছিলেন। তিনি ক্ষেত্র বিশেষে কলমও ধরেছেন। তাঁর লেখা কাওলুল হক(উর্দূ) এবং অছীয়ৎনামা(বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় তিনি আল-আদিররাতুল-মুহাম্মদিয়া নামে আরবীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেটি অপ্রকাশিত।
শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টা এবং সহযোগিতায় অসংখ্য মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা পোষণ করতো তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য এদেশের মুসলমানদের প্রতি জোর আহবান জানান। তিনি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদরাসার পাঠ্য তালিকার সংস্কারের জন্য দাবী জানান। তিনি পর্দার সাথে নারীদের শিক্ষা জরুরী বলেও মত প্রকাশ করেন। এমনকি নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যও তিনি উপদেশ দেন। একটি তথ্য অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপন করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার যে প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয় তিনি তার সদস্য নির্বাচিত হন।
তিনি ইসলামী সমাজ হতে শিরক বিদআত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্য ১৯১১ সালে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ‘আঞ্জুমানে ওয়াজীন’ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কাজ ছিল মুসলিম সমাজ হতে কুসংস্কার দূর করার জন্য ওয়াজের ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের জবাব দেওয়া এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা।
তিনি যমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর বাংলা আসামের সভাপতিও ছিলেন। এ সময়ে তিনি আযাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, “রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে আলেমদিগকে সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কাজ হইতেছে।” পরে ‘জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলা আসাম’ গঠন করেন।
১৯৩৮ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরিদান ও সাধারণ মুসলমানদের মুসলিম লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহবান জানান।
তিনি তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত মুসলমানদের পত্র-পত্রিকাগুলোকেও সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশ হয় তা হল-সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকর, মাসিক নবনূর, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক সোলতান, সাপ্তাহিক মুসলিম হিতৈষী, মাসিক ইসলাম দর্শন, সাপ্তাহিক হানাফী, মাসিক শরিয়তে ইসলাম প্র্রভৃতি।
বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর নকীব, সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, মুজাদ্দিদ, অলিয়ে কামিল এদেশের মুসলমানদের নয়নের মণি হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর ১৩৪৫ বাংলা সনের ৩ চৈত্র মোতাবিক ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরা শরীফের মিয়া পাড়া মহল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ এখানে এছালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর খলীফাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-মওলনা রুহুল আমীন, শর্ষিণার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন, মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী(যশোর), মওলানা আবদুল খালেক, মওলানা সদরুদ্দীন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা হাতেম আলী, দ্বারিয়াপুরের পীর মওলানা শাহ সূফী তোয়াজউদ্দীন আহমদ(রহ.) প্রমুখ।
\r\n\r\n
হযরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ.)
সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ) এক চির উজ্জ্বল নক্ষত্র। যখন দক্ষিণ বঙ্গের অলিতে গলিতে চলছিলো হিন্দু ও খৃস্টান মিশনারীদের অপদৌরাত্ম, যখন ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অপপ্রচারের ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করেছিলো তখনই এই মহান সূফী ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেন।
মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীমের(রহ.) পূর্বপুরুষ ছিলেন-হযরত শাহসূফী সুলতান আহমদ। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সময় যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। জানা যায়, সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি যশোর আগমন করেন এবং যশোর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর থেকে যান। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজা ছিলেন শূকদেব সিংহ রায়।
রাজা শূক দেব সিংহ রায় রাজা মানসিংহকে এবং সম্রাট আকবরকে খুশী করার উদ্দেশ্যে শাহ সূফী সুলতান আহমদকে বসবাসের জন্য রাজবাড়ীর খিড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী এলাকা পরে খড়কী এলাকায় পরিণত হয়। বর্তমানে খড়কী যশোর এলাকার একটি অংশ। যশোর সরকারী এম.এম. কলেজ এই খড়কীতে অবস্থিত।
মুগল আমল থেকে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত মওলানা শাহ আবদুল করীম সাহেবের বংশের লোকেরা যশোর অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে আসছেন।
যশোর শহরতলীস্থ খড়কী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারে হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীম ১৮৫২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ সালীম উদ্দীন চিশতী একজন কামিল পীর ছিলেন।
শাহ আবদুল করীম বাল্যকালেই পিতৃহারা হন এবং দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী(রহ)এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।
দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী দীনি ইলমের প্রাথমিক সবক দিয়ে তাঁর হাতেখড়ি দেন। পরে স্থানীয় বিদ্যালয় হতে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি দাদাকে হারান। দাদাকে হারিয়েও শাহ আবদুল করীম তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন নি। তিনি পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে জামা’আতে উলা পাস করেন।
শিক্ষা জীবন শেষে এই মহান মণীষী যশোর জেলা স্কুলে হেড মৌলবী হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন।
শিক্ষকতা করা অবস্থায় তাঁর ভেতর ‘ইলমে তাসাওউফ’ সম্বন্ধে জানার কৌতুহল জাগে এবং সে সম্বন্ধে জানার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েন। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার খালিক(রহ.) এর নিকট মুরীদ হন। এখানে দীর্ঘ বার বছর তিনি তাসাওউফ চর্চায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন এবং ইলমে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পীর তাঁকে নকশ বন্দীয়া মুজাদ্দীদিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া এবং সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার খিলাফত প্রদান করে স্বদেশ ইসলাম প্রচারের নির্দেশ হন।
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং সমাজে কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টা চালান। এ সময় অনেক বিধর্মীই তাঁর সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।
ব্যক্তিগত জীবনে শাহ আবদুল করীম অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে চলাফেরা করতেন। পিতার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি আড়ম্বরহীন, বিনয়ী ও নম্র জীবন যাপন করেছিলেন।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক সময় যশোর জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি এই সময় শাহ আবদুল করীমের একান্ত সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর লেখা আধ্যত্ম পুণ্যময় লকখী ছাড়া গল্পটি পীর আবদুল করীম সাহেবকে লক্ষ্য করে (রমনার পীর সাহেব) লেখা। গল্পের নায়ক রমজানকে ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের সমকালীন প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।
শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম একজন উচ্চস্তরের সাহিত্যিকও ছিলেন। ইলমে তাসাওউফের ওপর তিনি এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব নামক প্রায় তিন’শ পৃষ্ঠা একখানি পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব লিখেছেন, “বইখানি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, এ যাবত বাংলা ভাষায় সূফী বা তাসাউফ তত্ত্বমূলক যত বই লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এ খানি শ্রেষ্ঠ। আবদুল করীম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে একজন নিষ্ঠাবান সূফী, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জ্ঞানে এই রঙিন বইখানি সাধারণ পাঠকের জন্য এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে।
সুবিস্তৃত দশটি অধ্যায়ে তিনি তাসাওউফের দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ সূফী-খান্দানের ইতিকথা, শাজরানামা(পীর-পরম্পরা) ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। শেষ বা দশম অধ্যায়ে তিনি তাসাউফ তত্ত্বের মর্মকথা, অমুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি, যথা-বেদ উপনিষদ পুরানাদির সঙ্গে ইসলামী সূফীতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন।”
শাহ আবদুল করীম সাহেব গ্রন্থটি রচনা করেছেন তাঁর পীর হযরত খাজা আবু সা‘আদ মোহাম্মদ আবুদল খালেক সাহেব এর অনুপ্রেরণায়।
এ সম্বন্ধে শাহ আবদুল করীম সাহেব উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, “পীর সাহেব বলেছেন, তুমি নিজ ভাষায় স্পষ্টভাবে যেমত আমার শিক্ষা পাইয়াছ সেইরূপ একখন্ড কিতাব লিখ। যাহা বুঝিতে লোকের কষ্ট না হয় এবং সন্দেহ ভঞ্জন হয়। কারণ তাসাউফের বিদ্যা ক্রমশ লোপ পাইয়া যাইতেছে; কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞেস করিলে স্পষ্টভাবে তাহার উত্তর পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে; সুতরাং লোকের মূল উদ্দেশ্য পরম সৃষ্টিকর্তা খোদাতালাকে চেনার পথ একেবারে সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি সত্ত্বর কিতাব লিখিতে প্রবৃত্ত হও।”
পীরের নির্দেশ মোতাবিক লেখক তাঁর কিতাবখানি সর্বসাধারণ বোধ্য ভাষায় লিখেছেন। বলাবাহুল্য, ইসলামী চিন্তাধারার এক মৌলিক উৎসের সন্ধান দিয়েছে কিতাবখানি।
গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব শাহাদাত আলী আনসারী বলেন, ‘মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীম সাহেব নকশবন্দীয়া তরীকার একজন কামেল সূফী ছিলেন। সূফী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর গ্রন্থখানিতে প্রথম হতে চতূর্থ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি তাসাওফের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; পঞ্চম হতে নবম অধ্যায়ে সূফী সাধনায় কাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া এবং চিশতীয়া তরিকার বিশ্লেষণ করেছেন এবং দশম হতে শেষ অধ্যায়ে বেদ, পুরান প্রভৃতিতে প্রচলিত বিষয়বস্তুর তত্ত্ব তিনি উদঘাটন করেছেন এবং সূফী মতবাদের সাথে তার তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। তাসাওফ সম্পর্কে বাংলাভাষায় লিখিত এইরূপ দ্বিতীয় কোন বই পাওয়া যায় না।”
শাহ আবদুল করীম(রহ.) এর জীবদ্দশায় গ্রন্থটির দু’টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর। প্রকাশক ছিলেন মুনশী শেখ জমির উদ্দীন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে শাহ সাহেবের পুত্রদ্বয়(শাহ মুহাম্মদ আবু নাঈম এবং শাহ মুহাম্মদ আবুল খায়ের) লিখেছেন, “পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক রেভারেন্ড মওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবকে অত্র সংস্করণ দান করিলাম। টাইটেল পেজে কেবলমাত্র প্রকাশকের স্থানে তাঁহার নাম থাকিবে।”
গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ ৪০ বছর পর প্রখ্যাত সমাজসেবক ও সাহিত্যিক মরহুম মৌলভী ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৩৫৬ সালে এর চতূর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে ভূমিকা লেখেন শাহ সাহেবের পুত্র জনাব শাহ মুহাম্মদ আবুল খায়ের। পরবর্তীতে ১৩৮১ সালে তাঁর পৌত্র শাহ মোহাম্মদ আবদুল মতিন বইটির পঞ্চম সংস্করণ বের করেন। এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ বের হয়েছে ৩০ শে মার্চ ১৯৮৬। এ সংস্করণের প্রকাশক শাহ মোহাম্মদ আবুদল মতিন। তিনি বর্তমানে খড়কীর গদ্দীনশীন পীর।
এরশাদে খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব নামক তাসাওউফের উপর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত বিস্তারিত ও তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলেছেন “মোহাম্মদ আবুদল করীরেম খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব সম্পর্কে বাংলায় তাসাওউফ সম্পর্কিত বই আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।” বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, “প্রকৃতপক্ষে এ পুস্তকখানা সাধনার পথিকদের জন্য একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ.) আমাদের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।”
শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ.) ১৩২২ বাংলা সনের ৩০ অগ্রহায়ণ খড়কীস্থ নিজ খানকা শরীফে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। প্রতিদিন বহু যিয়ারতকারী আসেন। তাঁর নামে যশোর শহরে ‘শাহ আবদুল করীম সড়ক’ রয়েছে। তাঁর বংশধররা আজও ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। খড়কীর বর্তমান পীর হযরত মাওলানা শাহ আবদুল মতিন শাহ আবদুল করীমের পৌত্র।
\r\n\r\n
মহাকবি কায়কোবাদ
কে ঐ শোনাল মোরে
আজানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ
নাচিল ধমনী
কি মধুর
আজানের ধ্বনি।
যদি তোমাদেরকে এখন প্রশ্ন করি এ কবিতাটি কার লিখা তোমরা নিশ্চয় এক বাক্যে বলবে কবি কায়কোবাদের। হ্যাঁ কবি কায়কোবাদের ‘আজান’ কবিতার প্রথম স্তবক এটি। তিনি মহাকবি কায়কোবাদ নামেই সবার কাছে পরিচিত। আসলে তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। জানা যায়, হাফিজ উল্লাহ আল কোরেশী নামে তাঁর জনৈক পূর্ব পুরুষ বাদশাহ শাহাজানের সময়ে বাগদাদ নগরীর নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে দিল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। হাফিজ উল্লাহ আল কোরেশী ছিলেন আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত। যে কারণে তিনি সহজেই বাদশাহ শাহজাহানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বাদশাহ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে দিল্লী জামে মসজিদের সহকারী ইমামের পদে তাঁকে নিয়োগ দেন। এই হাফিজ উল্লাহ আল কোরেশীর প্রপৌত্র মাহবুব উল্লাহ আল কোরেশী দিল্লী হতে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং ফরিদপুর জেলার গোড়াইল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আমাদের আলোচ্য কবি এই মাহবুব উল্লাহ আল কোরেশীর প্রপৌত্র। তাঁর দাদার নাম নেয়ামত উল্লাহ আল কোরেশী এবং আব্বার নাম শাহমত উল্লাহ আল কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী।
মহাকবি কায়কোবাদ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম জরিফউন্নেছা খাতুন। কায়কোবাদ ছিলেন বাবা মায়ের প্রথম পুত্র। তাঁর অন্য দু’জন ভাই হলেক আবদুল খালেক ও আবদুল বারী যারা যথাক্রমে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের সার্জন ছিলেন।
কায়কোবাদের লেখাপড়া শুরু হয় পিতা শাহমত উল্লাহর কর্মস্থল ঢাকাতে। তিনি ঢাকার পগোজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অবশ্য ১১ বছর বয়সে মা এবং ১২ বছর বয়সে আব্বা মারা যাওয়ায় ইয়াতিম কবি নানাবাড়ি আগলাপাড়া গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে এক বছর সময় কাটান। পরে তিনি পুনরায় ঢাকাতে ফিরে এসে ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ সময়ে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর পিতা মওলবী ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী। অপরদিকে কবির সহপাঠী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা জাস্টিস জাহিদ সোহরাওয়ার্দী। ঢাকা মাদ্রাসায় কায়কোবাদ এন্ট্রাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। মাদ্রাসার শিক্ষা জীবন শেষ হলে তিনি ১৮৮৭ সালে ডাক বিভাগে চাকুরি নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৯ সালে চাকুরী জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ছাত্র জীবনেই তার ‘কুসুম কানন’ ও ‘বিরহ গোলাপ’ নামে দুটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
আনন্দের কথা হলো, এ কাব্য গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হলে তা পড়ে কাশিম বাজারের মহারাণী দশ টাকা এবং কাশীর ভূবন মোহিনী চতুর্ধারিণী পাঁচ টাকা পাঠিয়ে কিশোর কবি কায়কোবাদকে বরণ করে নেন। ঘটনাটি ছিল নিঃসন্দেহে কবির জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যাপার।
কর্মজীবনে প্রবেশ করার আগেই তিনি অভিভাবকদের মতানুযায়ী মামা হেদায়াত আলী সাহেবের বড় মেয়ে তাহেরউন্নেছা খাতুনকে বিয়ে করেন।
১৩০২ বঙ্গাব্দে ঢাকা হতে সৈয়দ এমদাদ আলীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় ‘অশ্রু মালা’ খন্ড কাব্যগ্রন্থটি। এ সময়ে কবি ময়মনসিংহের জামুরকী পোস্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন। অশ্রুমালা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই কায়কোবাদের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ঐ সময়কার সেরা কবি নবীনচন্দ্র সেন আলিপুর হতে কবিকে লিখে পাঠান-
‘মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারে, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাংলা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে।”
১৩১১ বাংলা সনে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি ‘মহাশ্মশান’ মহাকাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ মহাকাব্য। বাংলা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও ফররুখ আহমদ মহাকাব্য রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কায়কোবাদই মহাকাব্য রচনা করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে এ মহাকাব্য রচিত। তিনখন্ডে বিভক্ত ৮৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এ মহাকাব্য রচনায় দীর্ঘ দশ বছর সময় লেগেছিল।
এ মহাকাব্য সম্বন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, “মহাশ্মশান কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একটি উজ্জ্বল রত্ন। মহাশ্মশানের ন্যায় বৃহদাকার কাব্য বোধহয় বঙ্গ সাহিত্যে আর নেই।”
এই কাব্যের মাধ্যমে কবি মুসলমানদের জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন-
“পড়ে নাকি মনে সেই অতীত গৌরব?
সুদূর আরব ভূমে যে বীর জাতি
মধ্যাহ্ন মার্তন্ড প্রায় প্রচন্ড বিক্রমে
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে
আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
বিসর্জিয়া আত্মপ্রাণ কেমন বিক্রমে
স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য ‘আল্লা’ ‘আল্লা’ রবে
আজিও ধ্বনিত সেই নীলনদ তীরে।”
১৩২৮ বংগাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘বিশ্বমন্দির’ কাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভাওয়াল এলাকার মুসলমান জমিদার নুরুউদ্দিন হায়দারের একমাত্র পুত্র আলাউদ্দীন হায়দরকে তারই দেওয়ান সুধীর চন্দ্র জমিদারীর লোভে কূপে ফেলে হত্যা করে এবং এই কূপের উপর নির্মাণ করে শিবমন্দির। এই দুঃখজনক ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বিশ্বমন্দির কাব্য।
১ ফাল্গুন ১৩২৯ বংগাব্দে প্রকাশিত হয় ‘অমিয় ধারা’ খন্ড কাব্য। এ কাব্যে অনেকগুলি কবিতা রয়েছে। তবে কাব্যের প্রথম কবিতা ‘আজান’ খুবই জনপ্রিয় একটি কবিতা। যার প্রথম স্তবক আজকের লেখার শুরুতেই উল্লেখ করছি।
১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় কায়কোবাদের আরেকখানি মহাকাব্য ‘মহরম শরীফ’। কারবালার যুদ্ধের কারণ ও ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এ কাব্যে। ৩ খন্ডে সমাপ্ত এ কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা ‘শ্মশান ভস্ম’ কাব্য উপন্যাসখানি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কায়কোবাদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় –প্রেম পারিজাত, প্রেমের ফুল, প্রেমের রাণী, মন্দাকিণী ধারা প্রভৃতি কাব্য।
২ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খৃস্টাব্দে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কায়কোবাদকে ‘কাব্যভূষণ’, ‘বিদ্যাভূষণ’ ও ‘সাহিত্য রত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে ‘মাইকেল দি সেকেন্ড’ ও বলা হতো।
কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করার জন্য কায়কোবাদ কলকাতাও গিয়েছিলেন। কাজী সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি কায়কোবাদের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলেছিলেন, ‘ইনিই মহাকবি কায়কোবাদ, মহাশ্মশান অমর কাব্যের স্রষ্টা-আমাদের অগ্রপথিক।’ এ ঘটনা হতেই বুঝা যায় কায়কোবাদ কত বড় কবি ছিলেন।
ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্ত্বে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে কায়কোবাদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী কায়কোবাদকে সম্মাননা হিসেবে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেয়ার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণে তা আর দেওয়া হয় নি।
ব্রঙ্কো নিউমেনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২১ জুলাই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।
\r\n\r\n
মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা
ঘাস, লতা, ফুল, পাখি দিয়ে ঘেরা একটি জেলা। সমস্ত জায়গায় প্রায় সমতল। সাইক্লোন, বন্যা, ঝড় কোন কিছুই সেখানে তেমন একটা আঘাত হানে না। অধিবাসীদের ভেতর শান্ত সৌম্যভাব। সবাই যেন কবি। কথায় কথায় কাব্য ঝড়ে পড়ে। এমনিতেই তাদের কথাগুলি দারুণ মিষ্টি। সেই জেলাটির নাম যশোর। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জেলা অর্থাৎ প্রথম জেলা। ১৭৮৬ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই যশোরকে জেলা ঘোষণা করে। তারও আগে যশোর স্বাধীন রাজ্য ছিল। তখন নাম ছিল যশোর রাজ্য বা যশোরাদ্য দেশ। এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায়, রাজা মুকুট রায়, হযরত বড়খান গাজী, হযরত খান জাহান আলীর মত ব্যক্তিত্বরা। অবশ্য যশোর কবি সাহিত্যিকদের দেশ হিসাবে আবহমান কাল ধরে সকলের নিকট পরিচিত। সেই রূপ সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী হতে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, ডাঃ লুৎফর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. এম. সমশের আলী, সৈয়দ আলী আশরাফ পর্যন্ত সবাই এ জেলারই সুসন্তান। এজন্য যশোরকে কবি সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্র বলা হয়। আজ আমরা সেই যশোরেরই এক কৃতি সন্তান যিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও সংগ্রামী তাঁর কথা বলবো, তাঁর নাম মুনসী মেহেরউল্লা।
মুনসী মেহেরউল্লা ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার(বর্তমানে জেলা)অন্তর্গত কালিগঞ্জ থানার ঘোপ গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ঘোপ গ্রামটি ঐতিহাসিক বারবাজার সংলগ্ন। এই বারবাজার হতেই সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামের সুমহান বাণী প্রথম প্রচার করেন হযরত বড়খান গাজী(গাজী কালু চম্পাবতী)। এরপর যে মহান মনীষীর আগমনে বারবাজার ধন্য হয় তিনি হযরত খানজাহান আলী। তার বারো জন শিষ্যের নাম অনুসা্রেই এই স্থানের নাম হয়েছে বারবাজার। এখান থেকেই তিনি বাগেরহাট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মেহেরউল্লার পৈতৃকবাড়ি চুরামনকাটী(বর্তমানে মেহেরউল্লাহ নগর) সংলগ্ন ছাতিয়ানতলা গ্রামে। তাঁর আব্বা মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ারেছ উদ্দীন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন।
অল্পবয়সেই পিতৃহারা হওয়ার কারণে মুন্সী মেহেরউল্লাহ লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেন নি। তাই মায়ের তত্ত্বাবধানে ও নিজের চেষ্টায় তাঁর লেখাপড়া চলতে থাকে। কৈশোর বয়সে তিনি মৌলভী মেসবাহউদ্দীনের কাছে তিন বছর এবং পরে করচিয়া গ্রামের মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কাছে আরো তিন বছর আরবী, ঊর্দূ, ফারসী ভাষা ও সাহিত্য শিখেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কোরআন ও হাদীসে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করেন এবং শেখ সাদীর গুলিস্তা, বোস্তা ও পান্দেনামা মুখস্ত করেন।
কর্মজীবনের শুরুতে তিনি যশোর জেলা বোর্ডে একটি চাকুরি পান কিন্তু স্বাধীন মনোভাবের কারণে সে চাকুরী ছেড়ে দর্জির কাজ শুরু করেন। দর্জির কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন ও সাফল্য লাভ করেন। সেই সূত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর খরিদ্দার ছিলেন এবং তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে দোকান করে দেন।
যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল দড়াটানায় দর্জির দোকানে কাজ করতে করতে মুন্সী মেহেরউল্লাহ দেখতেন খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ। মিশনারীদের ভয়ভীতি ও প্রলোভনের ফলে প্রচুর নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান খৃস্টান ধর্মের দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছিল। কোনও রাজনৈতিক নেতাকে এগিয়ে আসতে না দেখে এর বিরুদ্ধে তরুণ দর্জি মুন্সী মেহেরউল্লাহ গর্জে উঠলেন সিংহের মত।
দার্জিলিং অবস্থানকালে তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি তোফাজ্জল মুকতাদী নামক একটি ঊর্দূগ্রন্থ হতে বিভিন্ন ধর্মের ত্রুটি বিচ্যূতিগুলি জেনে নিলেন। তাছাড়া হযরত সোলায়মান ওয়ার্সীর লেখা ‘কেন আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম’, ‘প্রকৃত সত্য কোথায়’ বই দুটি তার জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিল।
তিনি দার্জিলিং হতে ফিরে এলেন যশোরে। খৃস্টানদের মতই তিনি দড়াটানা মোড় হতে বাংলা আসাম ও ত্রিপুরার অলিতে গলিতে সভা সমাবেশ করে খৃস্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এ প্রচারকে বেগবান করার জন্য কোলকাতার নাখোদা মসজিদে বসে মুনসী শেখ আবদুর রহীম ও মুনসী রিয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গঠন করলেন নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি। সমিতির পক্ষ হতে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয় মুনসী মেহেরউল্লা ওপর।
মুনসী মেহেরউল্লার জ্বালাময়ী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে স্থান নিতে লাগল। যাদের মনে ঘুণ ধরেছিল তারা আবার মনটাকে ঠিক করে নিল। জনমিরুদ্দীনের মত তুখোড় খৃস্টানও কলেমা পড়ে পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলেন।
তিনি যে শুধু বক্তৃতা দিতে পারতেন তা নয়, তাঁর কলমের ধারও ছিল দু’ধারী তলোয়ারের মত। জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ খৃস্টাব্দে খৃস্টান বান্ধব পত্রিকায় ‘আসল কোরআন কোথায়’ শিরোনামে একটি উদ্ধত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। এতে জন সাহেব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আসল কোরআন কোথাও নেই। এহেন অযৌক্তিক প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন মুনসী মেহেরউল্লাহ ‘সুধাকর’ পত্রিকায় ‘ইসায়ী বা খৃস্টানী ধোকা ভঞ্জন’ শিরোনামের এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে। এরপর জন জমিরুদ্দীন সুধাকরে অপর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেন। উত্তরে মেহেরউল্লাহ ‘আসল কোরআন সর্বত্র’ শিরোনামের সুধাকরে অন্য একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী অঘোরনাথ বিশ্বাস, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার প্রমুখ খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণ মুনসী মেহেরউল্লার সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
মুনসী মেহেরউল্লা শুধু খৃস্টানদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেন নি, তিনি মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার দেখেছেন তার বিরুদ্ধেও ছিলেন খড়গহস্ত। এ সম্বন্ধে শেথ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর ‘কর্মবীর মুনসী মেহেরউল্লা’ গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “মুনসী মেহেরউল্লার নানা দিক দিয়ে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। তিনি বলতেন, মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে কিন্তু তৈয়ারী করিতে জানে না। পান খাইতে অজস্র পয়সা নষ্ট করে কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করেন। মুনসী মেহেরউল্লা সাহেব মুসলমানগণের মিঠাইয়ের দোকান করিতে, পানের বরজ তৈয়ার করিতে সর্বস্থানে উৎসাহ দিতেন, তাঁহার চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবতী হইয়াছিল।”
মুনসী মেহেরউল্লা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা রাখেন। তিনি নিজেই ১৯০১ সালে নিজ গ্রামের পাশের গ্রাম মনোহরপুরে মাদরাসায়ে কারামাতিয়া নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যেটা বর্তমানে মুনসী মেহেরউল্লা একাডেমী। তিনি বাংলা আসামের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি মুসলিম সমাজকে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।
আমরা এখন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর জন্য বক্তৃতা বিবৃতি দিই, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করে ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস উদযাপন করি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এরও অনেক আগে অল্প শিক্ষিত মুনসী মেহেরউল্লা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা কি তা হাড়ে হাড়ে বুঝে ছিলেন। যারা মাতৃভাষাকে ছোট করে দেখতো তাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, “মাতৃভাষা বাংলায় লেখাপড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম যে কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহার শরীর পরিপুষ্ঠ সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারা যে কি সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।”
উপস্থিত বুদ্ধি মুনসী মেহেরউল্লার এত প্রখর ছিল যে, তৎকালীন সময়ে মুসলমান, হিন্দু ও খৃস্টান সমাজে তাহার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না বললেই চলে। উপস্থিত তর্কে তিনি কারো কাছে পরাজিত হয়েছেন এমন কোন তথ্য এ যাবত আমাদের হাতে এসে পৌছেনি। বরং বাংলা আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। বন্ধুদের রহস্যমূলক প্রশ্নের উত্তর তিনি রহস্য করিয়াই দিতেন।
এই মহান সমাজ সেবক অনেকগুলি বইও লিখেছেন। তার মধ্যে ‘মেহেরুল এছলাম’, ‘হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা’, ‘বিধবা গঞ্জনা’, ‘রদ্দে খৃস্টান’ ও ‘দলিলুল এছলাম’ গ্রন্থগুলি খুবই পরিচিত। তাঁর লেখা সাধারণ পাঠকের কাছে খু্বই জনপ্রিয় ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই লিখেছেন, “যদিও আমি ভালো বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ে অভাব অনুভব করিতে হয় না।”
সাহিত্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁর সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে যে নামগুলি উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ।
তিনি বাংলার জনগণের মাঝে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, নোয়াখালির কবি আবদুর রহিম তাঁর আখলাকে আহমদিয়া নামক বইতে লিখেছেন-
মুনসী মেহেরউল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়াতের হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার।
মুনসী মেহেরউল্লা ১৯০৬ সালে তাঁর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন। পরের বছর মাত্র ৪৫ বছর বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ইসলামী রেনেসাঁর এ অগ্রনায়ক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা বাংলা ও আসাম শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সেই সময়ের পত্রপত্রিকায় তার মৃত্যু সংবাদসহ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় লিখেছেন-
যার সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগণে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্বময় অন্ধকার।
আজ মুনসী মেহেরউল্লা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু আছে তাঁর কর্মময় জীবন, আছে তাঁর রচিত সাহিত্য। কি করে একজন সামান্য শিক্ষিত এতিম বালক পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের জোরে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে পারে, কি করে খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার হাত হতে স্ব-সমাজকে রক্ষা করতে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মুনসী মেহেরউল্লা। ছোট বড় সবার উচিত তাঁর জীবন হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাঁর কর্মময় জীবনের এবং সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারও আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।
\r\n\r\n
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
উপমহাদেশের সাংবাদিকতা জগতের দিকপাল, মুসলিম গণজাগরণের নকীব, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার হাকীমপুর গ্রামের এক বিখ্যাত পরিবারে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর আগে এবং তাঁর সমসাময়িককালে উল্লেখযোগ্য অনেক মুসলমান খ্যাতিমান লেখক-সাংবাদিকগণ মাসিক, ত্রৈমাসিক, দৈনিক ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ করলেও সেগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম বাংলা সাংবাদিকতা একটা দীর্ঘস্থায়ী ভীত রচনা করেন, তাঁর প্রকাশিত ‘দৈনিক আজাদ’ (১৯৩৬-১৯৯২) ও মাসিক ‘মোহাম্মদী’ বৃটিশ আমলে আত্মপ্রকাশ করে সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে এবং পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরও কিছুকাল এই পত্রিকা দু’টির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। মুসলিম বাংলার নবজাগরণে, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে, সামাজিক সংস্কারে, লেখক সৃষ্টিতে ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এবং ১৯৮৪ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
\r\nশিশুকালে পিতা-মাতাকে হারানোর পর আত্মীয়ের তত্ত্ববধানে তিনি বেড়ে ওঠেন। অতপর তিনি লালিত আত্মীয়-স্বজনের প্রচেষ্টায় লেখাপড়া চালিয়ে যান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর খুব বেশি ছিল না। তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জটিল পরিস্থিতিই ১৯০০ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে এফএম পাস করেন।\r\n\r\nকলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর মওলানা আকরম খাঁ কর্মজীবনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেচে নিন। খুব অল্প বয়সেই আহলে হাদীস ও মোহাম্মদী আকবর পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা পেশায় হাতেখড়ি হয়।\r\nআহলে হাদীস ও মোহাম্মদী আকবর পত্রিকায় সাংবাদিকাতার মাধ্যমে সাংবাদিকতা জীবন শুরু করার পর মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত দি মোহাম্মদী ও আল-ইহসান পত্রিকার স¤পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়ে কলকাতা থেকে জামানা ও সেবক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪০ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে এর সম্পদনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি অবসর জীবনে চলে যান।\r\nমওলানা আকরাম খাঁ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ধর্মশাস্ত্রবেত্তা, সুপ-িত ব্যক্তি এবং শক্তিশালি গদ্যলেখক হিসেবে খ্যাতিমান। বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। মওলানা আকরাম খাঁ রচিত গ্রন্থাদি, বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় রচনা একজন সুপ-িত ব্যক্তি, চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক এবং শক্তিমান গদ্যশিল্পীকেই চিনিয়ে দেয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁর একাধিক প্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠক শ্রেণী ও বোদ্ধামহলে বেশ প্রশংসিত ও খ্যাত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যকয়েকটি হল,-\r\n
*** আমপারার বাংলা অনুবাদ\r\n*** মোস্তফা-চরিত\r\n*** মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য\r\n*** বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্ম\r\n*** মুসলীম বাংলার সামাজিক ইতিহাস\r\n*** তাফসীরুল কোরআন (১-৫ খন্ড, অনুবাদ)\r\n*** টীকা-ভাষ্য (অনুবাদ)\r\nমৌলিক রচনা ছাড়াও তাঁর বাংলায় অনুদীত গ্রন্থগুলো প্রমাণ করে তিনি যে একজন দক্ষ অনুবাদক এবং সুপ-িত ব্যাক্তি।
মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে রাজনীতি শুরু করেন। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।\r\n১৯১৮ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯২০ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিনি নিখিল ভারত খেলাফত আন্দোলন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি এবং মওলানা মজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। আকরাম খাঁর দায়িত্ব ছিল তুর্কি খেলাফত থেকে ফান্ড সংগ্রহ করা। ১৯২০-১৯২৩ সময়ের মধ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে জনসভা বা সম্মেলনের আয়োজন করে খেলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন গতিশীল করার চেষ্ঠা করেন।
১৯৪১ সালে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং একনাগাড়ে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।
১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে গেল তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে দূরে সরে যান এবং ১৯৬২ সালে আজাদের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদাতসমূহের চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্যক্তি পূজা, কবর পূজা ও অন্যান্য প্রচলিত রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ধারণ করেছিলেন।
তিনি ১৯৪৭ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১০১ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালের ১৮ আগষ্ট রাজধানী বংশালে আহলে হাদীস মসজিদে নামাযরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।
\r\n\r\n
আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ
....................................................................
নাম আবদুল করীম। উপাধি সাহিত্য বিশারদ ও সাহিত্য সাগর। আব্বার নাম মুনশী নুরুদ্দীন এবং দাদার নাম মোহাম্মদ নবী চৌধুরী। আবদুল করীমের পুরো নাম মুনশী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ। তবে তিনি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ নামেই পরিচিত। এমনকি শুধু সাহিত্য বিশারদ বললেই তাঁকেই বুঝানো হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংগ্রাহক, গবেষক, প্রবন্ধকার ও সম্পাদক। না, তিনি কবি বা মৌলিক কোন লেখক ছিলেন না। আর এ জন্যেই অনেকের কাছে তিনি কিছুটা অপরিচিত। কিন্তু তাই বলে তিনি মোটেও ছোট খাট কোনো ব্যক্তি নন। তিনি আমাদের বাঙলা সাহিত্য অঙ্গনের এক মহান মনীষী। যাকে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। সত্যি কথা বলতে কি পুরো বাঙ্গালি জাতি এই মহান মানুষটির কাছে ঋণী হয়ে আছেন।
সাহিত্য বিশারদ মুন্সি আবদুল করিম ১৮৬৯, মতান্তরে ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর পটিয়া মহকুমার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কাদির রাজার অধস্তন বংশধর। তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হাবিলাস মল্ল কোন এক সময় চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে ঐ দ্বীপের নামকরণ করা হয় হাবিলাস দ্বীপ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আবদুল করীম দুনিয়ার মুখ দেখার আগেই তাঁর পিতা মুনশী নুরউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাতা মিস্রীজান প্রখ্যাত পাঠান তরফদার দৌলত হামজা বংশের মেয়ে ছিলেন।
জন্মের কয়েক মাস আগে পিতার মৃত্যু এবং ১৭ বছর বয়সে মাতৃহীন আবদুল করিম দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির স্নেহছায়ায় এন্ট্রান্স পাস করেন এবং সচেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বাড়ির দহলিজেই। সেখানেই তিনি আরবি-ফারসি ও বাংলায় পড়া শুরু করেন। অতঃপর তিনি সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এক বছর পড়াশোনা করে তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তার দ্বিতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সঙ্গত কারণেই উনিশ শতকে এন্ট্রান্স পাস করতে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানেও পারদর্শী হতে হতো। চট্টগ্রাম কলেজে দু’বছর এফএ পড়ার পর ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক সম্পন্ন পরিবারের মতো তাদের পরিবারেও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অনিবার্য করে তোলে। এর সঙ্গে যোগ হয় শারীরিক অসুস্থতা। পরীক্ষার আগে তিনি টাইফয়েড এ আক্রান্ত হন। ফলে তার আর এফএ পরীক্ষা দেয়া হয়নি। এখানেই তার উচ্চ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।
১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবনের শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক হন। চট্টগ্রামে প্রথম সাব-জজ আদালতে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে কাজ করেন। পরে কবি নবীন সেনের সুপারিশে চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
\r\nআবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আজীবন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। বাঙালি লেখকেরা যখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ও অনুরাগে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তখন প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথির রণাবেণ এবং পুঁথি সম্পাদনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মূলত পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথির রণাবেণ ও পুঁথি সম্পাদন ছিল তার জীবনের ব্রত। বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপাদান পুঁথি পত্র ও এদেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগের লৌকজ-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের ‘রাধিকার মানভঙ্গ’, কবিবল্লভের ‘সত্যনারায়ণের পুথিঁ’, দ্বিজ রতিদেবের ‘মৃগলুব্ধ’ রামরাজার ‘মৃগলুব্ধ সম্বাদ’, দ্বিজ মাধবের ‘গঙ্গামঙ্গল’, আলী রাজার ‘জ্ঞানসাগর’, বাসুদেব ঘোষের ‘শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস’, মুক্তারাম সেনের ‘সারদামঙ্গল’, শেখ ফয়জুল্লাহর ‘গোরক্ষবিজয়’ ও আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ (খণ্ডাংশ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত। ‘ইসলামাবাদ’ (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস) ও ‘আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য’ (মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে রচিত) তাঁর দুটি মৌলিক গ্রন্থ।\r\n
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাল্যকাল থেকেই পুঁথিপত্রের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। সারা জীবন তার নেশা ছিল দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাকি-মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা পাঠ করা এবং সংগ্রহ করা। তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁর পিতামহ কর্তৃক সংগৃহীত কিছু পুঁথির সঙ্গে পরিচিত হন। এই পুঁথিগুলো পড়ে তিনি পুঁথি সংগ্রহে ও এ নিয়ে লিখতে আগ্রহী হন। এ পুঁথিগুলোর মধ্যেই পেয়ে যান ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’। সেসময় তিনি ছিলেন এফএ ক্লাসের ছাত্র। এ সময় তিনি আচার্য অক্ষয় সরকার সম্পাদিত ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকায় ‘প্রাচীন পদাবলী’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করেই মহাকবি নবীন চন্দ্রসেন সাহিত্যবিশারদের প্রতি আকৃষ্ট হন।
একান্ত শিশুকাল হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদকে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন পাঠক সংগ্রাহক ও তথ্যনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে দেখতে পাই। এই মহান মনীষী ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে ৮৩ বছর বয়সে চট্টগ্রামে ইন্তিকাল করেন।
\r\n\r\n
মহাকবি আল্লামা ইকবাল
‘আরব হামারা চীন হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম,--ওতন হ্যায়
সারা জাঁহা হামারা।’
কোন কোন মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে সৃষ্টি করেন দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য। শত ঝড়ঝঞ্জা বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সেসব মানুষ তাঁদের কাজ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে যান। আমরা আজকে এমন এক ব্যক্তিত্ব ও কবি পুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।
তোমরা হয়ত কোন না কোনভাবে শুনে থাকবে মহাকবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে। হয়ত কথাটা এজন্য বললাম যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কবি ইকবালকে জানার তেমন সুযোগ নেই। সত্যি কথা বলতে কি এই মহান কবিকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হচ্ছে।
কবি ইকবাল পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নামক স্থানে ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ নুর মোহাম্মদ এবং মাতার নাম ইমাম বীবী। কবির পিতা মাতা উভয়ই অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। কবির পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরবাসী সাপ্রু গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পন্ডিত ছিলেন। তাঁরা সুলতান জয়নুল আবেদীন ওরফে বুদ শাহ(১৪২১-১৪৭৩ খৃ) এর রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা শিয়ালকোটে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ষাট বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।
কবির পিতা শেখ নূর মোহাম্মদ উচ্চশিক্ষিত কোন মানুষ ছিলেন না কিন্তু তিনি একজন স্বনামধন্য পন্ডিত ছিলেন। যার কারণে শামসুল উলামা সৈয়দ মীর হাসান তাঁকে(কবির পিতাকে) অশিক্ষিত দার্শনিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
ইকবালের জন্মের ব্যাপারে কথিত আছে যে, একদিন তাঁর পিতা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশচারী একটি অসম্ভব সুন্দর কবুতর তার কোলে এসে পড়ল। পরে তিনি স্বপ্ন বিশারদের কাছে জানতে পারলেন অদূর ভবিষ্যতে তিনি একজন ভাগ্যবান পুত্রের বাপ হতে যাচ্ছেন। আরও কথিত আছে যে, সদ্যজাত ইকবালকে যখন পিতা নূর মোহাম্মদের কোলে দেওয়া হয় তখন তিনি সদ্যজাত শিশুপুত্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “বড় হয়ে দ্বীনের খেদমত করলে বেঁচে থাক, নচেৎ এখনি মরে যাও।” বুঝতে পারছ তাঁর স্নেহময় পিতা তাঁর কাছ হতে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের জন্য কি আশা করেছিলেন?
পিতা নূর মোহাম্মদের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে মাদরাসায় পড়ানোর কিন্তু উস্তাদ শামসুল উলামা মীর হাসানের পরামর্শে তাঁকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়। প্রাইমারী শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে শিয়ালকোট স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। এ স্কুল হতে তিনি ১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্কচ স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি একদিন দেরীতে ক্লাসে আসেন, ক্লাস টিচার তাঁর দেরিতে ক্লাসে আসার কারণ জানতে চাইলে বালক ইকবাল তৎক্ষণাত উত্তর দেন, “ইকবাল(সৌভাগ্য) দেরিতে আসে স্যার।” উত্তর শুনে পন্ডিত শিক্ষক তো ‘থ’। তিনি যে শুধু উপস্থিত বুদ্ধিতে দক্ষ ছিলেন তা নয়। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী। ১৮৮৮, ১৮৯১ ও ১৮৯৩ সালে যথাক্রমে প্রাথমিক বৃত্তি, নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি স্বর্ণপদক ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে স্কচ মিশন স্কুল কলেজে উন্নীত হলে ইকবাল এখানে এফ. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এফ.এ. পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং যথারীতি বৃত্তিসহ স্বর্ণপদক লাভ করেন।
১৮৯৫ সালে তিনি শিয়ালকোট হতে লাহোরে এসে লাহোর সরকারী কলেজে বি.এ ভর্তি হন। এখানে একটা খবর দিয়ে রাখি, ইকবাল যখন বি.এ পড়ার জন্য পিতার নিকট অনুমতি চাইলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন, ‘ছাত্র জীবন শেষ করার পর অবশিষ্ট জীবন ইসলামের খিদমতে ওয়াকফ করে দিতে হবে।’
হ্যাঁ, তিনি তাতেই রাজী হয়েছিলেন। আর সত্যি সত্যিই তাঁর সারাটা জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। লাহোর সরকারী কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি টি.ডব্লউ এর মত ভূবন বিখ্যাত একজন সুযোগ্য শিক্ষক পান যিনি ছিলেন আরবী ভাষায় সুপন্ডিত, দর্শনের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক। প্রতিভাবান ইকবালকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে আরনল্ড সাহেব তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আরবী ও ইংরেজিতে সমগ্র পাঞ্জাবে প্রথম স্থান নিয়ে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যে কারণে তিনি এবার দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর ১৮৯৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ পাস করেন। সাথে সাথে তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর সামান্য কিছুকাল পরই তিনি লাহোর সরকারী কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজের ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের খন্ডকালীন সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ সময়ে উর্দু ভাষায় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন। তাঁর জীবন ছিল ছকে বাঁধা। এ সম্বন্ধে ইসলামী বিশ্বকোষ লিখেছে, “তিনি ভোরে ওঠে ফজরের সালাত আদায় করতেন, অতঃপর উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তারপর কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করতেন এবং কিছু না খেয়ে কলেজে যেতেন। দুপুরে বাড়ি ফিরে আহার করতেন। অনেক সময় গভীর রাতে ওঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। একবার তিনি একাধারে দুই মাস এই রাত্রিকালীন সালাত আদায় করেন।’
১৯০৫ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মানসে লন্ডন গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, সূফী কবি আমীর খসরু ও মহাকবি গালিবের মাযার জিয়ারত করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময় তিনি শিক্ষক হিসেবে পান বিশ্ব খ্যাত দার্শনিক ডঃ এম সি ট্যাগার্টকে। এরপর তিনি পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। শেষে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারস্যের দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক সন্দর্ভ লিখে ১৯০৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপরের বছর লিংকন ইন হতে ব্যারিস্টারী পাস করেন। এ সময় তাঁর প্রিয় শিক্ষক স্যার আর্নল্ড লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশেষ কারণে কয়েক মাসের ছুটিতে গেলে ইকবাল ৬ মাসের জন্য তাঁর স্থানে আরবীর অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
১৯০৮ সালের ২৭ শে জুলাই তিনি দেশে ফিরে এলে লাহোরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন। তিনি লাহোরে ফিরে স্বপদে পুনর্বহাল হন এবং সরকারের অনুমতিক্রমে আইনব্যবসা শুরু করেন। অবশ্য দেড় বছর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে তিনি আইনব্যবসা শুরু করেন। তবে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, তিনি কখনই মাসিক খরচের পরিমাণ টাকা রোজগারের পর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করতেন না। আরও একটা কথা, তিনি যদি বুঝতেন কোন মোকদ্দমায় মক্কেলের তেমন কোন উপকার করতে পারবেন না তা’হলেও তিনি সে কেস গ্রহণ করতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।
ছাত্রাবস্থায় ১৮৯৬ সালে শিয়ালকোটের এক কবিতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। এরপর তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখে হায়দারাবাদের প্রখ্যাত কবি দাগের নিকট পাঠিয়ে দেন সংশোধনের জন্য। কবি দাগ কিশোর কবির এ কবিতাগুলি পেয়ে মনোযোগ সহকারে পড়েন ও চমৎকার একটি মন্তব্য লিখে পাঠান। কবি দাগ লিখেছিলেন, ‘এ কবিতাগুলি সংশোধন করার কোন দরকার নেই। এগুলো কবির স্বচ্ছ মনের সার্থক, সুন্দর ও অনবদ্য ভাব প্রকাশের পরিচয় দিচ্ছে।’ কবি ইকবাল এ চিঠি পেয়ে তো খুব উৎসাহ পেলেন। তাঁরপর হতে চললো তাঁর বিরামহীন কাব্যসাধনা। এরপর ১৯০০ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলাম-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় জীবনের প্রথম জনসমক্ষে তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘নালা ইয়াতীম’ বা অনাথের আর্তনাদ পাঠ করেন। কবিতাটি পড়ার পর চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। মানে কবিতাটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে কবিতাটি ছাপা হয় এবং এর প্রতিটি কপি সে সময় চার টাকা দামে বিক্রি হয়। বিক্রয়লব্ধ প্রচুর পরিমাণ টাকা ইয়াতিমদের সাহায্যার্থে চাঁদা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯০১ সালে তিনি ছোটদের জন্য লেখেন-মাকড়সা ও মাছি, পর্বত ও কাঠবিড়ালি, শিশুর প্রার্থনা, সহানুভূতি, পাখীর নালিশ, মায়ের স্বপ্ন প্রভৃতি কবিতা।
এরপর তিনি দু’হাতে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল, ‘স্বদেশপ্রেম, মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ, ইসলামের শ্বাশত আদর্শে তাওহীদভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, জাতির উত্থান-পতন, দলীয় কলহ ও অন্তর্দ্বন্ধ নিরসন প্রভৃতি বিষয় কবিতায় স্থান পেতো। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে তিনি বেলালী সুরে আহবান জানাতেন ক্লান্তিহীনভাবে। স্বকীয় আদর্শের সন্ধানে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।’
তাঁর কাব্যে এ ধরনের চিরন্তন আবেদন থাকার কারণে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। নানামুখি প্রতিভার অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বমহল হতে অকুন্ঠ সম্মান অর্জন করেন। মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একজন হিন্দু অধ্যাপক বলেছিলেন, “মুসলমানগণ ইকবালকে লক্ষবার তাঁদের সম্পদ বলে দাবি করতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন ধর্ম বা শ্রেণীবিশেষের সম্পদ নন-তিনি একান্তভাবে আমাদেরও।’’
১৯০১ সালে ‘হিমালাহ’ নামক কবিতাটি তৎকালীন সময়ের উর্দু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা ‘মাখযানে’ ছাপা হয়। এটিই পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতা। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে তিনি এসময় অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ১৯০৩ সালে লাহোর হতে অর্থনীতির ওপর তাঁর প্রথম পুস্তক ‘আল ইলমুল ইকতেসাদ’ প্রকাশিত হয়।
১৯২৪ সালে ‘বাঙ্গেদারা’ বা ঘন্টাধ্বনি নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আসরার-ই-খুদী’ বা ব্যক্তিত্বের গূঢ় রহস্য। এ কাব্যগ্রন্থটি ১৯২০ সালে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন ডঃ আর.এ.নিকোলসন। সাথে সাথে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে মহাকবি ও বিশ্বকবি আল্লামা ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে ‘আসরার-ই-খুদী’ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিশ্বের বহু ভাষায় এ কাব্যগ্রন্থটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।
১৯১১ ও ১৯১২ সালে পঠিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কবিতা ‘শিকওয়াহ’ বা অভিযোগ ও ‘জওয়াব-ই-শিকওয়াহ’ বা অভিযোগের জবাব উর্দু ভাষায় রচিত। এ দীর্ঘ দুটি কবিতার কাব্যগ্রন্থ দু’টির বাংলা ভাষায় একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় রচিত ‘পায়াম-ই-মাশরিক’ প্রাচ্যের বাণী কাব্যগ্রন্থটি। গ্রন্থটি আরবী, ইংরেজী, তুর্কী, জার্মান ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় ‘রামূয-ই-বেখুদী’ বা আত্মবিলোপের গুঢ়তত্ত্ব কাব্যগ্রন্থটি। মূলত এ গ্রন্থটি ‘আসরারে খুদী’র দ্বিতীয়াংশ। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থটির ৮৪ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ‘বালে জিবরীল’ বা জিবরাঈলের ডানা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘দরবারে কালীম’ বা মূসার লাঠির আঘাত কাব্যগ্রন্থটি। উর্দু ভাষায় রচিত এ কাব্যগ্রন্থটি আরবী ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েও প্রকাশিত হয়।
এর আগে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘যাবুরে আজম’ বা প্রাচ্যের ধর্ম সংগীত কাব্যগ্রন্থটি। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় রচিত ‘জাবীদ নামা’ বা অমর লিপি কাব্যগ্রন্থটি। এমনিভাবে একের পর এক তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত তিনি প্রাচ্যের সেই ভাগ্যবান কবি ব্যক্তিত্ব যার রচনা এত ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সত্যিই যদি বিশ্বকবি বিশেষণে কাউকে বিশেষিত করতেই হয় তবে সে সম্মানের অধিকারী নিঃসন্দেহে কবি আল্লামা ইকবাল। কবি নিজেও ছিলেন বহু ভাষাবিদ পন্ডিত। তিনি উর্দু, ফারসী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় লেখনি চালিয়েছেন।
কবি The Development of Metaphysics in Iran বা ‘প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান’ এই বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ সালে লন্ডন হতে এ থিসিস প্রকাশিত হয়।
এতক্ষণ তাঁকে কবি হিসেবে পরিচয় দিলাম। আসলে তিনি শুধুই কবি ছিলেন না। তিনি সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক আইনজ্ঞ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
১৯৩০ সালে নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি বিলেত গমন করেন ‘গোল টেবিল’ বৈঠকে যোগদানের জন্য। এই বৈঠকে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করেন। অবশ্য এর আগে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি চাই যে-পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান একটি রাষ্ট্রে পরিণত হউক। পৃথিবীর এই অংশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে হোক বা বাইরে হউক-অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনই আমার মতে মুসলমানদের শেষ নিয়তি।’ এই মত অনুযায়ীই পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এ জন্য তাঁকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার বলা হয়। অবশ্য তিনি ১৯৩৭ সালের ২১শে জুন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমি যেভাবে প্রস্তাব করছি সেভাবে পুনর্গঠিত মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্রই হল একমাত্র উপায়, যদ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ ভারত গড়ে উঠতে পারে এবং সাথে সাথে অমুসলিম আধিপত্য থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যেতে পারে। উত্তর পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদেরকে কেন একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃতি দেয়া হবে না-যাতে তারা ভারতের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পারে?’ এ উদ্ধৃতিতে তিনি যে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলেছিলেন তা নিশ্চয় বুঝা যায়। মূলত আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ত্বও তাঁরই চিন্তার ফসল। অথচ এ মহান ব্যক্তিত্ত্বকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর হতে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, একথা আগেই বলেছি। তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে যে কারণে তিনি নাকি পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। অথচ তিনি পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ারও বেশ আগে ১৯৩৮ সালের ২১শে এপৃল ইন্তিকাল করেন। আশা করি বুঝতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না যে, আমরা এ মহান ব্যক্তিত্ত্বকে অস্বীকার করে কি পরিমাণ মূর্খতায় ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সত্যি কথা আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু অনুদার বুদ্ধিজীবি এর জন্য দায়ী।
উপমহাদেশের এ প্রখ্যাত দার্শনিক কবি অসম্ভব দেশপ্রেমিক একজন মানুষ ছিলেন। লেখার শুরুতেই যে কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়েছি তার কাব্যানুবাদ এ রকমের-
‘আরব আমার, ভারত আমার, চীনও আমার-
নহে তো পর-
মুসলিম আমি,- জাহান জুড়িয়া
ছড়ানো রয়েছে আমার ঘর।’
দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সচেতনভাবে এ কবিকে বর্জন করা হয়। তার প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে জহুরুল হক নামকরণ করা, পাঠ্যতালিকা হতে তাঁর রচনা ও জীবনী বাদ দেয়া।
আমরা আশা করবো এখন হতে নতুন করে আবার আমরা ইকবাল চর্চায় ফিরে যাব। কবিকে তাঁর প্রকৃত সম্মানে সম্মানিত করবো। দেশের সব শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে তাঁর রচনা অন্তুর্ভুক্ত হওয়া এ জাতির কল্যাণের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন, সে দিকটা দেখার জন্য সরকারের প্রতি আহবান রইলো।
\r\n\r\n
ইসমাইল হোসেন সিরাজী
আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া,
উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া,
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া,
পূত বিভূ নাম স্মরণ করি।
সিরাজগঞ্জ শহরের ছোট্ট এক কামরায় বসে লিখে চলেছেন এক তরুণ তার আপন কওমকে জাগিয়ে তোলার জন্য। লিখে চলেছেন বৃটিশ বেনিয়াদের এদেশ হতে চিরতরে উৎখাত করার জন্য। এই বেনিয়া গোষ্ঠী সমস্ত ভারত উপমহাদেশ মুসলমানদের কাছ হতে ছিনিয়ে নেয়। ক্ষোভে দুঃখে মুসলমানগণ ইংরেজদের প্রবর্তিত অনেক কিছুই ত্যাগ করে। এমনকি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ হতেও নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। অপরদিকে হিন্দুরা এ সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষা দীক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানরা হয়ে পড়ে পঙ্গু কি শিক্ষা দীক্ষায়, কি সম্পদ বৈভবে। ঠিক এ সময়েই কলম তুলে নেন সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী। ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই তারিখে তিনি তৎকালীন পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ আবদুল করীম এবং মাতার নাম নুরজাহান বেগম। তারা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার মানুষ।
শিশু ইসমাইল হোসেনের লেখাপড়ার প্রথম সবক দেন তাঁর মা নূরজাহান খানম। নূরজাহান খানম তাঁর শিশুপুত্রকে প্রথমেই কোরআন শিক্ষা দেন। কোরআন শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করা হয়। মেধাবী ইসমাইল হোসেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সিরাজগঞ্জের বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে এ সম্ভাবনাময় তরুণ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাছাড়া স্বদেশের পরাধীনতা, সমগ্র মুসলিম জাহানের দুর্দশার জন্য বেদনাবোধ হতে সৃষ্টি উৎকন্ঠাও তাঁকে স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে বসে থাকতে দেয় নি। তোমরা জানলে আশ্চর্য হবে যে, তিনি এ সময়ে নির্যাতিত অবহেলিত, লাঞ্চিত ও পদদলিত মুসলিম জাতির জন্য বেদনাবিধুর, এতই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, মাত্র ১৬ বছর বয়সেই লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ যাত্রায় তিনি তুরস্কে যেতে পারেন নি ঠিক কিন্তু সেই যে মুসলিম জাহানের কল্যাণের মানসে ঘর হতে বের হলেন আর কখনই সুবোধ বালকের মত ঘরে বসে থাকেন নি। অবশ্য তিনি পরবর্তীকালের তাঁর বাল্যকালের স্বপ্নের তুরস্কে গিয়েছিলেন তা অনেক পরের কথা।
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সবচেয়ে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ হল ‘অনল প্রবাহ’। এটি ১৮৯৯ সনে মুনসী মেহেরউল্লা প্রথম প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি এত জনপ্রিয় ছিল যে ১৯০০ সালে আরো কিছু কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি আবার প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯০৮ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর এ সময়ই ‘অনল প্রবাহ’ ও লেখক বৃটিশ রাজশক্তির আক্রমণের শিকার হন। ‘অনল প্রবাহ’ বাজেয়াপ্ত হয় এবং লেখকের দু’বছর কারাদন্ড হয়। তিনিই প্রথম কবি যার কাব্যগ্রন্থ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় এবং তিনিই বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে কারাদন্ড ভোগকারী উপমহাদেশের প্রথম সাহিত্যিক। সিরাজীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হল উচ্ছ্বাস, উৎসব, উদ্বোধন কাব্য, মহাশিক্ষা কাব্য, স্পেন বিজয় কাব্য, প্রেমাঞ্জলী(গীতিকাব্য), সঙ্গীত সঞ্জীবনী ইত্যাদি।
মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ও মিথ্যা অপপ্রচার করতো তখন হিন্দু কবি সাহিত্যিকরা। বিশেষ করে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার লেখায় সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হেয় করার চেষ্টা করতেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী এ সমস্ত কুৎসিৎ লেখার জবাব দিতে গিয়ে উপন্যাসও রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে তারাবাই, ফিরোজা বেগম, নুরুদ্দীন, রায়নন্দিনী ও বংকিম দুহিতা। না, জবাব দিতে গিয়ে সিরাজী প্রতিআক্রমণ বা সাম্প্রদায়িক উস্কানি বেছে নেননি। সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উপন্যাসে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘রায় নন্দিনী’।
সিরাজী রচিত কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও সঙ্গীত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সংখ্যা ৩২টি। এগুলো হলো- কাব্যগ্রন্থ উচ্ছ্বাস (১৯০৭), নব উদ্দীপনা (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৮), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯৮৪), মহাশিক্ষা কাব্য প্রথম খন্ড (১৯৬৯), মহাশিক্ষা কাব্য দ্বিতীয় খন্ড (১৯৭১)। উপন্যাস- রায়নন্দিনী (১৯১৫), তারাবাঈ (১৯১৬), নূরউদ্দীন (১৯১৯)। প্রবন্ধ গ্রন্থ- মহানগরী কর্ডোভা (১৯০৭), স্ত্রীশিক্ষা (১৯০৭), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), সুচিন্তা প্রথম খন্ড (১৯১৬), তুর্কি নারী জীবন (১৯১৩), ভ্রমণ কাহিনী- তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১৩)। সঙ্গীত গ্রন্থ- সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), প্রেমাঞ্জলী (১৯১৬) প্রভৃতি। অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- সুধাঞ্জলী, গৌরব কাহিনী, কুসুমাঞ্জলী, আবে হায়াৎ, কাব্য কুসুমোদ্যান, পুস্পাঞ্জলী। অসমাপ্ত উপন্যাস- বঙ্গ ও বিহার বিজয় এবং জাহানারা।
১৯৪০ সালের ২২ মার্চ কলিকাতা ২/১ ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, সিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম- এর উদ্বোধন করা হয়। উক্ত দ্বারোঘাটন অনুষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে বলেন, ‘সিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে ভাবিতেন জ্যেষ্ঠ পুত্র-তুল্য। তাঁহার নিকট যে স্নেহ আমি জীবনে পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সঞ্চয়। ফরিদপুর কনফারেন্সে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সমগ্রজীবনই ছিল অনল প্রবাহ এবং আমার রচনায় সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ আছে। সাহিত্যিক ও রাজনীতিক ছাড়াও আমার চোখে তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন এক শক্তিমান দরবেশ রূপে। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন নাই, তুরস্কের রণক্ষেত্রে তিনি সেই মৃত্যুর সঙ্গে করিয়াছিলেন মুখোমুখি। তাই অন্তিমে মৃত্যু তাঁহার জন্য আনিয়া দিয়াছিল মহাজীবনের আস্বাদ।\'
বাংলাদেশের জন্য বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা মহান পুরুষ সিরাজীকে হীনমন্যতার কারণে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ। দেশের মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পাঠ্যসূচিতে সিরাজী রচনাবলী উপেক্ষিত। সিরাজীর লেখা থেকে বঞ্চিত এদেশের শিক্ষার্থীরা। সিরাজী সম্পর্কে তরুণ সমাজকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। অথচ সিরাজীর অনলবর্ষী বক্তৃতায় প্রকম্পিত হয়েছিলো ব্রিটিশ সিংহাসন। তাঁর কণ্ঠ ও লেখা থেকে বারুদের গন্ধ বের হতো। তাঁর বক্তৃতায় জেগে ওঠেছিলো লাখো লাখো তরুণ। সেখানে মুসলিম বা হিন্দু বলে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হয় নাই। ব্রিটিশ রাজ শুধু তাঁকে কারাবন্দীই করেনি, তার কবিতাও নিষিদ্ধ করেছিলো। সেই স্বাধীনচেতা মহাকবিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা অবমূল্যায়ন করছেন। যারা মুসলমানদেরকে লাইভস্টক বা গৃহপালিত পশু বলে আখ্যায়িত করছে, যারা আমাদেরকে কাক পক্ষী, দস্যু, তস্কর, দানব, অসুর, অনার্য, ইতর, নরপশু, ডাকাত বলে গালি দিয়েছে তাদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী ঘটা করে পালন করা হয়। তাদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের। অথচ সিরাজীর মত মহানায়কের রচনাবলী পাঠ্য বহির্ভূতই থেকে যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশের ক্রান্তিকালীন দুর্বিষহ অবস্থার প্রেক্ষিতে সিরাজীর মতো বিপ্লবী পুরুষের প্রসঙ্গ টেনে আনা অতীব জরুরী। ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান লিখেছেন, ‘বাংলাদেশী জাতি সৃষ্টির এই গঠনকালে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উদারতা, দৃঢ়তা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বাতন্ত্র্যবাদ, ঐতিহ্য চেতনা, সংস্কৃতি চেতনা, বিজ্ঞান-ইতিহাস ও সাহিত্য-চেতনা প্রভৃতি থেকে প্রেরণা আহরণ একান্ত কর্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত সারা উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে যে জাতীয় ঐক্যবোধ, জাগরণ স্পৃহা আপন জাতীয় সত্ত্বার পরিচয় ফুটিয়ে তোলার আকাক্মখা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াস তীব্র আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে সেই উদ্যম নিষ্ঠা ও কর্ম-চাঞ্চল্য একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে। আবশ্যক হয়ে উঠেছে আজ আবার নতুন করে ঘনিয়ে ওঠা বিভ্রান্তির, দিশাহীনতার দিগন্তের কালো আবরণ ভেদ করে আলোকবন্যা আবাহনের জন্য নতুন করে গর্জে ওঠা হাজার হাজার সিরাজীর।\'
মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই দুরারোগ্য পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম বিশ্বের এই মহান পুরুষ ইন্তিকাল করেন। জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বপ্রকার অনাচার, কদাচার, কুসংস্কার, অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সিংহের মত লড়ে গেছেন। না কোথাও কোন কারণে তিনি মাথা নত করেন নি।
\r\n\r\n
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি শতাব্দী। বিশিষ্টি ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ পন্ডিত, ধর্মবেত্তা ও সূফীসাধক। তিনি ছিলেন একাধারে ভাষাবিদ, গবেষক, লোকবিজ্ঞানী, অনুবাদক, পাঠসমালোচক, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক, কবি, ভাষাসৈনিক এবং একজন খাঁটি বাঙালি মুসলিম ও দেশপ্রেমিক। জ্ঞানপ্রদীপ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা ভাষার গবেষণায় অদ্বিতীয়।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাবা-মার পঞ্চম সন্তান। তাঁর বাবা মফিজ উদ্দিন আহমদ ছিলেন ইংরেজ আমলে সরকারি জরিপ বিভাগের একজন কর্মকর্তা। শহীদুল্লাহ মাতা হরুন্নেছা খাতুনের শিক্ষার প্রতি ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি বাড়িতে তাঁর পরিবার ও পেয়ারা গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের শিক্ষা দিতেন। প্রথম দিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম রাখা হয় মুহম্মদ ইব্রাহীম। কিন্তু পরবর্তীকালে পিতার পছন্দে আকিকা করে তাঁর নাম পুনরায় রাখা হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
ছোটবেলায় ঘরোয়া পরিবেশে শহীদুল্লাহ উর্দু, ফার্সী ও আরবি শেখেন এবং গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত পড়েন। পাঠশালার পড়া শেষ করে ভর্তি হন হাওড়া জেলা স্কুলে। স্কুলের ছাত্র থাকতেই বই পড়ার এবং নানা বিষয়ে জানার প্রতি ছিল তাঁর দারুণ নেশা। হাওড়া স্কুলের স্বনামখ্যাত ভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে\'র সংস্পর্শে এসে শহীদুল্লাহ ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। স্কুলজীবন থেকেই তিনি আরবী-ফার্সী-উর্দুর পাশাপাশি হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা পড়তে শিখেছিলেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্ত্বের সাথে সংস্কৃতসহ প্রবেশিকা পাশ করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে ১৯০৬ সালে এফ.এ. পাশ করেন। অসুস্থতার কারণে অধ্যায়নে সাময়িক বিরতির পর তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন ১৯১০ সালে। বাঙালি মুসলমান ছেলেদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অনার্স নিয়ে পাস করেন।
সংস্কৃতিতে অনার্স পাস করার পর সংস্কৃত নিয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করতে চাইলে তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁকে পড়াতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯১২ সালে এ বিভাগের প্রথম ছাত্র হিসেবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এর দু\'বছর পর ১৯১৪ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে বি.এল. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইউরোপ গমন করেন। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শণ চর্যাপদাবলি বিষয়ে গবেষণা করে ১৯২৮ সালে তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এ বছরই ধ্বনিতত্ত্বে মৌলিক গবেষণার জন্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লাভ করেন।
হম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে সিতাকুন্ডু উচ্চ বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি কিছুদিন ওকালতি প্র্যাকটিস করেন। তিনি বশিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর দিনেশ চন্দ্র সেনের অধীনে শরৎচন্দ্র লাহিরী রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সে বছরের ২ জুন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে স্থায়ী চাকুরিতে যোগদান করেন। একইসঙ্গে নিখরচে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সভাপতি নিযুক্ত হন। পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষকের এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষকের পূর্বপদে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি রীডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। একই বছর তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে ১৯৩৭ সালে স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের ৩০ জুন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে রীডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং একইসাথে উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ছয় বছর কলা অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা গড়ে তোলার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সেখানে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে (ফরাসি ভাষার) খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অস্থায়ী প্রাধ্যক্ষের এবং ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ইমেরিটাস নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার বাইরে তিনি করাচির উর্দু উন্নয়ন সংস্থার উর্দু অভিধান প্রকল্প, ঢাকায় বাংলা একাডেমীর \'পূর্ব পাকিস্তান ভাষার আদর্শ অভিধান প্রকল্প\' এবং ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের সদস্য, ইসলামিক একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলা একাডেমীর বাংলা পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার ও দাউদ সাহিত্য পুরস্কার কমিটির স্থায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা ও সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাজে Seminar on Traditional Culture in South-East Asia -তে তিনি UNESCO -র প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এর চেয়ারম্যান মনোনীত হন।
ভাষাবিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি সচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন, আয়ত্ত করেছিলেন বাইশটি ভাষা। তিনি বাংলা, উর্দু, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, পালি, আসাম, উড়িয়া, আরবী, ফার্সী, হিব্রু, আবেস্তান, ল্যাটিন,তিব্বর্তী, জার্মান, ফরাসী, প্রাচীন সিংহলী, পশতু, মুন্ডা, সিন্ধী, মারহাটী, মৈথালী ইত্যাদি ভাষা জানলেও ভাষার ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সানন্দে বলতেন, আমি বাংলা ভাষাই জানি। বাংলা যে সংস্কৃত ভাষা হতে জন্ম নেয় নি, একথা প্রথম তিনিই প্রমাণ করেন। তিনিই বলেন, “বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নহে; বরং দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।”
তাঁর প্রকাশনা গুলি হলো:\r\nগবেষণাগ্রন্থ: সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা (১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)।\r\nভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫) । প্রবন্ধ-পুস্তক: ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essay on Islam (1945), Traditional culture in East Pakistan (মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গে তাঁর যুগ্ম-সম্পাদনায় রচিত;১৯৬১)।
গল্পগ্রন্থ:
রকমারী(১৯৩১)।\r\nশিশুতোষ গ্রন্থ: শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রাসূলুল্লাহ (১৯৬২), সেকেলের রূপকথা (১৯৬৫) ।\r\nঅনুবাদ গ্রন্থ: দাওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম (১৯৪২), শিকওয়াহ ও জাওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), বিদ্যাপতিশতক (১৯৪৫), মহানবী (১৯৪৬), বাই অতনা মা (১৯৪৮), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Sayings of the Holly Prophet (1945), Buddist Mystic Songs (1960)।\r\nসংকলন: পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। এছাড়া তিনি ৪১টি পাঠ্যবই লিখেছেন, ২০টি বই সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০টিরও বেশি। ভাষাতত্ত্বের উপর রয়েছে তাঁর ৩৭টি রচনা। অন্যান্য বিষয়ে বাংলা ইংরেজী মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮০টি। এ ছাড়া তিনি তিনটি ছোটগল্প এবং ২৯টি কবিতা ও লিখেছেন।
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বহু মননশীল ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তিনি সম্পদনা করেছেন। তিনি আল এসলাম পাত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯২৫) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯২৮-২১) হিসেবে যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁরই সম্পাদনা ও প্রকাশনায় মুসলিম বাংলার প্রথম শিশু পত্রিকা \'আঙ্গুর\' (১৯২০) আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা \'দি পীস\' (১৯২৩), বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা \'বঙ্গভূমি\' (১৯৩৭) এবং পাক্ষিক \'তকবীর\' (১৯৪৭) সম্পাদনা করেন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক ও মাসিক জার্নাল সম্পাদনা করেন।
এই চলন্ত বিশ্বকোষ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তিটি ছিলেন পুরামাত্রায় ইসলামী শরীয়তের পাবন্দ। মুমিনের গুণাবলীগুলি তিনি তাঁর জীবনে ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)এর খলীফা। ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে এই মহান মনীষী ৮৪ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। মরহুমের লাশ তাঁরই নামে নামকরণকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পাশে ঐতিহাসিক মূসা মসজিদ প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।
\r\n\r\n
শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা ও চর্চার একটা গঠনমূলক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মীর মোশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯৯১), মোজাম্মেল হক(১৮৫০-১৯৬১), কায়কোবাদ(১৮৫৮-১৯৫১) যে ধারার সূচনা করেছিলেন পরবর্তীতে মুনসী মুহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩০), শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২) প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, সংগ্রামীগণ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের তুলনায় অনগ্রসর মুসলমানদের স্বরূপ সন্ধান, স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ ও তাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে। এ ক্ষেত্রে তারা সব দিক হতে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মুসলিম জাতীয় জাগরণের পথিকৃত মুনসী মেহেরউল্লার নিকট হতে। মুনসী মেহেরউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন পরাধীন দেশে বৈরী শাসনাধীনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন তাদের মধ্যে নবজাগরণের। আর এ নব জাগরণ সম্ভব করার জন্য তিনি নিজে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখালেখির সাথে সাথে গড়ে তুলেছিলেন একটি সাহিত্যিক সম্প্রদায়।
“শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ছিলেন সেই সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরই একজন। তাঁর জীবন সাধনার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল বাঙালী মুসলমানের জন্য সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাশীল আত্মপরিচয় নির্মাণে সহায়তা করা। ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য ভিত্তিক নবজাগরণমূলক কাব্য রচনা, ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ও প্রেরণাদায়ক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা, ধর্মীয় চেতনা ও মননশীলতা বিকাশে ‘সহায়ক সমৃদ্ধশালী বিদেশী সারাবান সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ও দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের চরিত-মানস গঠন উপযোগী শিশুতোষ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে একটি নব চেতনা জাগৃতির প্রত্যাশী ছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার মধ্যে সংকীর্ণতা রহিত মুক্তবুদ্ধি সঞ্জাত সম্প্রদায়গত সমৃদ্ধি কামনা ও সমাজ হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়।”(শেখ হবিবর রহমান-মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পৃ.৯)।
শেখ হবিবর রহমান নিজের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে ‘আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-
“আমার সাহিত্য বরাবর মোল্লা ধরনের; এইজন্য ইহা অনেকের নিকট উপেক্ষিত। নিয়ামত, আবেহায়াত ইত্যাদি ধরনের পুস্তকের নাম বোধ হয় মুসলমান সমাজে সর্বপ্রথম আমিই রাখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার বিবিধ পুস্তকে আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার এত অধিক যে, আমাদের মধ্যে আর কেহই তত অধিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। জাতীয়ভাবে জাতীয় শব্দের সংমিশ্রণে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি আমার জীবনের প্রধান একটি সাধনা।”
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ১৮৯০ মতান্তরে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তদানিন্তন যশোর জেলার বর্তমান মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলাধীন ঘোষগাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ দেরাজতুল্লাহ এবং দাদার নাম শেখ হেরাজতুল্লাহ। জানা যায় আরব দেশ হতে তাঁর পূর্ব পুরুষ এদেশে এসেছিলেন এবং ঘোষগাতি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন।
শেখ হবিবর রহমানরা দুই ভাই ছিলেন। তাঁর ছোটভাই শেখ ফজলর রহমানও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও ধর্ম প্রচার করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ‘পুলুম আঞ্জুমানে হেমায়তুল ইসলাম’ নামক ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের সম্পাদক ও ‘আলমগীর লাইব্রেরীর পক্ষে বড় ভাই শেখ হবিবর রহমানের বেশ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
শেখ হবিবর রহমানের লেখাপড়া গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। পরে পুলুম প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে উচ্চ প্রাথমিক পাঠ শেষ করে তিনি ফুলতলা ইউনিয়ন হাইস্কুলে ভর্তি হন। আরও পরে ১৯০৭ সালে সেখান হতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ১৯১০ সালে যশোর জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশের আগেই ১৯০৯ সালে তাঁর স্নেহময়ী পিতা ইন্তিকাল করেন। এজন্য তাঁর শিক্ষাজীবন দারুণ অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। পিতৃবিয়োগের পর তাঁকে বহু কষ্টে তাঁর যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হত। ১৯১৪ সালে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আরও পরে ১৯২২ সালে কলকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে এল.টি. ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে এল.টি. পাশ করেন।
ঐ বছরই তিনি বারাসাত গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। নয় মাস পরে তাঁকে মক্তব সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে খুলনায় বদলী করা হয়।
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নকে ১৯২৭ সালে খুলনা হতে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলী করা হয় এবং সেখানে ৪ বছর চাকুরী করার পরে ১৯৩০ সালে পুনরায় তাকে বারাকপুর সরকারী হাইস্কুলে বদলী করা হয়। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৪৪ সালে তিনি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।
খুলনা শহরে অবস্থানকালে তিনি পুনরায় ১৯৫১ সালে করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন এবং কর্মজীবন হতে দ্বিতীয়বারের মত ১৯৬০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তাঁর মধ্যে সৃজনশীল রচনার প্রেরণা দেখা যায়। এই সময়ে তিনি ‘গো-জাতির প্রতি অত্যাচার’ নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পয়গ্রাম কসবা মাইনর স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় মুনসী মুহম্মদ মেহেরউল্লা এক ধর্মসভায় গেলে সেখানে তিনি দুটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতা দু’টি শুনে মুনসী মেহেরউল্লা তাঁকে ‘শিশুকবি’ খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা ‘পেচক পন্ডিত’ নামের একটি কবিতা। কবিতাটি ১৩১৪ সনের ১৫ আশ্বিন ‘মোসলেম সুহৃদ’ এবং ১৮ আশ্বিন ‘মিহির ও সুধাকর’ পত্রিকায় ছাপা হয়।
মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯০৬ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘কোহিনুর কাব্য’। ফুলতলা(খুলনা) জুনিয়র মাদ্রাসার সেক্রেটারী মৌলভী মোহাম্মদ কাসেমের উপদেশে ‘বাংলা মৌলুদ শরীফ’ রচনা করতে গিয়ে এই মহাকাব্য রচনা করেন।
তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম ‘পারিজাত’, এটি ১৯১২ সালে যশোর হতে মৌলভী আলতাফ হোসেন প্রকাশ করেন। এরপর ১৯১৯ সালে দ্বিতীয়, ১৯২৪ সালে তৃতীয় এবং ১৯৩৩ সালে কাব্যগ্রন্থটির চতূর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কবির ছাত্রজীবনে ১৩১২ হতে মাঘ ১৩১৬ সময়ের মধ্যে লিখিত। ‘পারিজাত’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়। ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকা ‘পারিজাত’কে কবিতা কাননের যথার্থ পারিজাত বলে অভিহিত করে। পারিজাত পাঠ করে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এ কাব্যগ্রন্থকে String of small poems.............verses are melodious and the rhythm admirable বলে মন্তব্য করেন।
তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীঃ
কোহিনুর কাব্য, চেতনা কাব্য, আবেহায়াত কাব্য, নিয়ামত, বাঁশরী, গুলশান ইত্যাদি। ফারসী কবি শেখ সাদীর ‘গুলিস্তা’ ও ‘বুস্তা’র কাব্যনুবাদও তিনি করেন। এছাড়া আলগীয়, কর্মবীর মুনশী মেহের উল্লাহ, ভারত সম্রাট বাবর, সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী, মালাবারে ইসলাম প্রচার, দবরুল মুখতার, আমার সাহিত্য জীবন ইত্যাদি গদ্য রচনাতেও তিনি মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিশোর পাঠকদের জন্য তিনি রচনা করেছেন পরীর কাহিনী, মরনের পরে, ছোটদের হযরত মুসা, হাসির গল্প ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, শয়তানের সভা এবং শেখ সাদীর জীবনী ‘‘হায়াতে সাদী’’।
এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল-আজও মনে পড়ে (গল্প গ্রন্থ), জিন্দাপীর আলমগীর(জীবনী গ্রন্থ), মজার গল্প (নৈতিক কথামূলক), গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস (গদ্যগ্রন্থ), পরলোক প্রসঙ্গে ‘মরণের পরে’ (২য় খন্ড), শের সংহার কাব্য(কাব্যগ্রন্থ), সত্যের সন্ধান, ভাবিবার কথা, খোদাপ্রাপ্তির সোজাপথ ও দাদুর দফতর।
তাঁর উদ্যোগে ১৯১০ সালে ‘যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বাঙালী মুসলমানদের প্রথম সাহিত্য সংগঠন। এই সাহিত্য সংগঠনের নিকট হতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তীকালে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’ ১৯১২ সালে ও ‘মুসলিম সাহিত্য সমা ‘ ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি কলকাতার পারিজাত সাহিত্য কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বি.এ. ক্লাশের ছাত্র থাকাকালে ১৯১৪ সালে তিনি ‘মাসিক মোহাম্মদীর’ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা হতে প্রকাশিত ‘মাসিক বঙ্গনূর’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ‘নদীয়া সাহিত্য সভা’র পক্ষ হতে ‘সাহিত্যরত্ন’ উপাধি লাভ করেন।
১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিলিটারী কনভয়ের নীচে চাপা পড়ায় তাঁর পা ভেঙে যায়। ১৯৫৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমীতে ৩০ টি মুদ্রিত ও কয়েকটি অমুদ্রিত গ্রন্থ দান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ঐ সনেই তিনি কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।
১৯৬১ সালে ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমানের মৃত্যুতে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৬২ সালের ৭ মে ইন্তিকাল করেন। পরদিন ৮ মে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমীতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী(১ম খন্ড কাব্যগ্রন্থসমূহ) বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশিত হয়।
..................................................................................................................
\r\n\r\n
গোলাম মোস্তফাঃ একজন মুসলিম কবির প্রতিকৃতি
কবি গোলাম মোস্তফা বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক। তিনি বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমান জেলা) শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাজী গোলাম রব্বানী। মাতার মোসাম্মাৎ শরীফা খাতুন। তাঁর দাদা কাজী গোলাম সারওয়ার। গোলাম মোস্তফার পূর্বপুরুষ ছিলেন মুগল যুগে বিচার বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা। তাদের উপাধি ছিল কাজী। সেই সূত্রে গোলাম মোস্তফার পিতা, পিতামহ কাজী উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু গোলাম মোস্তফা নিজে কোন অর্জিত সম্মান বা প্রচলিত কৌলিণ্য প্রথার যৌক্তিকতা খুঁজে না পাওয়ায় কাজী উপাধি গ্রহণ করেননি। বহুকাল পূর্ব থেকেই মনোহর পুরের কাজী পরিবার ছিল আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষাতে সুপণ্ডিত। কবি গোলাম মোস্তফার জন্মসাল নিয়ে একটু কথা আছে। তিনি নিজেই “আমার জীবন স্মৃতি” তে লিখেছেন: ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় দুই বছর কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিলো সম্ভবত ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, বাংলা তারিখ ছিলো ১৩০৪ সালের ৭ ই পৌষ রবিবার।কবির স্মৃতিকথা থেকেই আমরা কবির সঠিক জন্ম সন, বাংলা মাসের হিসেব এবং দিনের নাম রবিবার পাই। কিন্তু ইংরেজি মাসের হিসেবটা উহ্য থেকে যায়। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখটা পরিবার থেকে সংরক্ষণ করা হয়নি। কবির পিতার দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে বড়– নামে এক কন্যা এবং কাজী গোলাম মোস্তফা ও কাজী গোলাম কাওসার নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তিনটি সন্তান তাঁরা যথাক্রমে কাজী গোলাম কুদ্দুস, মাজু এবং খুকি। কাজী গোলাম মোস্তফাই আমাদের প্রিয় কবি গোলাম মোস্তফা। এই পরিবারের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার নিবেকৃষ্ণ পুর গ্রামে। কবির মাতা ছিলেন একজন স্বভাব কবি। স্বভাব কবিত্ব ব্যক্তি মায়ের সাথে থেকে কবির মধ্যেও কবিত্ব ভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্নের পথিকৃত শিশুদের নিয়ে এমন শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী সিঞ্জিত লেখা যার কলমের ডগায় বেরিয়ে আসে, তিনিই ইসলামী রেনেসাঁর এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ স্বর কবি গোলাম মোস্তফা।
\r\nকৈশোর ও বাল্য জীবন\r\n\r\nকবির বাল্য জীবন নিজ গ্রাম মনোহর পুরেই কেটেছে। কুমার নদী বিধৌত মনোহরপুর গ্রামের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, সরল আতিথিয়তা বাৎসল্য গায়ে মেখেই কবি বেড়ে উঠে ছিলেন।তাঁর জন্মস্থান মুখরিত ছিল যমুনা, কুমার মধুমতি, চিত্রা, ভৈরব, ভদ্রা চন্দনা, নবগঙ্গা, হানু বারাসিয়া, মাথাভাঙ্গা আর কপোতাক্ষ প্রভৃতি সেকালের খরস্রোত নদীর কলতানে। বাংলাদেশে বোধকরি আর কোন জেলায় এত নদীর রূপালী ধারার মিলন ঘটেনি। এসব বহমান নদীর তীরে নারকেলÑখেজুর কুঞ্জ ঘেরা শ্যামল প্রকৃতি যে কোন ভাবুক মানুষের মনে সঞ্চার করে কাব্যকলার মাধুরি। এ গ্রামীন পাগলকরা সৌন্দর্যই শিশু গোলাম মোস্তফাকে ভাবুক করে গড়ে তোলে ও কবি হতে সাহায্য করে। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :
শারদ প্রভাত চাদিনীর রাত সুপ্তি নীরব ধরা\r\nআতট পূরতি সরসী সলিল পদ্ম পানায় ভরা।\r\nকলমী লতিকা ডাঁটায় ও পাতায় ছাইয়া ফেলেছে জল\r\nমাঝে মাঝে তার নানান রঙের ফুটেছে পুষ্পদল।
এই কবিতায় কবি তাঁর চারপাশের নদী প্রকৃতির এক অপূর্ব বর্ণনার মাধ্যমে কাব্যরস পিপাসুকে উপহার দিয়েছেন নিটোল ছন্দ সৌকর্ষ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তা। কবিতার মতই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক মোহনীয় রূপ গায়ে মেখেই কবির শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত হয়। গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্যই তাঁর প্রাণে প্রথম কবিত্বভাব জাগিয়েছিলো। বস্তুত এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশই ছিল A meet nurse for a Poetic Child তাইতো পরিণত বয়সে তিনি লিখতে পেরেছিলেন:
নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি গান\r\nছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন প্রাণ।\r\nএ বিশ্বের সবই আমি বাসিয়াছি ভালো\r\nআকাশ বাতাস জল রবি শশী তারকার আলো।
প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজ সরল মাটির গন্ধে বেড়ে উঠার কারণেই সারা জীবন কবির মধ্যে সরলতাবোধ, সম্প্রীতিবোধ, আতিথিয়তাবোধ, মানবতাবোধ তার ব্যক্তিত্বের সাথে মিশে ছিলো। কবি হতে পেরেছিল উদার ও সরলতার প্রতিক এক মানসভূমি। কিন্তু কবির বেড়ে ওঠার জীবনটা মোটেই স্বচ্ছন্দ ছিলো না। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তাকে সাফল্যের মুখ দেখতে হয়েছিল। কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন: আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফার হাতের লেখার মত তাঁর ভাষাও অতি সুন্দর ও মিষ্টি স্বচ্ছন্দ গতি একটুও বাধে না কোথাও। কিন্তু তাঁর জীবন অত সহজ ও স্বচ্ছন্দ ছিল না। তাঁর জ্ঞান পিপাসিত প্রতিভার তরীকে উজান পথে অনেক ঝড় ঝাপটার মুকাবিলা করে বেয়ে নিতে হয়েছে লক্ষ্যস্থলে। শৈশব কালেই সৎমা থাকায় স্বভাবতই বাপের অবহেলায় কখনও মামার বাড়ি কখনও নিজের বাড়ি থাকতে হতো। আর্থিক অনটনে শৈশবেই টিউশনি করতে হতো, তারপরও ক্লাসে ফাষ্ট হয়েছেন। তার জীবনকে সংগ্রামের মধ্যে পরিচালিত করার মাধ্যমে শৈশবের সে সংগ্রাম তিনি কাটিয়ে উঠে ছিলেন। জীবনকে সাজিয়েছিলেন বর্ণাঢ্যতায়। নিজ যোগ্যতা ও মেধার কারিশমায় চলমান জীবনকে করেছিলেন উচ্চকিত দ্যুতিময়।
\r\nশিক্ষা জীবন ও মানস গঠনঃ\r\n
শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগের কারণেই মাত্র চার বছর বয়সেই পিতা মুন্সি গোলাম রব্বানীর কাছে কবির লেখা পড়ার হাতে খড়ি হয়েছিল। মনোহরপুরের পাশ্ববর্তী দামুদিয়া গ্রামের পাঠ শালাতে প্রথমে শিশু গোলাম মোস্তফাকে ভর্তি করা হয়। এখানে কিছুদিন লেখাপড়ার পর কবিকে নিকটবর্তী ফাজিলপুর গ্রামের পাঠ শালাতে ভর্তি করা হয়।\r\nফাজিলপুর পাঠ শালায় দুই বছর লেখাপড়া করবার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় শৈলকুপা হাই স্কুলের নীচের শ্রেণীতে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে পুরস্কৃত হন।\r\nশৈলকুপা স্কুল থেকেই তিনি ১৪১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খুলনার দৌলতপুর কলেজ হতে ১৯১৬ সালে আই. এ. পাশ করেন। এরপর গোলাম মোস্তফা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের রাজধানী কোলকাতা গমন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি কোলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ঐ কলেজ থেকে ঐ বছর যশোরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩Ñ১৯৬৪ খৃ.) বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ. পাশ করেন। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪Ñ১৯৫০ খৃ.)ও রিপন কলেজে পড়াকালীন সময়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন।\r\nআর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাঁর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করার পর ১৯২২ সালে গোলাম মোস্তফা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. পাশ করেন। এরপর আর কোন একাডেমিক ডিগ্রী অর্জন না করলেও সারা জীবন শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা অর্জনের পেছনেই ব্যয় করেছেন।
\r\nউনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে যে সময়ের বৃত্তে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম হয়, সেই সময়টা বাঙালী মুসলমানদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়Ñকারণ এই পর্বে অন্তত: তিনটি ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতির মাত্রা ছিল অত্যন্ত দ্রুত। এগুলো হল: শিক্ষা, রাজনীতি এবং আর্থিক। অবিভক্ত ভারতের বাংলা প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের কোন প্রভাব ছিল না।বিশ ও ত্রিশ দশকে কৃষক প্রজাপার্টির অভ্যূদয় (১৯১৯ খৃ.), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মুসলমান নেতাদের বিজয় (১৯৩৭ খৃ.) এসবই বাঙালী মুসলমানদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। মুসলমানদের মধ্যে এর আগে যাঁরা নেতৃত্ব পদে ছিলেন তাঁরা প্রধানত অবাঙালী। বাঙালী সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে সমন্বয়ের সুযোগ ছিলো, বরাবরই তাঁরা তা এড়িয়ে গেছেন। বরং বাঙালী মুসলমানদের উপর ইসলামী সংস্কৃতির নামে যা চাপানোর চেষ্টা করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে আরব ও পারস্য দেশের সংস্কৃতি। এ সময়কালে বাঙালী মুসলমানরা বহু মাসিক অর্ধমাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা প্রকাশে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং সীমিত পর্যায়ে হলেও তাতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদীতার স্থান পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটই কবি গোলাম মোস্তফার বেড়ে ওঠা এবং তাঁর মানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।\r\n\r\nচাকুরি জীবনঃ\r\n
বি.এ পাস করার পর তিনি ১৯২০ সালে ব্যারাকপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই স্কুলে থাকা অবস্থায় তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি ব্যারাকপুর স্কুল থেকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে বদলি হন। সেখানে তিনি একটানা নয় বছর শিক্ষকতা করার পর কলিকাতা মাদ্রাসায় বদলী হন এবং এক সময় তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত একমাত্র কবি গোলাম মোস্তফা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান শিক্ষক বালিগঞ্জ স্কুলের উক্ত পদে আসীন হননি। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে একজন উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক।তৎকালে কলিকাতার কোন হাই স্কুলে গোলাম মোস্তফাই ছিলেন প্রথম মুসলমান হেডমাস্টার। তখনকার দিনে এই সম্মান খুব কম মুসলমানই পেয়েছেন। সেখান থেকে কবিকে বদলী করা হয় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। এরপর ১৯৪০ সালে তাঁকে বাকুড়া জেলা স্কুলে বদলী করা হয়। এ সম্পর্কে কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন: এরপর আব্বা বাঁকুরায় জেলা স্কুলে বদলি হলেন। কলকাতা মানুষের সমুদ্রের মাঝে যেমন জ্ঞানের মুক্তা কুড়াবার আনন্দ পেয়েছেন, তেমনি হুগলীতে নদীর স্রোত বইয়েছেন বিশ্বনবীর প্রবাহে। দেশের বাড়িতে পেতেন সমতার মমতার বিস্তার। বাঁকুড়ার পাহাড় পর্বত ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে কবিকে। সুষনিয়া পাহাড়ে পিকনিকে গিয়ে চূড়ায় বসে কবিতা লেখেন, গান করেন। সেখান থেকে ফরিদপুর বদলি হয়ে যান।\r\n১৯৪৬ সালে তাকে সর্বশেষ ফরিদপুর জেলা স্কুলে বদলী করা হয়।ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকেই তিনি ১৯৫০ সালে দীর্ঘ ত্রিশ বছর একটানা শিক্ষকতার মত মহান পেশার দায়িত্ব পালন করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।তিনি পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির সচিবরূপে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে কবি গোলাম মোস্তফা অবসর গ্রহণ করেন এবং নিজের খরিদ করা বাড়ি ঢাকার শান্তিনগরে ১১৮, মোস্তফা মঞ্জিলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন।\r\nএকান্ত নিবিড়ভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করার জন্যই তিনি নির্ধারিত সময়ের তিন বছর আগেই শিক্ষকতার মহান পেশা থেকে অবসর নেন।
\r\nসাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা ঃ\r\n
কবিতা কবির কল্পনা, কবিতা কবির শৈল্পিক উচ্চারণ। কবিতার শিল্পরূপ থেকেই কবির সময়চেতন সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, মিলন বিরহ, স্বপ্ন দ্রোহ ইত্যাদির শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ। একই কবিতায় সব রকম অনুভূতি থাকে না, কারণ কবির কবিতায় বিশেষ সময়ে বিশেষ চেতনায় প্রকাশিত হয় বিশেষ বিশেষ ভাব। কবি কল্পনায় ধরা পড়ে সেই ভাব, আপন কবিতার ভাষায় কবি তাকে শিল্পরূপ দেন।
\r\nকবি কল্পনার উৎস তাই সমাজ, এবং প্রকাশভঙ্গিতে থাকে তার সময়চেতনা। কবিতায় কবি যা বলতে চান তা পরিবেশ ও অবস্থানগত দ্বিধার কারণে কিংবা যে সমাজ কবি চান, আর যে সমাজে কবি বাস করেন, তার মধ্যের ব্যবধানে অতৃপ্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করেন, যা আঙ্গিকগত উৎকর্ষ পায়।\r\nভাব আর রূপের এক অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য থেকে জন্ম নেয় একটি কবিতা। এ কবিতা কবি রচনা করেন আপন মহিমায়। জীবনের সত্যকে তিনি যেভাবে আপন সত্ত্বায় ধারণ করেন, সেভাবেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় কবিতার প্রকাশভঙ্গি, শৈলী ও রূপ। সৃষ্টিসম প্রজ্ঞা, জৈবিক ক্ষমতা, সমাজ ও সময়ের প্রভাবের সমন্বয়ে কবির মর্মভূমি কবিতা নির্মাণে অদৃশ্য শক্তির মত কাজ করে যায় এমনকি কবির অজ্ঞাতসারে। তেমনি নিতান্ত অজ্ঞাতে অন্তরালে শিশু বয়সেই কবির মধ্যে কাব্য চিন্তার উন্মেষ ঘটে। পিতা, পিতামহের পুঁথি পাঠ , বিয়ের দাওয়াত রচনা ইত্যাদি থেকে তাঁর মধ্যে কবিত্ব ভাব জেগে ওঠে। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত কবি গোলাম মোস্তফার অবদান বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত।গোলাম মোস্তফা ছিলেন মূলত: কবি। কবি আমার জীবন স্মৃতিতে লিখেছেনÑ আমার বেশ মনে পড়ে, আমার কাব্য জীবনের প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ সালে। তখন আমি শৈলকুপা হাইস্কুলে পড়ছি। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেন একটা কাব্যিক ভাব আমার মধ্যে এলো।\r\n১৯১১ সালে কবি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি কাটানোর পর তাঁর এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি কবিতায় রচনা করেন। এটিই তাঁর প্রথম রচনা । কবিতাটি হল :
এস এস শীঘ্র এস ওহে ভ্রাতধন\r\nশীতল করহ প্রাণ দিয়া দরশন।\r\nছুটি ও ফুরাল স্কুল ও খুলিল,\r\nতবে আর এত দেরি কিসের কারণ।
পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতার নাম আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার (১৯১৩ খৃ.)। কবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ সম্পাদিত সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী তে ১৯১৩ সালে কবিতাটি ছাপা হয়। কবিতাটির রচনা ও প্রেক্ষাপটের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন,পারিপার্শি¦ক পরিবেশ এবং বন্ধুবর্গের প্রেরণায় গোলাম মোস্তফার অবরূব্ধ কাব্যপ্রবাহ ঝর্ণাপ্রবাহের মত বাইরে আত্মপ্রকাশ করল। সেই সময়ে ইউরোপ ভূÑখন্ডে বলকান যুদ্ধে তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমস্ত মুসলিম জাহানে একটা বিপর্যয়তার ছায়া নেমে এসেছিলো। এমন সময়ে হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, কামাল পাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে আদ্রিয়ানোপল পুনরূদ্ধার করেছেন। এই খবরে স্বজাতি বৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার নাম দিয়ে এক রাতের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। এরপর কবিতাটি তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মাদিতে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটি ছিলো এরূপ :
আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া\r\nধরায় আসিলো নামিয়া।
সেই সময় কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি সবই ছিলো নতুন। তাই এই কবিতাকে কেন্দ্র করে পাঠক মহলে একটা ব্যাপক আলোচনার ঝড় বয়ে গেল।বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নব ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৭ খৃ.), আল এসলাম (১৯১৫ খৃ.), সাধনা ( ১৯১৬ খৃ.), সহচর ( ১৯১৫ খৃ.), সওগাত ( ১৯১৭ খৃ.), মাসিক মোহাম্মদী (১৯১৬ খৃ.), ইসলাম দর্শন (১৯২৭ খৃ.), মাহে নও সত্য বার্তা (১৯৩৮ খৃ.), মোয়াজ্জিন ( ১৯৩৮ খৃ.) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় এসব কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। আল এসলাম (২য়ভাগ, ১৩২৩ সাল), (তয় ভাগ, ১৩২৪ সাল), (৪র্থ ভাগ, ১৩২৫ সাল), (৫ম ভাগ, ১৩২৬ সাল) পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
\r\nমৌলিক রচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। সমসাময়িক The Musalman, The star of India, The Morning News, The Pakistan Observer, The Down প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলো পাঠ করলে ইংরেজী ভাষার উপরও যে কবির যথেষ্ট দখল ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।\r\nMorning News তাঁর সর্ম্পকে মন্তব্য করেছিলো He is also a fine prose writer both in Bengali and English. বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জাগরণের পথিকৃতদের অন্যতম কবি গোলাম মোস্তফা জীবনের প্রথম থেকেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর লেখনি চালনা করেন।\r\n
তিনি নিজেই লিখেছেন: “যে যুগে আমার জন্ম সে যুগ বাংলার মুসলমানের অবক্ষয়ের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিলো কোন স্বাতন্ত্র, না ছিলো কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান ধারণা ও আশা আকাংক্ষা রূপায়িত হয় তাঁর মাতৃভাষার মধ্যে। সেই হিসেবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলিমের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও, আমার মনে জেগেছিলো আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দূর্জয় আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদে নয়Ñসহজ ভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ।”
\r\nউক্ত দৃষ্টি ভঙ্গিকে সামনে রেখেই ১৯১৩ সালের প্রথম লেখা প্রকাশ থেকে তাঁর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরকাল তাঁর লেখালেখির গতি অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুতোষ সাহিত্য, গান, জীবনী, অনুবাদ সাহিত্য লিখেছেন। পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক গোলাম মোস্তফা তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কল্যাণেই শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্বের সংগে ছিলেন নিবিড়ভাবে পরিচিত। এ কারণেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে বহু স্মরণীয় শিশু ও কিশোরÑকবিতা রচনা। তাঁর রচিত আলোকমালা (১৯৫৩ খৃ.), পথের আলো (১৯৫৩ খৃ.), নতুন আলো (১৯৫৪খৃ.) এবং আলোকমঞ্জুরী (১৯৫৪খৃ.) সিরিজগুলো শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান।\r\n\r\nধর্ম বিশ্বাসই গোলাম মোস্তফার চিন্তার ভিত্তিভূমি। জগত ও জীবনের প্রতিটি সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রগাঢ় ইসলামী ভাবধারায় সম্পৃক্ত।গোলাম মোস্তফার সর্বশ্রেষ্ট অবদান বিশ্বনবী (১৯৪২ খৃ.) বহুল সমাদৃত। তাঁর লেখালেখির পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত\r\n\r\nদুইটি উপন্যাস ঃ\r\n
১. রূপের নেশা (উপন্যাস, ১৩২৬ খৃ.), ২. ভাঙ্গা বুক (উপন্যাস, ১৯২১ খৃ.)।
\r\nআটটি মৌলিক কাব্যঃ\r\n
১. রক্ত রাগ (কবিতা, ১৯২৪ খৃ.), ২. খোশরোজ (কবিতা, ১৯২৯ খৃ.), ৩. সাহারা (কবিতা, ১৯৩৫ খৃ.), ৪. হাস্না হেনা (কবিতা, ১৯২৮খৃ.), ৫. কাব্যকাহিনী (কবিতা, ১৯৩৮ খৃ.), ৬. তারানা ই পাকিস্তান (কবিতা, ১৯৫৬ খৃ.), ৭. বনি আদম, প্রথম খণ্ড (কবিতা, ১৯৫৮ খৃ.), ৮. আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি (কিশোর কবিতা, ১৯৮০ খৃ.)।
\r\n৫ টি কাব্যানুবাদ ও ১টি গল্প সংকলনঃ\r\n
১. মোসাদ্দস ই হালী (অনুবাদ কবিতা, ১৯৪১ খৃ.), ২. কালাম ই ইকবাল (কবিতা, ইকবাল কাব্যের অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.), ৩. শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা, ১৯৬০ খৃ.), ৪. জবাব ই শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা, ১৯৬০ খৃ.), ৫. আল কুরআন (বাংলা কাব্য অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.), জয় পরাজয় (গল্প, ‘রাসাইলু ইখওয়ানুস্ সাফা ১৯৬৯ খৃ. ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।
\r\n৩টি কাব্য সংকলন ঃ\r\n
১.বুলবুলিস্তান (কাব্য সংকলন, ১৯৪৯ খৃ.), ২. কাব্য গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (কবিতা আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১৯৭১ খৃ.), ৩. কাব্য সংকলন (কবিতা সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত, ১৯৬০ খৃ.)।
\r\n৪টি জীবনী গ্রন্থঃ\r\n
১.বিশ্বনবী (জীবনী, ১৯৪২ খৃ.), ২. মরু দুলাল (জীবনী, ১৯৪৮ খৃ.), ৩. বিশ্ব নবীর\r\nবৈশিষ্ট্য (জীবনী, ১৯৬০ খৃ.), ৪. হযরত আবুবকর (জীবনী, ১৯৬৫ খৃ.)।
\r\n২টি ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থঃ\r\n
১. ইসলাম ও জিহাদ ( ১৯৪৭ খৃ.), ২. ইসলাম ও কমিউনিজম (ধর্ম, ১৯৪৯ খৃ.)।
\r\n৩টি রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ:
১. ইতিহাস পরিচয় (রাজনীতি, পাঠ্য, ১৯৪৭ খৃ.); ২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (রাজনীতি, তা: বি:)। ৩.অবিস্মরণীয় বই, (ইতিহাস সম্পাদনা, ১৯৬০ খৃ.);
\r\n১টি প্রবন্ধ সংকলন:
আমার চিন্তাধারা (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬২ খৃ.), ও
\r\n১টি গানের সংকলন:
গীতি সঞ্চয়ন (গান, ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত: ১৯৬৫ খৃ., ১৯৬৮ খৃ. )।
\r\nপাঠ্য পুস্তক :
আলোক মঞ্জরী, (১৯৫৩ খৃ.), পথের আলো (১৯৫৩ খৃ.), নতুন আলো (১৯৫৪খৃ.), ইসলামী নীতিকথা (১৯৫৩ খৃ.), মনিমুকুর, ইতিহাস পরিচয় (১৯৪৭ খৃ.), ইতিকাহিনী, নতুন বাংলা ব্যকরণ, নতুন ব্যকরণ, মঞ্জু লেখা ইত্যাদি।
\r\nগ্রন্থসমূহ থেকেই বোঝা যায় কবি গোলাম মোস্তফা শুধু একজন কবিই ছিলেন না, সাহিত্যের নানা শাখায় ছিলো তাঁর স্বতস্ফূর্ত বিচরণ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন চৌকষ লেখক। তাঁর অবদান সাহিত্যের নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে আছে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্য, জীবনী, গবেষণা, পাঠ্যপুস্তক, চিন্তাধারাসহ সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁর অবদানঅপরিসীম। তিনি তাঁর কাব্যের বিরাট একটা অংশ, গদ্যের বেশির ভাগ জুড়ে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করে গেছেন। ইসলামী ঐতিহ্য চেতনায় নিজেকে ব্যপ্ত রেখেছেন। কবি গোলাম মোস্তফার প্রতিভা শুধু লেখনি মুখেই প্রকাশ পায়নি, তাঁর সাহিত্য রচনায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শেষ অবদান হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] এর জীবনী। একজন কবি, একজন সাহিত্যিক, একজন প্রবন্ধকার, একজন জীবনীকার, একজন উপন্যাসিক, একজন গীতিকার, সর্বোপরি একজন লেখক হিসেবেএখানেই তিনি সার্থক।\r\n
তাঁর রচিত শিশুদের মন মাতানো অসংখ্য ছড়া/কবিতা ইত্যাদি রয়েছে-
ক. আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,\r\nওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
............................................
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,\r\nঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।(কিশোর)।
খ. খুকুমনি জনম নিল যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখতে এল কতই খুশী ভরে। (কিশোর)।
গ. এই করিনু পণ মোরা এই করিনু পণ\r\nফুলের মতো গড়ব মোরা মোদের এই জীবন।\r\nহাসব মোরা সহজ সুখে গন্ধ রবে লুকিয়ে বুকে\r\nমোদের কাছে এলে সবার জুড়িয়ে যাবে মন। (শিশুর পণ)।
ঘ. নুরু, পুশি, আয়েশা, শফি সবাই এসেছে\r\nআম বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।\r\nরাঁধুনিদের শখের রাঁধার পড়ে গেছ ধুম,\r\nবোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।
*****************************
ধূলোবালির কোর্মা-পোলাও আর সে কাদার পিঠে,\r\nমিছিমিছি খেয়া সবাই, বলে- বেজায় মিঠে।\r\nএমন সময় হঠাৎ আমি যেই পড়েছি এসে,\r\nপালিয়ে গেল দুষ্টুরা সব খিলখিলিয়ে হেসে। (বনভোজন)।
বিটিভির এক সময়ের জনপ্রিয় ‘নতুন কুঁড়ি’র সূচনা সঙ্গীত কবির কিশোর কবিতা হতেই নেওয়া হয়েছে।
কবি গোলাম মোস্তফা আমাদের সকলের মনমত করে সূরা ফাতিহার ছন্দোবদ্ধ ভাবানুবাদ লিখেছেন,
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি\r\nবিচার দিনের স্বামী।\r\nযত গুণগান হে চির মহান\r\nতোমারি অন্তর্যামী।
তাছাড়া তাঁর লেখা হামদ, নাত আমাদের দেশের ছেলে বুড়ো সকলের প্রিয়।
তাঁর প্রকাশিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে রক্তরাগ, হাস্নাহেনা, খোশরোজ, সাহারা, কাব্যকাহিনী, এবং অনুবাদগ্রন্থ মুসাদ্দাসই হালী, তারানা ই পাকিস্তান, বনি আদম, অনুবাদ কাব্য-আল কুরআন, কালামে ইকবাল ও শিকওয়াও জবাব ই শিকওয়া এবং কবিতা সংকলন বুলবুলিস্তান। এছাড়া লিখেছেন ‘বিশ্বনবী’র মত পাঠক নন্দিত বিশালাকার গদ্য গ্রন্থ। তিনি কবি আল্লামা ইকবালের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি নজরুল ইসলামকে নিয়ে এ ছড়াটি লিখেছেন-
কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গেছিলাম
ভায়া গান গায় দিনরাত
সে লাফ দেয় তিন হাত
প্রাণে হর্ষের ঢেউ বয়
ধরার পর তার কেউ নয়।
তিনি বাংলা একাডেমী, টেক্সট বুক বোর্ড, করাচীর বুলবুল একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি(১৯৪৯), পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডি এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন।
১৯৬০ সালে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব, প্রেসিডেন্ট পদক ও আরো পাঁচ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার লাভ করেন। ঐ ১৯৬০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৬১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানী লেখকবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।
১৩ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমাদের প্রাণপ্রিয় এই মহান কবি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর রূহের মাগফিরাত দিন।
\r\n\r\n
বিদ্রোহী শাহজাদা
ছোটটো একটি গ্রাম। তাও আবার আমাদের এই বাংলাদেশে নয়। একেবারে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার অজপাড়াগাঁয়ে। চারদিকে ধান কাউনের উম উম গন্ধ। পাখ-পাখালির কিচির মিচির আওয়াজ। সন্ধ্যায় শোনা যায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝাঁঝাল ডাক। কি সুন্দর তাই না? এই গ্রামের মানুষ আবার লেটো গান ভালবাসতো। একদিন রাতে তারা ‘লেটো’ গানের আসর বসালো। আশ-পাশের বিশ গ্রামের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে গান শুনতে!
গানতো নয়, লড়াই! পুরোপুরি দুই দলের লড়াই। তবে গোলা বন্ধুক দিয়ে নয়, কবিতা দিয়ে। কি মজার কান্ড বলতো। তুমুল লড়াইয়ের পর এক পক্ষ হারে হারে অবস্থা ঠিক তখনি ঐ দলের এক পুঁচকে ছেলে লাফ দিয়ে উঠলো। এই ধরো তোমাদেরই মত বয়স বা তারও কম। হাত পা নাচিয়ে মাথার চুল দুলিয়ে গান শুরু করলো। এক এক করে বিপক্ষ দলের সব কটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। কি তাজ্জব ব্যাপার। ঐ অতটুকু ছেলে এতকিছু জানে কারোরই বিশ্বাস হয় না। সবারই মনে উঁকিঝুঁকি মারছে নানা প্রশ্ন। এ শাহজাদা কোত্থেকে এল? কি তার পরিচয়? শাহজাদাটি কিন্তু বিপক্ষ দলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হলো না। সে নিজেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিপক্ষ দলকে হারিয়ে দিলো। সমস্ত আসর উল্লাসে ফেটে পড়ল। পুচকে শাহজাদাটি ততক্ষণে মানুষের মাথার উপর পুতুলের মত নাচছে। দলের সরদার জিতে যাওয়ার আনন্দে বাগ বাগ হয়ে জড়িয়ে ধরলেন শাহজাদাকে। বললেন-
‘ওরে আমার ব্যাঙাচি
বড় হয়ে তুই একদিন সাপ হবি।’
সরদারের কথা কিন্তু ঘটেছিল, সে খুউব বড় কবি হয়েছিল। কি তোমরা পরিচয় জানার জন্য উসখুস করছো তাই না? অবশ্য করার কথা। তবে এসো তোমাদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই-তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত এবং প্রিয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি আমাদের জাতীয় কবি।
১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। চুরুলিয়া গ্রামটি আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া ব্লকে অবস্থিত। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। তার বাবা ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম| তারা ছিলেন তিন ভাই এবং বোন। তার সহোদর তিন ভাই ও দুই বোনের নাম হল: সবার বড় কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন, বোন উম্মে কুলসুম। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল \"দুখু মিয়া\"।
তোমরা হয়তো ভাবছ শাহজাদাদেরতো হাতী শালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি কত কিছু থাকে, এ শাহজাদাটিরও নিশ্চয়ই আছে। আসলে এ শাহজাদার এসব কিছুই নেই। বরং বলা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত, একেবারে মিসকীনি হালত। কিন্তু হলে কি হবে? তাঁর মনটাতো আর মিসকিন নয়, একেবারে শাহজাদার শাহজাদা। ঐ যে তোমরা শুনছো না পাতালপুরির ঐ ঘুমন্ত শাহজাদার কথা। সেই যে রূপার কাঠি আর জিয়ন কাঠির পরশে রাজকন্যার ঘুম ভাঙলো! আমাদের আজকের শাহজাদা সেই পাতালপুরীতে যেতে চান কিন্তু ঐ রকম ঘুমাতে না, সবকিছুকে ভেঙে চুরে নিজের হাতের মুঠোয় নেবার জন্য। যেমন তিনি বলেছেন-
পাতাল ফুঁড়ে নামবো আমি
উঠবো আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগত দেখব আমি
আপনা হাতের মুঠোয় পুরে।
মাত্র আট বছর বয়সে আব্বা মারা যাওয়ায় সংসারের হাল ধরতে হয় তাঁকে। এ জন্য লেখাপড়ার ইতি টেনে ঐ বয়সেই কখনো মসজিদের ইমামতি, কখনো মক্তবের শিক্ষকতা করে সংসার চালাতে থাকেন। কিন্তু যারা চিরবিদ্রোহী তাঁরা চায় স্বাধীন জীবন। গ্রাম হতে চলে এসে আসানসোল শহরে রুটির দোকানে চাকরি নেন। কষ্টের কথা ছড়ায় বলতেন এভাবে-
মাখতে মাখতে গমের আটা
ঘামে ভিজতো আমার গা’টা।
এখান হতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি হন। এরপর ভর্তি হন রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল হাই স্কুলে। যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র ঠিক সেই সময়েই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই হাবিলদার হন। এইখান হতেই তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। পত্র-পত্রিকায় প্রচুর কবিতা ছাপা হতে থাকে তাঁর। ১৯১৯ সালে ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ শেষ হয়। দেশে ফিরেই লিখেন বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’। কি পড়নি-
বল বীর-
বল উন্নত মম শির।
হ্যাঁ এই কবিতা আমাদের কবি শাহজাদাকে এক রাতের মধ্যেই বিদ্রোহী শাহজাদাতে পরিণত করে। এরপর দু’হাতে লিখতে থাকেন অজস্র লেখা। এ লেখাগুলোর প্রায় সবগুলিই ছিল অন্যায়, অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে। সে সময়কার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি শক্ত হাতে কলম ধরেন। তাঁর কলমের ডগা দিয়ে বেরুতে থাকে লকলকে আগুন। তিনি লেখেন-
এদেশ ছাড়বি কিনা বল
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।
আরও লেখেন ‘ভাঙার গান’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘প্রলয় শিখার’ মত বিদ্রোহী কাব্য। ইংরেজ সরকার রেগে গেলেন, কবিকে ঢোকালেন জেলে। কিন্তু জেলে ঢোকালে কি হবে? তিনি সেখান থেকেই অন্যান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোষণা করলেন-
এই শিকল পরা ছল মোদের
এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবো রে বিকল।
তিনি আরো বললেন-
কারার ঐ লৌহ–কপাট\r\nভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত –জমাট\r\nশিকল –পূজার পাষাণ –বেদী!\r\nওরে ও তরুণ ঈশান!\r\nবাজা তোর প্রলয় –বিষাণ ! ধ্বংস –নিশান\r\nউঠুক প্রাচী –র প্রাচীর ভেদি’।। ইত্যাদি।
গানের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী শাহজাদা সবার ওপরে। গানের মুকুটহীন এই সম্রাট এর রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা অন্য সকলের চেয়ে বেশি।
তিনি ছোটদের মনের কথাটা খুলে বলতে পারতেন। আর কেউ তাঁর মত সুন্দর করে বলতে পারেন নি। তাই তিনি সবার মত ছোটদেরও আত্মার আত্মীয়, একান্ত আপনজন। যেমন-
\"আমি হব সকাল বেলার পাখি\r\nসবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি।\r\n\"সুয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,\r\n\'হয়নি সকাল, ঘুমোও এখন\', মা বলবেন রেগে।
\r\nবলব আমি- \'আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাক,\r\nহয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাক\'?\r\nআমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে ?\r\nতোমার ছেলে উঠবে মা গো রাত পোহাবে তবে।\r\n
‘খুকু ও কাঠ বেড়ালী’ ছড়াটি কি তোমাদের মনে পড়ে? হ্যাঁ! কি যেন-
কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?\r\nগুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?
\r\nবেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও-\r\nডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,\r\nখাও একা পাও যেথায় যেটুক!\r\nবাতাবি-নেবু সকলগুলো\r\nএকলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!\r\n\r\nতবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?\r\nছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!
‘ভোর হলো’ কবিতাটি তোমাদের সবারই একান্ত প্রিয়, কি বলো? সবার মুখস্ত আছে নিশ্চয়ই-
ভোর হল, দোর খোল,\r\nখুকুমণি ওঠ রে।
ঐ ডাকে জুঁই শাখে,\r\n‘ফুল খুকী ছোট রে।
খুলি’ হাল তুলি’ পাল\r\nঐ তরী চলল।
এই বার এই বার\r\nখুকু চোখ খুলল।
এত বড় কবি হয়েও তিনি ছিলেন খুব হাসি-খুশী ও রসিক মানুষ। হো হো করে অট্টহাসি হাসতেন। ছোটরা যে নানা দাদার সাথে হাসি তামাশা করে কবি সেটা তাঁর ‘খাঁদু দাদু’ কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেছেন।
যেমন-
অমা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং।
ওঁর নাকটাকে কে করল খাঁদা র্যাঁদা বুলিয়ে?
চামচিকে ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গরুর পিঠে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অমা! আমি হেসেই মরি নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং
ওঁর খ্যাদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় ‘টু’।
ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এরাম! ওয়াক থুঃ।
কাছিম যেন উপুর হয়ে ছাড়িয়ে আছেন ঠ্যাং।
অমা! আমি হেসেই মরি, নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং।
দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়- নাক\r\nঘুম দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজতো সাতটা শাঁখ।\r\nদিদিমা তাই থ্যাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন!\r\nঅ মা! আমি হেসে মরি, ন্যাক ডেঙ্গাডেং ড্যাং।
বিয়ের মত খোশ খবর পেলে ছোটরা যে কি মজা পায়, নিজেরাই বিয়ে করার জন্য বায়না ধরে। ‘খোকার খুশী’ কবিতায় কবি সুন্দর করে ছোটদের মনের ভাবটা তুলে ধরেছেন-
কি যে ছাই ধানাই পানাই ,
সারাদিন বাজছে সানাই।
এদিকে কারুর গা নাই
আজিনা মামার বিয়ে!
বিবাহ! বাহ কি মজা
সারাদিন গন্ডা গজা
গপাগপ খাওনা সোজা
দেয়ালে ঠৈসান দিয়ে।।
এই কবিতারই শেষে বলেছেন-
সত্যি, কওনা মামা
আমাদের অমনি জামা
অমনি মাথায় ধামা
দেবেনা বিয়ে দিয়ে?
মামীমা আসলে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাহ! কি মজার খবর।
আমি রোজ করব বিয়ে।।
ওদিকে ‘খোকার বুদ্ধি’ কবিতা পড়লে তো হাসিতে দম আটকে আসতে চাইবে।
সাতটি লাঠিতে ফড়িং মারেন
এমনি পালোয়ান।
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লো সেদিন
আস্ত আলোয়ান!
ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বল? কি এর উচিত সাজা?
‘খোকার গল্প বলা’ কবিতাটাতো আরো মজার, আরো আনন্দের। বলতে গেলে তোমাদের জন্য এক থালা গরম সন্দেশ।
মা ডেকে কন, ‘ খোকন-মণি! গপ্প তুমি জান?
\r\nকও তো দেখি বাপ!’\r\n\r\nকাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ\r\n\r\nবললে খোকন, গপ্প জানি, জানি আমি গানও!’\r\n\r\nব’লেই ক্ষুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল-\r\n\r\n‘একদা এক হাঁড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!’\r\n
এই কবিতার অন্যত্র বলেছেন-
একদিন না রাজা-
হরিণ শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা
রাণী গেলেন তুলতে কলমি শাক
বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে-
হাতীর ম-মতন একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার করে।
‘পিলে পটকা’ কবিতাটিতেও প্রচুর হাসির খোরাক মিলে-
উটমুখো সে সুঁটকো হাশিম
পেট যেন ঠিক ভুটকো কাছিম।
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি-
ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি।
তিন কেনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচকা চোখে; হন্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোবনে ঢ্যাঙা!
নিট পিঠে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা।
কল্পনাপ্রবণ শিশুরা কল্পনায় সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি জমায়।
যেমন-
থাকব না’ক বদ্ধ ঘরে\r\nদেখব এবার জগৎটাকে\r\nকেমন করে ঘুরছে মানুষ\r\nযুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে\r\nছুটছে তারা কেমন করে,\r\nকিসের নেশায় কেমন করে\r\nমরছে যে বীর লাখে লাখে।\r\nকিসের আশায় করছে তারা\r\nবরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কবির এই সংকল্প কবিতাটি শিশু মনের চিরন্তন খোরাক। কবিতাটিতে শিশু মনের নানা কথা বলা হয়েছে, যা শিশুদের জন্য একান্ত আপন। কবিতাটির শেষ দু’লাইন হচ্ছে-
পাতাল ফেড়ে নামব আমি\r\nউঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,\r\nবিশ্বজগৎ দেখব আমি\r\nআপন হাতের মুঠোয় পুরে।
অন্যত্র ‘সাত ভাই চম্পা’ কবিতায় কবি লিখেছেন-
সপ্ত সাগর পাড়ি দেব আমি সওদাগর
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত-মধুকর।
সব কালের সব ধরনের শিশুদের ফলমূল চুরি করে খাওয়ার মত রোমাঞ্চকর অভ্যেস প্রচলিত আছে। আম, জাম, লিচু এগুলো তাদের কাছে লোভনীয়ও বটে। তবে এ সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে করা সম্ভব নয়, বিপদ আপদ এসে ঘাড়ে চাপে। সে কথাটি কবির ‘লিচুচোর’ কবিতায় অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।
বাবুদের তাল-পুকুরে\r\nহাবুদের ডাল-কুকুরে\r\nসে কি বাস করলে তাড়া,\r\nবলি থাম একটু দাড়া।
পুকুরের ঐ কাছে না\r\nলিচুর এক গাছ আছে না\r\nহোথা না আস্তে গিয়ে\r\nয়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে\r\nগাছে গো যেই চড়েছি\r\nছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা মড়াত করে\r\nপড়েছি সরাত জোরে।\r\nপড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,\r\nসে ছিল গাছের আড়েই।\r\nব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,\r\nধুমাধুম গোটা দুচ্চার\r\nদিলে খুব কিল ও ঘুষি\r\nএকদম জোরসে ঠুসি।
তাঁর ঝিঙে ফুল কবিতা অপূর্ব ছন্দে রচিত। ছোটরা যখন কবিতা পড়ে তখন তারা ছন্দের দোলায় দুলে ওঠে-
ঝিঙে ফুল। ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে
ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল
ঝিঙে ফুল----।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল।।
মোটকথা কবির ছিল একটা সুন্দর শিশু মন। যে মন দিয়ে তিনি বাংলার প্রতিটি শিশুর মনের কথা বুঝতে পারতেন।
কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কবি লেখার কাজ বেশিদিন চালাতে পারেন নি। কলম গেল বন্ধ হয়ে, মুখের ভাষাও আর শুনতে পেলনা কেউ। এরপরও দীর্ঘ ছত্রিশ বছর বেঁচে থাকার পর আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরের পিজি হাসপাতালে ১৯৭৬ সালের ২৯শে অগাস্ট তারিখে ‘বিদ্রোহী শাহজাদা’ সবার সাথে বিদ্রোহ করে সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ সবার যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমালেন। ইন্নালিল্লাহে ----------রাজিউন।
কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর তার কবর যেন মসজিদের পাশে হয়।
মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশেই তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। একবার এসে তোমাদের প্রিয় ‘বিদ্রোহী শাহজাদার’ কবরটি যিয়ারত করে যেও। কেমন?
\r\n\r\n
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন
আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই।
হ্যাঁ। এ জসীম উদ্দীনে কবিতার লাইন। জসীম উদ্দীনের কবিতার ধরনই আলাদা, স্বাদই আলাদা। তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ আষয় বিষয়, সাধারণ মানুষের জীবন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যিকার অর্থে এমনটি আর কোন কবি সাহিত্যিক করেন নি। যার কারণে বাংলার মানুষ তাদের এই প্রিয় কবিকে পল্লীকবি বিশেষণে বিশেষিত করেছে।
১৯০৩ সালে ১ জানুয়ারী ফরিদপুর সংলগ্ন তাম্বুলখানা গ্রামে মামার বাড়িতে জসীম উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাসও ফরিদপুর জেলা শহরের উপকন্ঠ গোবিন্দপুর গ্রামে। কবির পিতার নাম মৌলভী আনসার উদ্দীন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আনসারউদ্দীন সাহেব এর হাত দু’টি ছিল আজানুলম্বিত এবং মুখ ভরা ছিল চাপ দাড়ি। এতে করে কবির পিতাকে অসম্ভব সুপুরুষ ও সুদর্শন মনে হত। তা’ছাড়া সাদা ধুতি পরে, গায়ে পাঞ্জাবী চাপিয়ে যখন মাথায় টুপি দিতেন তখন তাঁকে আরো আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ মনে হত। সাদা পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন কবির পিতা গ্রামের এম.ই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।
জসীম উদ্দীনের লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয় তাঁর পিতা আনসার উদ্দীনের হাতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পার্শ্ববর্তী শোভারামপুরের আম্বিকা পন্ডিতের পাঠশালায়। এখান থেকে তিনি গ্রামের এম.ই স্কুলে চলে আসেন এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করেন। ঐ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালে তাঁকে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। আজন্ম রসিক জসীম উদ্দীন এ স্কুলে ভর্তি হবার পর স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল তা অত্যন্ত রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “সন্নাসীর ভক্ত হইয়া আমি পায়ে জুতা পরিতাম না। পাড়হীন সাদা কাপড় পড়িতাম। ক্লাসের ছাত্ররা প্রায় সবাই শহরবাসী। আামকে তাহারা গ্রাম্য ভূতের মতই মনে করিত। আমি কাহারো কাছে যাইয়া বসিলে সে অন্যত্র বসে। আমি শত চেষ্টা করিয়াও কাহারো সাথে ভাব জমাতে পারি নাই। আমি সঙ্কোচে পেছনের বেঞ্চে আমার চাচাতো ভাই নেহাজ উদ্দীনের সঙ্গে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিতাম। শিক্ষকেরা অন্য ছাত্রদের লইয়া কতো হাসি তামাসা করিতেন, এটা ওটা প্রশ্ন করিতেন। আমাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।”
বুঝতেই পারছো, কবির এ বর্ণনার মধ্যে তাঁর ছোটকালের ব্যথাতুর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শত অবহেলার মধ্যেও এ স্কুল হতেই কবি ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হতে ১৯২৪ সালে আই.এ এবং ১৯২৯ সালে বি.এ পাশ করেন। বিএ পাশ করার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন।
জসীম উদ্দীনের বাল্যকাল খুবই আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে কেটেছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, “আমাদের দু’খানা খড়ের ঘর। চারিধারে নলখাগড়ার বেড়া। চাটাইয়ের কেয়ার বা ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা আটকানো হয়। সেই ঘরের অর্ধেক খানিতে বাঁশের মাচা। মাচায় ধানের বেড়ি, হাড়ি-পাতিল থরে থরে সাজানো। সামনে সুন্দর কারুকার্য্ খচিত বাঁশের পাতলা বাখারী দিয়া নক্সা করা একখানি বাঁশ টাঙান।............এই ঘরের মেঝেতে সপ বিছাইয়া আমরা শুইয়া থাকিতাম।-----বাজান ঘর-সংসারের কাজ ফেলিয়া স্কুলে যাওয়া আসা করিতেন বলিয়া দাদা ছমির উদ্দীন মোল্লা বাজানের ওপর বড়ই চটা ছিলেন। বাজান তাঁহার একমাত্র পুত্র। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সংসারের সকল কাজ দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। কোনো কঠিন কাজ করিতে কষ্টসাধ্য হইলে তিনি বাজানকে খুব গালমন্দ করিতেন।” সত্যিই কবি সবদিক থেকে এদেশের মানুষের হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছির মানুষ ছিলেন।
কবির পিতা আনছারউদ্দীন সাহেব যেমন অত্যন্ত পরিপাটি ও ছিমছাম মানুষ ছিলেন, কবি ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ অগোছালো ছিলেন। বাল্যকালে কবি এক সাধুর শিষ্য হয়েছিলেন। সাধুর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে তিনি সাধুর জীবন গ্রহণের মানসে ঐ বাল্যকালেই পায়ে জুতা পরিতেন না, গায়ে জামা পরতেন না। শুধুমাত্র পাড়হীন একখন্ড সাদা ধুতির মত কাপড় দিয়েই সব কাজ চালাতেন। কখনো যদি জামা পরেছেন তো সে জামা হতো বোতামহীন।
কবির বাবা আনসারউদ্দীন ও একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কথায় কথায় কবিতা ছড়া বাঁধতে পারতেন বলে জানা যায়। এ প্রসংগে ইসলামী বিশ্বকোষ লিখেছে, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ অনুরাগ। তাঁহার কবিত্বও শক্তিও ছিল। গাজীপুর উপজেলার কবি গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। জসীমউদ্দীন উত্তরাধিকার সূত্রে সকল পৈতৃক গুণের অধিকারী হয়েছিলেন।”
দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন জসীম উদ্দীন রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতা যা ১৯২৬ সালে ‘কল্লোল’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘কবর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর রাতারাতিই জসীম উদ্দীনের কবিখ্যাতি বাঙালী পাঠকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-নজরুল যুগে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের এ কবিতা পড়ে ডঃ দীনেস চন্দ্র সেন কবিকে লিখেন, “দুরাগত রাখালের বংশী ধ্বনির মত তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।” ডঃ সেন ইংরেজী পত্রিকা Forward এ জসীম উদ্দীনের ওপর একটি পুরো ইংরেজী প্রবন্ধ লিখেন, যার শিরোনম ছিল `An young mohammadan poet’.
সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো, কবি যখন বিএ ক্লাসের ছাত্র তখনই এই ‘কবর’ কবিতাটি পুস্তকে সংকলিত হয় এবং ম্যাট্রিক ক্লাসে পাঠ্য হয়।
ছাত্রাবস্থায়ই কবি কর্মজীবনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৪ সালে তিনি ৭০ টাকা আর্থিক মাসোহারার বিনিময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পল্লী সাহিত্য সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। এম.এ পাস করার পূর্ব পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর ড. দীনেস চন্দ্র সেনের অধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতন লাহিড়ী রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।
১৯৩৭ সালে কবি বিবাহ করেন। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৪ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগের পাবলিসিটি অফিসার পদে যোগ দেন এবং ১৯৬৮ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এ সময়ে কন্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন তাঁর সহকর্মী ছিলেন।
কবির মনটি ছিল আকাশের মত উদার। আর সে মানুষ যদি হয় গায়ের লোক, বা তোমাদের শিশু কিশোর তা’হলে তো কথাই নেই। ছোট সুন্দর ফুটফুটে খুকী দেখলে কবি অমনি খলবলিয়ে বলে উঠেন-
“এই খুকীটি আমায় যদি একটু আদর করে
একটি ছোট কথা শোনায় ভালবাসায় ভরে;
তবে আমি বেগুন গাছে টুনটুনিদের ঘরে,
যত নাচন ছড়িয়ে আছে আনব হরণ করে;
তবে আমি রূপকথারি রূপের নদী দিয়ে,
চলে যাব সাত সাগরে রতন মানিক নিয়ে;
তবে আমি আদর হয়ে জড়াব তার গায়,
নুপুর হয়ে ঝুমুর ঝুমুর বাজত দুটি পায়।”
আসমানী কবিতায় দরিদ্র, অভাব অনটনে জর্জরিত শিশুদের নিয়ে তিনি লিখেছেন-
“পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের কখান হাড়,
সাক্ষী দিছে অনাহারে ক’দিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হ’তে হাসির প্রদীপ রাশি
তারপরেতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।”
এমনি দরদ দিয়ে লিখতে পারা সত্যি সবার পক্ষে সম্ভব নয়।
ছোটদেরকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছেন-
“আমার বাড়ি যাইও পথিক
বসতে দেবো পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেবো
শালি ধানের চিড়ে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব
বিন্নী ধানের খই
ঘরে আছে ফুল বাতাসা
চিনি পাতা দই।”
কি জিহবায় পানি এসে যাচ্ছে, তাই না? আবার শহুরে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে লিখেছেন-
“তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে
আমাদের ছোট গায়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায়
উদাসী বনের বায়।”
ইত্যাদি হাজারো উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে তাঁর লেখা হতে।
তাঁর শিশুতোষ লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে- হাসু, একপয়সার বাঁশি, ডালিম কুমার এবং বাংগালীর হাসির গল্প ১ম ও দ্বিতীয় খন্ড। তিনি শুধু ছোটদের জন্যই লিখেন নি, বড়দের নিয়েও প্রচুর লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কাব্য ২০ খানা, নাটক ১৩ খানা, জারী ও মুর্শিদী গানের সম্পাদনা করেছেন দু’খানা বই।
কবির বহুল পাঠ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ও রাখালী। যা দেশে বিদেশে কবিকে বহুল পরিচিতি ও খ্যাতির আসনে সমাসীন করেছে।
নকশী কাঁথার মাঠ, বেদের মেয়ে, বাংলাদেশের হাসির গল্প ও জসীম উদ্দীনের নির্বাচিত কবিতা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কবি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ‘হলদে পরীর দেশ’ নামক গ্রন্থের জন্য ইউনেসকো পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে বাঙালীর এই প্রিয় কবি, পল্লী কবিকে বাংলা একাডেমী কোন সম্মানে ভূষিত করেনি। এটা বাংলা একাডেমী ও এ জাতির জন্য সত্যিই লজ্জার। অবশ্য তাঁর বাসস্থান ‘পলাশ বাড়ি’ যে রোডে অবস্থিত তার নাম ‘কবি জসীম উদ্দীন স্মরণী’ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের নাম ‘কবি জসীম উদ্দীন হল’ রাখা হয়েছে।
কবি জসীম উদ্দীন তাঁর নিজ বাসভবন ‘পলাশ বাড়ি’তে ১৯৫৩ সাল হতে একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করে আসছিলেন, যা আমৃত্যু জারি রেখেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তারিখে সাহিত্য সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সাহিত্যিক সাংবাদিক মোদাব্বের ও কবি আজিজুর রহমান উপস্থিত হয়ে সাহিত্য সভার বদলে কবির জানাযা পড়েছিলেন। অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তারিখে বাংলার আপামর জনসাধারণের নয়নের মণি পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
\r\n\r\n
বন্দে আলী মিয়া
তোমাদেরকে এখন এমন এক ব্যক্তিত্বের কথা বলব যিনি তাঁর সিংহভাগ সময় এবং শ্রম তোমাদের জন্যই ব্যয় করেছেন। তিনি হলেন কবি বন্দে আলী মিয়া। জানি এ নামটি তোমাদের পরিচিত ও প্রিয়। বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালের ১৭ জানুয়ারী পাবনা শহরের শহরতলীর রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম মুনসী উমেদ আলী মিয়া এবং মাতার নাম নেকজান নেছা। সাহিত্যে প্রায় সকল বিষয়ে-ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী, রহস্য-রোমান্স, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি নিয়ে তিনি লিখেছেন। এসব বিষয়ে তিনি বড়দের জন্য যেমন লিখেছেন, ছোটদের জন্য লিখেছেন তার ঢের বেশি। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন স্বার্থক শিশু সাহিত্যিক।
কবি বন্দে আলী মিয়ার শিক্ষা জীবন শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর স্নেহময়ী পিতা ইন্তিকাল করেন। মা নেকজান নেছা ইয়াতীম শিশুপুত্রকে গ্রামের মজুমদার একাডেমীতে ভর্তি করে দেন এবং এখান হতেই ১৯২৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছবি আঁকতে কবি খুব ভালবাসতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসের পর তিনি কলকাতার বৌ বাজারে অবস্থিত ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর উৎসাহে তিনি টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদত কলেজে আই.এ ভর্তি হন। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে মফস্বলের কলেজ ভাল না লাগায় ১৯২৯ সালে কলেজ ত্যাগ করেন ও তাঁর আর পড়াশোনা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এরপরই বন্দে আলী মিয়া মায়ের একান্ত আগ্রহে বগুড়া শহরের বৃন্দাবন পাড়া নিবাসী রাবেয়া নামের এক সুন্দরী রমনীকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে ওঠেন।
কবি বন্দে আলী মিয়া ১৯৩০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং একটানা কুড়ি বছর এ চাকরিতে বহাল ছিলেন। এই শিক্ষকতার জীবনেই তিনি শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভালভাবে শিশুমনকে জানার সুযোগ পান। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে শিশুদের মতই সহজ সরল ছিলেন। তাঁর মুখে সব সময় হাসির একটা মিষ্টি ঝিলিক ছড়িয়ে পড়তো। দেখামাত্রই ছোটদেরকে কাছে টানার তাঁর চমৎকার সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল। শিশুদের কাছে তিনি কবি দাদু হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে ‘ছেলে ঘুমানো’ নামক শিশু অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিদিন শিশু উপযোগী গল্প গান ইত্যাদি লিখে দিতেন।
কবি নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ‘বেঙ্গল গেজেট’ পত্রিকায় তাঁর ‘ছিন্নমূল’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে কবির শিশু কিশোরদের উপযোগী প্রথম বই ‘চোর জামাই’ প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের ছবিগুলি কবির নিজের হাতে আঁকা। ‘চোর জামাই’ প্রকাশিত হওয়ার পর কবি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ছবি এঁকেও কবি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আঁকা মোনাজাতের ছবিটি ব্যাপক প্রচার ও প্রশংসা লাভ করে।
কবি বন্দে আলী মিয়ার তোমাদের জন্য লেখা অনেক মনগড়া কবিতা রয়েছে।
যেমন-
আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দিঘী,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি। (আমাদের গ্রাম)।
কি চমৎকার কবিতা, তাই না? কবিতাটি ভিতর কোন যুক্তাক্ষর নেই। কারণ কবি শিশু মন বুঝতেন, তাঁদের কষ্টের কথা বুঝতেন। তাই তিনি যতদূর সম্ভব সহজ সরল অথচ সুন্দর ভাষায় লিখেছেন।
তিনি লিখেছেন-
আয় আয় পিস পিস,
দেখ ভাই ময়না,
চুপ চুপ, গোলমাল
কথা আর কয় না। (আফরোজার পুষি)।
ব্যাঙের বিয়ে ছড়াতে লিখেছেন-
ছোট কোলা ব্যাং
ডাকে গ্যাং গ্যাং।
তার নাকি বিয়ে
টুপি মাথায় দিয়ে।
কবি বন্দে আলী মিয়ার প্রায় পৌণে দুইশত বই এর মাঝে ১২৫ খানা বই-ই ছোটদের উপযোগী। এর মধ্যে ইতিহাস আশ্রয়ী বই, যেমন-ছোটদের বিষাদ সিন্ধু, তাজমহল, কোহিনূর, কারবালার কাহিনী ইত্যাদি। তিনি কোরআন ও হাদীসের কাহিনী নিয়েও গল্প লিখেছেন, আবার গুলিস্তাঁর গল্প, ঈশপের গল্প, দেশ-বিদেশের গল্প, শাহনামার গল্প। তিনি অনেকগুলি জীবনী লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আমাদের নবী, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত ফাতিমা, হযরত মূসা, তাপসী রাবেয়া, সিরাজউদ্দৌলা, হাজী মহসিন, ছোটদের নজরুল ইত্যাদি।
এসব লেখার মধ্য দিয়ে তিনি আগামী দিনের নাগরিক শিশু কিশোরদের চরিত্র গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন-
‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।’
ইসলামের সুমহান আদর্শ শিশুদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য পবিত্র কুরআনের ১৫টি কাহিনী নিয়ে তিনি ১৫টি গল্প লিখেছেন। হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় লেখা এ গল্পগুলি হল-আদি মানব ও আজাযিল, স্বর্গচ্যুতি, হাবিল ও কাবিল, মহাপ্লাবন, আদ জাতির ধ্বংস, ছামুদ জাতির ধ্বংস, বলদর্পী নমরুদ, হাজেরার নির্বাসন, কোরবানী, কাবা গৃহের প্রতিষ্ঠা, ইউসুফ ও জুলেখা, সাদ্দাদের বেহেশত, পাপাচারী জমজম, কৃপণ কারুন, ফেরাউন ও মূসা ইত্যাদি।
পবিত্র হাদীস হতে ১৪টি কাহিনী নিয়ে তিনি লিখেছেন ১৪টি গল্প। বইয়ের নাম দিয়েছেন-‘হাদীসের গল্প’। এ বইয়ের গল্পগুলি এ রকম-দীন জনে দয়া করো, সত্য নিষ্ঠার পুরস্কার, ক্ষুধাতুরে খাদ্য দাও, স্বল্প কথা, খোড়া শয়তানের বাহাদুরী ইত্যাদি।
তাঁর গল্প লেখার নমুনা এরকম-‘এক দেশের এক রাজা। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে হীরামানিক, তবু রাজার মনে সুখ নেই। রাজার কোন ছেলে পুলে নেই। একটি মেয়েও যদি হতো তবু রাজা-রাণীর মনে সুখ থাকতো।’
অন্যত্র লিখেছেন-
বাঘঃ হালুম-খক খক খেঁকশিয়াল সাহেব। আদাব।
খেঁকশিয়ালঃ মাননীয় বাঘ বাহাদুর যে, আসুন, আসুন, আদাব। আপনি বনের বাদশা, শত কাজ ফেলে সময় করে যে আমার পুত্রের বিবাহে আসতে পেরেছেন-আমার নসিব। আপনার পলাশ ডাংগায় সবাইকে যে দাওয়াত করেছিলুম, তারা এখনো এসে পৌছুলেন না।
বাঘঃ আমি না আসলে তো কউ আগে আসতে পারেন না। ঐ যে আসছেন সবাই। কি হে পন্ডিত এত দেরী যে?
শৃগালঃ ক্যাহুয়া, ক্যাহুয়া। একটু দেরী হুয়া। আসবার পথে একটা রামছাগলের বাচ্চা পেলুম। নাশতাটা না সেরে আসি কি করে? জানিতো বিয়ে বাড়িতে কখন বরাতে জুটবে বলা যায় না। (বিড়ালের প্রবেশ)।
বাঘঃ পন্ডিত রসিক লোক, নাশতা হয়েছে ভালই হয়েছে। এই যে সরকার সাহেব, আদাব।
বিড়ালঃ আদাব, খেঁকশিয়াল সাহেব। আপনার পুত্রকে এই ইদুরের মুক্তা মালা ছড়া আমার আশীর্বাদ দেবেন।
খেঁকশিয়ালঃ এসব আবার কেন? নিমন্ত্রণ পত্রে তো উল্লেখ ছিল, ‘লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়’। তা মালাছড়া যখন এনেছেন-(কুমীরের প্রবেশ)
‘খেঁক শিয়ালের দাওয়াত’ (টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার)।
কার না ভাল লাগে পশুদের এমন চমৎকার সংলাপ? কবি বন্দে আলী মিয়া শিশু কিশোর উপযোগী জীবনী গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন অসম্ভব হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে। তিনি ‘আমাদের নবী’ গ্রন্থে মহানবী(সা) সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। সেই চাঁদের আলোকে চারিদিক পুলকিত। বিবি আমিনা এক ঘরে ছটফট করেছেন। প্রহরের পর প্রহর কাটতে থাকে। নিখিল বিশ্ব স্তব্ধ নীরব। রাতের শেষ প্রহর, চাঁদ আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। বিবি আমিনার আঁধার ঘর আলোকিত করে একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ট হলেন।
………..বাতাস ছুটে এসে খর্জুর বীথি আর আঙ্গুর গুচ্ছকে খোশ আমদেদ জানিয়ে গেল। জাফরানের খুশবু এই খবর নিয়ে ছুটলো মরু আরবের দিগ দিগন্তে।
এসেছে দীনের নবী
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
তাঁহারি রওশানিতে
জাহান হলো উজ্জ্বালা।।
এ প্রাণস্পর্শী বর্ণনা নিঃসন্দেহে বড়দেরও হৃদয় না কেড়ে পারে না।
কবি বন্দে আলী মিয়ার লেখার প্রশংসা করেছেন বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিকপালেরা। এর মধ্যে রয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাকবি কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদ্দীন, কবি সমালোচক আবদুল কাদির প্রমুখ। আর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ওপর জ্ঞানগর্ভ একটি পুরো প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা ব্যাপড় সাড়া ফেলেছিল। কবির কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে শিশু সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান করে। আর ১৯৬৫ সালে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট পুরস্কার।
এই নিরলস শিশু সাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়া ২৮ জুন, ১৯৭৯ সালে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। আমাদের জানামতে তাঁর ২৫ টা অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে যা বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করি। তাঁর রচনাবলীও প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।
\r\n\r\n
রাজপুত্তুর কবি
এই হিং নেবে হিং, কিসমিস, খুবানি, আঙুর, পেস্তা, বাদাম, আখরোটঃ নে-বে। লম্বা পিরহানের জেবে কলসী ভাঙা চাড়া, কড়ি এসব ভরে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে দরাজ গলায় হেঁকে চলেছে এক কিশোর। বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখ। যেন সে দুটি চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে সত্যের দ্যুতি। লম্বা বাঁকানো বাঁশির মত নাক, প্রশস্ক কপাল, ঘাড় অবধি নেমে যাওয়া ঝাঁকড়া চুল-সব মিলিয়ে এক অপরূপ রাজপুত্তুর। কাবুলিওয়ালা সাজার ইচ্ছায় যে রাজপুত্তুর বেশ হাঁক-ডাক করতো।
রাজপুত্তুরটির যেমন ছিল দরাজ গলা, আগুনঝরা চোখ, বাবরীদোলানো চুল, তেমনি ছিল দুরন্ত সাহস। ভয় কখনো তাঁর দিলে বাসা বাঁধেনি। যা সত্য, যা সুন্দর তা সে আজীবনই মেনে চলেছে, সমাজেও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।
তোমরা হয়ত ভাবছ, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের কোন কথা বলছি। না, আসলে তা নয়। এর রাজপুত্তুরটি রাজমহল আমাদের দেশের এক গন্ডগ্রামে। অতীতকালে তাঁর এলাকাটা শাসন করেছে রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা বিক্রমাদিত্য, খান জাহান আলীর মত রাজা বাদশাহরা। হ্যাঁ, দেশটির নাম যশোরাদ্য দেশ। পরে এটা যশোর জেলা নামে পরিচিত হয়। এ জেলারই মাগুরা মহকুমার আওতাধীন মাঝাইল গ্রামে সে রাজমহল। রাজপুত্তুরটির নাম ফররুখ। পুরো নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ।
১৯১৮ সালের ১০ই জুন ফররুখ আহমদ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। মায়ের নাম বেগম রওশন আখতার। মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান তিনি।
গ্রামের স্কুলেই তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এরপর কলকাতার তালতলি মডেল স্কুলে, বালিগঞ্জ হাইস্কুলে, খুলনা জেলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। খুলনা জেলা স্কুল হতে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। বালিগঞ্জ হাই স্কুলে পড়াকালে কবি গোলাম মোস্তফাকে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান। আর খুলনা জেলা স্কুলে পান কবি আবুল হাশিম ও অধ্যাপক আবুল ফজলকে শিক্ষক হিসেবে। কলকাতার রিপন কলেজ হতে ১৯৩৯ সালে তিনি আইএ পাশ করেন। পরে দর্শনে অনার্স নিয়ে বিএ ভর্তি হন। আরো পরে ইংরেজিতে অনার্স নেন। কিন্তু ঐ পর্য্ন্ত যে কোন কারণেই হোক তাঁর আর অনার্স পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।
হ্যাঁ, রাজপুত্তুরটি ছিলেন সত্যি সত্যিই রাজপুত্তুরের মত। যখন হাঁটতেন মনে হত কেশর দুলিয়ে সিংহের বাচ্চা হেঁটে যাচ্ছে। হাঙর কুমিরকে থোড়াই কেয়ার করে দলবল নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি বলতেন, ‘হাঙর কুমির যদি থাকে, আমার ভয়েই তারা পালিয়ে যাবে।’ সারা জীবন এমনই তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, কারো কাছে কোনদিন কোন কারণে মাথা নত করেন নি।
রাজপুত্তুরটি ছিলেন খুবই ভাবুক প্রকৃতির। রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ হেসে উঠতো তখন বিছানা ছেড়ে চলে যেতেন ডাহুক ডাকা বাঁশঝাড়টার কাছে। চুপচাপ শুনতেন ডাহুকের ডাক আর কবিতা লিখেতেন-
রাত্রিভর ডাহুকের ডাক……
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি
কানপেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।
আবার-
তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে আসে পালক মেঘের অন্তরালে
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।
মাঝে মাঝে তিনি বাড়ির পুচকে পুচকে পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেড়াতে বের হতেন্, যেন রাজপুত্তুরের হরিণ শিকার। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন মধুমতির তীরে। পলকহীনভাবে দেখতেন নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার জাহাজের আনাগোনা। শুনতেন মাঝি-মাল্লার দাঁড় ফেলার শব্দ, হাঁক-ডাক। এসব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন। সাথীদেরকে এসময় দিতেন ভূগোলের জ্ঞান। বলতেন, “পাহাড় হতে এসেছে এই নদী। তারপর চলে গেছে দক্ষিণে, সেখানে আছে বঙ্গোপসাগর, তারপর আরব সাগর। নৌকা চড়ে ভেসে যেতে কোনো বাধা নেই, কোনো মানা নেই। কিন্তু সাবধান, হুঁশিয়ার। আসবে ঝড়, উঠবে তুফান, বড় বড় কুমীর আর হাঙর মাতামাতি করবে। আল্লাহ আল্লাহ করে নৌকা ছাড়লে আর কোন ভয় নেই।”
কবি ফররুখ আহমদ চেয়েছিলেন এই ঘূনে ধরা সমাজটাকে ভেঙ্গে একটা সুন্দর সমাজ গড়তে।
তাঁর কথায়-
আল্লাহর দেওয়া বিশ্ববিধান
ইসলামী শরীয়ত
যে বিধানে মোরা গড়িয়া তুলিব
এই পাক হুকুমত।।
তৌহিদে রাখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস
আমরা সৃজিব নয়া ইতিহাস
দেবো আশ্বাস দুনিয়ার বুকে
দেখাব নতুন পথ।।
সারা মুসলিম দুনিয়াকে বেঁধে
একতার জিনজিরে
ফিরায়ে আনাব হারানো সুদিন
নয়া জামানার তীরে।।
আলী, উসমান, উমরের দান
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান
নেব ফেরা মোর আবূ বকরের
সত্য সে খেলাফত।
কবির দৃঢ় বিশ্বাস আগের দিনে যারা জাতির নেতৃত্ব দিয়েছে, তাঁদের ত্রুটির কারণেই আজ মুসলিম জাতি এই খারাপ অবস্থায় পৌছেছে। যেমন-
শুধু গাফলাতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছে তুলে
আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে,
মুসাফির দল বসি,
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের,
সেতারা শশী।
মোদের খেলাধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্ববরী। (পাঞ্জেরী)।
সারা দুনিয়ায় আবার নতুন করে মুসলিম জাগরণ শুরু হয়েছে। আবার যেন নতুন সূর্য্ ওঠার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন-
কেটেছে রঙ্গিন মখমল দিন, নতুন
সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,……….
…………………………………………
নতুন পানিতে সফর এবার এ
মাঝি সিন্দাবাদ। (সিন্দাবাদ)।
কিন্তু আমাদের জাতির নেতারা যখন হতাশ, সাহসহারা তখনো রাজপুত্তুর তার সাহসে ভর দিয়ে বলেছেন-
আজকে তোমায় পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে। (সাত সাগরের মাঝি)।
কবির রাজপুত্তুরটি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এই দৃঢ় প্রত্যয়ী রাজপুত্তুরটি তার জীবনেও ইসলামী অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। কোন ঝড়, কোন বিপদ তাঁকে এপথ হতে চুল পরিমাণও সরাতে পারে নি।
তিনি বিপদ মুসিবতের সময় ভেঙ্গে পড়াকে ঘৃণা করতেন। এই সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাওয়াটাও মোটেই পছন্দ করতেন না। কবি লিখেছেন-
তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে
খোদার মদদ ছাড়া
পরের ওপর ভরসা ছেড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়া।
এমনিভাবে তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে দেশ জাতির মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য অনেক ভাল ভাল বই লিখেছেন। যেমন-‘পাখির বাসা’, ‘হরফের ছড়া’, ‘নতুন লেখা’, ‘ছড়ার আসর’, ‘নয়া জামাত’, ‘চিড়িয়াখানা’ ইত্যাদি। ‘পাখির বাসা’ বইটির জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও কবি পেয়েছেন-বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।
\r\n\r\n
এক সংগ্রামী চেচেন নেতা জওহর দুদায়েভ
সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার এক মুসলিম জনপদের নাম রাশিয়া। সত্যি কথা বলতে কি ১৯৯১ সালের ১লা নভেম্বরের আগে বাংলাদেশের মানুষ জানতো না এই মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ চেচনিয়ার কথা। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ জনগণও এই জনপদটির খবর রাখত না। ১৯৯১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ রাশিয়া ১৫টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন চেচনিয়া স্বাধীনতার ডাক দেয়। রাশিয়ার পনেরটি প্রজাতন্ত্রের বাইরে নব্বইটি স্বায়ত্ত্বশাসিত অঙ্গ প্রজাতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলোর মধ্যে চেচনিয়া একটি।
৬০০০ বর্গমাইল আয়তনের এ ক্ষুদ্র জনপদের লোকসংখ্যা ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত ছিল ১২ লাখ ৮৯ হাজার ৭০০ জন। চেচনিয়ার রাজধানীর নাম গ্রোজনী যার লোকসংখ্যা ছিল ৪ লাখের ওপরে। গ্রোজনী শব্দের অর্থ দুর্দম্য, দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, জাদরেল ইত্যাদি।
বর্তমানে যুদ্ধের কারণে সমগ্র চেচনিয়াতে মাত্র ৪ লাখের মত লোক অবস্থান করছে, বাকীরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে প্রায় ২ লাখের মত চেচেন মারা গিয়েছে বলে জানা যায়। এর আগে ১৯৪৪ সালে স্টালিন সরকার গণহত্যার মাধ্যমে ‘মুসলিম সমস্যা’ সমাধানের লক্ষ্যে জোরপূর্বক ১২ লক্ষ (ঐ সময় চেচনিয়ায় ১২ লক্ষ মুসলমান ছিল) চেচেন মুসলিমকে কাজাখাস্তানে নির্বাসনে পাঠায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ১২ লক্ষ চেচেন মুসলিমদের মধ্যে ৩ লক্ষ পথেই মারা যায়।
ইতিহাস হতে জানা যায়, চেচনিয়ার পার্শ্ববর্তী দাগাস্থানের দ্বারবন্ধ শহরে ৬৪৩ সালে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়। এর আগে ৬৩৯ সালে আরবরা আজরাবাইজান দখল করে নেয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে পুরো দ্বারবন্ধ এলাকায় ইসলাম প্রসার লাভ করে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী চেচনিয়াতে ইসলাম প্রবেশ করতে সময় লাগে। পন্ডিতদের মতে, ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে চেচনিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করে। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে এসে চেচেন মুসলমানদের ওপর রুশ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। ১৫৯৪ সালে মুসলিম বনাম রুশ বাহিনী উত্তর দাগাস্থানের পুলাক নদীর তীরে রুশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। হঠে যায় রুশ বাহিনী। ১৬০৪ সালে রুশ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আঘাত হেনে আবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা রুশ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই বিরাট বিজয় ছিনিয়ে আনে। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর সেই যুদ্ধের শুরু।
জাতীয়তার দিক হতে চেচেনরা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অধিকাংশ জনসংখ্যা তুর্কী বংশোদ্ভুত মুসলমান। জার শাসন ও পরবর্তীকালে সত্তর বছরে কমউনিস্ট শাসনামলে চেচেন মুসলমানদের চেতনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। ইতিহাস সাক্ষী চেচনিয়া কোন কালেই রাশিয়ার অংশ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চেচনিয়াকে জোরপূর্বক রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। বহুকাল ধরে রুশরা বারবার চেচেনদের ওপর হামলা চালিয়েছে কিন্তু চেচেন মুসলমানরা কোনকালেই এই অন্যায় আধিপত্য মেনে নেয় নি। বরং তাদের বিরুদ্ধে ইমাম শেখ মসুর উশুরমা(১৭৩২), শেখ মোহাম্মদ, গাজী মোহাম্মদ, গামজাতবেক, শে হাজী ইসমাঈল, মোল্লা মোহাম্মদ, জামাল উদ্দীন ও ইমাম শামিলরা আপোসহীন জিহাদ পরিচালনা করেছেন। ১৮৫৯ সালের ২৫ শে অগাস্ট ইমাম শামীল রুশ বাহিনীর কাছে সম্মানজনক আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। গুনিব গ্রামের এ যুদ্ধে ইমাম শামিলের সর্বশেষ ৪০০ মুরীদের প্রায় সবাই শহীদ হন। তারপরও ১৮৫৯-৬৪ সালে পর্যন্ত চেচেনরা ককেশাসের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে চেচেনরা জার্মানকে সমর্থন দেয়ায় স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ চেচেনকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে কাজাখস্থানে নির্বাসন দন্ড প্রদান করে। এই নির্বাসন চলাকালে ১৯৪৪ সালের ১৫ এপ্রিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ পিয়ার ভোমায়াস্কা এলাকার ইয়ালখের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা ছিলেন মূসা এবং মাতার নাম ছিল আলেপতিনা কেদোরভনা দুদায়েভ। দুদায়েভের আব্বা ছিলেন জাতিতে চেচেন এবং মা ছিলেন রুশ। মোট ৭ ভাই বোনের মাঝে দুদায়েভ ছিলেন সবার ছোট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়ায় তাঁর আব্বা ও বড় ভাইকে শহীদ করে দেয় স্টালিনবাহিনী।
দুদায়েভ রাডিকাফ কাজে ইলেক্ট্রনিক্স্রের ওপর দু’বছর পড়াশোনার পর সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের রাশিয়ার তাম্বর শহরের বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেনেদ্র তাঁর সামরিক শিক্ষা শুরু হয়। জাতিগতভাবেই রুশরা অন্তর থেকেই চেচেনদের ঘৃণা করে। এরপরও জওহর দুদায়েভ আপন প্রতিভা বলে সমস্ত প্রকার বাধা অতিক্রম করে রাশিয়ার সেরা সামরিক স্কুল ইউরি গ্যাগারিন এয়ারফোর্স একাডেমী, মস্কোতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গতানুগতিক নিয়মে দুদায়েভ ১৯৬৮ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্য্ন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৬-৭৯ পর্যন্ত দুদায়েভ রাশিয়ার এয়ারফোর্স রেজিমেন্ট এর চীফ অব স্টাফ, ১৯৭৯-৯০ কমান্ডার অব ডিভিশন এবং ১৯৯০ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এরপর দুদায়েভ ১৯৯০-৯১ সেশনের জন্য চেচেন জাতির মহাসম্মেলনের নির্বাহী কমিটির প্রধান ছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ ও অলঙ্কৃত করেন।
জওহর দুদায়েভ আল্লা নাম্নী এক রুশ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে ছিল।
দুদায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর মাঝে জাতীয় চেতনা ও অতীত ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে চেচেত জাতির ভেতর তাঁদের পূর্ণ মুসলিমসত্ত্বা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তারা সে বছরেই দুদায়েভের নেতৃত্বে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, যে স্বাধীনতা ছিল চেচেন জাতির আবহমানকালের লালিত স্বপ্ন। ১৯৯৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন যখন তার তিন ডিভিশন সৈন্যকে চেচনিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন তখন দুদায়েভ চেচেন জাতির আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে ওঠেন। চিরসংগ্রামী চেচেন জনগণ তাঁর নেতৃত্বে সুশিক্ষিত বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে মরনপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা যে কোন স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
১৯৯৫ সালে দুদায়েভের বড় ছেলে রুশদের অস্ত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে শহীদ হন এবং ১৯৯৬ সালের গোড়ার দিকে তাঁর জামাতা সালমান রাদুয়েভও শহীদ হন।
দুদায়েভের প্রিয় শখ ছিল কারাতে ও সঙ্গীত। তিনি পুশকিন ও লের মগুভের কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। কারণ ছিল এ দু’জন কবি ককেশাসকে অত্যন্ত ভালবেসেছিলেন এবং ককেশাসের উপর তাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা আছে।
দুদায়েভ কুরআন তিলাওয়াত করতে ও শুনতে ভালবাসতেন। তিনি খুব ফুল প্রিয় লোক ছিলেন। যে কারণে ফুলের বাগান পর্যন্ত করেছেন। দৈহিকভাবে ছোটখাট এ মানুষটি ছিলেন প্রাণোচ্ছ্বল জীবন্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এখনকার কিংবদন্তী।
চেচনিয়াকে নিয়ে ছিল তার সীমাহীন স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন চেচনিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি চেচনিয়ার মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। চেচনিয়াকে তিনি ১৯৯১-১৯৯৪ পর্যন্ত তিন বছরের কিছু বেশি সময় স্বাধীন রাখতে পেরেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি এক দুদায়েভই ছিলেন চেচেন জাতির স্বাধীনতার প্রতীক। দুর্ধর্ষ ককেশীয় চেচেন জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী।
আজাদী পাগল চেচেনরা পাহাড়ী অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ২১শে এপৃল ১৯৯৬ তারিখে চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতোভয় মহানায়ক, চেচেনদের নয়নের মনি, চিরসংগ্রামী নেতা জওহর দুদায়েভ স্যাটেলাইট ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গ্রোজনী হতে ৩০ কিমি দূরে জেখেসু গ্রামের একটি মাঠে শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় তিনি চেচেন সংকট নিরসনের জন্য মধ্যস্থতার ব্যাপারে স্যাটেলাইট টেলিফোনে আলাপ করছিলেন। জানা যায়, কাপুরুষ ইয়েলৎসিন বাহিনী কৌশলে স্যাটেলাইট টেলিফোনের অবস্থান জেনে নিয়ে রুশ বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। ইতিহাস বলে চেচেন মুসলমানরা আজাদী পাগল এক যোদ্ধা জাতি। সত্যিই তারা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। আর যারা মৃত্যুকে ভয় পায় না, বিজয় তাদের অনিবার্য। হতে পারে সেটা সময় সাপেক্ষ। প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ শহীদ হলেও চেচনিয়ার ঘরে ঘরে হাজার হাজার দুদায়েভ এখন তৈরী হবে, জন্ম নেবে।
--- সমাপ্ত ---
', 'সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবনকথা - ১ম খন্ড', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b7%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9c%e0%a7%80%e0%a6%ac', '', '', '2019-10-24 13:21:14', '2019-10-24 07:21:14', '
সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবনকথা - - ১ম খন্ড
নাসির হেলাল
\r\n\r\n\r\n
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
\r\n\r\n
১ম খন্ড
ভূমিকা
যে জাতি তার গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করে না, সে জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি বাঙালী জাতি, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ক্ষেত্রে কথাটি হাড়ে হাড়ে সত্যি। তারা তাদের পূর্বসুরী গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা তো দূরের কথা খোঁজ খবরটুকুও রাখেন না। তাছাড়া বর্তমান প্রজন্মে এসে যতটুকু বা মূল্যায়ন করার চেষ্টা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও খন্ডিত। ঠুনকো স্বার্থের কারণে কাউকে বা অহেতুক বিরাট বিশাল করে দেখানো হচ্ছে আবার কাউকে খাটো করতে করতে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটিই সত্য নয়। ফলে জাতি বিভ্রান্ত হচ্ছে, প্রকৃত গুণীরা ক্রমে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছেন।
সেই দায়ভার থেকেই আমরা ‘মুসলিম মনীষীদের জীবনী’ ধারাবাহিকভাবে জাতির সামনে তুলে ধরার পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রথম খন্ডে দেশী-বিদেশী মোট ২০ জন মুসলিম মনীষীর সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল জীবনী তুলে ধরা হল। এদের মধ্যে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ইসলাম প্রচার, রাজনীতি নানা অঙ্গনের মনীষীরা রয়েছেন। আমরা বয়োক্রম অনুযায়ী শিরোনাম সাজিয়েছি।
এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুলোর ভিতর কয়েকটি লেখা কিশোর তরুণদের উদ্দেশ্য করে লেখা। তবে আমাদের বিশ্বাস তথ্যবহুল ঐ লেখাগুলো বড়দের উপকারে আসবে।
‘সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবনকথা’ প্রথম খন্ডে যে লেখাগুলো স্থান পেল-তাতে যদি কারো চোখে কোন ভুল তথ্য ধরা পড়ে তা আমাদের লিখে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।
বিনীত
নাসির হেলাল
১/জি/৯, মীরবাগ
ঢাকা ১২১৭।
\r\n\r\n
মহাকবি শেখ সাদী
প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন। ডাক নাম মসলেহউদ্দীন। আর উপাধি বা খেতাব হচ্ছে সাদী। আসল নাম নয়, তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন উপধি ‘সাদী’ নিয়ে। মানে শেখ সাদী নামে। জানা যায় কবির আব্বা তৎকালীন শিরাজের বাদশাহ আতাবক সাদ বেন জঙ্গীর সেক্রেটারী ছিলেন। কবি নিজে তুকলাবীন সাদ জঙ্গীর রাজত্বকালে কবিতা লিখতেন, এ কারণেই তিনি তার নামের সঙ্গে সাদী উপাধি যোগ করেন এবং পরবর্তীকালে শেখ সাদী নামেই পরিচিত হয়ে হন।
শেখ সাদীর জন্মসনের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবুও মোটামুটি বলা যায় তিনি ৫৮০ হিজরী মোতাবেক ১১৮৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু তারিখ সবার মতে৬৯১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২ খৃস্টাব্দ।
পরহেজগার পিতার সাহচর্যেই শেখ সাদী শিশুকাল অতিক্রম করেন। পিতার দেখাদেখি সাদীও নামায, রোযা ও রাত্রিকালীন ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। পিতার উৎসাহে কুরআন অধ্যয়নে তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। বলা যায় দরবেশ পিতার আদর্শেই আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠেন শেখ সাদী।
বাল্যকালেই সাদীর পিতা ইন্তিকাল করেন। পিতার ইন্তিকালের পর সাদী পুণ্যবতী ও গুণবতী মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকেন। এ সময়ে তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তির স্নেহধন্য হন। তিনি হলেন তাঁরই শ্রদ্ধাভাজন মামা আল্লামা কুতুবুদ্দীন শিরাজী। যিনি কিনা হালাকু খাঁর অন্যতম দরবারী বন্ধু ছিলেন।
তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সূত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁর নিজের লেখা হতে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন-তিনি যখন নিতান্ত ছোট তখন তাঁর আব্বা লেখার জন্য তাঁকে একটি ‘তখতি’ ও হাতের আঙ্গুলে পরার জন্য একটি সোনার আঙটি কিনে দেন্। কিন্তু এক মিষ্টি বিক্রেতা কবিকে মিষ্টি দিয়ে ভুলিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট দেয়। আংটি খোয়া গেলেও একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে কবি মিষ্টি খুব পছন্দ করতেন।
একবার ঈদের দিন ঈদের ভিড়ে শেখ সাদী পিতার জামার প্রান্ত ধরে হাঁটছিলেন, যেন পিতা হতে তিনি আলাদা না হয়ে যান। কিন্তু পথে খেলাধুলায় মত্ত ছেলেদের দেখে জামার প্রান্ত ছেড়ে তিনি তাদের দলে ভিড়ে যান। পরবর্তীতে শেখ সাদীর আব্বা যখন তাঁকে ফিরে পান তখন রেগে গিয়ে বলেন, “গাধা! তোকে না বলেছিলাম কাপড় ছাড়িস না।”
জানা যায়, একবার তিনি তাঁর আব্বার সাথে সারারাত ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিলেন। এ সময় ঘরের অন্যান্যরা ঘুমে অচেতন ছিল। এ অবস্থা দেখে সাদী তাঁর আব্বাকে বললেন, ‘দেখছেন, এসব লোক কেমন সংজ্ঞাহীন হয়ে ঘুমাচ্ছে। কারো এতটুকুও সৌভাগ্য হচ্ছেনা যে, উঠে দু’রাকাত নামায পড়ে।’ এ কথার উত্তরে সাদীর পিতা বললেন, ‘তুমি যদি শুয়ে থাকতে তবেই ভাল হতো; তাহলে পরচর্চা হতে বিরত থাকতে।’
শেখ সাদীর প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মহান পিতার নিকট হয়েছিল। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। এ সময়ে তিনি শিরাজের প্রখ্যাত আলেম উলামাদের সংস্পর্শে আসেন এবং জ্ঞান আহরণ করতেন।
প্রথম দিকে তিনি শিরাজের সুলতান গছদদৌলা প্রতিষ্ঠিত গছদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি আরো কয়েকটি মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণ করেন। এ সময়ে দেশের শাসক আতাবক জঙ্গী দেশ জয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে দেশ গঠনে উদাসীন ছিলেন। ফলে দেশের অস্থিতিশীল পরিবেশে সেখানে শিক্ষার কোন পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। এমতাবস্থায় শেখ সাদী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মানসে বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত মাদরাসা নিযামিয়ায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসার যাত্রকাল হতে মুতুওল্লী ছিলেন শিরাজের স্বনামখ্যাত আলেম শেখ আবু ইসহাক শিরাজী। শেখ সাদী অল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং বৃত্তি লাভ করেন।
মাদ্রাসা নিযামিয়ায় অধ্যয়নকালে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তৎকালীন সময়ের বিশ্ববিখ্যাত আলেম আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে জৌজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি ছিলেন তাফসীর ও হাদীসশাস্ত্রে তখনকার ইমাম। ইবনে জৌজীর আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। শেখ সাদী আল্লামা শাহবুদ্দীন সুহরাবদীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন।
শিশুকাল হতে যদিও শেখ সাদী ফকিরী ও দরবেশী জীবন বেশি পছন্দ করতেন তবুও তিনি জ্ঞান অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন, ‘দরবেশ শুধু নিজকে বাঁচানোর চেষ্টায়ই থাকে। অপরপক্ষে আলেমদের চেষ্টা থাকে নিজের সাথে অন্য ডুবন্ত লোকদের বাঁচিয়ে তোলার।’
শেখ সাদী বাগদাদের লেখাপড়া শেষ করে দেশভ্রমণে বের হন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন-
ত্রিশ বছর লেখাপড়ায়
ত্রিশ বছর দেশভ্রমণে
ত্রিশ বছর গ্রন্থ রচনায়
ত্রিশ বছর আধ্যাত্মিক চিন্তায়।
শোনা যায় তাঁর জীবনের উক্ত চারটি পর্যায় যেদিন পূর্ণ হয় সেদিনই নাকি তিনি ইন্তিকাল করেন। শেখ সাদী দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে এমন পান্ডিত্য অর্জন করেন যে তিনি আঠারটি ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হন। এর ভেতর অনেকগুলি ভাষা তার মাতৃভাষার মতই ছিল। আর তিনি এত অধিক দেশ ভ্রমণ করেন যে ইবনে বতুতা ছাড়া প্রাচ্য দেশীয় পর্যটকদের মধ্যে কেউই এত অধিক দেশ ভ্রমণ করেন নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি পায়ে হেঁটে চৌদ্দবার হজ্জ্ব পালন করেছিলেন। তিনি তার সফরকালে অসংখ্য নদী এমনকি পারস্যোপসাগর, ভারত মহাসাগর, ওমান সাগর, আরব সাগর প্রভৃতি পাড়ি জমিয়েছেন। আর সঞ্চয় করেছেন জ্ঞানের রাজ্যে অসংখ্য মনি মুক্তা, হিরা-জহরত।
দেশ ভ্রমণকালে শেখ সাদী এক সময়ে কোন কারণে দামেশকবাসীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে ফিলিস্তিনের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে তখনকার খৃস্টানদের হাতে বন্দী হন। খৃস্টানগণ বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হতে আনীত ইহুদী বন্দীদের সাথে কবিকে খন্দক খননের কাজে নিয়োজিত করে। একদিন সৌভাগ্যক্রতে তাঁর পিতার এক বন্ধু তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি দশ দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনেন এবং একশত আশরাফী দেনমোহর ধার্য করে নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু সাদীর এ স্ত্রী অতন্ত বাচাল ছিলেন বলে এই বিয়ে বেশিদিন টিকে নি। তিনি একদিন সাদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘তুমি কি পূর্ব জীবনের কথা ভুলে গেছ? তুমিতো সেই ব্যক্তি যাকে আমার পিতা দশটি রোপ্য দিনার দিয়ে মুক্ত করেছেন।’ উত্তরে কবি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, তিনি দশ দিনারে মুক্ত করে একশত আশরাফী দিয়ে পুনরায় বন্দী করেছেন।’
ভারত ভ্রমণকালের একটা ঘটনা তাঁর বুসতাঁ কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল সোমনাথ মন্দিরের। কবির মুখেই শুনি সেই ঘটনা, “আমি সোমনাথ এসে যখন দেখতে পেলাম হাজার হাজার লোক এসে মূতির নিকট নিজ নিজ মনস্কামনা হাসিলের জন্য পূজা দিচ্ছে তখন আমি বিস্মিত হলাম। হাজার হাজার জীবিত লোক এক প্রাণহীন মূর্তির নিকট মনষ্কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা জানাচ্ছে।”
একদিন আমি এক ব্রাহ্মণের নিকট যেয়ে এর রহস্য জানতে চাইলাম। ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনে মন্দিরের পূজারীদের ডেকে আনলো-তারা এসে ক্রোধ ভরে আমাকে চারিদিক হতে ঘিরে ফেললো, আমি তখন সমূহ বিপদ দেখে বললাম, তোমাদের দেবতার অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়…….তবে আমি এখানে নতুন এসেছি, এ মহান দেবতার পূজাদি কিভাবে দিতে হবে জানি না বলে জানতে চেয়েছি। আমাকে তা শিখিয়ে দাও যেন ঠিক পূজা করতে পারি।
তখন পূজারিগণ খুশি হয়ে আমাকে পূজার ধরন ধারণ শিখিয়ে দিয়ে মন্দিরে নিয়ে গেল। তারা আরও বলল, আজ রাতে তুমি মন্দিরে থাক তখন এ দেবতার শক্তি দেখতে পাবে।
আমি সারারাত মন্দিরে কাটালাম। ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তখন মূর্তি একখানা হাত উঠিয়ে পূজারীদের আশীর্বাদ করল। তখন সকলেই জয় জয় করে উঠল। এরপর নিশ্চিন্ত মনে সকলে চলে গেল। ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে হেসে বলল, কি বল, এখন বিশ্বাস হল তো!
আমি বাহ্যিকভাবে কেঁদে কেঁদে আপন মূর্খতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। তখন ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হয়ে মূর্তির নিকট নিয়ে গেলে আমি তার হাত চুম্বন করে সম্মান জানালাম। এরপর যেন সত্যিকার ব্রাহ্মণ হয়ে আমি নিশ্চিন্তে মন্দিরে আসা যাওয়া করতে লাগলাম।
আর এক রাত্রে সকলে চলে গেলে, আমি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মূর্তির নিকট গিয়ে এর ভেদ জানতে চাইলাম। আমার চোখে পড়ল মূর্তির পিছনে একখানি পর্দার আড়ালে রশি ধরে একজন পূজারী বসে আছে। রশির একদিক মূর্তির সাথে বাঁধা। সে পূজারী যখন রশি ধরে টানে তখনই মূর্তির হাত উপরে উঠে যায় আর সাধারণ লোক তাকেই মূর্তির শক্তি বলে নাচতে থাকে।
সে পূজারী পর্দার আড়াল হতে যখন দেখতে পেল আমি তাদের গোপন রহস্য জেনে ফেলেছি তখন সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি তখন প্রাণের ভয়ে তাকে ধরে এক কূপে ফেলে দিলাম।
এরপর সে রাতেই সোমনাথ ছাড়লাম। ভারতের পথে ইমনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হেযাজে এসে পৌছলাম।”
শেখ সাদী হলেন বিশ্ববিখ্যাত ক’জন কবির মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত গুঁলিস্তা ও বুঁসতা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অনেকে মনে করেন, এই গ্রন্থ দুটি অধ্যয়ন ব্যতীত ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন অপূর্ণ থেকে যায়। এ গ্রন্থ দুটি একত্রে ‘সাদী নামাহ’ নামে পরিচিত। নৈতিকতা বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ হল বুঁসতা। আর নৈতিকতা বিষয়ক গদ্যগ্রন্থ হল গুঁলিস্তা। গুলিস্তাঁয় লেখক অত্যন্ত সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নৈতিকতার বিষয় আশয় গল্পোচ্ছলে পরিবেশন করেছেন। এর ভেতর অবশ্য কবিতাও আছে। এমন কি কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতিও লেখক ব্যবহার করেছেন নিজের বক্তব্যকে সুন্দর ও জোরালো করার জন্য।
সাদী ছিলেন অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী। এ ব্যাপারে মাওলানা আবদুর রহমান জামী বলেছেন, ‘রুমীর মসনবী, আনোয়ারীর কাসিদা এবং সাদীর গযল সমপর্যায়ের।’ তিনি আরো মনে করতেন যে, শেখ সাদী বিশ্ব বিখ্যাত লেখক আমীর খসরুর চেয়েও বড় লেখক। অবশ্য আমীর খসরু নিজেও তার ‘সেপাহর মসনবী’ গ্রন্থে শেখ সাদীকে গযলের উস্তাদ হিসেবে স্বীকার করেছেন।
শেখ সাদীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে চমৎকার একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হল-‘শিরাজের এক ব্যক্তি সাদীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এক রাতে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পেলেন, েএকজন ফেরেশতা একখানি নূরের বরতন নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন। ঐ ব্যক্তি জানতে চাইলেন এ কি ব্যাপার? ফেরেশতা জবাবে বললেন, সাদীর একটি কবিতা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে-সে জন্য বেহেশতের এ উপহার। কবিতাটি হল-
জ্ঞানিদের চোখে
গাছের ঐ সবুজ পাতা
খোদা তত্ত্বের
এক একখানি গ্রন্থ।
ঐ ব্যক্তির যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন সেই রাতেই সাদীর গযলটির ব্যাপারে স্বপ্নে দেখা খোশ খবর জানতে গেলেন। আশ্চর্য! লোকটি দেখেন উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে শেখ সাদী সেই কবিতাটিই পড়ছেন।’
আরো একটি ঘটনা, শেখ সাদী তখন দেশ বিদেশে বেশ মশহুর হয়ে পড়েছেন। একদিন শিরাজ হতে ষোল শ মাইল দূরের কাশগড়ে বেড়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন ছোট বড় সবাই তাঁর নাম জানে ও তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ।
সাদী উঠেছিলেন কাশগড়ের জামে মসজিদে। সেখানে একজন ছাত্র আল্লামা যমখশীর একটি গ্রন্থ হাতে নিয়ে বলেছিল, ‘কোরবে যায়েদ মির’।
ছাত্রটির কথা শুনে শেখ সাদী বললেন, ‘খাওয়ারযমের ও তাঁর শত্রুর মাঝে সন্ধি হয়ে গেছে তবে যায়েদ ও মীরের ঝগড়া এখনো চলছে।’ ছাত্রটি একথা শুনে সাদীকে বললো, জনাবের দেশ কোথায়?
‘শিরাজ’।
তবে তো সাদীকে চিনেন। তাঁর দু/একটি কালাম শুনাবেন কি?
আরবীতে কিছু কালাম বললেন সাদী।
যদি দু’একটি ফারসী কালাম শুনাতেন। ছাত্রটি বলল।
একটি ফরাসী বয়াত পেশ করলেন সাদী।
পরে যখন ছাত্রটি জানলো ‘ইনিই সেই মহাকবি শেখ সাদী। তখন সে করজোড়ে কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, কাশগড়ে যদি কিছুকাল অবস্থান করেন তো খেদমত করতে পারতাম।’
কিন্তু সাদী কাশগড়ে আর থাকতে পারেন নি। তিনি সেখান হতে তিবরীজ চলে যান।
অনেক ইংরেজ লেখক শেখ সাদীকে প্রাচ্যের শেক্সপীয়র বলে আখ্যায়িত করেছেন।
শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল-
১. গুলিসতাঁ ২. বুস্তুাঁ ৩. করিমা ৪. সাহাবিয়া ৫. কাসায়েদে ফারসী ৬. কাসায়েদে আরাবীয়া ৭. গযলিয়াত ৮. কুল্লিয়াত ইত্যাদি।
বুস্তাঁ ও গুলিসতাঁ গ্রন্থ দুটি এশিয়ায় সব থেকে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই গ্রন্থ দুটির অনেক কথায় পারশ্য সাহিত্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে।
পন্ডিতদের মতে গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে ফারসি ভাষায় ৪ খানি গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। তা হল-
মহাকবি ফেরদাউসী’র-------শাহনামা
জালালুদ্দীন রুমি’র ------- মসনবী
শামসুদ্দীন হাফেযে’র------- দিওয়ান
এবং শেখ সাদীর-------------গুলিস্তাঁ
গুলিসতাঁ উপদেশমূলক চমৎকার সব গল্পে ভরপুর। যেমন-‘এক বাদশাহ এক অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেন। লোকটি বহু কাকুতি মিনতি করেও যখন কিছু হল না তখন বাদশাহকে গালি দিয়ে বসল। বাদশাহ তার কথা বুঝতে না পেরে উজিরের নিকট জানতে চাইলেন সে কি বলেছে।
সেই উজির ছিলেন নেক মেযাজের, তাই তিনি লোকটির উপকারার্থে বললেনঃ হুযুর লোকটি বলছে-যিনি রাগ দমন করে অপরাধ করেন, তিনি খোদার বন্ধু। একথা শুনে বাদশাহ খুশি হয়ে লোকটিকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। অন্য একজন হিংসুক স্বভাবের উজির ছিলেন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, হুযুর এ মিথ্যা কথা। লোকটি আপনাকে মন্দ বলেছে।
তা শুনে বাদশাহ বললেন, তোমার কথা সত্য হলেও অন্য উজিরের মিথ্যার চেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাতে ছিল পরোপকারের উদ্দেশ্য-আর তোমার কথায় অনিষ্ঠের অভিসন্ধি।’ বাদশাহ লোকটিকে ক্ষমাই করেছিলেন।
এমনি সব গল্প দিয়ে ভরা রয়েছে গুলিসতাঁ যার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। শেখ সাদী দৈহিকভাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন। কষ্টসহিষ্ঞু এ মানুষটি প্রচন্ড উদারও ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে দেশের পর দেশ ভ্রমণ করেছেন। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, নদী-নালা সবই তাঁর পায়ের তলায় হার মেনেছে। এমনকি তিনি ফকির দরবেশের ন্যায় এসব পথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খালি পায়ে পাড়ি জমিয়েছেন।
এ ধরনের ভ্রমণে যে নানা ধরনের দুঃখ কষ্ট আসে তা ভুক্তভোগীরা জানেন। শেখ সাদীর জীবনেও নানা বিপদ আপদ এসেছ এবং তিনি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একবার তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। এ ব্যাপারে গুলিস্তাঁ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘আমি কখনো কালের কঠোরতা ও আকাশের নির্মমতার ব্যাপারে অভিযোগ করিনি। তবে একবার আমি ধৈর্য্ ধরে রাখতে পারিনি। আমার পায়ে জুতা ছিলনা এবং জুতা কিনার মত অর্থও ছিল না। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কুফার মসজিদে গিয়ে উঠলাম। তথায় গিয়ে দেখি একটি লোক শুয়ে আছে যার একখানি পা-ই নেই। তখন খোদাকে শোকর জানিয়ে নিজের খালি পা থাকাও গনিমত মনে করলাম।’
শেখ সাদী তাঁর দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য বিচিত্র সব ঘটনা দেখেছেন। তিনি দেখেছেন-বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান পতন। তিনি উজিরের ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখেছেন। আবার ভিক্ষুককে দেখেছেন উজির বনে যেতে। তিনি এও দেখেছেন মুসলিম সাম্রাজ্যের শৌর্য্ বীর্য্, সাথে সাথে পতনের দৃশ্য। তাঁরই সামনে তাতারদের হাতে সাত লক্ষ মুসলমান খুন হয়েছে। খোরাসানের চারটি শহর, বলখ, মরদ, হেরাত এবং নিশাপুর ধ্বংস হতে দেখেছেন।
শেখ সাদী বড় বড় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন। এ সময়ে তিনি দেখেছেন ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে মানুষ মারা যায়। তিনি নিজেই আরবী একটি মর্সিয়ায় বলেছেন-
আব্বাসীয় খেলাফতের ধ্বংসের পর
যে সমাধান হয়েছে
খোদা তার সহায় হোক।
কেননা
যায়েদের বিপদ
উমরের চোখ খুলবে।
এই মহান মনীষী কবিকুল শিরোমণি শেখ সাদী ৬৯১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২ খৃস্টাব্দে আতাবকানের বংশের রাজত্বের শেষ সময়ে শিরাজ নগরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশত কুড়ি বৎসর। শিরাজ নগরীর দিলকুশার এক মাইল পূর্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে কবিকে সমাহিত করা হয়।
\r\n\r\n
মহাকবি হাফিজ সিরাজী
“হে হাফিজ তোমার বাণী চিরন্তনের মত মহান। কেননা, তার জন্য আদি ও অন্ত নেই। তোমার ভাষা আসমানের গম্বুজের মত একাকী নিজের ওপরই স্থিত। তোমার গজলের অর্ধেকটায় বা প্রথম কলিতে কিংবা অন্য কোন অংশের মধ্যে মোটেও পার্থক্য করা যায় না। কেননা এর সবটাই সৌন্দর্য্ ও পূর্ণতার নিদর্শন। একদিন যদি পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়, হে আসমানী হাফিজ! আমার প্রত্যাশা যে, একমাত্র তোমার সাথে ও তোমার পাশে থাকবো। তোমার সঙ্গে শরাব পান করব। তোমার মতই প্রেমে আত্মহারা হব। কেননা এটাই আমার জীবনের গৌরব ও বেঁচে থাকার পাথেয়।” (ওয়ালফ গঙ্গ গ্যেটে)
যার সম্বন্ধে মহাকবি গ্যেটে একথা বলেছেন তিনি হলেন বিশ্বের কবিকুল শিরোমনি হাফিজ শিরাজি। তাঁর পুরো নাম হলো খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী। বিশ্বের বিরল কবি ব্যক্তিত্ব হাফিজ শিরাজি। ৭১০ হতে ৭৩০ হিজরী সনের মধ্যে ইরানের শিরাজ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বাহাউদ্দীন সুলগারী। কবি শিরাজ ছিলেন পিতা সুলগারীর কনিষ্ঠ পুত্র। কবির দাদা ছিলেন ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের ‘কুপাই’ নামক স্থানের অধিবাসী। আতাবক শাসন আমলে তিনি সপরিবারে কুপাই ত্যাগ করে ফারছ এর রাজধানী শিরাজ নগরীর রুকনাবাদ নামক মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। কবির মায়ের জন্মস্থান ছিল ‘কাজেরুণ’ নামক স্থানে।
হাফিজ শিরাজী অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। যে কারণে পাঠশালায় গমনের পরিবর্তে রুটি রুজির তাগিদে তিনি একটি রুটির দোকানে কাজ নেন। এখানে তাঁকে শেষ রাত পর্যন্ত কঠোর শ্রম দিতে হত। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুলের জীবনের সাথে একান্ত মিল দেখতে পাই। কাজী নজরুল ইসলামও শিশুকালে ইয়াতিম হন এবং জীবিকার জন্য রুটির দোকানে কাজ নেন। কবি শিরাজী যে পথ দিয়ে রুটির দোকানে যেতেন ঐ পথেই ছিল একটি মক্তব। আসা-যাওয়ার পথে তাঁর মনে কোরআন শিক্ষার ইচ্ছা জাগে। তিনি মক্তবে ভর্তি হন এবং রুটির দোকানে কাজের পাশাপাশি লেখাপড়ার কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিরাজী সমস্ত কুরআন কন্ঠস্থ করেন ও লেখাপড়ায় অশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তোমরা শুনলে বিস্মিত হবে যে, তিনি চৌদ্দটি পদ্ধতিতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন,
‘হে হাফেজানে জাহান ছুবন্দে জাম না কারদ
লতায়েফে হুকমী বা নেকাতে কোরআনী।’
অর্থাৎ, ‘জগতের মাঝে এমন হাফেজ পাবে নাকো খুঁজে,
আমার মত যে কুরআনের তত্ত্বে দর্শন বুঝে’।
জানা যায় তিনি রুটির দোকানে কাজ করে যে কাজ করতেন তা চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে একভাগ তাঁর মায়ের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষকদের জন্য, তৃতীয় ভাগ ফকীর মিসকীনদের জন্য এবং চতুর্থভাগ রাখতেন নিজের হাত খরচের জন্য। কবির দিওয়ানে ই হাফিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিকহ), হাদীস, ন্যায়শাস্ত্র (কালাম), তাফসীর, ফার্সী সাহিত্য ইত্যাদিতে সুপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি তিনি জ্যোতিষ বিজ্ঞানের জ্ঞানও আয়ত্ব করেছিলেন।
কবি শিরাজী তাঁর যৌবনকালেই লেখালেখিতে হাত পাকিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যতদূর সম্ভব তিনি শাহ শেখ আবু ইছহাকের প্রশংসা কীর্তন আছে। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশাই তিনি মুজাফফর বংশীয়দের শাসনকালও অবলোকন করেন। যাই হোক কবি তাঁর জীবদ্দশাতেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জনে সক্ষম হন। যদিও তাঁর সময়টা ছিল সাহিত্য ও কাব্যচর্চার জন্য খুবই খারাপ সময়। কারণ এ সময়টাতে তাঁর দেশে নানা রকম হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ বিরাজমান ছিল।
কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্তবৃন্দ তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। বাগদাদের সর্বগুণান্বিত সুলতান আহমদ বিন আবেস কবি হাফিজকে বাগদাদে পাওয়ার জন্য বারবার আমন্ত্রণ পাঠাতে থাকেন কিন্তু কবি প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ঐ সময় কোথাও যেতে রাযী ছিলেন না। তাই সম্রাটের আহবানকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
ইস্পাহানের শাসনকর্তার মন্ত্রী উম্মাদ বিন মাহমুদ কবিকে দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু কবি এ দাওয়াতও কবুল করেন নি। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান শাহ মাহমুদ কবি সাহিত্যিকদের অসম্ভব সম্মান করতেন। দেশ বিদেশের কবি সাহিত্যিকদের তিনি নানা সম্মানে সম্মানিত করতেন। এ সময়ে কবি হাফিজ দাক্ষিণাত্যে আসার জন্য ইরাদা করেছিলেন কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।
বাঙালীদের জন্য গর্বের বিষয় হল, সে সময়কাল বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ কবি শিরাজীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি না আসতে পারলেও সে কথা তার কবিতায় লিখে গেছেন। কথিত আছে গিয়াসউদ্দীনের তিনজন প্রিয় দাসী ছিলেন – এদের নাম সরব, গুল ও লালা।
সুলতান একদিন এ চরণটি ফাঁদলেন—
‘সাকী হাদীসে সারবো গোলো লালা মিরওয়াদ’ কিন্তু আর পরবর্তী চরণটি পূরণ করতে পারলেন না। সভাকবিরাও সুলতানের মনপুত কিছু দিতে পারলেন না। তখন সুলতান উক্ত লাইনটি কবি হাফিজ শিরাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবি হাফিজ শিরাজী এর উত্তরে কবিতাটি পূর্ণ করে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবিতাটি এ রকম-
‘সাকী হাদীসে সারবো গোলো লালা মিরওয়াদ
ওইন বাহাস বা সালাসায় গোসালা মিরওয়াদ।
…………………………………………….
হাফিজ যে শওকে মজলেসে সুলতান গিয়াছোদ্দিন
খামুশ মালো কে কারে তু আজ লালা মিরওয়াদ।
কবিতাটির শেষ দু’লাইনের অর্থ হলো-‘হে হাফিজ সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মজলিসে চুপ করে থেকোনা, কেননা তাঁর কাজ কান্নার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।’
কবি শিরাজী সুলতান গিয়াসউদ্দীনের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর বাংলায় আসার জন্য মনস্থির করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু সাইক্লোন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে আসতে পারেন নি। আমাদের গর্ব হল কবিকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে বাংলা ও বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ইরানের সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।
কবি হাফিজ শিরাজী কাব্য প্রতিভা ও দর্শন সারা পৃথিবীর কাব্যা মোদী ও চিন্তাশীল মনকে যুগে যুগে নাড়া দিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার মহান কবি ও চিন্তাবিদ গ্যেটে(১৭৩৯-১৮৩২)বলেন, ‘হঠাৎ প্রাচ্যের আসমানী খুশবু এবং ইরানের পথ-প্রান্তর হতে প্রবাহিত চিরন্তন প্রাণ সঞ্জীবণী সমীরণের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন এক অলৌকিক ব্যক্তিকে চিনতে পারলাম, যার বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আমাকে আপাদমস্তক তার জন্য পাগল করেছে।’ মহাকবি গ্যেটে হাফিজের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে, ‘একটি সময়ের জন্য সবকিছুকে এবং সবাইকে ভুলে যান এবং নিজেকে ফার্সী ভাষার এই কবির ক্ষুদ্র ভক্ত বলে অনুভব করেন।’ এমন কি তিনি হাফিজের প্রেমানুভূতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকাব্য ফাউস্ট (FAUST) রচনা করেন। যেটাকে পাশ্চাত্য দিওয়ান বলা হয়।
বাংলা ভাষাভাষী কবি সাহিত্যিকদেরও তিনি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরতো নিজে ১৯৩২ সালে ইরানের শিরাজ নগরে কবির মাজারে উপস্থিত হয়ে ম্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন। এমনকি কবির পিতা মহর্ষি দেবন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এই ব্যাপারে লিখেছেন, ‘আমি জানি যে হাফিজের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতাকে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ঞবদের দর্শন ও সঙ্গীত ততখানি করতে পারত না। হাফিজ ছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক আনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিকতেন না। হাফিজের কবিতাই তাঁর সৃষ্টির আকাঙ্খাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তার ক্ষুধা নিবারণ করত এবং হাফিজ তাঁর তৃষ্ঞা মিটাত।’ জানা যায় মহর্ষি দেবন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরো দিওয়ান মুখস্ত ছিল।
গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ঞচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কান্তিচান্দ্র ঘোষ, হরেন্দ্র নাথ দেব প্রমুখ বিখ্যাত কবিরা কবি হাফিজের বহু রুবাইয়াৎ ও গযল অনুবাদ করেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজকে এত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন যে, তাঁর পুত্র বুলবুলের মৃত্যুশয্যায় বসেও তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন। তিনি ফার্সী থেকে মোট ৭৩ টি রুবাই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি যেদিন অনুবাদ শেষ করেন সেদিন কবি পুত্র বুলবুল ইন্তিকাল করেন। কবি তাই বেদনার সাথে লিখেছেন, ‘আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলাদশে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইরানের কবি সম্রাট হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। কিন্তু তিনি আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারতেন না।’
ফার্সী সাহিত্যের আলোচনা করে লেখা গ্রন্থটি হচ্ছে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ‘পারস্য প্রতিভা’। এ গ্রন্থে কবি হাফিজের ওপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন লিখেছেন, ‘ইরানের কবি’। অবশ্য এ গ্রন্থে ‘শামসুদ্দিন হাফিজ’ নামে যে নিবন্ধটি আছে তা তেমন তথ্যবহুল নয়।
বাংলা ভাষায় দিওয়ানে হাফিজের বহু অনুবাদ হয়েছে। এরমধ্যে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অনুবাদ কর্মটি বাংলা ভাষার এক অসামান্য প্রকাশনা। এ বইয়ের দীর্ঘ উপক্রমিনাতে তিনি হাফিজকে বাংলা ভাষাভাষির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে কাজী আকরাম হোসেনের অনুবাদটিও চমৎকার। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার দু’জন আধুনিক কবি যারা প্রগতিবাদী হিসেবেও পরিচিত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুবাশ মুখোপাধ্যায় কবি হাফিজের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছেন।
কবির ৬০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, ‘কবি হাফিজ আমাদের চিন্তায় ও মননে বহুকাল বিদ্যমান ছিলেন। বাংলা কবিতায় আবার তিনি নতুন করে জাগ্রত হচ্ছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষায় হাফিজ ছিলেন অনেক বড় প্রতিভা, অনেক বড় কবি এবং প্রেমিক। কবির কুরআনের ওপর দক্ষতা দেখে সমকালীন একজন পীর মুর্শিদ তাঁকে হাফিজ উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ব্যাপার কবি নিজেই লিখেছেন-
‘হাফিজ! তোমার চেয়ে সুন্দর গান আর দেখিনাই আর কারো
তোমার মুখের লুকানো কোরান সে তো সুন্দর আরো।’
কবি ছিলেন একজন সুন্দর প্রেমিক। তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে লিখেছেন-
‘প্রেয়সী মোর ছিল যে হায় পরীর মত অপসরী
পা থেকে তার কেশাগ্রতক নিটোল যেন ঠিক পরী।’
কবি তাঁর আদরের সন্তানের মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে লিখেছেন-
‘মোর নয়ন মণি দীলের মেওয়া তাহার তরে কাঁদে প্রাণ
হাসতে হাসতে চলে গেল, শোকে আমি ম্যূহমান।’
যদিও এখানে আপন সন্তানের জন্য কবি হাফিজ এ আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু এ শোক বাণী জগতের সব পুত্রহারা পিতৃ হৃদয়কে নাড়া না দিয়ে পারে না।
ও যাহ! একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি। দিগ্বিজয়ী মঙ্গল বীর তৈমুর লঙ কবির একটি কবিতা বুঝতে না পেরে কবিকে তলব করেন। কবিতাটি ছিল-
সেই শিরাজী প্রেমিক যদি জয় করে মোরে এই হিয়ারে
তার গালের তিলে বিলিয়ে দেব সমরকন্দ আর বুখারারে। (দিওয়ানে হাফিজ-গজল নং ৩)।
তৈমুর লঙ কবির কাজে জানতে চাইলেন, এ কবিতা কার? কবি যখন স্বীকার করলেন এ তারই কবিতা, তখন তৈমুর লং বললেন, ‘আমি হাজার হাজার সৈন্যের রক্তের বিনিময়ে হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে যা দখল করেছি, হাজারো লক্ষ ধন সম্পদ রত্নরাজির বিনিময়ে যা গড়ে তুলেছি, আর তুমি নারীর গালের কালো তিলের বিনিময়ে তা বিলিয়ে দিতে চাচ্ছ?
কবি বুঝলেন, যুদ্ধবাজ তৈমুরের মাথায় কাব্যের মহিমা ঢোকার কথা নয়। কবি তাই বিনীতভাবে বললেন, ‘মহামান্য বাদশাহ। এভাবে দান খয়রাত করতে গিয়েই তো আমার আজ এ দীন হীন অবস্থা। আপনি আমার মত করেন নি বলেই তো আপনি আজ জগদ্বিখ্যাত সম্রাট।’
কবি হাফিজের উপস্থিত চমৎকার উত্তরে তৈমুর লং খুশি হলেন। তিনি কবিকে সোনার আশরাফী উপহার দিয়ে বিদায় করলেন।
বিশ্বখ্যাত এই মহান কবি খাজা সামশুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী ৭৯১ হিজরী সালে শিরাজ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কবির মাজার শিরাজ নগরেই অবস্থিত। এখন এলাকাটি ‘হাফেজিয়া’ নামে প্রসিদ্ধ।
\r\n\r\n
হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)
ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সমস্ত ওলীয়ে কামেল ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছেন এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত উলূঘ খান জাহান(র.) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ মহান মনীষীর সাথে যে সমস্ত শিষ্যগণ ছিলেন তাঁরাও স্ব স্ব মহিমায় খ্যাতিমান হয়ে আছেন। কিন্তু এই বাংলার সন্তান একেবারে খাস বাঙালী কোন শিষ্য, হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.) এর মত যশস্বী হতে পারেন নি।
আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে মুহাম্মদ তাহির জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে নীলকান্ত বলেছেন-
‘পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইলো সর্বনাশ।’
তাঁর পূর্ব নাম ছিল গোবিন্দ ঠাকুর। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে খাট চোখে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘তাঁহার পূবে কি নাম ছিল জানিনা, জানিয়াও কোন কাজ নেই। এখন তাঁহার নাম তাহির।(যশোহর খুলনার ইতিহাস. ১ম খন্ড ৩৩৩ পৃষ্ঠা, শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র)। অবশ্য এ.এফ.এম. আবদুল জলীল সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, ‘বহুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিল গোবিন্দলাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি খান জাহানের বিশেষ প্রিয় পাত্র ও আমত্য ছিলেন।’(সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা-এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)। তিনি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী(র.) এর পরশে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রধান সহচরে পরিণত হন। হযরত উলুঘ খান জাহান আলীর এ দেশীয় শিষ্যদের মধ্যে হযরত পীর অলী মুহাম্মদ তাহিরই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জননন্দিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমারা পীরেলি নামে পরিচিত হন।
পীরেলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ. এফ. এম. আবদুল জলীল সাহেব লিখেছেন, ‘পয়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর অলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোহর অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ খান জাহানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করেন। তাঁহার নাম মুহাম্মদ তাহের। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। সতীশ বাবু তাহার সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়ো আত্মহিংসাই করিয়াছেন। কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ্য লাভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতি ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।’(সুন্দরবনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড ৩৩২, এ.এফ.এম আবদুল জলীল)। এ. এফ. এম. আবদুল জলীল অন্যত্র লিখেছেন-‘খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহি প্রাচীন হিন্দু প্রধান। সেনহাটি, মুলঘর কালিয়া প্রভৃতি স্থানের বহুপূর্বে এখানে উচ্চশ্রেণীর বসবাস ছিল। এই গ্রামের নাম ছিল পয়োগ্রাম, এখনও এ নাম আছে। এখানকার রায় চৌধুরী বংশের তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ তুর্ক আফগান আমলের প্রথম দিকে এ ব্রাহ্মণ বংশ রাজ সরকার হইতে সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহারা কনোজাগত ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ইহার গুড়ি বা গুড়গাঞী ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত। এই বংশের কৃতি সন্তান দক্ষিণা নারায়ণ ও নাগরা নাথ। কথিত আছে যে দক্ষিণা নারায়ণ দক্ষিণ ডিহি এবং নাগর উত্তর ডিহির সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।
দক্ষিণ ডিহি নামের সহিত দক্ষিণা নারায়ণের সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নাগর বেজের ডাঙ্গায় একটি হাট বসাইয়াছিলেন। উহার নাগরের হাট নামে পরিচিত ছিল। খান জাহানের আমলে চৌধুরীগণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন। নাগর নিঃসন্তান। ভ্রাতা দক্ষিণা নারায়ণের চারিপুত্র ছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব এই নবগত শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালিদের উৎপত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (সুন্দরবনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড ৩৩২, এ.এফ.এম আবদুল জলীল)।
এ সম্পর্কে মি. ওমালি বলেন, ‘খান জাহান একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ নিতে থাকেন। ইহাতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী মোহাম্মদ তাহের (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি) বলেন যে, ‘ঘ্রাণেন কার্ধ বোজনং’ অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধভোজন। খান জাহান পরে একদিন খানাপিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহার নাকে কাপড় দিলে খান জাহান বলেন, যখন ঘ্রাণে অর্ধভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তদনুসারে তাহের ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাহেরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি হিন্দু থাকিয়া যান। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দু পীরালি এবং তাহেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীরালি বলত। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এদেশে পীরালি গান এবং বহু কাহিনী রচিত হয়। ঐকান্তিক ধর্ম নিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহের পীরালি আখ্যা পান।”(সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৩/৩৩৪ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
অন্য এক বর্ণনা মতে “মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে জয়দেব ও কাবদেব এর অন্তরের মিল ছিল না। তাহের মনে মনে তাঁহাদিগকে মুসলমান করার চেষ্টা করিতেন। এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহা কতটুকু সত্য তাহা জানি না। গল্পটি বর্ণনা করিতেছি-একদিন রমজানের সময় তাহের রোজা রাখিয়াছেন। দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ বসিয়া আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার বাটি হইতে একটি সুগন্ধী নেবু আনিয়া তাহাকে উপহার দেন। পীরআলী নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময় কামদেব বলিলেন হুজুর, ঘ্রাণে অর্ধভোজন-আপনি গন্ধ শুকিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন? এ কথার পর পীরআলী ব্রাহ্মণের প্রতি চটিয়া যান। গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবেন। নির্ধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহের প্রাঙ্গনে গো-মাংসের সহিত নানারকম মশলা দিয়া রন্ধনকার্য্ ধুমধামের সহিত চলিল। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপুর। জয়দেব ও কামদেব নাকে কাপড় দিয়া প্রতিরোধ করিতেছিলেন। পীরআলী নাকে কাপড় কেন জিজ্ঞাসা করিলে কামদের মাংস রন্ধনের কথা উল্লেখ করেন। পীরআলী নেবুর গল্প উল্লেখ করিয়া বলেন-‘এখানে গো-মাংস রান্না হইতেছে। ইহাতে আপনার অর্ধেক ভোজন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি জাতিচ্যূত হইয়াছেন।’
অতঃপর জয়দেব ও কামদেব উক্ত মাংস খাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। পীরআলী তাঁহাদিগকে জামাল উদ্দীন, কামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়া আমত্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দু্ই ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীরালি ব্রাহ্মণ নামে সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহাই পীরালি সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিকথা।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৩/৩৩৪ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
এ প্রসঙ্গে জনৈক নীলকান্তের বরাত দিয়ে ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ গ্রন্থে ঘটকদিগের পুঁথি থেকে কিছু উল্লেখ করেছেন, তা হল-
খানজাহান মহামান পাতশা নফর।
যশোর সনন্দে লয়ে করিল সফর।।
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।।
পূর্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি।
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি।।
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ।।
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় হইল হাজির।।
এখানে লেখক খান জাহানকে কোন মুসলমান সুলতানের সনদ প্রাপ্ত প্রশাসক বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর মুহাম্মদ তাহিরের পরিচয় তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নয় বরং কোন নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলমান হয়েছে। প্রকারান্তরে লেখক(সম্ভবত) বলতে চেয়েছেন ইসলাম প্রচার এদেশে কৌশলে হয়েছে। পুঁথির অন্যত্র এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-
আঙ্গিনায় বসে আছে উজির তাহির।
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির।।
রোজার সে দিন পীর উপবাস ছিল।
হেনকালে একজন নেবু এনে দিল।।
গন্ধামোদে চারিদিক ভরপুর হইল।
বাহবা বাহবা বলে নাকেতে ধরিল।।
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন।
বসে ছিল সেইখানে বুদ্ধি বিচক্ষণ।।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।
ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে।।
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোহের মনে কৈলা স্থির।।
দিন পরে মজলিস করিল তাহির।
জয়দেব কামদেব হইল হাজির।।
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
শত শত বকরী আর গো-মাংস রন্ধন।।
পলান্ডু রশুন গন্ধে সভা ভরপুর।
সেই সভায় ছিল আরও ব্রাহ্মণ প্রচুর।।
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে বলে কত পালাইল।।
কামদেব জয়দেব করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন।।
জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।।
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি তো চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা।।
উপায় না ভাবিয়া দোহে প্রমাদ গণিল।
হিতে বিপরীত দেখি শরমে মরিল।।
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর।
থতমত খেয়ে দোহ হইল অস্থির।।
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
পীরালি হইল তাঁরা হইল জাতি ভ্রষ্ট।।
কামাল জামাল নাম হইল দোহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ে গেল হাহাকার।।
তখন ডাকিয়া দোহে আলী খানজাহান।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান।।
‘নবদীক্ষিত জামালউদ্দীন ও কামাল উদ্দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পাইয়া সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব খান জাহানের পয়গাম তৈরির পরেই হয়েছে। কথিত আছে খান জাহান তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বাগেরহাট অবস্থানকালে এই দুই ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে তথায় আসিতেন। বাগের হাটের পশ্চিমে সোনাতলা গ্রামে আজিও কামাল খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৬ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
ছল ছাতুরী বা কলা কৌশল নয় ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমানরা পীরেলি নামে পরিচিত হন। আর যে হিন্দু মুসলমান হতেন, তার হিন্দু আত্মীয়রা ঐ বংশের লোকদেরকে সমাজচ্যূত করত। তারা পীরেলি ব্রাহ্মণ বা পীরেলি কায়স্থ নামে পরিচিত হন। এই পীরেলিদেরকে কুলীণ ব্রাহ্মণরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতেন-
মোসলমানের গোস্ত ভাতে
জাত গেল তোর পথে পথে
ওরেও পীরেলী বামন।
জানা যায়, ‘পীরেলি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বহন করতো। তাই দেখতে পাই, কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিঙ্গিয়ার মুস্তফী পরিবার, দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী পরিবার, খুলনার পিঠাভোগের ঠাকুর পরিবার, এই পীরালিদের উত্তরাধিকার হিসাবে চিহ্নিত। কবি রবীন্দ্রনাথও এই পীরালি ঠাকুর পরিবারেই সন্তান।
সংশ্রব দোষে রায় চৌধুরী পরিবারের লোকেরা পুত্র কন্যার বিবাহ লইয়া বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা প্রতিপত্তি ও অর্থ বলে সমাজকে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে লাগিল। ইহাদের সহিত কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং আরও কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে পতিত হইয়াছিল। কলিকাতার ঠাকুরগণ ভট্টনারায়ণের সন্তান এবং কুশারী গাঁঞিভুক্ত ব্রাহ্মণ। খুলনা জেলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিল। পীঠাভোগের কুশারীগণ রায় চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পীরালি হন।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৭ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)। ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, ব্রাহ্মণ কান্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অংশের ১৭২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, ‘বর্তমান কালে খুলনা জেলার অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী মহাশয়েরা চেঙ্গুটিয়ার গুড় চৌধুরীগণের ন্যায় শক্তিশালী প্রবল শ্রোত্রিয় জমিদার ছিলেন। ইহারা শান্ডিল্য ভট্টনারায়ণ পুত্র দীন কুশারীর বংশধর। যে সময় শুকদেব রায় চৌধুরী বিশেষ বিখ্যাত জমিদার হইয়াছিলেন।ইনি পিঠাভোগের কুশারী বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত খানের কোন আত্মীয় হওয়াই সম্ভব।’(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কান্ড, তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ অংশের ১৭২ পৃ., নরেন্দ্রনাথ বসু)।
“কুশারী বংশের পঞ্চানন থেকেই পরবর্তীকালে কলকাতার বিখ্যাত জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।”(খুলনা জেলায় ইসলাম, মুহম্মদ আবু তালিব, পৃ. ৭১)।
অন্যদিকে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁকে অনেকেই পীরালী বংশোদ্ভুত মনে করেন। এ প্রসঙ্গে এ.এফ.এম. আবদুল জলীল বলেন, “মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এই পীরালী বংশের কৃতি সন্তান। তাঁহার আত্মীয় স্বজন পীরালি খাঁ বলিয়া পরিচিত। আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার বংশ পীরালি তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, গৌড়ের সুলতান যদু বা জালাল উদ্দীনের সময় হইতে তাঁহারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর। (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৭ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
এ বিষয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, “সমস্ত রায় চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিণত হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বংশ খান চৌধুরী নহে, শুধু খাঁ উপাধিধারী।”(সুন্দরবনের ইতিহাস, ৩৩৭ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
অন্যত্র এ.এফ.এম. আবদুল জলিল সাহেব লিখেছেন, ‘কলিকাতা এবং স্থানীয় সম্ভাব্য সমস্ত সূত্র হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিলাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর যেরূপ রক্তের সম্পর্ক, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সম্পর্ক ঠিক ততটুকু।’ (সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খন্ড ৩৩৮ পৃ., এ.এফ.এম. আবদুল জলীল)।
“হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির পয়গ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। জানা যায়, পরে তিনি খলিফাতাবাদ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।”(হযরত খানজাহান আলী(র), পৃ. ৬-সেলিম আহমদ)।
প্রখ্যাত গবেষক জনাব অধ্যাপক আবূ তালিব বৈষ্ঞব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, “সত্যি বলতে কি, পীরালি আবু তাহিরই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বসূরী। আবূ তাহিরের আবির্ভাব যাদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, শ্রী চৈতন্য তাদেরকে বৈষ্ঞব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।(খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃ.-মুহাম্মদ আবূ তালিব)।
এরপরই তালিব সাহেব বলেছেন, “ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে পীরালী সাহেব শ্রীচৈতন্যের দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁরই পথের অনুসারী ছিলেন। আরও বলা যেতে পারে, নির্যাতিত হিন্দু পীরালী সমাজ একাধারে চৈতন্যের ধর্ম ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।(খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃ.-মুহাম্মদ আবূ তালিব)।
যা হোক পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় পয়গ্রাম কসবায়। “হযরত খানজাহান এই গ্রামটিকে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত রাজধানী শহর করার সুসংবাদ প্রদান করেন। এবং অবিলম্বে গ্রামটিকে একটি ‘কসবা’ বা শহরে পরিণত করেন। (খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৮ পৃ.-মুহাম্মদ আবূ তালিব)।
পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের জন্মস্থান হচ্ছে যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার(বর্তমানে জেলা) পেড়োলি গ্রামে। হযরত পীর আলী’র নামেই গ্রামটির নামকরণ হয় ‘পীরালী’। বর্তমানে নামটির বিকৃত রূপ হচ্ছে ‘পেড়োলি’।
হযরত পীর আলী’র নিকট এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ মুসলমান হন যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ আর ছিলনা বললেই চলে। এজন্য অন্যান্য হিন্দু ব্রাহ্মণগণ ভয় পেয়ে যান ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর স্বাক্ষ্য মেলে-
পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যবেত যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ জবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।।
কবি আরো বলেন-
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গায়েতে নবদ্বীপের হৈল সর্ববনাস।।
অথবা
“বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের আড়ে।
৮৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৪৫৯ সালে এ মহান কামেলে দ্বীন ও ইসলাম প্রচারক ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাজার বাগেরহাট হযরত উলূঘ খান জাহান আলীর(র) মাজারের পাশেই আছে। এ সম্বন্ধে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন, “মুহাম্মদ তাহির এখানে মারা যান নাই, এখানে মাত্র তাঁহার একটি শূন্যগর্ভ সমাধিবেদী গাঁথা রহিয়াছে।…..বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন রাখা কর্তব্য এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সেই একই জেলহ্জ্জ মাসে মুহাম্মদ তাহিরের জন্য এই স্মৃতি স্তম্ভ গঠিত করিয়া রাখিয়া যান। সমাধির উপরিভাগটি প্রায় খান জাহানে সমাধির ন্যায়, তবে ইহার ভিতরে কিছুই নাই, সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা যায়।” (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৮, সতীশ চন্দ্র মিত্র)। সতীশ বাবুর এই মন্তব্যের সহিত আমরা কোনভাবেই একমত হতে পারিনা। কবরের নীচে এ ধরনের সুড়ঙ্গের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রযেছে। তা’ছাড়া আমরা পূর্বেই তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেছি।
তাঁর শিলালিপিতে লেখা আছে, “হাজিহি রওজাতুন মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি ওয়া হাজিহি সাখরিয়া তুল লিহাবীবিহি এসমুহু মুহাম্মদ তাহির ছালাছা সিত্তিনা ওয়া সামানিয়াতা।” অর্থাৎ এই স্থান বেহেশতের বাগিচা সদৃশ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর মাযার, নাম-আবু তাহির, ওফাতকাল-৮৬৩ হি/১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। এই একই বৎসর হযরত খান জাহান (রঃ) এর ওফাত হয়।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি
\r\n\r\n
মহাকবি আলাওল
আমরা যাকে নিয়ে আজ আলোচনা করব তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি। আধুনিককালেও যাঁকে মহাকবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এইএই বহুভাষাবিদ পন্ডিত, অনুবাদক মহাকবি আলোচনার পূর্বে তাঁর যুগ সম্বন্ধে জেনে নিলে মনে হয় সবার জন্য সুবিধা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরাতন বলে মনে করা হয়। এই হাজার বছরকে পন্ডিতরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন-প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। ৬৫০ হতে ১২০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, ১২০১ হতে ১৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০১ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগ। অবশ্য হিন্দু পন্ডিতরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ১২০১ হতে ১৩৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ বলে থাকেন। কারণ এই দেড়শ বছর মুসলমানদের ভারত আগমন তথা বাংলাদেশ দখলের দরুণ কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে তারা মনে করে। অথচ সত্যি কথা হলো এই সময়েও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন শূন্য পূরাণ, কলিমা জালাল বা নিরঞ্জনের রুষ্মা, ডাক ও খনার বচন, সেক শুভোদয়া ইত্যাদি।
কবিগুরু মহাকবি আলাওল বা আলাউল এই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৫৯৭ খৃস্টাব্দে কারো কারো মতে ১৬০৫ বা ১৬০৭ খৃস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য দু’একজন পন্ডিত ব্যক্তি আলাওলের জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে বলে মনে করেন। কিন্তু কবির নিজের উক্তিকে সামনে রেখে প্রায় সকল পন্ডিতগণই ফরিদপুর জেলার জালালপুরের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কবির পিতা ছিলেন ফতেহাবাদের রাজ্যেশ্বর মজলিশ কুতুবের মন্ত্রী। কবি তাঁর পদ্মাবতী কাব্যে আত্মকথায় লিখেছেন—
মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তাহাতে জালাল পুর অতি পূণ্যস্থান।।
বহুগুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা।।
মজলিস কুতুব তখত অধিপতি।
মুই দীনহীন তান অমাত্য সন্তুতি।।
মহাকবি আলাওল ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত এক কবি। তিনি কৈশর বয়সে মন্ত্রী পিতার সাথে কার্যোপলক্ষে কোথাও যাত্রাকালে পথিমধ্যে দুর্ধর্ষ হার্মাদ জলদস্যূর কবলে পড়েন। কবির পিতা জলদস্যুদের হাতে শহীদ হন। কবি আহত হলেও প্রাণে রক্ষা পান। এরপর অনেক দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি আরাকানে এসে উপস্থিত হন। বেঁচে থাকার তাগিদে কবি মগরাজার সেনাবাহিনীতে রাজ-আসোয়ারের চাকরি গ্রহণ করেন। রাজ আসোয়ার মানে অশ্বারোহী সৈনিক। এ সময় আরাকান রাজসভায় একটি চমৎকার সাহিত্যিখ আবহাওয়া বিরাজ করছিল। গুণী ব্যক্তিদেরকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হত সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। কবি নিজেই লিখেছেন-
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পন্ডিত, গুণবন্ত।।
ফলে অচিরেই কবি আলাওলের গুণগরিমা, বিদ্যা বুদ্ধি ও সাহিত্য প্রতিভার কথা অভিজাত মহলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। কবি বলেন,
তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরেরে।
অন্নবস্ত্র দিয়ে সবে পোষন্ত আদরে।।
মূলত এখান থেকেই আলাওলের কাব্য সাধানার শুরু এবং এক আমত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ক্রমাগত ১৬৫১ খৃ. হতে ১৬৭৩ খৃ. পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মাঝে কবির উপর বয়ে যায় অনেক ঝড়ঝঞ্জা। কবিকে অনেক কষ্ট ক্লেশে নিপতিত হতে হয়। ১৬৫৯ খৃ. শাহসূজা বাংলাদেশ হতে বিতাড়িত হয়ে আরাকান রাজ্যে আশ্রয় লাভ করেন। যে কোন কারণেই হোক ১৬৯১ খৃ. তিনি আরাকান রাজ্যের বিরাগভাজন হয়ে নিহত হন। এ সময়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কবি আলাওল কারারুদ্ধ হন। পঞ্চাশ দিন কারাভোগের পর কবি মুক্তি পান। কিন্তু প্রতিকুল পরিবেশে সবাই কবির বিরুদ্ধে চলে যায়, ফলে তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ঠিক এ সময়ে কবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবির দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায়। এমনকি এ সময় তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রোসাঙ্গ রাজসভার আমত্য সৈয়দ মূসা, সমরসচিব সৈয়দ মুহাম্মদ খান, রাজমন্ত্রী নবরাজ মজলিশ, অন্যতম সচিব শ্রীমন্ত সোলেমান প্রমুখদের নজরে আসেন। ফলে পুনরায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।
তোমরা জানলে খুশি হবে যে, সেই যুগেও মহাকবি আলাওলের জানা ছিল অনেকগুলি ভাষা। তিনি মৈথিল, ব্রজভাখা, ঠেট, খাড়িবোলির মত উত্তর ভারতের উপভাষা ছাড়াও বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে সমান দখল রাখতেন। অপর দিকে তাসাউফ ও যোগতন্ত্রেও ছিল পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান। যার কারণে তিনি অনুবাদে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সত্যি কথা বলতে তাঁর মত অনুবাদক কদাচিৎ দু/একজন মিলে। তিনি কাব্য ক্ষেত্রে ছিলেন স্বচ্ছন্দ্য। কাব্যতত্ত্ব, অলংকার শাস্ত্র ও ছন্দবিজ্ঞান ছিল তাঁর আয়ত্ত্বে। এমনকি তিনি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলায় প্রয়োগ করেন। তার রোসাঙ্গে তিনি তো সঙ্গীত শিক্ষক রূপেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
আলাওল অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে-
১. পদ্মাবতীঃ প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিম মুহাম্মদ জায়সী ‘পদুমাবত’ কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ১৬৫১ খৃস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল ‘পদ্মাবতী’ অনুবাদ করেন। এ কাব্যটি আলাওলের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।
২. সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামানঃ আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের পরামর্শে ও উৎসাহে এ কাব্য লেখা শুরু করেন এবং পরে ১৬৬৯ খৃস্টাব্দে রোসাঙ্গ রাজের আমত্য সৈয়দ মূসার অনুরোধক্রমে তা সমাপ্ত করেন। এটি প্রেম মূলক কাহিনী কাব্য।
৩. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানীঃ দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য আমত্য সুলায়মানের অনুরোধে ও উৎসাহে ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি আলাওলের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।
৪. সপ্তপয়কারঃ পারস্য কবি নিজামীর সপ্তপয়কর নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। রোসাঙ্গরাজের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহাম্মদের আদেশে ১৬৬০ খৃস্টাব্দে আলাওল এটির অনুবাদ করেন।
৫. তোহফাঃ এ গ্রন্থটিও অনুবাদ। বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর ‘তোহফাতুন নেসায়েহ’ নামক ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে আলাওল এ কাব্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। এটি আলাওলের পঞ্চম রচনা।
৬. সেকান্দর নামাঃ এ ষষ্ঠ নম্বর কাব্যটি নিজামী গঞ্জভীর ফারসী সেকান্দর নামা গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল এ কাব্যটি সম্ভবত ১৬৭২ খৃস্টাব্দে রচনা করেন। আরাকান রাজ চন্দ্র সুর্ধমার নবরাজ উপাধীধারী মজলিস নামক জনৈক আমত্যের অনুরোধে আলাওল সেকান্দরনামা অনুবাদ করেন।
সঙ্গীতবিদ হিসেবেও আলাওলের প্রচুর খ্যাতি ছিল। তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বেশ কিছু গীতও রচনা করেছেন। অপরদিকে তিনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ঞবপদও রচনা করেছেন।
কবি ‘মুকীম’ তার সম্বন্ধে লিখেছেন-
গৌরবাসী রৈল আমি রোসাঙ্গের ধাম
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম।
যদিও কবি আলাওলের রচনা অনুবাদ প্রধান তবুও তার অনুবাদ মৌলিক রচনার সমপর্যায়ের। এই অসাধারণ প্রতিভাবান কবি, মহাকবি আলাওল আনুমানিক ৭৬ বছর বয়সে ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।
\r\n\r\n
শাহসূফী মুজাদ্দিদে যামান আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.)
চৌদ্দশতকে উপমহাদেশে যে সমস্ত পীরে কামেলের পরিচয় আমরা পাই, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সময়ে ভারত উপমহাদেশে এত ব্যাপকভাবে গৃহীত আর কোন ব্যক্তি হতে পারেন নি। যার কারণে তিনি উভয় বাংলায় মুসলমানতো বটেই হিন্দুদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। সত্যি কথা বলতে কি এখনো পর্যন্ত তাঁর মুরীদগণ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এই সূফী শ্রেষ্ঠ ও ইসলাম প্রচারক আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরায় ১২৫৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যেটা বর্তমানে ফুরফুরা শরীফ নামে পরিচিত। জন্মের মাত্র ৯ মাস পর তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোলাম মুকতাদীর। মাতা মুহব্বতুন্নিসা এতিম পুত্র আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) কে লালন পালন করেন এবং তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।
হযরত আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। প্রথমে সিতাপুর মাদরাসা, পরবর্তীতে হুগলী মুহসিনিয়া মাদরাসায় পড়ালেখা করেন। কৃতিত্বের সাথে তিনি মুহসিনিয়া মাদরাসা থেকে তদানীন্তন মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী জামাতে উলা পাশ করেন। পরে কলকাতা সিন্ধুরিয়া পট্টির মসজিদে হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ অধ্যয়ন করেন। মাওলনা বিলায়েত (রহ.) এর নিকট কলকাতা নাখোদা মসজিদে তিনি মানতিক হিকমা প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মদীনা শরীফে যান। সেখানে তিনি হাদীস ও হাদীস সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে তিনি একনাগাড়ে ১৮ বছর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। এমনকি নিরলস অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃত পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং কুতুবুল ইরশাদ হযরত ফতেহ আলী(রহ.) এর নিকট বয়’আত হয়ে ইলমে তাসাওফের সকল তরীকার পূর্ণ কামিলিয়াত হাসিল করেন এবং খিলাফত লাভ করেন।
তিনি শরীয়তের একান্ত পাবন্দ একজন পীরে কামিল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শরীয়ত ব্যতীত মারিফত হয় না। এজন্যই বাংলা, আসামে তাঁর অগণিত মুরীদও একই পন্থা অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, শুধু পীরের সন্তান হলেই পীর হওয়া যায় না। তিনি যে বংশের হউন না কেন যদি শরীয়ত মারিফত ইত্যাদিতে কামিল হন তবে তিনিই পীর হতে পারেন।
হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রহ.) ছিলেন একজন সুবক্তা। যার কারণে তিনি বাংলা আসামের গ্রামে গ্রামে প্রতিটি অলিগলিতে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতে পেরেছিলেন। তিনি ক্ষেত্র বিশেষে কলমও ধরেছেন। তাঁর লেখা কাওলুল হক(উর্দূ) এবং অছীয়ৎনামা(বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় তিনি আল-আদিররাতুল-মুহাম্মদিয়া নামে আরবীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেটি অপ্রকাশিত।
শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টা এবং সহযোগিতায় অসংখ্য মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা পোষণ করতো তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য এদেশের মুসলমানদের প্রতি জোর আহবান জানান। তিনি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদরাসার পাঠ্য তালিকার সংস্কারের জন্য দাবী জানান। তিনি পর্দার সাথে নারীদের শিক্ষা জরুরী বলেও মত প্রকাশ করেন। এমনকি নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যও তিনি উপদেশ দেন। একটি তথ্য অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপন করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার যে প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয় তিনি তার সদস্য নির্বাচিত হন।
তিনি ইসলামী সমাজ হতে শিরক বিদআত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্য ১৯১১ সালে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ‘আঞ্জুমানে ওয়াজীন’ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কাজ ছিল মুসলিম সমাজ হতে কুসংস্কার দূর করার জন্য ওয়াজের ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের জবাব দেওয়া এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা।
তিনি যমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর বাংলা আসামের সভাপতিও ছিলেন। এ সময়ে তিনি আযাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, “রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে আলেমদিগকে সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কাজ হইতেছে।” পরে ‘জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলা আসাম’ গঠন করেন।
১৯৩৮ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরিদান ও সাধারণ মুসলমানদের মুসলিম লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহবান জানান।
তিনি তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত মুসলমানদের পত্র-পত্রিকাগুলোকেও সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশ হয় তা হল-সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকর, মাসিক নবনূর, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক সোলতান, সাপ্তাহিক মুসলিম হিতৈষী, মাসিক ইসলাম দর্শন, সাপ্তাহিক হানাফী, মাসিক শরিয়তে ইসলাম প্র্রভৃতি।
বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর নকীব, সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, মুজাদ্দিদ, অলিয়ে কামিল এদেশের মুসলমানদের নয়নের মণি হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী(রহ.) দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর ১৩৪৫ বাংলা সনের ৩ চৈত্র মোতাবিক ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরা শরীফের মিয়া পাড়া মহল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ এখানে এছালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর খলীফাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-মওলনা রুহুল আমীন, শর্ষিণার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন, মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী(যশোর), মওলানা আবদুল খালেক, মওলানা সদরুদ্দীন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা হাতেম আলী, দ্বারিয়াপুরের পীর মওলানা শাহ সূফী তোয়াজউদ্দীন আহমদ(রহ.) প্রমুখ।
\r\n\r\n
হযরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ.)
সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ) এক চির উজ্জ্বল নক্ষত্র। যখন দক্ষিণ বঙ্গের অলিতে গলিতে চলছিলো হিন্দু ও খৃস্টান মিশনারীদের অপদৌরাত্ম, যখন ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অপপ্রচারের ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করেছিলো তখনই এই মহান সূফী ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেন।
মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীমের(রহ.) পূর্বপুরুষ ছিলেন-হযরত শাহসূফী সুলতান আহমদ। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সময় যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। জানা যায়, সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি যশোর আগমন করেন এবং যশোর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর থেকে যান। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজা ছিলেন শূকদেব সিংহ রায়।
রাজা শূক দেব সিংহ রায় রাজা মানসিংহকে এবং সম্রাট আকবরকে খুশী করার উদ্দেশ্যে শাহ সূফী সুলতান আহমদকে বসবাসের জন্য রাজবাড়ীর খিড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী এলাকা পরে খড়কী এলাকায় পরিণত হয়। বর্তমানে খড়কী যশোর এলাকার একটি অংশ। যশোর সরকারী এম.এম. কলেজ এই খড়কীতে অবস্থিত।
মুগল আমল থেকে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত মওলানা শাহ আবদুল করীম সাহেবের বংশের লোকেরা যশোর অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে আসছেন।
যশোর শহরতলীস্থ খড়কী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারে হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীম ১৮৫২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ সালীম উদ্দীন চিশতী একজন কামিল পীর ছিলেন।
শাহ আবদুল করীম বাল্যকালেই পিতৃহারা হন এবং দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী(রহ)এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।
দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী দীনি ইলমের প্রাথমিক সবক দিয়ে তাঁর হাতেখড়ি দেন। পরে স্থানীয় বিদ্যালয় হতে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি দাদাকে হারান। দাদাকে হারিয়েও শাহ আবদুল করীম তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন নি। তিনি পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে জামা’আতে উলা পাস করেন।
শিক্ষা জীবন শেষে এই মহান মণীষী যশোর জেলা স্কুলে হেড মৌলবী হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন।
শিক্ষকতা করা অবস্থায় তাঁর ভেতর ‘ইলমে তাসাওউফ’ সম্বন্ধে জানার কৌতুহল জাগে এবং সে সম্বন্ধে জানার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েন। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার খালিক(রহ.) এর নিকট মুরীদ হন। এখানে দীর্ঘ বার বছর তিনি তাসাওউফ চর্চায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন এবং ইলমে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পীর তাঁকে নকশ বন্দীয়া মুজাদ্দীদিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া এবং সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার খিলাফত প্রদান করে স্বদেশ ইসলাম প্রচারের নির্দেশ হন।
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং সমাজে কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টা চালান। এ সময় অনেক বিধর্মীই তাঁর সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।
ব্যক্তিগত জীবনে শাহ আবদুল করীম অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে চলাফেরা করতেন। পিতার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি আড়ম্বরহীন, বিনয়ী ও নম্র জীবন যাপন করেছিলেন।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক সময় যশোর জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি এই সময় শাহ আবদুল করীমের একান্ত সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর লেখা আধ্যত্ম পুণ্যময় লকখী ছাড়া গল্পটি পীর আবদুল করীম সাহেবকে লক্ষ্য করে (রমনার পীর সাহেব) লেখা। গল্পের নায়ক রমজানকে ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের সমকালীন প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।
শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম একজন উচ্চস্তরের সাহিত্যিকও ছিলেন। ইলমে তাসাওউফের ওপর তিনি এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব নামক প্রায় তিন’শ পৃষ্ঠা একখানি পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব লিখেছেন, “বইখানি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, এ যাবত বাংলা ভাষায় সূফী বা তাসাউফ তত্ত্বমূলক যত বই লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এ খানি শ্রেষ্ঠ। আবদুল করীম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে একজন নিষ্ঠাবান সূফী, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জ্ঞানে এই রঙিন বইখানি সাধারণ পাঠকের জন্য এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে।
সুবিস্তৃত দশটি অধ্যায়ে তিনি তাসাওউফের দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ সূফী-খান্দানের ইতিকথা, শাজরানামা(পীর-পরম্পরা) ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। শেষ বা দশম অধ্যায়ে তিনি তাসাউফ তত্ত্বের মর্মকথা, অমুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি, যথা-বেদ উপনিষদ পুরানাদির সঙ্গে ইসলামী সূফীতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন।”
শাহ আবদুল করীম সাহেব গ্রন্থটি রচনা করেছেন তাঁর পীর হযরত খাজা আবু সা‘আদ মোহাম্মদ আবুদল খালেক সাহেব এর অনুপ্রেরণায়।
এ সম্বন্ধে শাহ আবদুল করীম সাহেব উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, “পীর সাহেব বলেছেন, তুমি নিজ ভাষায় স্পষ্টভাবে যেমত আমার শিক্ষা পাইয়াছ সেইরূপ একখন্ড কিতাব লিখ। যাহা বুঝিতে লোকের কষ্ট না হয় এবং সন্দেহ ভঞ্জন হয়। কারণ তাসাউফের বিদ্যা ক্রমশ লোপ পাইয়া যাইতেছে; কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞেস করিলে স্পষ্টভাবে তাহার উত্তর পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে; সুতরাং লোকের মূল উদ্দেশ্য পরম সৃষ্টিকর্তা খোদাতালাকে চেনার পথ একেবারে সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি সত্ত্বর কিতাব লিখিতে প্রবৃত্ত হও।”
পীরের নির্দেশ মোতাবিক লেখক তাঁর কিতাবখানি সর্বসাধারণ বোধ্য ভাষায় লিখেছেন। বলাবাহুল্য, ইসলামী চিন্তাধারার এক মৌলিক উৎসের সন্ধান দিয়েছে কিতাবখানি।
গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব শাহাদাত আলী আনসারী বলেন, ‘মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীম সাহেব নকশবন্দীয়া তরীকার একজন কামেল সূফী ছিলেন। সূফী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর গ্রন্থখানিতে প্রথম হতে চতূর্থ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি তাসাওফের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; পঞ্চম হতে নবম অধ্যায়ে সূফী সাধনায় কাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া এবং চিশতীয়া তরিকার বিশ্লেষণ করেছেন এবং দশম হতে শেষ অধ্যায়ে বেদ, পুরান প্রভৃতিতে প্রচলিত বিষয়বস্তুর তত্ত্ব তিনি উদঘাটন করেছেন এবং সূফী মতবাদের সাথে তার তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। তাসাওফ সম্পর্কে বাংলাভাষায় লিখিত এইরূপ দ্বিতীয় কোন বই পাওয়া যায় না।”
শাহ আবদুল করীম(রহ.) এর জীবদ্দশায় গ্রন্থটির দু’টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর। প্রকাশক ছিলেন মুনশী শেখ জমির উদ্দীন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে শাহ সাহেবের পুত্রদ্বয়(শাহ মুহাম্মদ আবু নাঈম এবং শাহ মুহাম্মদ আবুল খায়ের) লিখেছেন, “পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক রেভারেন্ড মওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবকে অত্র সংস্করণ দান করিলাম। টাইটেল পেজে কেবলমাত্র প্রকাশকের স্থানে তাঁহার নাম থাকিবে।”
গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ ৪০ বছর পর প্রখ্যাত সমাজসেবক ও সাহিত্যিক মরহুম মৌলভী ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৩৫৬ সালে এর চতূর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে ভূমিকা লেখেন শাহ সাহেবের পুত্র জনাব শাহ মুহাম্মদ আবুল খায়ের। পরবর্তীতে ১৩৮১ সালে তাঁর পৌত্র শাহ মোহাম্মদ আবদুল মতিন বইটির পঞ্চম সংস্করণ বের করেন। এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ বের হয়েছে ৩০ শে মার্চ ১৯৮৬। এ সংস্করণের প্রকাশক শাহ মোহাম্মদ আবুদল মতিন। তিনি বর্তমানে খড়কীর গদ্দীনশীন পীর।
এরশাদে খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব নামক তাসাওউফের উপর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত বিস্তারিত ও তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলেছেন “মোহাম্মদ আবুদল করীরেম খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব সম্পর্কে বাংলায় তাসাওউফ সম্পর্কিত বই আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।” বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, “প্রকৃতপক্ষে এ পুস্তকখানা সাধনার পথিকদের জন্য একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ.) আমাদের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।”
শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ.) ১৩২২ বাংলা সনের ৩০ অগ্রহায়ণ খড়কীস্থ নিজ খানকা শরীফে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। প্রতিদিন বহু যিয়ারতকারী আসেন। তাঁর নামে যশোর শহরে ‘শাহ আবদুল করীম সড়ক’ রয়েছে। তাঁর বংশধররা আজও ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। খড়কীর বর্তমান পীর হযরত মাওলানা শাহ আবদুল মতিন শাহ আবদুল করীমের পৌত্র।
\r\n\r\n
মহাকবি কায়কোবাদ
কে ঐ শোনাল মোরে
আজানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ
নাচিল ধমনী
কি মধুর
আজানের ধ্বনি।
যদি তোমাদেরকে এখন প্রশ্ন করি এ কবিতাটি কার লিখা তোমরা নিশ্চয় এক বাক্যে বলবে কবি কায়কোবাদের। হ্যাঁ কবি কায়কোবাদের ‘আজান’ কবিতার প্রথম স্তবক এটি। তিনি মহাকবি কায়কোবাদ নামেই সবার কাছে পরিচিত। আসলে তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। জানা যায়, হাফিজ উল্লাহ আল কোরেশী নামে তাঁর জনৈক পূর্ব পুরুষ বাদশাহ শাহাজানের সময়ে বাগদাদ নগরীর নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে দিল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। হাফিজ উল্লাহ আল কোরেশী ছিলেন আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত। যে কারণে তিনি সহজেই বাদশাহ শাহজাহানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বাদশাহ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে দিল্লী জামে মসজিদের সহকারী ইমামের পদে তাঁকে নিয়োগ দেন। এই হাফিজ উল্লাহ আল কোরেশীর প্রপৌত্র মাহবুব উল্লাহ আল কোরেশী দিল্লী হতে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং ফরিদপুর জেলার গোড়াইল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আমাদের আলোচ্য কবি এই মাহবুব উল্লাহ আল কোরেশীর প্রপৌত্র। তাঁর দাদার নাম নেয়ামত উল্লাহ আল কোরেশী এবং আব্বার নাম শাহমত উল্লাহ আল কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী।
মহাকবি কায়কোবাদ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম জরিফউন্নেছা খাতুন। কায়কোবাদ ছিলেন বাবা মায়ের প্রথম পুত্র। তাঁর অন্য দু’জন ভাই হলেক আবদুল খালেক ও আবদুল বারী যারা যথাক্রমে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের সার্জন ছিলেন।
কায়কোবাদের লেখাপড়া শুরু হয় পিতা শাহমত উল্লাহর কর্মস্থল ঢাকাতে। তিনি ঢাকার পগোজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অবশ্য ১১ বছর বয়সে মা এবং ১২ বছর বয়সে আব্বা মারা যাওয়ায় ইয়াতিম কবি নানাবাড়ি আগলাপাড়া গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে এক বছর সময় কাটান। পরে তিনি পুনরায় ঢাকাতে ফিরে এসে ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ সময়ে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর পিতা মওলবী ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী। অপরদিকে কবির সহপাঠী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা জাস্টিস জাহিদ সোহরাওয়ার্দী। ঢাকা মাদ্রাসায় কায়কোবাদ এন্ট্রাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। মাদ্রাসার শিক্ষা জীবন শেষ হলে তিনি ১৮৮৭ সালে ডাক বিভাগে চাকুরি নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৯ সালে চাকুরী জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ছাত্র জীবনেই তার ‘কুসুম কানন’ ও ‘বিরহ গোলাপ’ নামে দুটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
আনন্দের কথা হলো, এ কাব্য গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হলে তা পড়ে কাশিম বাজারের মহারাণী দশ টাকা এবং কাশীর ভূবন মোহিনী চতুর্ধারিণী পাঁচ টাকা পাঠিয়ে কিশোর কবি কায়কোবাদকে বরণ করে নেন। ঘটনাটি ছিল নিঃসন্দেহে কবির জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যাপার।
কর্মজীবনে প্রবেশ করার আগেই তিনি অভিভাবকদের মতানুযায়ী মামা হেদায়াত আলী সাহেবের বড় মেয়ে তাহেরউন্নেছা খাতুনকে বিয়ে করেন।
১৩০২ বঙ্গাব্দে ঢাকা হতে সৈয়দ এমদাদ আলীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় ‘অশ্রু মালা’ খন্ড কাব্যগ্রন্থটি। এ সময়ে কবি ময়মনসিংহের জামুরকী পোস্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন। অশ্রুমালা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই কায়কোবাদের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ঐ সময়কার সেরা কবি নবীনচন্দ্র সেন আলিপুর হতে কবিকে লিখে পাঠান-
‘মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারে, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাংলা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে।”
১৩১১ বাংলা সনে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি ‘মহাশ্মশান’ মহাকাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ মহাকাব্য। বাংলা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও ফররুখ আহমদ মহাকাব্য রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কায়কোবাদই মহাকাব্য রচনা করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে এ মহাকাব্য রচিত। তিনখন্ডে বিভক্ত ৮৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এ মহাকাব্য রচনায় দীর্ঘ দশ বছর সময় লেগেছিল।
এ মহাকাব্য সম্বন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, “মহাশ্মশান কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একটি উজ্জ্বল রত্ন। মহাশ্মশানের ন্যায় বৃহদাকার কাব্য বোধহয় বঙ্গ সাহিত্যে আর নেই।”
এই কাব্যের মাধ্যমে কবি মুসলমানদের জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন-
“পড়ে নাকি মনে সেই অতীত গৌরব?
সুদূর আরব ভূমে যে বীর জাতি
মধ্যাহ্ন মার্তন্ড প্রায় প্রচন্ড বিক্রমে
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে
আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
বিসর্জিয়া আত্মপ্রাণ কেমন বিক্রমে
স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য ‘আল্লা’ ‘আল্লা’ রবে
আজিও ধ্বনিত সেই নীলনদ তীরে।”
১৩২৮ বংগাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘বিশ্বমন্দির’ কাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভাওয়াল এলাকার মুসলমান জমিদার নুরুউদ্দিন হায়দারের একমাত্র পুত্র আলাউদ্দীন হায়দরকে তারই দেওয়ান সুধীর চন্দ্র জমিদারীর লোভে কূপে ফেলে হত্যা করে এবং এই কূপের উপর নির্মাণ করে শিবমন্দির। এই দুঃখজনক ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বিশ্বমন্দির কাব্য।
১ ফাল্গুন ১৩২৯ বংগাব্দে প্রকাশিত হয় ‘অমিয় ধারা’ খন্ড কাব্য। এ কাব্যে অনেকগুলি কবিতা রয়েছে। তবে কাব্যের প্রথম কবিতা ‘আজান’ খুবই জনপ্রিয় একটি কবিতা। যার প্রথম স্তবক আজকের লেখার শুরুতেই উল্লেখ করছি।
১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় কায়কোবাদের আরেকখানি মহাকাব্য ‘মহরম শরীফ’। কারবালার যুদ্ধের কারণ ও ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এ কাব্যে। ৩ খন্ডে সমাপ্ত এ কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা ‘শ্মশান ভস্ম’ কাব্য উপন্যাসখানি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কায়কোবাদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় –প্রেম পারিজাত, প্রেমের ফুল, প্রেমের রাণী, মন্দাকিণী ধারা প্রভৃতি কাব্য।
২ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খৃস্টাব্দে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কায়কোবাদকে ‘কাব্যভূষণ’, ‘বিদ্যাভূষণ’ ও ‘সাহিত্য রত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে ‘মাইকেল দি সেকেন্ড’ ও বলা হতো।
কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করার জন্য কায়কোবাদ কলকাতাও গিয়েছিলেন। কাজী সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি কায়কোবাদের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলেছিলেন, ‘ইনিই মহাকবি কায়কোবাদ, মহাশ্মশান অমর কাব্যের স্রষ্টা-আমাদের অগ্রপথিক।’ এ ঘটনা হতেই বুঝা যায় কায়কোবাদ কত বড় কবি ছিলেন।
ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্ত্বে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে কায়কোবাদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী কায়কোবাদকে সম্মাননা হিসেবে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেয়ার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণে তা আর দেওয়া হয় নি।
ব্রঙ্কো নিউমেনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২১ জুলাই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।
\r\n\r\n
মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা
ঘাস, লতা, ফুল, পাখি দিয়ে ঘেরা একটি জেলা। সমস্ত জায়গায় প্রায় সমতল। সাইক্লোন, বন্যা, ঝড় কোন কিছুই সেখানে তেমন একটা আঘাত হানে না। অধিবাসীদের ভেতর শান্ত সৌম্যভাব। সবাই যেন কবি। কথায় কথায় কাব্য ঝড়ে পড়ে। এমনিতেই তাদের কথাগুলি দারুণ মিষ্টি। সেই জেলাটির নাম যশোর। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জেলা অর্থাৎ প্রথম জেলা। ১৭৮৬ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই যশোরকে জেলা ঘোষণা করে। তারও আগে যশোর স্বাধীন রাজ্য ছিল। তখন নাম ছিল যশোর রাজ্য বা যশোরাদ্য দেশ। এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায়, রাজা মুকুট রায়, হযরত বড়খান গাজী, হযরত খান জাহান আলীর মত ব্যক্তিত্বরা। অবশ্য যশোর কবি সাহিত্যিকদের দেশ হিসাবে আবহমান কাল ধরে সকলের নিকট পরিচিত। সেই রূপ সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী হতে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, ডাঃ লুৎফর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. এম. সমশের আলী, সৈয়দ আলী আশরাফ পর্যন্ত সবাই এ জেলারই সুসন্তান। এজন্য যশোরকে কবি সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্র বলা হয়। আজ আমরা সেই যশোরেরই এক কৃতি সন্তান যিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও সংগ্রামী তাঁর কথা বলবো, তাঁর নাম মুনসী মেহেরউল্লা।
মুনসী মেহেরউল্লা ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার(বর্তমানে জেলা)অন্তর্গত কালিগঞ্জ থানার ঘোপ গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ঘোপ গ্রামটি ঐতিহাসিক বারবাজার সংলগ্ন। এই বারবাজার হতেই সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামের সুমহান বাণী প্রথম প্রচার করেন হযরত বড়খান গাজী(গাজী কালু চম্পাবতী)। এরপর যে মহান মনীষীর আগমনে বারবাজার ধন্য হয় তিনি হযরত খানজাহান আলী। তার বারো জন শিষ্যের নাম অনুসা্রেই এই স্থানের নাম হয়েছে বারবাজার। এখান থেকেই তিনি বাগেরহাট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মেহেরউল্লার পৈতৃকবাড়ি চুরামনকাটী(বর্তমানে মেহেরউল্লাহ নগর) সংলগ্ন ছাতিয়ানতলা গ্রামে। তাঁর আব্বা মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ারেছ উদ্দীন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন।
অল্পবয়সেই পিতৃহারা হওয়ার কারণে মুন্সী মেহেরউল্লাহ লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেন নি। তাই মায়ের তত্ত্বাবধানে ও নিজের চেষ্টায় তাঁর লেখাপড়া চলতে থাকে। কৈশোর বয়সে তিনি মৌলভী মেসবাহউদ্দীনের কাছে তিন বছর এবং পরে করচিয়া গ্রামের মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কাছে আরো তিন বছর আরবী, ঊর্দূ, ফারসী ভাষা ও সাহিত্য শিখেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কোরআন ও হাদীসে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করেন এবং শেখ সাদীর গুলিস্তা, বোস্তা ও পান্দেনামা মুখস্ত করেন।
কর্মজীবনের শুরুতে তিনি যশোর জেলা বোর্ডে একটি চাকুরি পান কিন্তু স্বাধীন মনোভাবের কারণে সে চাকুরী ছেড়ে দর্জির কাজ শুরু করেন। দর্জির কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন ও সাফল্য লাভ করেন। সেই সূত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর খরিদ্দার ছিলেন এবং তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে দোকান করে দেন।
যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল দড়াটানায় দর্জির দোকানে কাজ করতে করতে মুন্সী মেহেরউল্লাহ দেখতেন খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ। মিশনারীদের ভয়ভীতি ও প্রলোভনের ফলে প্রচুর নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান খৃস্টান ধর্মের দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছিল। কোনও রাজনৈতিক নেতাকে এগিয়ে আসতে না দেখে এর বিরুদ্ধে তরুণ দর্জি মুন্সী মেহেরউল্লাহ গর্জে উঠলেন সিংহের মত।
দার্জিলিং অবস্থানকালে তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি তোফাজ্জল মুকতাদী নামক একটি ঊর্দূগ্রন্থ হতে বিভিন্ন ধর্মের ত্রুটি বিচ্যূতিগুলি জেনে নিলেন। তাছাড়া হযরত সোলায়মান ওয়ার্সীর লেখা ‘কেন আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম’, ‘প্রকৃত সত্য কোথায়’ বই দুটি তার জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিল।
তিনি দার্জিলিং হতে ফিরে এলেন যশোরে। খৃস্টানদের মতই তিনি দড়াটানা মোড় হতে বাংলা আসাম ও ত্রিপুরার অলিতে গলিতে সভা সমাবেশ করে খৃস্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এ প্রচারকে বেগবান করার জন্য কোলকাতার নাখোদা মসজিদে বসে মুনসী শেখ আবদুর রহীম ও মুনসী রিয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গঠন করলেন নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি। সমিতির পক্ষ হতে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয় মুনসী মেহেরউল্লা ওপর।
মুনসী মেহেরউল্লার জ্বালাময়ী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে স্থান নিতে লাগল। যাদের মনে ঘুণ ধরেছিল তারা আবার মনটাকে ঠিক করে নিল। জনমিরুদ্দীনের মত তুখোড় খৃস্টানও কলেমা পড়ে পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলেন।
তিনি যে শুধু বক্তৃতা দিতে পারতেন তা নয়, তাঁর কলমের ধারও ছিল দু’ধারী তলোয়ারের মত। জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ খৃস্টাব্দে খৃস্টান বান্ধব পত্রিকায় ‘আসল কোরআন কোথায়’ শিরোনামে একটি উদ্ধত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। এতে জন সাহেব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আসল কোরআন কোথাও নেই। এহেন অযৌক্তিক প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন মুনসী মেহেরউল্লাহ ‘সুধাকর’ পত্রিকায় ‘ইসায়ী বা খৃস্টানী ধোকা ভঞ্জন’ শিরোনামের এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে। এরপর জন জমিরুদ্দীন সুধাকরে অপর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেন। উত্তরে মেহেরউল্লাহ ‘আসল কোরআন সর্বত্র’ শিরোনামের সুধাকরে অন্য একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী অঘোরনাথ বিশ্বাস, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার প্রমুখ খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণ মুনসী মেহেরউল্লার সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
মুনসী মেহেরউল্লা শুধু খৃস্টানদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেন নি, তিনি মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার দেখেছেন তার বিরুদ্ধেও ছিলেন খড়গহস্ত। এ সম্বন্ধে শেথ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর ‘কর্মবীর মুনসী মেহেরউল্লা’ গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “মুনসী মেহেরউল্লার নানা দিক দিয়ে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। তিনি বলতেন, মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে কিন্তু তৈয়ারী করিতে জানে না। পান খাইতে অজস্র পয়সা নষ্ট করে কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করেন। মুনসী মেহেরউল্লা সাহেব মুসলমানগণের মিঠাইয়ের দোকান করিতে, পানের বরজ তৈয়ার করিতে সর্বস্থানে উৎসাহ দিতেন, তাঁহার চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবতী হইয়াছিল।”
মুনসী মেহেরউল্লা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা রাখেন। তিনি নিজেই ১৯০১ সালে নিজ গ্রামের পাশের গ্রাম মনোহরপুরে মাদরাসায়ে কারামাতিয়া নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যেটা বর্তমানে মুনসী মেহেরউল্লা একাডেমী। তিনি বাংলা আসামের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি মুসলিম সমাজকে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।
আমরা এখন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর জন্য বক্তৃতা বিবৃতি দিই, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করে ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস উদযাপন করি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এরও অনেক আগে অল্প শিক্ষিত মুনসী মেহেরউল্লা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা কি তা হাড়ে হাড়ে বুঝে ছিলেন। যারা মাতৃভাষাকে ছোট করে দেখতো তাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, “মাতৃভাষা বাংলায় লেখাপড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম যে কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহার শরীর পরিপুষ্ঠ সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারা যে কি সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।”
উপস্থিত বুদ্ধি মুনসী মেহেরউল্লার এত প্রখর ছিল যে, তৎকালীন সময়ে মুসলমান, হিন্দু ও খৃস্টান সমাজে তাহার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না বললেই চলে। উপস্থিত তর্কে তিনি কারো কাছে পরাজিত হয়েছেন এমন কোন তথ্য এ যাবত আমাদের হাতে এসে পৌছেনি। বরং বাংলা আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। বন্ধুদের রহস্যমূলক প্রশ্নের উত্তর তিনি রহস্য করিয়াই দিতেন।
এই মহান সমাজ সেবক অনেকগুলি বইও লিখেছেন। তার মধ্যে ‘মেহেরুল এছলাম’, ‘হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা’, ‘বিধবা গঞ্জনা’, ‘রদ্দে খৃস্টান’ ও ‘দলিলুল এছলাম’ গ্রন্থগুলি খুবই পরিচিত। তাঁর লেখা সাধারণ পাঠকের কাছে খু্বই জনপ্রিয় ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই লিখেছেন, “যদিও আমি ভালো বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ে অভাব অনুভব করিতে হয় না।”
সাহিত্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁর সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে যে নামগুলি উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ।
তিনি বাংলার জনগণের মাঝে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, নোয়াখালির কবি আবদুর রহিম তাঁর আখলাকে আহমদিয়া নামক বইতে লিখেছেন-
মুনসী মেহেরউল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়াতের হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার।
মুনসী মেহেরউল্লা ১৯০৬ সালে তাঁর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন। পরের বছর মাত্র ৪৫ বছর বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ইসলামী রেনেসাঁর এ অগ্রনায়ক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা বাংলা ও আসাম শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সেই সময়ের পত্রপত্রিকায় তার মৃত্যু সংবাদসহ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় লিখেছেন-
যার সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগণে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্বময় অন্ধকার।
আজ মুনসী মেহেরউল্লা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু আছে তাঁর কর্মময় জীবন, আছে তাঁর রচিত সাহিত্য। কি করে একজন সামান্য শিক্ষিত এতিম বালক পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের জোরে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে পারে, কি করে খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার হাত হতে স্ব-সমাজকে রক্ষা করতে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মুনসী মেহেরউল্লা। ছোট বড় সবার উচিত তাঁর জীবন হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাঁর কর্মময় জীবনের এবং সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারও আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।
\r\n\r\n
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
উপমহাদেশের সাংবাদিকতা জগতের দিকপাল, মুসলিম গণজাগরণের নকীব, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার হাকীমপুর গ্রামের এক বিখ্যাত পরিবারে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর আগে এবং তাঁর সমসাময়িককালে উল্লেখযোগ্য অনেক মুসলমান খ্যাতিমান লেখক-সাংবাদিকগণ মাসিক, ত্রৈমাসিক, দৈনিক ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ করলেও সেগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম বাংলা সাংবাদিকতা একটা দীর্ঘস্থায়ী ভীত রচনা করেন, তাঁর প্রকাশিত ‘দৈনিক আজাদ’ (১৯৩৬-১৯৯২) ও মাসিক ‘মোহাম্মদী’ বৃটিশ আমলে আত্মপ্রকাশ করে সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে এবং পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরও কিছুকাল এই পত্রিকা দু’টির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। মুসলিম বাংলার নবজাগরণে, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে, সামাজিক সংস্কারে, লেখক সৃষ্টিতে ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এবং ১৯৮৪ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
\r\nশিশুকালে পিতা-মাতাকে হারানোর পর আত্মীয়ের তত্ত্ববধানে তিনি বেড়ে ওঠেন। অতপর তিনি লালিত আত্মীয়-স্বজনের প্রচেষ্টায় লেখাপড়া চালিয়ে যান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর খুব বেশি ছিল না। তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জটিল পরিস্থিতিই ১৯০০ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে এফএম পাস করেন।\r\n\r\nকলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর মওলানা আকরম খাঁ কর্মজীবনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেচে নিন। খুব অল্প বয়সেই আহলে হাদীস ও মোহাম্মদী আকবর পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা পেশায় হাতেখড়ি হয়।\r\nআহলে হাদীস ও মোহাম্মদী আকবর পত্রিকায় সাংবাদিকাতার মাধ্যমে সাংবাদিকতা জীবন শুরু করার পর মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত দি মোহাম্মদী ও আল-ইহসান পত্রিকার স¤পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়ে কলকাতা থেকে জামানা ও সেবক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪০ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে এর সম্পদনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি অবসর জীবনে চলে যান।\r\nমওলানা আকরাম খাঁ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ধর্মশাস্ত্রবেত্তা, সুপ-িত ব্যক্তি এবং শক্তিশালি গদ্যলেখক হিসেবে খ্যাতিমান। বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। মওলানা আকরাম খাঁ রচিত গ্রন্থাদি, বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় রচনা একজন সুপ-িত ব্যক্তি, চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক এবং শক্তিমান গদ্যশিল্পীকেই চিনিয়ে দেয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁর একাধিক প্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠক শ্রেণী ও বোদ্ধামহলে বেশ প্রশংসিত ও খ্যাত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যকয়েকটি হল,-\r\n
*** আমপারার বাংলা অনুবাদ\r\n*** মোস্তফা-চরিত\r\n*** মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য\r\n*** বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্ম\r\n*** মুসলীম বাংলার সামাজিক ইতিহাস\r\n*** তাফসীরুল কোরআন (১-৫ খন্ড, অনুবাদ)\r\n*** টীকা-ভাষ্য (অনুবাদ)\r\nমৌলিক রচনা ছাড়াও তাঁর বাংলায় অনুদীত গ্রন্থগুলো প্রমাণ করে তিনি যে একজন দক্ষ অনুবাদক এবং সুপ-িত ব্যাক্তি।
মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে রাজনীতি শুরু করেন। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।\r\n১৯১৮ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯২০ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিনি নিখিল ভারত খেলাফত আন্দোলন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি এবং মওলানা মজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। আকরাম খাঁর দায়িত্ব ছিল তুর্কি খেলাফত থেকে ফান্ড সংগ্রহ করা। ১৯২০-১৯২৩ সময়ের মধ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে জনসভা বা সম্মেলনের আয়োজন করে খেলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন গতিশীল করার চেষ্ঠা করেন।
১৯৪১ সালে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং একনাগাড়ে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।
১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে গেল তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে দূরে সরে যান এবং ১৯৬২ সালে আজাদের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদাতসমূহের চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্যক্তি পূজা, কবর পূজা ও অন্যান্য প্রচলিত রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ধারণ করেছিলেন।
তিনি ১৯৪৭ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১০১ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালের ১৮ আগষ্ট রাজধানী বংশালে আহলে হাদীস মসজিদে নামাযরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।
\r\n\r\n
আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ
....................................................................
নাম আবদুল করীম। উপাধি সাহিত্য বিশারদ ও সাহিত্য সাগর। আব্বার নাম মুনশী নুরুদ্দীন এবং দাদার নাম মোহাম্মদ নবী চৌধুরী। আবদুল করীমের পুরো নাম মুনশী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ। তবে তিনি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ নামেই পরিচিত। এমনকি শুধু সাহিত্য বিশারদ বললেই তাঁকেই বুঝানো হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংগ্রাহক, গবেষক, প্রবন্ধকার ও সম্পাদক। না, তিনি কবি বা মৌলিক কোন লেখক ছিলেন না। আর এ জন্যেই অনেকের কাছে তিনি কিছুটা অপরিচিত। কিন্তু তাই বলে তিনি মোটেও ছোট খাট কোনো ব্যক্তি নন। তিনি আমাদের বাঙলা সাহিত্য অঙ্গনের এক মহান মনীষী। যাকে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। সত্যি কথা বলতে কি পুরো বাঙ্গালি জাতি এই মহান মানুষটির কাছে ঋণী হয়ে আছেন।
সাহিত্য বিশারদ মুন্সি আবদুল করিম ১৮৬৯, মতান্তরে ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর পটিয়া মহকুমার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কাদির রাজার অধস্তন বংশধর। তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হাবিলাস মল্ল কোন এক সময় চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে ঐ দ্বীপের নামকরণ করা হয় হাবিলাস দ্বীপ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আবদুল করীম দুনিয়ার মুখ দেখার আগেই তাঁর পিতা মুনশী নুরউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাতা মিস্রীজান প্রখ্যাত পাঠান তরফদার দৌলত হামজা বংশের মেয়ে ছিলেন।
জন্মের কয়েক মাস আগে পিতার মৃত্যু এবং ১৭ বছর বয়সে মাতৃহীন আবদুল করিম দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির স্নেহছায়ায় এন্ট্রান্স পাস করেন এবং সচেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বাড়ির দহলিজেই। সেখানেই তিনি আরবি-ফারসি ও বাংলায় পড়া শুরু করেন। অতঃপর তিনি সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এক বছর পড়াশোনা করে তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তার দ্বিতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সঙ্গত কারণেই উনিশ শতকে এন্ট্রান্স পাস করতে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানেও পারদর্শী হতে হতো। চট্টগ্রাম কলেজে দু’বছর এফএ পড়ার পর ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক সম্পন্ন পরিবারের মতো তাদের পরিবারেও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অনিবার্য করে তোলে। এর সঙ্গে যোগ হয় শারীরিক অসুস্থতা। পরীক্ষার আগে তিনি টাইফয়েড এ আক্রান্ত হন। ফলে তার আর এফএ পরীক্ষা দেয়া হয়নি। এখানেই তার উচ্চ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।
১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবনের শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক হন। চট্টগ্রামে প্রথম সাব-জজ আদালতে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে কাজ করেন। পরে কবি নবীন সেনের সুপারিশে চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
\r\nআবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আজীবন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। বাঙালি লেখকেরা যখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ও অনুরাগে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তখন প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথির রণাবেণ এবং পুঁথি সম্পাদনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মূলত পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথির রণাবেণ ও পুঁথি সম্পাদন ছিল তার জীবনের ব্রত। বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপাদান পুঁথি পত্র ও এদেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগের লৌকজ-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের ‘রাধিকার মানভঙ্গ’, কবিবল্লভের ‘সত্যনারায়ণের পুথিঁ’, দ্বিজ রতিদেবের ‘মৃগলুব্ধ’ রামরাজার ‘মৃগলুব্ধ সম্বাদ’, দ্বিজ মাধবের ‘গঙ্গামঙ্গল’, আলী রাজার ‘জ্ঞানসাগর’, বাসুদেব ঘোষের ‘শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস’, মুক্তারাম সেনের ‘সারদামঙ্গল’, শেখ ফয়জুল্লাহর ‘গোরক্ষবিজয়’ ও আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ (খণ্ডাংশ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত। ‘ইসলামাবাদ’ (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস) ও ‘আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য’ (মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে রচিত) তাঁর দুটি মৌলিক গ্রন্থ।\r\n
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাল্যকাল থেকেই পুঁথিপত্রের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। সারা জীবন তার নেশা ছিল দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাকি-মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা পাঠ করা এবং সংগ্রহ করা। তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁর পিতামহ কর্তৃক সংগৃহীত কিছু পুঁথির সঙ্গে পরিচিত হন। এই পুঁথিগুলো পড়ে তিনি পুঁথি সংগ্রহে ও এ নিয়ে লিখতে আগ্রহী হন। এ পুঁথিগুলোর মধ্যেই পেয়ে যান ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’। সেসময় তিনি ছিলেন এফএ ক্লাসের ছাত্র। এ সময় তিনি আচার্য অক্ষয় সরকার সম্পাদিত ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকায় ‘প্রাচীন পদাবলী’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করেই মহাকবি নবীন চন্দ্রসেন সাহিত্যবিশারদের প্রতি আকৃষ্ট হন।
একান্ত শিশুকাল হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদকে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন পাঠক সংগ্রাহক ও তথ্যনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে দেখতে পাই। এই মহান মনীষী ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে ৮৩ বছর বয়সে চট্টগ্রামে ইন্তিকাল করেন।
\r\n\r\n
মহাকবি আল্লামা ইকবাল
‘আরব হামারা চীন হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম,--ওতন হ্যায়
সারা জাঁহা হামারা।’
কোন কোন মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে সৃষ্টি করেন দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য। শত ঝড়ঝঞ্জা বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সেসব মানুষ তাঁদের কাজ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে যান। আমরা আজকে এমন এক ব্যক্তিত্ব ও কবি পুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।
তোমরা হয়ত কোন না কোনভাবে শুনে থাকবে মহাকবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে। হয়ত কথাটা এজন্য বললাম যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কবি ইকবালকে জানার তেমন সুযোগ নেই। সত্যি কথা বলতে কি এই মহান কবিকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হচ্ছে।
কবি ইকবাল পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নামক স্থানে ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ নুর মোহাম্মদ এবং মাতার নাম ইমাম বীবী। কবির পিতা মাতা উভয়ই অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। কবির পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরবাসী সাপ্রু গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পন্ডিত ছিলেন। তাঁরা সুলতান জয়নুল আবেদীন ওরফে বুদ শাহ(১৪২১-১৪৭৩ খৃ) এর রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা শিয়ালকোটে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ষাট বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।
কবির পিতা শেখ নূর মোহাম্মদ উচ্চশিক্ষিত কোন মানুষ ছিলেন না কিন্তু তিনি একজন স্বনামধন্য পন্ডিত ছিলেন। যার কারণে শামসুল উলামা সৈয়দ মীর হাসান তাঁকে(কবির পিতাকে) অশিক্ষিত দার্শনিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
ইকবালের জন্মের ব্যাপারে কথিত আছে যে, একদিন তাঁর পিতা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশচারী একটি অসম্ভব সুন্দর কবুতর তার কোলে এসে পড়ল। পরে তিনি স্বপ্ন বিশারদের কাছে জানতে পারলেন অদূর ভবিষ্যতে তিনি একজন ভাগ্যবান পুত্রের বাপ হতে যাচ্ছেন। আরও কথিত আছে যে, সদ্যজাত ইকবালকে যখন পিতা নূর মোহাম্মদের কোলে দেওয়া হয় তখন তিনি সদ্যজাত শিশুপুত্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “বড় হয়ে দ্বীনের খেদমত করলে বেঁচে থাক, নচেৎ এখনি মরে যাও।” বুঝতে পারছ তাঁর স্নেহময় পিতা তাঁর কাছ হতে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের জন্য কি আশা করেছিলেন?
পিতা নূর মোহাম্মদের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে মাদরাসায় পড়ানোর কিন্তু উস্তাদ শামসুল উলামা মীর হাসানের পরামর্শে তাঁকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়। প্রাইমারী শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে শিয়ালকোট স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। এ স্কুল হতে তিনি ১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্কচ স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি একদিন দেরীতে ক্লাসে আসেন, ক্লাস টিচার তাঁর দেরিতে ক্লাসে আসার কারণ জানতে চাইলে বালক ইকবাল তৎক্ষণাত উত্তর দেন, “ইকবাল(সৌভাগ্য) দেরিতে আসে স্যার।” উত্তর শুনে পন্ডিত শিক্ষক তো ‘থ’। তিনি যে শুধু উপস্থিত বুদ্ধিতে দক্ষ ছিলেন তা নয়। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী। ১৮৮৮, ১৮৯১ ও ১৮৯৩ সালে যথাক্রমে প্রাথমিক বৃত্তি, নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি স্বর্ণপদক ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে স্কচ মিশন স্কুল কলেজে উন্নীত হলে ইকবাল এখানে এফ. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এফ.এ. পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং যথারীতি বৃত্তিসহ স্বর্ণপদক লাভ করেন।
১৮৯৫ সালে তিনি শিয়ালকোট হতে লাহোরে এসে লাহোর সরকারী কলেজে বি.এ ভর্তি হন। এখানে একটা খবর দিয়ে রাখি, ইকবাল যখন বি.এ পড়ার জন্য পিতার নিকট অনুমতি চাইলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন, ‘ছাত্র জীবন শেষ করার পর অবশিষ্ট জীবন ইসলামের খিদমতে ওয়াকফ করে দিতে হবে।’
হ্যাঁ, তিনি তাতেই রাজী হয়েছিলেন। আর সত্যি সত্যিই তাঁর সারাটা জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। লাহোর সরকারী কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি টি.ডব্লউ এর মত ভূবন বিখ্যাত একজন সুযোগ্য শিক্ষক পান যিনি ছিলেন আরবী ভাষায় সুপন্ডিত, দর্শনের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক। প্রতিভাবান ইকবালকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে আরনল্ড সাহেব তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আরবী ও ইংরেজিতে সমগ্র পাঞ্জাবে প্রথম স্থান নিয়ে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যে কারণে তিনি এবার দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর ১৮৯৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ পাস করেন। সাথে সাথে তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর সামান্য কিছুকাল পরই তিনি লাহোর সরকারী কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজের ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের খন্ডকালীন সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ সময়ে উর্দু ভাষায় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন। তাঁর জীবন ছিল ছকে বাঁধা। এ সম্বন্ধে ইসলামী বিশ্বকোষ লিখেছে, “তিনি ভোরে ওঠে ফজরের সালাত আদায় করতেন, অতঃপর উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তারপর কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করতেন এবং কিছু না খেয়ে কলেজে যেতেন। দুপুরে বাড়ি ফিরে আহার করতেন। অনেক সময় গভীর রাতে ওঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। একবার তিনি একাধারে দুই মাস এই রাত্রিকালীন সালাত আদায় করেন।’
১৯০৫ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মানসে লন্ডন গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, সূফী কবি আমীর খসরু ও মহাকবি গালিবের মাযার জিয়ারত করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময় তিনি শিক্ষক হিসেবে পান বিশ্ব খ্যাত দার্শনিক ডঃ এম সি ট্যাগার্টকে। এরপর তিনি পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। শেষে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারস্যের দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক সন্দর্ভ লিখে ১৯০৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপরের বছর লিংকন ইন হতে ব্যারিস্টারী পাস করেন। এ সময় তাঁর প্রিয় শিক্ষক স্যার আর্নল্ড লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশেষ কারণে কয়েক মাসের ছুটিতে গেলে ইকবাল ৬ মাসের জন্য তাঁর স্থানে আরবীর অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
১৯০৮ সালের ২৭ শে জুলাই তিনি দেশে ফিরে এলে লাহোরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন। তিনি লাহোরে ফিরে স্বপদে পুনর্বহাল হন এবং সরকারের অনুমতিক্রমে আইনব্যবসা শুরু করেন। অবশ্য দেড় বছর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে তিনি আইনব্যবসা শুরু করেন। তবে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, তিনি কখনই মাসিক খরচের পরিমাণ টাকা রোজগারের পর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করতেন না। আরও একটা কথা, তিনি যদি বুঝতেন কোন মোকদ্দমায় মক্কেলের তেমন কোন উপকার করতে পারবেন না তা’হলেও তিনি সে কেস গ্রহণ করতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।
ছাত্রাবস্থায় ১৮৯৬ সালে শিয়ালকোটের এক কবিতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। এরপর তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখে হায়দারাবাদের প্রখ্যাত কবি দাগের নিকট পাঠিয়ে দেন সংশোধনের জন্য। কবি দাগ কিশোর কবির এ কবিতাগুলি পেয়ে মনোযোগ সহকারে পড়েন ও চমৎকার একটি মন্তব্য লিখে পাঠান। কবি দাগ লিখেছিলেন, ‘এ কবিতাগুলি সংশোধন করার কোন দরকার নেই। এগুলো কবির স্বচ্ছ মনের সার্থক, সুন্দর ও অনবদ্য ভাব প্রকাশের পরিচয় দিচ্ছে।’ কবি ইকবাল এ চিঠি পেয়ে তো খুব উৎসাহ পেলেন। তাঁরপর হতে চললো তাঁর বিরামহীন কাব্যসাধনা। এরপর ১৯০০ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলাম-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় জীবনের প্রথম জনসমক্ষে তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘নালা ইয়াতীম’ বা অনাথের আর্তনাদ পাঠ করেন। কবিতাটি পড়ার পর চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। মানে কবিতাটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে কবিতাটি ছাপা হয় এবং এর প্রতিটি কপি সে সময় চার টাকা দামে বিক্রি হয়। বিক্রয়লব্ধ প্রচুর পরিমাণ টাকা ইয়াতিমদের সাহায্যার্থে চাঁদা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯০১ সালে তিনি ছোটদের জন্য লেখেন-মাকড়সা ও মাছি, পর্বত ও কাঠবিড়ালি, শিশুর প্রার্থনা, সহানুভূতি, পাখীর নালিশ, মায়ের স্বপ্ন প্রভৃতি কবিতা।
এরপর তিনি দু’হাতে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল, ‘স্বদেশপ্রেম, মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ, ইসলামের শ্বাশত আদর্শে তাওহীদভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, জাতির উত্থান-পতন, দলীয় কলহ ও অন্তর্দ্বন্ধ নিরসন প্রভৃতি বিষয় কবিতায় স্থান পেতো। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে তিনি বেলালী সুরে আহবান জানাতেন ক্লান্তিহীনভাবে। স্বকীয় আদর্শের সন্ধানে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।’
তাঁর কাব্যে এ ধরনের চিরন্তন আবেদন থাকার কারণে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। নানামুখি প্রতিভার অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বমহল হতে অকুন্ঠ সম্মান অর্জন করেন। মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একজন হিন্দু অধ্যাপক বলেছিলেন, “মুসলমানগণ ইকবালকে লক্ষবার তাঁদের সম্পদ বলে দাবি করতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন ধর্ম বা শ্রেণীবিশেষের সম্পদ নন-তিনি একান্তভাবে আমাদেরও।’’
১৯০১ সালে ‘হিমালাহ’ নামক কবিতাটি তৎকালীন সময়ের উর্দু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা ‘মাখযানে’ ছাপা হয়। এটিই পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতা। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে তিনি এসময় অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ১৯০৩ সালে লাহোর হতে অর্থনীতির ওপর তাঁর প্রথম পুস্তক ‘আল ইলমুল ইকতেসাদ’ প্রকাশিত হয়।
১৯২৪ সালে ‘বাঙ্গেদারা’ বা ঘন্টাধ্বনি নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আসরার-ই-খুদী’ বা ব্যক্তিত্বের গূঢ় রহস্য। এ কাব্যগ্রন্থটি ১৯২০ সালে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন ডঃ আর.এ.নিকোলসন। সাথে সাথে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে মহাকবি ও বিশ্বকবি আল্লামা ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে ‘আসরার-ই-খুদী’ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিশ্বের বহু ভাষায় এ কাব্যগ্রন্থটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।
১৯১১ ও ১৯১২ সালে পঠিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কবিতা ‘শিকওয়াহ’ বা অভিযোগ ও ‘জওয়াব-ই-শিকওয়াহ’ বা অভিযোগের জবাব উর্দু ভাষায় রচিত। এ দীর্ঘ দুটি কবিতার কাব্যগ্রন্থ দু’টির বাংলা ভাষায় একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় রচিত ‘পায়াম-ই-মাশরিক’ প্রাচ্যের বাণী কাব্যগ্রন্থটি। গ্রন্থটি আরবী, ইংরেজী, তুর্কী, জার্মান ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় ‘রামূয-ই-বেখুদী’ বা আত্মবিলোপের গুঢ়তত্ত্ব কাব্যগ্রন্থটি। মূলত এ গ্রন্থটি ‘আসরারে খুদী’র দ্বিতীয়াংশ। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থটির ৮৪ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ‘বালে জিবরীল’ বা জিবরাঈলের ডানা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘দরবারে কালীম’ বা মূসার লাঠির আঘাত কাব্যগ্রন্থটি। উর্দু ভাষায় রচিত এ কাব্যগ্রন্থটি আরবী ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েও প্রকাশিত হয়।
এর আগে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘যাবুরে আজম’ বা প্রাচ্যের ধর্ম সংগীত কাব্যগ্রন্থটি। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় রচিত ‘জাবীদ নামা’ বা অমর লিপি কাব্যগ্রন্থটি। এমনিভাবে একের পর এক তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত তিনি প্রাচ্যের সেই ভাগ্যবান কবি ব্যক্তিত্ব যার রচনা এত ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সত্যিই যদি বিশ্বকবি বিশেষণে কাউকে বিশেষিত করতেই হয় তবে সে সম্মানের অধিকারী নিঃসন্দেহে কবি আল্লামা ইকবাল। কবি নিজেও ছিলেন বহু ভাষাবিদ পন্ডিত। তিনি উর্দু, ফারসী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় লেখনি চালিয়েছেন।
কবি The Development of Metaphysics in Iran বা ‘প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান’ এই বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ সালে লন্ডন হতে এ থিসিস প্রকাশিত হয়।
এতক্ষণ তাঁকে কবি হিসেবে পরিচয় দিলাম। আসলে তিনি শুধুই কবি ছিলেন না। তিনি সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক আইনজ্ঞ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
১৯৩০ সালে নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি বিলেত গমন করেন ‘গোল টেবিল’ বৈঠকে যোগদানের জন্য। এই বৈঠকে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করেন। অবশ্য এর আগে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি চাই যে-পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান একটি রাষ্ট্রে পরিণত হউক। পৃথিবীর এই অংশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে হোক বা বাইরে হউক-অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনই আমার মতে মুসলমানদের শেষ নিয়তি।’ এই মত অনুযায়ীই পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এ জন্য তাঁকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার বলা হয়। অবশ্য তিনি ১৯৩৭ সালের ২১শে জুন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমি যেভাবে প্রস্তাব করছি সেভাবে পুনর্গঠিত মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্রই হল একমাত্র উপায়, যদ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ ভারত গড়ে উঠতে পারে এবং সাথে সাথে অমুসলিম আধিপত্য থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যেতে পারে। উত্তর পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদেরকে কেন একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃতি দেয়া হবে না-যাতে তারা ভারতের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পারে?’ এ উদ্ধৃতিতে তিনি যে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলেছিলেন তা নিশ্চয় বুঝা যায়। মূলত আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ত্বও তাঁরই চিন্তার ফসল। অথচ এ মহান ব্যক্তিত্ত্বকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর হতে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, একথা আগেই বলেছি। তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে যে কারণে তিনি নাকি পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। অথচ তিনি পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ারও বেশ আগে ১৯৩৮ সালের ২১শে এপৃল ইন্তিকাল করেন। আশা করি বুঝতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না যে, আমরা এ মহান ব্যক্তিত্ত্বকে অস্বীকার করে কি পরিমাণ মূর্খতায় ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সত্যি কথা আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু অনুদার বুদ্ধিজীবি এর জন্য দায়ী।
উপমহাদেশের এ প্রখ্যাত দার্শনিক কবি অসম্ভব দেশপ্রেমিক একজন মানুষ ছিলেন। লেখার শুরুতেই যে কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়েছি তার কাব্যানুবাদ এ রকমের-
‘আরব আমার, ভারত আমার, চীনও আমার-
নহে তো পর-
মুসলিম আমি,- জাহান জুড়িয়া
ছড়ানো রয়েছে আমার ঘর।’
দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সচেতনভাবে এ কবিকে বর্জন করা হয়। তার প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে জহুরুল হক নামকরণ করা, পাঠ্যতালিকা হতে তাঁর রচনা ও জীবনী বাদ দেয়া।
আমরা আশা করবো এখন হতে নতুন করে আবার আমরা ইকবাল চর্চায় ফিরে যাব। কবিকে তাঁর প্রকৃত সম্মানে সম্মানিত করবো। দেশের সব শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে তাঁর রচনা অন্তুর্ভুক্ত হওয়া এ জাতির কল্যাণের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন, সে দিকটা দেখার জন্য সরকারের প্রতি আহবান রইলো।
\r\n\r\n
ইসমাইল হোসেন সিরাজী
আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া,
উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া,
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া,
পূত বিভূ নাম স্মরণ করি।
সিরাজগঞ্জ শহরের ছোট্ট এক কামরায় বসে লিখে চলেছেন এক তরুণ তার আপন কওমকে জাগিয়ে তোলার জন্য। লিখে চলেছেন বৃটিশ বেনিয়াদের এদেশ হতে চিরতরে উৎখাত করার জন্য। এই বেনিয়া গোষ্ঠী সমস্ত ভারত উপমহাদেশ মুসলমানদের কাছ হতে ছিনিয়ে নেয়। ক্ষোভে দুঃখে মুসলমানগণ ইংরেজদের প্রবর্তিত অনেক কিছুই ত্যাগ করে। এমনকি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ হতেও নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। অপরদিকে হিন্দুরা এ সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষা দীক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানরা হয়ে পড়ে পঙ্গু কি শিক্ষা দীক্ষায়, কি সম্পদ বৈভবে। ঠিক এ সময়েই কলম তুলে নেন সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী। ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই তারিখে তিনি তৎকালীন পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ আবদুল করীম এবং মাতার নাম নুরজাহান বেগম। তারা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার মানুষ।
শিশু ইসমাইল হোসেনের লেখাপড়ার প্রথম সবক দেন তাঁর মা নূরজাহান খানম। নূরজাহান খানম তাঁর শিশুপুত্রকে প্রথমেই কোরআন শিক্ষা দেন। কোরআন শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করা হয়। মেধাবী ইসমাইল হোসেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সিরাজগঞ্জের বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে এ সম্ভাবনাময় তরুণ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাছাড়া স্বদেশের পরাধীনতা, সমগ্র মুসলিম জাহানের দুর্দশার জন্য বেদনাবোধ হতে সৃষ্টি উৎকন্ঠাও তাঁকে স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে বসে থাকতে দেয় নি। তোমরা জানলে আশ্চর্য হবে যে, তিনি এ সময়ে নির্যাতিত অবহেলিত, লাঞ্চিত ও পদদলিত মুসলিম জাতির জন্য বেদনাবিধুর, এতই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, মাত্র ১৬ বছর বয়সেই লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ যাত্রায় তিনি তুরস্কে যেতে পারেন নি ঠিক কিন্তু সেই যে মুসলিম জাহানের কল্যাণের মানসে ঘর হতে বের হলেন আর কখনই সুবোধ বালকের মত ঘরে বসে থাকেন নি। অবশ্য তিনি পরবর্তীকালের তাঁর বাল্যকালের স্বপ্নের তুরস্কে গিয়েছিলেন তা অনেক পরের কথা।
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সবচেয়ে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ হল ‘অনল প্রবাহ’। এটি ১৮৯৯ সনে মুনসী মেহেরউল্লা প্রথম প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি এত জনপ্রিয় ছিল যে ১৯০০ সালে আরো কিছু কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি আবার প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯০৮ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর এ সময়ই ‘অনল প্রবাহ’ ও লেখক বৃটিশ রাজশক্তির আক্রমণের শিকার হন। ‘অনল প্রবাহ’ বাজেয়াপ্ত হয় এবং লেখকের দু’বছর কারাদন্ড হয়। তিনিই প্রথম কবি যার কাব্যগ্রন্থ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় এবং তিনিই বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে কারাদন্ড ভোগকারী উপমহাদেশের প্রথম সাহিত্যিক। সিরাজীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হল উচ্ছ্বাস, উৎসব, উদ্বোধন কাব্য, মহাশিক্ষা কাব্য, স্পেন বিজয় কাব্য, প্রেমাঞ্জলী(গীতিকাব্য), সঙ্গীত সঞ্জীবনী ইত্যাদি।
মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ও মিথ্যা অপপ্রচার করতো তখন হিন্দু কবি সাহিত্যিকরা। বিশেষ করে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার লেখায় সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হেয় করার চেষ্টা করতেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী এ সমস্ত কুৎসিৎ লেখার জবাব দিতে গিয়ে উপন্যাসও রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে তারাবাই, ফিরোজা বেগম, নুরুদ্দীন, রায়নন্দিনী ও বংকিম দুহিতা। না, জবাব দিতে গিয়ে সিরাজী প্রতিআক্রমণ বা সাম্প্রদায়িক উস্কানি বেছে নেননি। সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উপন্যাসে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘রায় নন্দিনী’।
সিরাজী রচিত কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও সঙ্গীত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সংখ্যা ৩২টি। এগুলো হলো- কাব্যগ্রন্থ উচ্ছ্বাস (১৯০৭), নব উদ্দীপনা (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৮), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯৮৪), মহাশিক্ষা কাব্য প্রথম খন্ড (১৯৬৯), মহাশিক্ষা কাব্য দ্বিতীয় খন্ড (১৯৭১)। উপন্যাস- রায়নন্দিনী (১৯১৫), তারাবাঈ (১৯১৬), নূরউদ্দীন (১৯১৯)। প্রবন্ধ গ্রন্থ- মহানগরী কর্ডোভা (১৯০৭), স্ত্রীশিক্ষা (১৯০৭), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), সুচিন্তা প্রথম খন্ড (১৯১৬), তুর্কি নারী জীবন (১৯১৩), ভ্রমণ কাহিনী- তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১৩)। সঙ্গীত গ্রন্থ- সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), প্রেমাঞ্জলী (১৯১৬) প্রভৃতি। অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- সুধাঞ্জলী, গৌরব কাহিনী, কুসুমাঞ্জলী, আবে হায়াৎ, কাব্য কুসুমোদ্যান, পুস্পাঞ্জলী। অসমাপ্ত উপন্যাস- বঙ্গ ও বিহার বিজয় এবং জাহানারা।
১৯৪০ সালের ২২ মার্চ কলিকাতা ২/১ ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, সিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম- এর উদ্বোধন করা হয়। উক্ত দ্বারোঘাটন অনুষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে বলেন, ‘সিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে ভাবিতেন জ্যেষ্ঠ পুত্র-তুল্য। তাঁহার নিকট যে স্নেহ আমি জীবনে পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সঞ্চয়। ফরিদপুর কনফারেন্সে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সমগ্রজীবনই ছিল অনল প্রবাহ এবং আমার রচনায় সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ আছে। সাহিত্যিক ও রাজনীতিক ছাড়াও আমার চোখে তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন এক শক্তিমান দরবেশ রূপে। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন নাই, তুরস্কের রণক্ষেত্রে তিনি সেই মৃত্যুর সঙ্গে করিয়াছিলেন মুখোমুখি। তাই অন্তিমে মৃত্যু তাঁহার জন্য আনিয়া দিয়াছিল মহাজীবনের আস্বাদ।\'
বাংলাদেশের জন্য বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা মহান পুরুষ সিরাজীকে হীনমন্যতার কারণে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ। দেশের মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পাঠ্যসূচিতে সিরাজী রচনাবলী উপেক্ষিত। সিরাজীর লেখা থেকে বঞ্চিত এদেশের শিক্ষার্থীরা। সিরাজী সম্পর্কে তরুণ সমাজকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। অথচ সিরাজীর অনলবর্ষী বক্তৃতায় প্রকম্পিত হয়েছিলো ব্রিটিশ সিংহাসন। তাঁর কণ্ঠ ও লেখা থেকে বারুদের গন্ধ বের হতো। তাঁর বক্তৃতায় জেগে ওঠেছিলো লাখো লাখো তরুণ। সেখানে মুসলিম বা হিন্দু বলে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হয় নাই। ব্রিটিশ রাজ শুধু তাঁকে কারাবন্দীই করেনি, তার কবিতাও নিষিদ্ধ করেছিলো। সেই স্বাধীনচেতা মহাকবিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা অবমূল্যায়ন করছেন। যারা মুসলমানদেরকে লাইভস্টক বা গৃহপালিত পশু বলে আখ্যায়িত করছে, যারা আমাদেরকে কাক পক্ষী, দস্যু, তস্কর, দানব, অসুর, অনার্য, ইতর, নরপশু, ডাকাত বলে গালি দিয়েছে তাদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী ঘটা করে পালন করা হয়। তাদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের। অথচ সিরাজীর মত মহানায়কের রচনাবলী পাঠ্য বহির্ভূতই থেকে যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশের ক্রান্তিকালীন দুর্বিষহ অবস্থার প্রেক্ষিতে সিরাজীর মতো বিপ্লবী পুরুষের প্রসঙ্গ টেনে আনা অতীব জরুরী। ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান লিখেছেন, ‘বাংলাদেশী জাতি সৃষ্টির এই গঠনকালে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উদারতা, দৃঢ়তা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বাতন্ত্র্যবাদ, ঐতিহ্য চেতনা, সংস্কৃতি চেতনা, বিজ্ঞান-ইতিহাস ও সাহিত্য-চেতনা প্রভৃতি থেকে প্রেরণা আহরণ একান্ত কর্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত সারা উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে যে জাতীয় ঐক্যবোধ, জাগরণ স্পৃহা আপন জাতীয় সত্ত্বার পরিচয় ফুটিয়ে তোলার আকাক্মখা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াস তীব্র আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে সেই উদ্যম নিষ্ঠা ও কর্ম-চাঞ্চল্য একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে। আবশ্যক হয়ে উঠেছে আজ আবার নতুন করে ঘনিয়ে ওঠা বিভ্রান্তির, দিশাহীনতার দিগন্তের কালো আবরণ ভেদ করে আলোকবন্যা আবাহনের জন্য নতুন করে গর্জে ওঠা হাজার হাজার সিরাজীর।\'
মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই দুরারোগ্য পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম বিশ্বের এই মহান পুরুষ ইন্তিকাল করেন। জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বপ্রকার অনাচার, কদাচার, কুসংস্কার, অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সিংহের মত লড়ে গেছেন। না কোথাও কোন কারণে তিনি মাথা নত করেন নি।
\r\n\r\n
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি শতাব্দী। বিশিষ্টি ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ পন্ডিত, ধর্মবেত্তা ও সূফীসাধক। তিনি ছিলেন একাধারে ভাষাবিদ, গবেষক, লোকবিজ্ঞানী, অনুবাদক, পাঠসমালোচক, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক, কবি, ভাষাসৈনিক এবং একজন খাঁটি বাঙালি মুসলিম ও দেশপ্রেমিক। জ্ঞানপ্রদীপ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা ভাষার গবেষণায় অদ্বিতীয়।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাবা-মার পঞ্চম সন্তান। তাঁর বাবা মফিজ উদ্দিন আহমদ ছিলেন ইংরেজ আমলে সরকারি জরিপ বিভাগের একজন কর্মকর্তা। শহীদুল্লাহ মাতা হরুন্নেছা খাতুনের শিক্ষার প্রতি ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি বাড়িতে তাঁর পরিবার ও পেয়ারা গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের শিক্ষা দিতেন। প্রথম দিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম রাখা হয় মুহম্মদ ইব্রাহীম। কিন্তু পরবর্তীকালে পিতার পছন্দে আকিকা করে তাঁর নাম পুনরায় রাখা হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
ছোটবেলায় ঘরোয়া পরিবেশে শহীদুল্লাহ উর্দু, ফার্সী ও আরবি শেখেন এবং গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত পড়েন। পাঠশালার পড়া শেষ করে ভর্তি হন হাওড়া জেলা স্কুলে। স্কুলের ছাত্র থাকতেই বই পড়ার এবং নানা বিষয়ে জানার প্রতি ছিল তাঁর দারুণ নেশা। হাওড়া স্কুলের স্বনামখ্যাত ভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে\'র সংস্পর্শে এসে শহীদুল্লাহ ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। স্কুলজীবন থেকেই তিনি আরবী-ফার্সী-উর্দুর পাশাপাশি হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা পড়তে শিখেছিলেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্ত্বের সাথে সংস্কৃতসহ প্রবেশিকা পাশ করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে ১৯০৬ সালে এফ.এ. পাশ করেন। অসুস্থতার কারণে অধ্যায়নে সাময়িক বিরতির পর তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন ১৯১০ সালে। বাঙালি মুসলমান ছেলেদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অনার্স নিয়ে পাস করেন।
সংস্কৃতিতে অনার্স পাস করার পর সংস্কৃত নিয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করতে চাইলে তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁকে পড়াতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯১২ সালে এ বিভাগের প্রথম ছাত্র হিসেবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এর দু\'বছর পর ১৯১৪ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে বি.এল. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইউরোপ গমন করেন। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শণ চর্যাপদাবলি বিষয়ে গবেষণা করে ১৯২৮ সালে তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এ বছরই ধ্বনিতত্ত্বে মৌলিক গবেষণার জন্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লাভ করেন।
হম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে সিতাকুন্ডু উচ্চ বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি কিছুদিন ওকালতি প্র্যাকটিস করেন। তিনি বশিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর দিনেশ চন্দ্র সেনের অধীনে শরৎচন্দ্র লাহিরী রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সে বছরের ২ জুন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে স্থায়ী চাকুরিতে যোগদান করেন। একইসঙ্গে নিখরচে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সভাপতি নিযুক্ত হন। পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষকের এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষকের পূর্বপদে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি রীডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। একই বছর তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে ১৯৩৭ সালে স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের ৩০ জুন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে রীডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং একইসাথে উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ছয় বছর কলা অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা গড়ে তোলার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সেখানে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে (ফরাসি ভাষার) খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অস্থায়ী প্রাধ্যক্ষের এবং ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ইমেরিটাস নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার বাইরে তিনি করাচির উর্দু উন্নয়ন সংস্থার উর্দু অভিধান প্রকল্প, ঢাকায় বাংলা একাডেমীর \'পূর্ব পাকিস্তান ভাষার আদর্শ অভিধান প্রকল্প\' এবং ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের সদস্য, ইসলামিক একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলা একাডেমীর বাংলা পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার ও দাউদ সাহিত্য পুরস্কার কমিটির স্থায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা ও সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাজে Seminar on Traditional Culture in South-East Asia -তে তিনি UNESCO -র প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এর চেয়ারম্যান মনোনীত হন।
ভাষাবিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি সচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন, আয়ত্ত করেছিলেন বাইশটি ভাষা। তিনি বাংলা, উর্দু, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, পালি, আসাম, উড়িয়া, আরবী, ফার্সী, হিব্রু, আবেস্তান, ল্যাটিন,তিব্বর্তী, জার্মান, ফরাসী, প্রাচীন সিংহলী, পশতু, মুন্ডা, সিন্ধী, মারহাটী, মৈথালী ইত্যাদি ভাষা জানলেও ভাষার ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সানন্দে বলতেন, আমি বাংলা ভাষাই জানি। বাংলা যে সংস্কৃত ভাষা হতে জন্ম নেয় নি, একথা প্রথম তিনিই প্রমাণ করেন। তিনিই বলেন, “বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নহে; বরং দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।”
তাঁর প্রকাশনা গুলি হলো:\r\nগবেষণাগ্রন্থ: সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা (১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)।\r\nভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫) । প্রবন্ধ-পুস্তক: ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essay on Islam (1945), Traditional culture in East Pakistan (মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গে তাঁর যুগ্ম-সম্পাদনায় রচিত;১৯৬১)।
গল্পগ্রন্থ:
রকমারী(১৯৩১)।\r\nশিশুতোষ গ্রন্থ: শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রাসূলুল্লাহ (১৯৬২), সেকেলের রূপকথা (১৯৬৫) ।\r\nঅনুবাদ গ্রন্থ: দাওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম (১৯৪২), শিকওয়াহ ও জাওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), বিদ্যাপতিশতক (১৯৪৫), মহানবী (১৯৪৬), বাই অতনা মা (১৯৪৮), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Sayings of the Holly Prophet (1945), Buddist Mystic Songs (1960)।\r\nসংকলন: পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। এছাড়া তিনি ৪১টি পাঠ্যবই লিখেছেন, ২০টি বই সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০টিরও বেশি। ভাষাতত্ত্বের উপর রয়েছে তাঁর ৩৭টি রচনা। অন্যান্য বিষয়ে বাংলা ইংরেজী মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮০টি। এ ছাড়া তিনি তিনটি ছোটগল্প এবং ২৯টি কবিতা ও লিখেছেন।
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বহু মননশীল ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তিনি সম্পদনা করেছেন। তিনি আল এসলাম পাত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯২৫) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯২৮-২১) হিসেবে যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁরই সম্পাদনা ও প্রকাশনায় মুসলিম বাংলার প্রথম শিশু পত্রিকা \'আঙ্গুর\' (১৯২০) আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা \'দি পীস\' (১৯২৩), বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা \'বঙ্গভূমি\' (১৯৩৭) এবং পাক্ষিক \'তকবীর\' (১৯৪৭) সম্পাদনা করেন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক ও মাসিক জার্নাল সম্পাদনা করেন।
এই চলন্ত বিশ্বকোষ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তিটি ছিলেন পুরামাত্রায় ইসলামী শরীয়তের পাবন্দ। মুমিনের গুণাবলীগুলি তিনি তাঁর জীবনে ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)এর খলীফা। ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে এই মহান মনীষী ৮৪ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। মরহুমের লাশ তাঁরই নামে নামকরণকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পাশে ঐতিহাসিক মূসা মসজিদ প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।
\r\n\r\n
শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা ও চর্চার একটা গঠনমূলক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মীর মোশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯৯১), মোজাম্মেল হক(১৮৫০-১৯৬১), কায়কোবাদ(১৮৫৮-১৯৫১) যে ধারার সূচনা করেছিলেন পরবর্তীতে মুনসী মুহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩০), শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২) প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, সংগ্রামীগণ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের তুলনায় অনগ্রসর মুসলমানদের স্বরূপ সন্ধান, স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ ও তাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে। এ ক্ষেত্রে তারা সব দিক হতে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মুসলিম জাতীয় জাগরণের পথিকৃত মুনসী মেহেরউল্লার নিকট হতে। মুনসী মেহেরউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন পরাধীন দেশে বৈরী শাসনাধীনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন তাদের মধ্যে নবজাগরণের। আর এ নব জাগরণ সম্ভব করার জন্য তিনি নিজে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখালেখির সাথে সাথে গড়ে তুলেছিলেন একটি সাহিত্যিক সম্প্রদায়।
“শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ছিলেন সেই সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরই একজন। তাঁর জীবন সাধনার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল বাঙালী মুসলমানের জন্য সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাশীল আত্মপরিচয় নির্মাণে সহায়তা করা। ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য ভিত্তিক নবজাগরণমূলক কাব্য রচনা, ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ও প্রেরণাদায়ক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা, ধর্মীয় চেতনা ও মননশীলতা বিকাশে ‘সহায়ক সমৃদ্ধশালী বিদেশী সারাবান সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ও দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের চরিত-মানস গঠন উপযোগী শিশুতোষ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে একটি নব চেতনা জাগৃতির প্রত্যাশী ছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার মধ্যে সংকীর্ণতা রহিত মুক্তবুদ্ধি সঞ্জাত সম্প্রদায়গত সমৃদ্ধি কামনা ও সমাজ হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়।”(শেখ হবিবর রহমান-মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পৃ.৯)।
শেখ হবিবর রহমান নিজের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে ‘আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-
“আমার সাহিত্য বরাবর মোল্লা ধরনের; এইজন্য ইহা অনেকের নিকট উপেক্ষিত। নিয়ামত, আবেহায়াত ইত্যাদি ধরনের পুস্তকের নাম বোধ হয় মুসলমান সমাজে সর্বপ্রথম আমিই রাখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার বিবিধ পুস্তকে আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার এত অধিক যে, আমাদের মধ্যে আর কেহই তত অধিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। জাতীয়ভাবে জাতীয় শব্দের সংমিশ্রণে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি আমার জীবনের প্রধান একটি সাধনা।”
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ১৮৯০ মতান্তরে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তদানিন্তন যশোর জেলার বর্তমান মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলাধীন ঘোষগাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ দেরাজতুল্লাহ এবং দাদার নাম শেখ হেরাজতুল্লাহ। জানা যায় আরব দেশ হতে তাঁর পূর্ব পুরুষ এদেশে এসেছিলেন এবং ঘোষগাতি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন।
শেখ হবিবর রহমানরা দুই ভাই ছিলেন। তাঁর ছোটভাই শেখ ফজলর রহমানও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও ধর্ম প্রচার করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ‘পুলুম আঞ্জুমানে হেমায়তুল ইসলাম’ নামক ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের সম্পাদক ও ‘আলমগীর লাইব্রেরীর পক্ষে বড় ভাই শেখ হবিবর রহমানের বেশ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
শেখ হবিবর রহমানের লেখাপড়া গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। পরে পুলুম প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে উচ্চ প্রাথমিক পাঠ শেষ করে তিনি ফুলতলা ইউনিয়ন হাইস্কুলে ভর্তি হন। আরও পরে ১৯০৭ সালে সেখান হতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ১৯১০ সালে যশোর জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশের আগেই ১৯০৯ সালে তাঁর স্নেহময়ী পিতা ইন্তিকাল করেন। এজন্য তাঁর শিক্ষাজীবন দারুণ অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। পিতৃবিয়োগের পর তাঁকে বহু কষ্টে তাঁর যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হত। ১৯১৪ সালে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আরও পরে ১৯২২ সালে কলকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে এল.টি. ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে এল.টি. পাশ করেন।
ঐ বছরই তিনি বারাসাত গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। নয় মাস পরে তাঁকে মক্তব সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে খুলনায় বদলী করা হয়।
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নকে ১৯২৭ সালে খুলনা হতে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলী করা হয় এবং সেখানে ৪ বছর চাকুরী করার পরে ১৯৩০ সালে পুনরায় তাকে বারাকপুর সরকারী হাইস্কুলে বদলী করা হয়। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৪৪ সালে তিনি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।
খুলনা শহরে অবস্থানকালে তিনি পুনরায় ১৯৫১ সালে করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন এবং কর্মজীবন হতে দ্বিতীয়বারের মত ১৯৬০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তাঁর মধ্যে সৃজনশীল রচনার প্রেরণা দেখা যায়। এই সময়ে তিনি ‘গো-জাতির প্রতি অত্যাচার’ নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পয়গ্রাম কসবা মাইনর স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় মুনসী মুহম্মদ মেহেরউল্লা এক ধর্মসভায় গেলে সেখানে তিনি দুটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতা দু’টি শুনে মুনসী মেহেরউল্লা তাঁকে ‘শিশুকবি’ খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা ‘পেচক পন্ডিত’ নামের একটি কবিতা। কবিতাটি ১৩১৪ সনের ১৫ আশ্বিন ‘মোসলেম সুহৃদ’ এবং ১৮ আশ্বিন ‘মিহির ও সুধাকর’ পত্রিকায় ছাপা হয়।
মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯০৬ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘কোহিনুর কাব্য’। ফুলতলা(খুলনা) জুনিয়র মাদ্রাসার সেক্রেটারী মৌলভী মোহাম্মদ কাসেমের উপদেশে ‘বাংলা মৌলুদ শরীফ’ রচনা করতে গিয়ে এই মহাকাব্য রচনা করেন।
তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম ‘পারিজাত’, এটি ১৯১২ সালে যশোর হতে মৌলভী আলতাফ হোসেন প্রকাশ করেন। এরপর ১৯১৯ সালে দ্বিতীয়, ১৯২৪ সালে তৃতীয় এবং ১৯৩৩ সালে কাব্যগ্রন্থটির চতূর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কবির ছাত্রজীবনে ১৩১২ হতে মাঘ ১৩১৬ সময়ের মধ্যে লিখিত। ‘পারিজাত’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়। ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকা ‘পারিজাত’কে কবিতা কাননের যথার্থ পারিজাত বলে অভিহিত করে। পারিজাত পাঠ করে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এ কাব্যগ্রন্থকে String of small poems.............verses are melodious and the rhythm admirable বলে মন্তব্য করেন।
তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীঃ
কোহিনুর কাব্য, চেতনা কাব্য, আবেহায়াত কাব্য, নিয়ামত, বাঁশরী, গুলশান ইত্যাদি। ফারসী কবি শেখ সাদীর ‘গুলিস্তা’ ও ‘বুস্তা’র কাব্যনুবাদও তিনি করেন। এছাড়া আলগীয়, কর্মবীর মুনশী মেহের উল্লাহ, ভারত সম্রাট বাবর, সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী, মালাবারে ইসলাম প্রচার, দবরুল মুখতার, আমার সাহিত্য জীবন ইত্যাদি গদ্য রচনাতেও তিনি মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিশোর পাঠকদের জন্য তিনি রচনা করেছেন পরীর কাহিনী, মরনের পরে, ছোটদের হযরত মুসা, হাসির গল্প ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, শয়তানের সভা এবং শেখ সাদীর জীবনী ‘‘হায়াতে সাদী’’।
এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল-আজও মনে পড়ে (গল্প গ্রন্থ), জিন্দাপীর আলমগীর(জীবনী গ্রন্থ), মজার গল্প (নৈতিক কথামূলক), গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস (গদ্যগ্রন্থ), পরলোক প্রসঙ্গে ‘মরণের পরে’ (২য় খন্ড), শের সংহার কাব্য(কাব্যগ্রন্থ), সত্যের সন্ধান, ভাবিবার কথা, খোদাপ্রাপ্তির সোজাপথ ও দাদুর দফতর।
তাঁর উদ্যোগে ১৯১০ সালে ‘যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বাঙালী মুসলমানদের প্রথম সাহিত্য সংগঠন। এই সাহিত্য সংগঠনের নিকট হতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তীকালে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’ ১৯১২ সালে ও ‘মুসলিম সাহিত্য সমা ‘ ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি কলকাতার পারিজাত সাহিত্য কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বি.এ. ক্লাশের ছাত্র থাকাকালে ১৯১৪ সালে তিনি ‘মাসিক মোহাম্মদীর’ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা হতে প্রকাশিত ‘মাসিক বঙ্গনূর’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ‘নদীয়া সাহিত্য সভা’র পক্ষ হতে ‘সাহিত্যরত্ন’ উপাধি লাভ করেন।
১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিলিটারী কনভয়ের নীচে চাপা পড়ায় তাঁর পা ভেঙে যায়। ১৯৫৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমীতে ৩০ টি মুদ্রিত ও কয়েকটি অমুদ্রিত গ্রন্থ দান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ঐ সনেই তিনি কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।
১৯৬১ সালে ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমানের মৃত্যুতে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৬২ সালের ৭ মে ইন্তিকাল করেন। পরদিন ৮ মে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমীতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী(১ম খন্ড কাব্যগ্রন্থসমূহ) বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশিত হয়।
..................................................................................................................
\r\n\r\n
গোলাম মোস্তফাঃ একজন মুসলিম কবির প্রতিকৃতি
কবি গোলাম মোস্তফা বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক। তিনি বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমান জেলা) শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাজী গোলাম রব্বানী। মাতার মোসাম্মাৎ শরীফা খাতুন। তাঁর দাদা কাজী গোলাম সারওয়ার। গোলাম মোস্তফার পূর্বপুরুষ ছিলেন মুগল যুগে বিচার বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা। তাদের উপাধি ছিল কাজী। সেই সূত্রে গোলাম মোস্তফার পিতা, পিতামহ কাজী উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু গোলাম মোস্তফা নিজে কোন অর্জিত সম্মান বা প্রচলিত কৌলিণ্য প্রথার যৌক্তিকতা খুঁজে না পাওয়ায় কাজী উপাধি গ্রহণ করেননি। বহুকাল পূর্ব থেকেই মনোহর পুরের কাজী পরিবার ছিল আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষাতে সুপণ্ডিত। কবি গোলাম মোস্তফার জন্মসাল নিয়ে একটু কথা আছে। তিনি নিজেই “আমার জীবন স্মৃতি” তে লিখেছেন: ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় দুই বছর কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিলো সম্ভবত ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, বাংলা তারিখ ছিলো ১৩০৪ সালের ৭ ই পৌষ রবিবার।কবির স্মৃতিকথা থেকেই আমরা কবির সঠিক জন্ম সন, বাংলা মাসের হিসেব এবং দিনের নাম রবিবার পাই। কিন্তু ইংরেজি মাসের হিসেবটা উহ্য থেকে যায়। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখটা পরিবার থেকে সংরক্ষণ করা হয়নি। কবির পিতার দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে বড়– নামে এক কন্যা এবং কাজী গোলাম মোস্তফা ও কাজী গোলাম কাওসার নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তিনটি সন্তান তাঁরা যথাক্রমে কাজী গোলাম কুদ্দুস, মাজু এবং খুকি। কাজী গোলাম মোস্তফাই আমাদের প্রিয় কবি গোলাম মোস্তফা। এই পরিবারের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার নিবেকৃষ্ণ পুর গ্রামে। কবির মাতা ছিলেন একজন স্বভাব কবি। স্বভাব কবিত্ব ব্যক্তি মায়ের সাথে থেকে কবির মধ্যেও কবিত্ব ভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্নের পথিকৃত শিশুদের নিয়ে এমন শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী সিঞ্জিত লেখা যার কলমের ডগায় বেরিয়ে আসে, তিনিই ইসলামী রেনেসাঁর এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ স্বর কবি গোলাম মোস্তফা।
\r\nকৈশোর ও বাল্য জীবন\r\n\r\nকবির বাল্য জীবন নিজ গ্রাম মনোহর পুরেই কেটেছে। কুমার নদী বিধৌত মনোহরপুর গ্রামের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, সরল আতিথিয়তা বাৎসল্য গায়ে মেখেই কবি বেড়ে উঠে ছিলেন।তাঁর জন্মস্থান মুখরিত ছিল যমুনা, কুমার মধুমতি, চিত্রা, ভৈরব, ভদ্রা চন্দনা, নবগঙ্গা, হানু বারাসিয়া, মাথাভাঙ্গা আর কপোতাক্ষ প্রভৃতি সেকালের খরস্রোত নদীর কলতানে। বাংলাদেশে বোধকরি আর কোন জেলায় এত নদীর রূপালী ধারার মিলন ঘটেনি। এসব বহমান নদীর তীরে নারকেলÑখেজুর কুঞ্জ ঘেরা শ্যামল প্রকৃতি যে কোন ভাবুক মানুষের মনে সঞ্চার করে কাব্যকলার মাধুরি। এ গ্রামীন পাগলকরা সৌন্দর্যই শিশু গোলাম মোস্তফাকে ভাবুক করে গড়ে তোলে ও কবি হতে সাহায্য করে। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :
শারদ প্রভাত চাদিনীর রাত সুপ্তি নীরব ধরা\r\nআতট পূরতি সরসী সলিল পদ্ম পানায় ভরা।\r\nকলমী লতিকা ডাঁটায় ও পাতায় ছাইয়া ফেলেছে জল\r\nমাঝে মাঝে তার নানান রঙের ফুটেছে পুষ্পদল।
এই কবিতায় কবি তাঁর চারপাশের নদী প্রকৃতির এক অপূর্ব বর্ণনার মাধ্যমে কাব্যরস পিপাসুকে উপহার দিয়েছেন নিটোল ছন্দ সৌকর্ষ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তা। কবিতার মতই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক মোহনীয় রূপ গায়ে মেখেই কবির শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত হয়। গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্যই তাঁর প্রাণে প্রথম কবিত্বভাব জাগিয়েছিলো। বস্তুত এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশই ছিল A meet nurse for a Poetic Child তাইতো পরিণত বয়সে তিনি লিখতে পেরেছিলেন:
নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি গান\r\nছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন প্রাণ।\r\nএ বিশ্বের সবই আমি বাসিয়াছি ভালো\r\nআকাশ বাতাস জল রবি শশী তারকার আলো।
প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজ সরল মাটির গন্ধে বেড়ে উঠার কারণেই সারা জীবন কবির মধ্যে সরলতাবোধ, সম্প্রীতিবোধ, আতিথিয়তাবোধ, মানবতাবোধ তার ব্যক্তিত্বের সাথে মিশে ছিলো। কবি হতে পেরেছিল উদার ও সরলতার প্রতিক এক মানসভূমি। কিন্তু কবির বেড়ে ওঠার জীবনটা মোটেই স্বচ্ছন্দ ছিলো না। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তাকে সাফল্যের মুখ দেখতে হয়েছিল। কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন: আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফার হাতের লেখার মত তাঁর ভাষাও অতি সুন্দর ও মিষ্টি স্বচ্ছন্দ গতি একটুও বাধে না কোথাও। কিন্তু তাঁর জীবন অত সহজ ও স্বচ্ছন্দ ছিল না। তাঁর জ্ঞান পিপাসিত প্রতিভার তরীকে উজান পথে অনেক ঝড় ঝাপটার মুকাবিলা করে বেয়ে নিতে হয়েছে লক্ষ্যস্থলে। শৈশব কালেই সৎমা থাকায় স্বভাবতই বাপের অবহেলায় কখনও মামার বাড়ি কখনও নিজের বাড়ি থাকতে হতো। আর্থিক অনটনে শৈশবেই টিউশনি করতে হতো, তারপরও ক্লাসে ফাষ্ট হয়েছেন। তার জীবনকে সংগ্রামের মধ্যে পরিচালিত করার মাধ্যমে শৈশবের সে সংগ্রাম তিনি কাটিয়ে উঠে ছিলেন। জীবনকে সাজিয়েছিলেন বর্ণাঢ্যতায়। নিজ যোগ্যতা ও মেধার কারিশমায় চলমান জীবনকে করেছিলেন উচ্চকিত দ্যুতিময়।
\r\nশিক্ষা জীবন ও মানস গঠনঃ\r\n
শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগের কারণেই মাত্র চার বছর বয়সেই পিতা মুন্সি গোলাম রব্বানীর কাছে কবির লেখা পড়ার হাতে খড়ি হয়েছিল। মনোহরপুরের পাশ্ববর্তী দামুদিয়া গ্রামের পাঠ শালাতে প্রথমে শিশু গোলাম মোস্তফাকে ভর্তি করা হয়। এখানে কিছুদিন লেখাপড়ার পর কবিকে নিকটবর্তী ফাজিলপুর গ্রামের পাঠ শালাতে ভর্তি করা হয়।\r\nফাজিলপুর পাঠ শালায় দুই বছর লেখাপড়া করবার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় শৈলকুপা হাই স্কুলের নীচের শ্রেণীতে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে পুরস্কৃত হন।\r\nশৈলকুপা স্কুল থেকেই তিনি ১৪১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খুলনার দৌলতপুর কলেজ হতে ১৯১৬ সালে আই. এ. পাশ করেন। এরপর গোলাম মোস্তফা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের রাজধানী কোলকাতা গমন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি কোলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ঐ কলেজ থেকে ঐ বছর যশোরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩Ñ১৯৬৪ খৃ.) বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ. পাশ করেন। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪Ñ১৯৫০ খৃ.)ও রিপন কলেজে পড়াকালীন সময়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন।\r\nআর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাঁর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করার পর ১৯২২ সালে গোলাম মোস্তফা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. পাশ করেন। এরপর আর কোন একাডেমিক ডিগ্রী অর্জন না করলেও সারা জীবন শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা অর্জনের পেছনেই ব্যয় করেছেন।
\r\nউনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে যে সময়ের বৃত্তে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম হয়, সেই সময়টা বাঙালী মুসলমানদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়Ñকারণ এই পর্বে অন্তত: তিনটি ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতির মাত্রা ছিল অত্যন্ত দ্রুত। এগুলো হল: শিক্ষা, রাজনীতি এবং আর্থিক। অবিভক্ত ভারতের বাংলা প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের কোন প্রভাব ছিল না।বিশ ও ত্রিশ দশকে কৃষক প্রজাপার্টির অভ্যূদয় (১৯১৯ খৃ.), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মুসলমান নেতাদের বিজয় (১৯৩৭ খৃ.) এসবই বাঙালী মুসলমানদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। মুসলমানদের মধ্যে এর আগে যাঁরা নেতৃত্ব পদে ছিলেন তাঁরা প্রধানত অবাঙালী। বাঙালী সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে সমন্বয়ের সুযোগ ছিলো, বরাবরই তাঁরা তা এড়িয়ে গেছেন। বরং বাঙালী মুসলমানদের উপর ইসলামী সংস্কৃতির নামে যা চাপানোর চেষ্টা করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে আরব ও পারস্য দেশের সংস্কৃতি। এ সময়কালে বাঙালী মুসলমানরা বহু মাসিক অর্ধমাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা প্রকাশে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং সীমিত পর্যায়ে হলেও তাতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদীতার স্থান পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটই কবি গোলাম মোস্তফার বেড়ে ওঠা এবং তাঁর মানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।\r\n\r\nচাকুরি জীবনঃ\r\n
বি.এ পাস করার পর তিনি ১৯২০ সালে ব্যারাকপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই স্কুলে থাকা অবস্থায় তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি ব্যারাকপুর স্কুল থেকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে বদলি হন। সেখানে তিনি একটানা নয় বছর শিক্ষকতা করার পর কলিকাতা মাদ্রাসায় বদলী হন এবং এক সময় তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত একমাত্র কবি গোলাম মোস্তফা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান শিক্ষক বালিগঞ্জ স্কুলের উক্ত পদে আসীন হননি। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে একজন উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক।তৎকালে কলিকাতার কোন হাই স্কুলে গোলাম মোস্তফাই ছিলেন প্রথম মুসলমান হেডমাস্টার। তখনকার দিনে এই সম্মান খুব কম মুসলমানই পেয়েছেন। সেখান থেকে কবিকে বদলী করা হয় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। এরপর ১৯৪০ সালে তাঁকে বাকুড়া জেলা স্কুলে বদলী করা হয়। এ সম্পর্কে কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন: এরপর আব্বা বাঁকুরায় জেলা স্কুলে বদলি হলেন। কলকাতা মানুষের সমুদ্রের মাঝে যেমন জ্ঞানের মুক্তা কুড়াবার আনন্দ পেয়েছেন, তেমনি হুগলীতে নদীর স্রোত বইয়েছেন বিশ্বনবীর প্রবাহে। দেশের বাড়িতে পেতেন সমতার মমতার বিস্তার। বাঁকুড়ার পাহাড় পর্বত ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে কবিকে। সুষনিয়া পাহাড়ে পিকনিকে গিয়ে চূড়ায় বসে কবিতা লেখেন, গান করেন। সেখান থেকে ফরিদপুর বদলি হয়ে যান।\r\n১৯৪৬ সালে তাকে সর্বশেষ ফরিদপুর জেলা স্কুলে বদলী করা হয়।ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকেই তিনি ১৯৫০ সালে দীর্ঘ ত্রিশ বছর একটানা শিক্ষকতার মত মহান পেশার দায়িত্ব পালন করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।তিনি পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির সচিবরূপে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে কবি গোলাম মোস্তফা অবসর গ্রহণ করেন এবং নিজের খরিদ করা বাড়ি ঢাকার শান্তিনগরে ১১৮, মোস্তফা মঞ্জিলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন।\r\nএকান্ত নিবিড়ভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করার জন্যই তিনি নির্ধারিত সময়ের তিন বছর আগেই শিক্ষকতার মহান পেশা থেকে অবসর নেন।
\r\nসাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা ঃ\r\n
কবিতা কবির কল্পনা, কবিতা কবির শৈল্পিক উচ্চারণ। কবিতার শিল্পরূপ থেকেই কবির সময়চেতন সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, মিলন বিরহ, স্বপ্ন দ্রোহ ইত্যাদির শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ। একই কবিতায় সব রকম অনুভূতি থাকে না, কারণ কবির কবিতায় বিশেষ সময়ে বিশেষ চেতনায় প্রকাশিত হয় বিশেষ বিশেষ ভাব। কবি কল্পনায় ধরা পড়ে সেই ভাব, আপন কবিতার ভাষায় কবি তাকে শিল্পরূপ দেন।
\r\nকবি কল্পনার উৎস তাই সমাজ, এবং প্রকাশভঙ্গিতে থাকে তার সময়চেতনা। কবিতায় কবি যা বলতে চান তা পরিবেশ ও অবস্থানগত দ্বিধার কারণে কিংবা যে সমাজ কবি চান, আর যে সমাজে কবি বাস করেন, তার মধ্যের ব্যবধানে অতৃপ্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করেন, যা আঙ্গিকগত উৎকর্ষ পায়।\r\nভাব আর রূপের এক অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য থেকে জন্ম নেয় একটি কবিতা। এ কবিতা কবি রচনা করেন আপন মহিমায়। জীবনের সত্যকে তিনি যেভাবে আপন সত্ত্বায় ধারণ করেন, সেভাবেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় কবিতার প্রকাশভঙ্গি, শৈলী ও রূপ। সৃষ্টিসম প্রজ্ঞা, জৈবিক ক্ষমতা, সমাজ ও সময়ের প্রভাবের সমন্বয়ে কবির মর্মভূমি কবিতা নির্মাণে অদৃশ্য শক্তির মত কাজ করে যায় এমনকি কবির অজ্ঞাতসারে। তেমনি নিতান্ত অজ্ঞাতে অন্তরালে শিশু বয়সেই কবির মধ্যে কাব্য চিন্তার উন্মেষ ঘটে। পিতা, পিতামহের পুঁথি পাঠ , বিয়ের দাওয়াত রচনা ইত্যাদি থেকে তাঁর মধ্যে কবিত্ব ভাব জেগে ওঠে। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত কবি গোলাম মোস্তফার অবদান বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত।গোলাম মোস্তফা ছিলেন মূলত: কবি। কবি আমার জীবন স্মৃতিতে লিখেছেনÑ আমার বেশ মনে পড়ে, আমার কাব্য জীবনের প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ সালে। তখন আমি শৈলকুপা হাইস্কুলে পড়ছি। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেন একটা কাব্যিক ভাব আমার মধ্যে এলো।\r\n১৯১১ সালে কবি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি কাটানোর পর তাঁর এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি কবিতায় রচনা করেন। এটিই তাঁর প্রথম রচনা । কবিতাটি হল :
এস এস শীঘ্র এস ওহে ভ্রাতধন\r\nশীতল করহ প্রাণ দিয়া দরশন।\r\nছুটি ও ফুরাল স্কুল ও খুলিল,\r\nতবে আর এত দেরি কিসের কারণ।
পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতার নাম আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার (১৯১৩ খৃ.)। কবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ সম্পাদিত সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী তে ১৯১৩ সালে কবিতাটি ছাপা হয়। কবিতাটির রচনা ও প্রেক্ষাপটের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন,পারিপার্শি¦ক পরিবেশ এবং বন্ধুবর্গের প্রেরণায় গোলাম মোস্তফার অবরূব্ধ কাব্যপ্রবাহ ঝর্ণাপ্রবাহের মত বাইরে আত্মপ্রকাশ করল। সেই সময়ে ইউরোপ ভূÑখন্ডে বলকান যুদ্ধে তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমস্ত মুসলিম জাহানে একটা বিপর্যয়তার ছায়া নেমে এসেছিলো। এমন সময়ে হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, কামাল পাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে আদ্রিয়ানোপল পুনরূদ্ধার করেছেন। এই খবরে স্বজাতি বৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার নাম দিয়ে এক রাতের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। এরপর কবিতাটি তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মাদিতে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটি ছিলো এরূপ :
আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া\r\nধরায় আসিলো নামিয়া।
সেই সময় কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি সবই ছিলো নতুন। তাই এই কবিতাকে কেন্দ্র করে পাঠক মহলে একটা ব্যাপক আলোচনার ঝড় বয়ে গেল।বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নব ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৭ খৃ.), আল এসলাম (১৯১৫ খৃ.), সাধনা ( ১৯১৬ খৃ.), সহচর ( ১৯১৫ খৃ.), সওগাত ( ১৯১৭ খৃ.), মাসিক মোহাম্মদী (১৯১৬ খৃ.), ইসলাম দর্শন (১৯২৭ খৃ.), মাহে নও সত্য বার্তা (১৯৩৮ খৃ.), মোয়াজ্জিন ( ১৯৩৮ খৃ.) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় এসব কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। আল এসলাম (২য়ভাগ, ১৩২৩ সাল), (তয় ভাগ, ১৩২৪ সাল), (৪র্থ ভাগ, ১৩২৫ সাল), (৫ম ভাগ, ১৩২৬ সাল) পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
\r\nমৌলিক রচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। সমসাময়িক The Musalman, The star of India, The Morning News, The Pakistan Observer, The Down প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলো পাঠ করলে ইংরেজী ভাষার উপরও যে কবির যথেষ্ট দখল ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।\r\nMorning News তাঁর সর্ম্পকে মন্তব্য করেছিলো He is also a fine prose writer both in Bengali and English. বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জাগরণের পথিকৃতদের অন্যতম কবি গোলাম মোস্তফা জীবনের প্রথম থেকেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর লেখনি চালনা করেন।\r\n
তিনি নিজেই লিখেছেন: “যে যুগে আমার জন্ম সে যুগ বাংলার মুসলমানের অবক্ষয়ের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিলো কোন স্বাতন্ত্র, না ছিলো কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান ধারণা ও আশা আকাংক্ষা রূপায়িত হয় তাঁর মাতৃভাষার মধ্যে। সেই হিসেবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলিমের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও, আমার মনে জেগেছিলো আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দূর্জয় আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদে নয়Ñসহজ ভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ।”
\r\nউক্ত দৃষ্টি ভঙ্গিকে সামনে রেখেই ১৯১৩ সালের প্রথম লেখা প্রকাশ থেকে তাঁর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরকাল তাঁর লেখালেখির গতি অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুতোষ সাহিত্য, গান, জীবনী, অনুবাদ সাহিত্য লিখেছেন। পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক গোলাম মোস্তফা তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কল্যাণেই শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্বের সংগে ছিলেন নিবিড়ভাবে পরিচিত। এ কারণেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে বহু স্মরণীয় শিশু ও কিশোরÑকবিতা রচনা। তাঁর রচিত আলোকমালা (১৯৫৩ খৃ.), পথের আলো (১৯৫৩ খৃ.), নতুন আলো (১৯৫৪খৃ.) এবং আলোকমঞ্জুরী (১৯৫৪খৃ.) সিরিজগুলো শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান।\r\n\r\nধর্ম বিশ্বাসই গোলাম মোস্তফার চিন্তার ভিত্তিভূমি। জগত ও জীবনের প্রতিটি সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রগাঢ় ইসলামী ভাবধারায় সম্পৃক্ত।গোলাম মোস্তফার সর্বশ্রেষ্ট অবদান বিশ্বনবী (১৯৪২ খৃ.) বহুল সমাদৃত। তাঁর লেখালেখির পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত\r\n\r\nদুইটি উপন্যাস ঃ\r\n
১. রূপের নেশা (উপন্যাস, ১৩২৬ খৃ.), ২. ভাঙ্গা বুক (উপন্যাস, ১৯২১ খৃ.)।
\r\nআটটি মৌলিক কাব্যঃ\r\n
১. রক্ত রাগ (কবিতা, ১৯২৪ খৃ.), ২. খোশরোজ (কবিতা, ১৯২৯ খৃ.), ৩. সাহারা (কবিতা, ১৯৩৫ খৃ.), ৪. হাস্না হেনা (কবিতা, ১৯২৮খৃ.), ৫. কাব্যকাহিনী (কবিতা, ১৯৩৮ খৃ.), ৬. তারানা ই পাকিস্তান (কবিতা, ১৯৫৬ খৃ.), ৭. বনি আদম, প্রথম খণ্ড (কবিতা, ১৯৫৮ খৃ.), ৮. আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি (কিশোর কবিতা, ১৯৮০ খৃ.)।
\r\n৫ টি কাব্যানুবাদ ও ১টি গল্প সংকলনঃ\r\n
১. মোসাদ্দস ই হালী (অনুবাদ কবিতা, ১৯৪১ খৃ.), ২. কালাম ই ইকবাল (কবিতা, ইকবাল কাব্যের অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.), ৩. শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা, ১৯৬০ খৃ.), ৪. জবাব ই শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা, ১৯৬০ খৃ.), ৫. আল কুরআন (বাংলা কাব্য অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.), জয় পরাজয় (গল্প, ‘রাসাইলু ইখওয়ানুস্ সাফা ১৯৬৯ খৃ. ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।
\r\n৩টি কাব্য সংকলন ঃ\r\n
১.বুলবুলিস্তান (কাব্য সংকলন, ১৯৪৯ খৃ.), ২. কাব্য গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (কবিতা আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১৯৭১ খৃ.), ৩. কাব্য সংকলন (কবিতা সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত, ১৯৬০ খৃ.)।
\r\n৪টি জীবনী গ্রন্থঃ\r\n
১.বিশ্বনবী (জীবনী, ১৯৪২ খৃ.), ২. মরু দুলাল (জীবনী, ১৯৪৮ খৃ.), ৩. বিশ্ব নবীর\r\nবৈশিষ্ট্য (জীবনী, ১৯৬০ খৃ.), ৪. হযরত আবুবকর (জীবনী, ১৯৬৫ খৃ.)।
\r\n২টি ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থঃ\r\n
১. ইসলাম ও জিহাদ ( ১৯৪৭ খৃ.), ২. ইসলাম ও কমিউনিজম (ধর্ম, ১৯৪৯ খৃ.)।
\r\n৩টি রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ:
১. ইতিহাস পরিচয় (রাজনীতি, পাঠ্য, ১৯৪৭ খৃ.); ২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (রাজনীতি, তা: বি:)। ৩.অবিস্মরণীয় বই, (ইতিহাস সম্পাদনা, ১৯৬০ খৃ.);
\r\n১টি প্রবন্ধ সংকলন:
আমার চিন্তাধারা (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬২ খৃ.), ও
\r\n১টি গানের সংকলন:
গীতি সঞ্চয়ন (গান, ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত: ১৯৬৫ খৃ., ১৯৬৮ খৃ. )।
\r\nপাঠ্য পুস্তক :
আলোক মঞ্জরী, (১৯৫৩ খৃ.), পথের আলো (১৯৫৩ খৃ.), নতুন আলো (১৯৫৪খৃ.), ইসলামী নীতিকথা (১৯৫৩ খৃ.), মনিমুকুর, ইতিহাস পরিচয় (১৯৪৭ খৃ.), ইতিকাহিনী, নতুন বাংলা ব্যকরণ, নতুন ব্যকরণ, মঞ্জু লেখা ইত্যাদি।
\r\nগ্রন্থসমূহ থেকেই বোঝা যায় কবি গোলাম মোস্তফা শুধু একজন কবিই ছিলেন না, সাহিত্যের নানা শাখায় ছিলো তাঁর স্বতস্ফূর্ত বিচরণ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন চৌকষ লেখক। তাঁর অবদান সাহিত্যের নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে আছে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্য, জীবনী, গবেষণা, পাঠ্যপুস্তক, চিন্তাধারাসহ সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁর অবদানঅপরিসীম। তিনি তাঁর কাব্যের বিরাট একটা অংশ, গদ্যের বেশির ভাগ জুড়ে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করে গেছেন। ইসলামী ঐতিহ্য চেতনায় নিজেকে ব্যপ্ত রেখেছেন। কবি গোলাম মোস্তফার প্রতিভা শুধু লেখনি মুখেই প্রকাশ পায়নি, তাঁর সাহিত্য রচনায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শেষ অবদান হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] এর জীবনী। একজন কবি, একজন সাহিত্যিক, একজন প্রবন্ধকার, একজন জীবনীকার, একজন উপন্যাসিক, একজন গীতিকার, সর্বোপরি একজন লেখক হিসেবেএখানেই তিনি সার্থক।\r\n
তাঁর রচিত শিশুদের মন মাতানো অসংখ্য ছড়া/কবিতা ইত্যাদি রয়েছে-
ক. আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,\r\nওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
............................................
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,\r\nঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।(কিশোর)।
খ. খুকুমনি জনম নিল যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখতে এল কতই খুশী ভরে। (কিশোর)।
গ. এই করিনু পণ মোরা এই করিনু পণ\r\nফুলের মতো গড়ব মোরা মোদের এই জীবন।\r\nহাসব মোরা সহজ সুখে গন্ধ রবে লুকিয়ে বুকে\r\nমোদের কাছে এলে সবার জুড়িয়ে যাবে মন। (শিশুর পণ)।
ঘ. নুরু, পুশি, আয়েশা, শফি সবাই এসেছে\r\nআম বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।\r\nরাঁধুনিদের শখের রাঁধার পড়ে গেছ ধুম,\r\nবোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।
*****************************
ধূলোবালির কোর্মা-পোলাও আর সে কাদার পিঠে,\r\nমিছিমিছি খেয়া সবাই, বলে- বেজায় মিঠে।\r\nএমন সময় হঠাৎ আমি যেই পড়েছি এসে,\r\nপালিয়ে গেল দুষ্টুরা সব খিলখিলিয়ে হেসে। (বনভোজন)।
বিটিভির এক সময়ের জনপ্রিয় ‘নতুন কুঁড়ি’র সূচনা সঙ্গীত কবির কিশোর কবিতা হতেই নেওয়া হয়েছে।
কবি গোলাম মোস্তফা আমাদের সকলের মনমত করে সূরা ফাতিহার ছন্দোবদ্ধ ভাবানুবাদ লিখেছেন,
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি\r\nবিচার দিনের স্বামী।\r\nযত গুণগান হে চির মহান\r\nতোমারি অন্তর্যামী।
তাছাড়া তাঁর লেখা হামদ, নাত আমাদের দেশের ছেলে বুড়ো সকলের প্রিয়।
তাঁর প্রকাশিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে রক্তরাগ, হাস্নাহেনা, খোশরোজ, সাহারা, কাব্যকাহিনী, এবং অনুবাদগ্রন্থ মুসাদ্দাসই হালী, তারানা ই পাকিস্তান, বনি আদম, অনুবাদ কাব্য-আল কুরআন, কালামে ইকবাল ও শিকওয়াও জবাব ই শিকওয়া এবং কবিতা সংকলন বুলবুলিস্তান। এছাড়া লিখেছেন ‘বিশ্বনবী’র মত পাঠক নন্দিত বিশালাকার গদ্য গ্রন্থ। তিনি কবি আল্লামা ইকবালের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি নজরুল ইসলামকে নিয়ে এ ছড়াটি লিখেছেন-
কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গেছিলাম
ভায়া গান গায় দিনরাত
সে লাফ দেয় তিন হাত
প্রাণে হর্ষের ঢেউ বয়
ধরার পর তার কেউ নয়।
তিনি বাংলা একাডেমী, টেক্সট বুক বোর্ড, করাচীর বুলবুল একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি(১৯৪৯), পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডি এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন।
১৯৬০ সালে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব, প্রেসিডেন্ট পদক ও আরো পাঁচ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার লাভ করেন। ঐ ১৯৬০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৬১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানী লেখকবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।
১৩ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমাদের প্রাণপ্রিয় এই মহান কবি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর রূহের মাগফিরাত দিন।
\r\n\r\n
বিদ্রোহী শাহজাদা
ছোটটো একটি গ্রাম। তাও আবার আমাদের এই বাংলাদেশে নয়। একেবারে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার অজপাড়াগাঁয়ে। চারদিকে ধান কাউনের উম উম গন্ধ। পাখ-পাখালির কিচির মিচির আওয়াজ। সন্ধ্যায় শোনা যায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝাঁঝাল ডাক। কি সুন্দর তাই না? এই গ্রামের মানুষ আবার লেটো গান ভালবাসতো। একদিন রাতে তারা ‘লেটো’ গানের আসর বসালো। আশ-পাশের বিশ গ্রামের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে গান শুনতে!
গানতো নয়, লড়াই! পুরোপুরি দুই দলের লড়াই। তবে গোলা বন্ধুক দিয়ে নয়, কবিতা দিয়ে। কি মজার কান্ড বলতো। তুমুল লড়াইয়ের পর এক পক্ষ হারে হারে অবস্থা ঠিক তখনি ঐ দলের এক পুঁচকে ছেলে লাফ দিয়ে উঠলো। এই ধরো তোমাদেরই মত বয়স বা তারও কম। হাত পা নাচিয়ে মাথার চুল দুলিয়ে গান শুরু করলো। এক এক করে বিপক্ষ দলের সব কটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। কি তাজ্জব ব্যাপার। ঐ অতটুকু ছেলে এতকিছু জানে কারোরই বিশ্বাস হয় না। সবারই মনে উঁকিঝুঁকি মারছে নানা প্রশ্ন। এ শাহজাদা কোত্থেকে এল? কি তার পরিচয়? শাহজাদাটি কিন্তু বিপক্ষ দলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হলো না। সে নিজেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিপক্ষ দলকে হারিয়ে দিলো। সমস্ত আসর উল্লাসে ফেটে পড়ল। পুচকে শাহজাদাটি ততক্ষণে মানুষের মাথার উপর পুতুলের মত নাচছে। দলের সরদার জিতে যাওয়ার আনন্দে বাগ বাগ হয়ে জড়িয়ে ধরলেন শাহজাদাকে। বললেন-
‘ওরে আমার ব্যাঙাচি
বড় হয়ে তুই একদিন সাপ হবি।’
সরদারের কথা কিন্তু ঘটেছিল, সে খুউব বড় কবি হয়েছিল। কি তোমরা পরিচয় জানার জন্য উসখুস করছো তাই না? অবশ্য করার কথা। তবে এসো তোমাদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই-তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত এবং প্রিয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি আমাদের জাতীয় কবি।
১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। চুরুলিয়া গ্রামটি আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া ব্লকে অবস্থিত। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। তার বাবা ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম| তারা ছিলেন তিন ভাই এবং বোন। তার সহোদর তিন ভাই ও দুই বোনের নাম হল: সবার বড় কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন, বোন উম্মে কুলসুম। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল \"দুখু মিয়া\"।
তোমরা হয়তো ভাবছ শাহজাদাদেরতো হাতী শালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি কত কিছু থাকে, এ শাহজাদাটিরও নিশ্চয়ই আছে। আসলে এ শাহজাদার এসব কিছুই নেই। বরং বলা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত, একেবারে মিসকীনি হালত। কিন্তু হলে কি হবে? তাঁর মনটাতো আর মিসকিন নয়, একেবারে শাহজাদার শাহজাদা। ঐ যে তোমরা শুনছো না পাতালপুরির ঐ ঘুমন্ত শাহজাদার কথা। সেই যে রূপার কাঠি আর জিয়ন কাঠির পরশে রাজকন্যার ঘুম ভাঙলো! আমাদের আজকের শাহজাদা সেই পাতালপুরীতে যেতে চান কিন্তু ঐ রকম ঘুমাতে না, সবকিছুকে ভেঙে চুরে নিজের হাতের মুঠোয় নেবার জন্য। যেমন তিনি বলেছেন-
পাতাল ফুঁড়ে নামবো আমি
উঠবো আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগত দেখব আমি
আপনা হাতের মুঠোয় পুরে।
মাত্র আট বছর বয়সে আব্বা মারা যাওয়ায় সংসারের হাল ধরতে হয় তাঁকে। এ জন্য লেখাপড়ার ইতি টেনে ঐ বয়সেই কখনো মসজিদের ইমামতি, কখনো মক্তবের শিক্ষকতা করে সংসার চালাতে থাকেন। কিন্তু যারা চিরবিদ্রোহী তাঁরা চায় স্বাধীন জীবন। গ্রাম হতে চলে এসে আসানসোল শহরে রুটির দোকানে চাকরি নেন। কষ্টের কথা ছড়ায় বলতেন এভাবে-
মাখতে মাখতে গমের আটা
ঘামে ভিজতো আমার গা’টা।
এখান হতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি হন। এরপর ভর্তি হন রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল হাই স্কুলে। যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র ঠিক সেই সময়েই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই হাবিলদার হন। এইখান হতেই তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। পত্র-পত্রিকায় প্রচুর কবিতা ছাপা হতে থাকে তাঁর। ১৯১৯ সালে ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ শেষ হয়। দেশে ফিরেই লিখেন বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’। কি পড়নি-
বল বীর-
বল উন্নত মম শির।
হ্যাঁ এই কবিতা আমাদের কবি শাহজাদাকে এক রাতের মধ্যেই বিদ্রোহী শাহজাদাতে পরিণত করে। এরপর দু’হাতে লিখতে থাকেন অজস্র লেখা। এ লেখাগুলোর প্রায় সবগুলিই ছিল অন্যায়, অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে। সে সময়কার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি শক্ত হাতে কলম ধরেন। তাঁর কলমের ডগা দিয়ে বেরুতে থাকে লকলকে আগুন। তিনি লেখেন-
এদেশ ছাড়বি কিনা বল
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।
আরও লেখেন ‘ভাঙার গান’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘প্রলয় শিখার’ মত বিদ্রোহী কাব্য। ইংরেজ সরকার রেগে গেলেন, কবিকে ঢোকালেন জেলে। কিন্তু জেলে ঢোকালে কি হবে? তিনি সেখান থেকেই অন্যান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোষণা করলেন-
এই শিকল পরা ছল মোদের
এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবো রে বিকল।
তিনি আরো বললেন-
কারার ঐ লৌহ–কপাট\r\nভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত –জমাট\r\nশিকল –পূজার পাষাণ –বেদী!\r\nওরে ও তরুণ ঈশান!\r\nবাজা তোর প্রলয় –বিষাণ ! ধ্বংস –নিশান\r\nউঠুক প্রাচী –র প্রাচীর ভেদি’।। ইত্যাদি।
গানের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী শাহজাদা সবার ওপরে। গানের মুকুটহীন এই সম্রাট এর রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা অন্য সকলের চেয়ে বেশি।
তিনি ছোটদের মনের কথাটা খুলে বলতে পারতেন। আর কেউ তাঁর মত সুন্দর করে বলতে পারেন নি। তাই তিনি সবার মত ছোটদেরও আত্মার আত্মীয়, একান্ত আপনজন। যেমন-
\"আমি হব সকাল বেলার পাখি\r\nসবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি।\r\n\"সুয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,\r\n\'হয়নি সকাল, ঘুমোও এখন\', মা বলবেন রেগে।
\r\nবলব আমি- \'আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাক,\r\nহয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাক\'?\r\nআমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে ?\r\nতোমার ছেলে উঠবে মা গো রাত পোহাবে তবে।\r\n
‘খুকু ও কাঠ বেড়ালী’ ছড়াটি কি তোমাদের মনে পড়ে? হ্যাঁ! কি যেন-
কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?\r\nগুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?
\r\nবেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও-\r\nডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,\r\nখাও একা পাও যেথায় যেটুক!\r\nবাতাবি-নেবু সকলগুলো\r\nএকলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!\r\n\r\nতবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?\r\nছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!
‘ভোর হলো’ কবিতাটি তোমাদের সবারই একান্ত প্রিয়, কি বলো? সবার মুখস্ত আছে নিশ্চয়ই-
ভোর হল, দোর খোল,\r\nখুকুমণি ওঠ রে।
ঐ ডাকে জুঁই শাখে,\r\n‘ফুল খুকী ছোট রে।
খুলি’ হাল তুলি’ পাল\r\nঐ তরী চলল।
এই বার এই বার\r\nখুকু চোখ খুলল।
এত বড় কবি হয়েও তিনি ছিলেন খুব হাসি-খুশী ও রসিক মানুষ। হো হো করে অট্টহাসি হাসতেন। ছোটরা যে নানা দাদার সাথে হাসি তামাশা করে কবি সেটা তাঁর ‘খাঁদু দাদু’ কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেছেন।
যেমন-
অমা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং।
ওঁর নাকটাকে কে করল খাঁদা র্যাঁদা বুলিয়ে?
চামচিকে ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গরুর পিঠে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অমা! আমি হেসেই মরি নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং
ওঁর খ্যাদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় ‘টু’।
ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এরাম! ওয়াক থুঃ।
কাছিম যেন উপুর হয়ে ছাড়িয়ে আছেন ঠ্যাং।
অমা! আমি হেসেই মরি, নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং।
দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়- নাক\r\nঘুম দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজতো সাতটা শাঁখ।\r\nদিদিমা তাই থ্যাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন!\r\nঅ মা! আমি হেসে মরি, ন্যাক ডেঙ্গাডেং ড্যাং।
বিয়ের মত খোশ খবর পেলে ছোটরা যে কি মজা পায়, নিজেরাই বিয়ে করার জন্য বায়না ধরে। ‘খোকার খুশী’ কবিতায় কবি সুন্দর করে ছোটদের মনের ভাবটা তুলে ধরেছেন-
কি যে ছাই ধানাই পানাই ,
সারাদিন বাজছে সানাই।
এদিকে কারুর গা নাই
আজিনা মামার বিয়ে!
বিবাহ! বাহ কি মজা
সারাদিন গন্ডা গজা
গপাগপ খাওনা সোজা
দেয়ালে ঠৈসান দিয়ে।।
এই কবিতারই শেষে বলেছেন-
সত্যি, কওনা মামা
আমাদের অমনি জামা
অমনি মাথায় ধামা
দেবেনা বিয়ে দিয়ে?
মামীমা আসলে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাহ! কি মজার খবর।
আমি রোজ করব বিয়ে।।
ওদিকে ‘খোকার বুদ্ধি’ কবিতা পড়লে তো হাসিতে দম আটকে আসতে চাইবে।
সাতটি লাঠিতে ফড়িং মারেন
এমনি পালোয়ান।
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লো সেদিন
আস্ত আলোয়ান!
ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বল? কি এর উচিত সাজা?
‘খোকার গল্প বলা’ কবিতাটাতো আরো মজার, আরো আনন্দের। বলতে গেলে তোমাদের জন্য এক থালা গরম সন্দেশ।
মা ডেকে কন, ‘ খোকন-মণি! গপ্প তুমি জান?
\r\nকও তো দেখি বাপ!’\r\n\r\nকাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ\r\n\r\nবললে খোকন, গপ্প জানি, জানি আমি গানও!’\r\n\r\nব’লেই ক্ষুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল-\r\n\r\n‘একদা এক হাঁড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!’\r\n
এই কবিতার অন্যত্র বলেছেন-
একদিন না রাজা-
হরিণ শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা
রাণী গেলেন তুলতে কলমি শাক
বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে-
হাতীর ম-মতন একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার করে।
‘পিলে পটকা’ কবিতাটিতেও প্রচুর হাসির খোরাক মিলে-
উটমুখো সে সুঁটকো হাশিম
পেট যেন ঠিক ভুটকো কাছিম।
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি-
ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি।
তিন কেনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচকা চোখে; হন্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোবনে ঢ্যাঙা!
নিট পিঠে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা।
কল্পনাপ্রবণ শিশুরা কল্পনায় সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি জমায়।
যেমন-
থাকব না’ক বদ্ধ ঘরে\r\nদেখব এবার জগৎটাকে\r\nকেমন করে ঘুরছে মানুষ\r\nযুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে\r\nছুটছে তারা কেমন করে,\r\nকিসের নেশায় কেমন করে\r\nমরছে যে বীর লাখে লাখে।\r\nকিসের আশায় করছে তারা\r\nবরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কবির এই সংকল্প কবিতাটি শিশু মনের চিরন্তন খোরাক। কবিতাটিতে শিশু মনের নানা কথা বলা হয়েছে, যা শিশুদের জন্য একান্ত আপন। কবিতাটির শেষ দু’লাইন হচ্ছে-
পাতাল ফেড়ে নামব আমি\r\nউঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,\r\nবিশ্বজগৎ দেখব আমি\r\nআপন হাতের মুঠোয় পুরে।
অন্যত্র ‘সাত ভাই চম্পা’ কবিতায় কবি লিখেছেন-
সপ্ত সাগর পাড়ি দেব আমি সওদাগর
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত-মধুকর।
সব কালের সব ধরনের শিশুদের ফলমূল চুরি করে খাওয়ার মত রোমাঞ্চকর অভ্যেস প্রচলিত আছে। আম, জাম, লিচু এগুলো তাদের কাছে লোভনীয়ও বটে। তবে এ সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে করা সম্ভব নয়, বিপদ আপদ এসে ঘাড়ে চাপে। সে কথাটি কবির ‘লিচুচোর’ কবিতায় অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।
বাবুদের তাল-পুকুরে\r\nহাবুদের ডাল-কুকুরে\r\nসে কি বাস করলে তাড়া,\r\nবলি থাম একটু দাড়া।
পুকুরের ঐ কাছে না\r\nলিচুর এক গাছ আছে না\r\nহোথা না আস্তে গিয়ে\r\nয়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে\r\nগাছে গো যেই চড়েছি\r\nছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা মড়াত করে\r\nপড়েছি সরাত জোরে।\r\nপড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,\r\nসে ছিল গাছের আড়েই।\r\nব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,\r\nধুমাধুম গোটা দুচ্চার\r\nদিলে খুব কিল ও ঘুষি\r\nএকদম জোরসে ঠুসি।
তাঁর ঝিঙে ফুল কবিতা অপূর্ব ছন্দে রচিত। ছোটরা যখন কবিতা পড়ে তখন তারা ছন্দের দোলায় দুলে ওঠে-
ঝিঙে ফুল। ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে
ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল
ঝিঙে ফুল----।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল।।
মোটকথা কবির ছিল একটা সুন্দর শিশু মন। যে মন দিয়ে তিনি বাংলার প্রতিটি শিশুর মনের কথা বুঝতে পারতেন।
কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কবি লেখার কাজ বেশিদিন চালাতে পারেন নি। কলম গেল বন্ধ হয়ে, মুখের ভাষাও আর শুনতে পেলনা কেউ। এরপরও দীর্ঘ ছত্রিশ বছর বেঁচে থাকার পর আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরের পিজি হাসপাতালে ১৯৭৬ সালের ২৯শে অগাস্ট তারিখে ‘বিদ্রোহী শাহজাদা’ সবার সাথে বিদ্রোহ করে সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ সবার যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমালেন। ইন্নালিল্লাহে ----------রাজিউন।
কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর তার কবর যেন মসজিদের পাশে হয়।
মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশেই তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। একবার এসে তোমাদের প্রিয় ‘বিদ্রোহী শাহজাদার’ কবরটি যিয়ারত করে যেও। কেমন?
\r\n\r\n
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন
আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই।
হ্যাঁ। এ জসীম উদ্দীনে কবিতার লাইন। জসীম উদ্দীনের কবিতার ধরনই আলাদা, স্বাদই আলাদা। তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ আষয় বিষয়, সাধারণ মানুষের জীবন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যিকার অর্থে এমনটি আর কোন কবি সাহিত্যিক করেন নি। যার কারণে বাংলার মানুষ তাদের এই প্রিয় কবিকে পল্লীকবি বিশেষণে বিশেষিত করেছে।
১৯০৩ সালে ১ জানুয়ারী ফরিদপুর সংলগ্ন তাম্বুলখানা গ্রামে মামার বাড়িতে জসীম উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাসও ফরিদপুর জেলা শহরের উপকন্ঠ গোবিন্দপুর গ্রামে। কবির পিতার নাম মৌলভী আনসার উদ্দীন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আনসারউদ্দীন সাহেব এর হাত দু’টি ছিল আজানুলম্বিত এবং মুখ ভরা ছিল চাপ দাড়ি। এতে করে কবির পিতাকে অসম্ভব সুপুরুষ ও সুদর্শন মনে হত। তা’ছাড়া সাদা ধুতি পরে, গায়ে পাঞ্জাবী চাপিয়ে যখন মাথায় টুপি দিতেন তখন তাঁকে আরো আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ মনে হত। সাদা পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন কবির পিতা গ্রামের এম.ই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।
জসীম উদ্দীনের লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয় তাঁর পিতা আনসার উদ্দীনের হাতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পার্শ্ববর্তী শোভারামপুরের আম্বিকা পন্ডিতের পাঠশালায়। এখান থেকে তিনি গ্রামের এম.ই স্কুলে চলে আসেন এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করেন। ঐ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালে তাঁকে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। আজন্ম রসিক জসীম উদ্দীন এ স্কুলে ভর্তি হবার পর স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল তা অত্যন্ত রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “সন্নাসীর ভক্ত হইয়া আমি পায়ে জুতা পরিতাম না। পাড়হীন সাদা কাপড় পড়িতাম। ক্লাসের ছাত্ররা প্রায় সবাই শহরবাসী। আামকে তাহারা গ্রাম্য ভূতের মতই মনে করিত। আমি কাহারো কাছে যাইয়া বসিলে সে অন্যত্র বসে। আমি শত চেষ্টা করিয়াও কাহারো সাথে ভাব জমাতে পারি নাই। আমি সঙ্কোচে পেছনের বেঞ্চে আমার চাচাতো ভাই নেহাজ উদ্দীনের সঙ্গে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিতাম। শিক্ষকেরা অন্য ছাত্রদের লইয়া কতো হাসি তামাসা করিতেন, এটা ওটা প্রশ্ন করিতেন। আমাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।”
বুঝতেই পারছো, কবির এ বর্ণনার মধ্যে তাঁর ছোটকালের ব্যথাতুর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শত অবহেলার মধ্যেও এ স্কুল হতেই কবি ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হতে ১৯২৪ সালে আই.এ এবং ১৯২৯ সালে বি.এ পাশ করেন। বিএ পাশ করার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন।
জসীম উদ্দীনের বাল্যকাল খুবই আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে কেটেছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, “আমাদের দু’খানা খড়ের ঘর। চারিধারে নলখাগড়ার বেড়া। চাটাইয়ের কেয়ার বা ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা আটকানো হয়। সেই ঘরের অর্ধেক খানিতে বাঁশের মাচা। মাচায় ধানের বেড়ি, হাড়ি-পাতিল থরে থরে সাজানো। সামনে সুন্দর কারুকার্য্ খচিত বাঁশের পাতলা বাখারী দিয়া নক্সা করা একখানি বাঁশ টাঙান।............এই ঘরের মেঝেতে সপ বিছাইয়া আমরা শুইয়া থাকিতাম।-----বাজান ঘর-সংসারের কাজ ফেলিয়া স্কুলে যাওয়া আসা করিতেন বলিয়া দাদা ছমির উদ্দীন মোল্লা বাজানের ওপর বড়ই চটা ছিলেন। বাজান তাঁহার একমাত্র পুত্র। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সংসারের সকল কাজ দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। কোনো কঠিন কাজ করিতে কষ্টসাধ্য হইলে তিনি বাজানকে খুব গালমন্দ করিতেন।” সত্যিই কবি সবদিক থেকে এদেশের মানুষের হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছির মানুষ ছিলেন।
কবির পিতা আনছারউদ্দীন সাহেব যেমন অত্যন্ত পরিপাটি ও ছিমছাম মানুষ ছিলেন, কবি ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ অগোছালো ছিলেন। বাল্যকালে কবি এক সাধুর শিষ্য হয়েছিলেন। সাধুর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে তিনি সাধুর জীবন গ্রহণের মানসে ঐ বাল্যকালেই পায়ে জুতা পরিতেন না, গায়ে জামা পরতেন না। শুধুমাত্র পাড়হীন একখন্ড সাদা ধুতির মত কাপড় দিয়েই সব কাজ চালাতেন। কখনো যদি জামা পরেছেন তো সে জামা হতো বোতামহীন।
কবির বাবা আনসারউদ্দীন ও একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কথায় কথায় কবিতা ছড়া বাঁধতে পারতেন বলে জানা যায়। এ প্রসংগে ইসলামী বিশ্বকোষ লিখেছে, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ অনুরাগ। তাঁহার কবিত্বও শক্তিও ছিল। গাজীপুর উপজেলার কবি গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। জসীমউদ্দীন উত্তরাধিকার সূত্রে সকল পৈতৃক গুণের অধিকারী হয়েছিলেন।”
দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন জসীম উদ্দীন রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতা যা ১৯২৬ সালে ‘কল্লোল’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘কবর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর রাতারাতিই জসীম উদ্দীনের কবিখ্যাতি বাঙালী পাঠকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-নজরুল যুগে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের এ কবিতা পড়ে ডঃ দীনেস চন্দ্র সেন কবিকে লিখেন, “দুরাগত রাখালের বংশী ধ্বনির মত তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।” ডঃ সেন ইংরেজী পত্রিকা Forward এ জসীম উদ্দীনের ওপর একটি পুরো ইংরেজী প্রবন্ধ লিখেন, যার শিরোনম ছিল `An young mohammadan poet’.
সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো, কবি যখন বিএ ক্লাসের ছাত্র তখনই এই ‘কবর’ কবিতাটি পুস্তকে সংকলিত হয় এবং ম্যাট্রিক ক্লাসে পাঠ্য হয়।
ছাত্রাবস্থায়ই কবি কর্মজীবনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৪ সালে তিনি ৭০ টাকা আর্থিক মাসোহারার বিনিময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পল্লী সাহিত্য সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। এম.এ পাস করার পূর্ব পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর ড. দীনেস চন্দ্র সেনের অধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতন লাহিড়ী রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।
১৯৩৭ সালে কবি বিবাহ করেন। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৪ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগের পাবলিসিটি অফিসার পদে যোগ দেন এবং ১৯৬৮ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এ সময়ে কন্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন তাঁর সহকর্মী ছিলেন।
কবির মনটি ছিল আকাশের মত উদার। আর সে মানুষ যদি হয় গায়ের লোক, বা তোমাদের শিশু কিশোর তা’হলে তো কথাই নেই। ছোট সুন্দর ফুটফুটে খুকী দেখলে কবি অমনি খলবলিয়ে বলে উঠেন-
“এই খুকীটি আমায় যদি একটু আদর করে
একটি ছোট কথা শোনায় ভালবাসায় ভরে;
তবে আমি বেগুন গাছে টুনটুনিদের ঘরে,
যত নাচন ছড়িয়ে আছে আনব হরণ করে;
তবে আমি রূপকথারি রূপের নদী দিয়ে,
চলে যাব সাত সাগরে রতন মানিক নিয়ে;
তবে আমি আদর হয়ে জড়াব তার গায়,
নুপুর হয়ে ঝুমুর ঝুমুর বাজত দুটি পায়।”
আসমানী কবিতায় দরিদ্র, অভাব অনটনে জর্জরিত শিশুদের নিয়ে তিনি লিখেছেন-
“পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের কখান হাড়,
সাক্ষী দিছে অনাহারে ক’দিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হ’তে হাসির প্রদীপ রাশি
তারপরেতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।”
এমনি দরদ দিয়ে লিখতে পারা সত্যি সবার পক্ষে সম্ভব নয়।
ছোটদেরকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছেন-
“আমার বাড়ি যাইও পথিক
বসতে দেবো পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেবো
শালি ধানের চিড়ে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব
বিন্নী ধানের খই
ঘরে আছে ফুল বাতাসা
চিনি পাতা দই।”
কি জিহবায় পানি এসে যাচ্ছে, তাই না? আবার শহুরে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে লিখেছেন-
“তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে
আমাদের ছোট গায়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায়
উদাসী বনের বায়।”
ইত্যাদি হাজারো উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে তাঁর লেখা হতে।
তাঁর শিশুতোষ লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে- হাসু, একপয়সার বাঁশি, ডালিম কুমার এবং বাংগালীর হাসির গল্প ১ম ও দ্বিতীয় খন্ড। তিনি শুধু ছোটদের জন্যই লিখেন নি, বড়দের নিয়েও প্রচুর লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কাব্য ২০ খানা, নাটক ১৩ খানা, জারী ও মুর্শিদী গানের সম্পাদনা করেছেন দু’খানা বই।
কবির বহুল পাঠ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ও রাখালী। যা দেশে বিদেশে কবিকে বহুল পরিচিতি ও খ্যাতির আসনে সমাসীন করেছে।
নকশী কাঁথার মাঠ, বেদের মেয়ে, বাংলাদেশের হাসির গল্প ও জসীম উদ্দীনের নির্বাচিত কবিতা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কবি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ‘হলদে পরীর দেশ’ নামক গ্রন্থের জন্য ইউনেসকো পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে বাঙালীর এই প্রিয় কবি, পল্লী কবিকে বাংলা একাডেমী কোন সম্মানে ভূষিত করেনি। এটা বাংলা একাডেমী ও এ জাতির জন্য সত্যিই লজ্জার। অবশ্য তাঁর বাসস্থান ‘পলাশ বাড়ি’ যে রোডে অবস্থিত তার নাম ‘কবি জসীম উদ্দীন স্মরণী’ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের নাম ‘কবি জসীম উদ্দীন হল’ রাখা হয়েছে।
কবি জসীম উদ্দীন তাঁর নিজ বাসভবন ‘পলাশ বাড়ি’তে ১৯৫৩ সাল হতে একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করে আসছিলেন, যা আমৃত্যু জারি রেখেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তারিখে সাহিত্য সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সাহিত্যিক সাংবাদিক মোদাব্বের ও কবি আজিজুর রহমান উপস্থিত হয়ে সাহিত্য সভার বদলে কবির জানাযা পড়েছিলেন। অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তারিখে বাংলার আপামর জনসাধারণের নয়নের মণি পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
\r\n\r\n
বন্দে আলী মিয়া
তোমাদেরকে এখন এমন এক ব্যক্তিত্বের কথা বলব যিনি তাঁর সিংহভাগ সময় এবং শ্রম তোমাদের জন্যই ব্যয় করেছেন। তিনি হলেন কবি বন্দে আলী মিয়া। জানি এ নামটি তোমাদের পরিচিত ও প্রিয়। বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালের ১৭ জানুয়ারী পাবনা শহরের শহরতলীর রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম মুনসী উমেদ আলী মিয়া এবং মাতার নাম নেকজান নেছা। সাহিত্যে প্রায় সকল বিষয়ে-ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী, রহস্য-রোমান্স, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি নিয়ে তিনি লিখেছেন। এসব বিষয়ে তিনি বড়দের জন্য যেমন লিখেছেন, ছোটদের জন্য লিখেছেন তার ঢের বেশি। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন স্বার্থক শিশু সাহিত্যিক।
কবি বন্দে আলী মিয়ার শিক্ষা জীবন শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর স্নেহময়ী পিতা ইন্তিকাল করেন। মা নেকজান নেছা ইয়াতীম শিশুপুত্রকে গ্রামের মজুমদার একাডেমীতে ভর্তি করে দেন এবং এখান হতেই ১৯২৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছবি আঁকতে কবি খুব ভালবাসতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসের পর তিনি কলকাতার বৌ বাজারে অবস্থিত ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর উৎসাহে তিনি টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদত কলেজে আই.এ ভর্তি হন। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে মফস্বলের কলেজ ভাল না লাগায় ১৯২৯ সালে কলেজ ত্যাগ করেন ও তাঁর আর পড়াশোনা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এরপরই বন্দে আলী মিয়া মায়ের একান্ত আগ্রহে বগুড়া শহরের বৃন্দাবন পাড়া নিবাসী রাবেয়া নামের এক সুন্দরী রমনীকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে ওঠেন।
কবি বন্দে আলী মিয়া ১৯৩০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং একটানা কুড়ি বছর এ চাকরিতে বহাল ছিলেন। এই শিক্ষকতার জীবনেই তিনি শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভালভাবে শিশুমনকে জানার সুযোগ পান। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে শিশুদের মতই সহজ সরল ছিলেন। তাঁর মুখে সব সময় হাসির একটা মিষ্টি ঝিলিক ছড়িয়ে পড়তো। দেখামাত্রই ছোটদেরকে কাছে টানার তাঁর চমৎকার সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল। শিশুদের কাছে তিনি কবি দাদু হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে ‘ছেলে ঘুমানো’ নামক শিশু অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিদিন শিশু উপযোগী গল্প গান ইত্যাদি লিখে দিতেন।
কবি নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ‘বেঙ্গল গেজেট’ পত্রিকায় তাঁর ‘ছিন্নমূল’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে কবির শিশু কিশোরদের উপযোগী প্রথম বই ‘চোর জামাই’ প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের ছবিগুলি কবির নিজের হাতে আঁকা। ‘চোর জামাই’ প্রকাশিত হওয়ার পর কবি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ছবি এঁকেও কবি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আঁকা মোনাজাতের ছবিটি ব্যাপক প্রচার ও প্রশংসা লাভ করে।
কবি বন্দে আলী মিয়ার তোমাদের জন্য লেখা অনেক মনগড়া কবিতা রয়েছে।
যেমন-
আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দিঘী,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি। (আমাদের গ্রাম)।
কি চমৎকার কবিতা, তাই না? কবিতাটি ভিতর কোন যুক্তাক্ষর নেই। কারণ কবি শিশু মন বুঝতেন, তাঁদের কষ্টের কথা বুঝতেন। তাই তিনি যতদূর সম্ভব সহজ সরল অথচ সুন্দর ভাষায় লিখেছেন।
তিনি লিখেছেন-
আয় আয় পিস পিস,
দেখ ভাই ময়না,
চুপ চুপ, গোলমাল
কথা আর কয় না। (আফরোজার পুষি)।
ব্যাঙের বিয়ে ছড়াতে লিখেছেন-
ছোট কোলা ব্যাং
ডাকে গ্যাং গ্যাং।
তার নাকি বিয়ে
টুপি মাথায় দিয়ে।
কবি বন্দে আলী মিয়ার প্রায় পৌণে দুইশত বই এর মাঝে ১২৫ খানা বই-ই ছোটদের উপযোগী। এর মধ্যে ইতিহাস আশ্রয়ী বই, যেমন-ছোটদের বিষাদ সিন্ধু, তাজমহল, কোহিনূর, কারবালার কাহিনী ইত্যাদি। তিনি কোরআন ও হাদীসের কাহিনী নিয়েও গল্প লিখেছেন, আবার গুলিস্তাঁর গল্প, ঈশপের গল্প, দেশ-বিদেশের গল্প, শাহনামার গল্প। তিনি অনেকগুলি জীবনী লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আমাদের নবী, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত ফাতিমা, হযরত মূসা, তাপসী রাবেয়া, সিরাজউদ্দৌলা, হাজী মহসিন, ছোটদের নজরুল ইত্যাদি।
এসব লেখার মধ্য দিয়ে তিনি আগামী দিনের নাগরিক শিশু কিশোরদের চরিত্র গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন-
‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।’
ইসলামের সুমহান আদর্শ শিশুদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য পবিত্র কুরআনের ১৫টি কাহিনী নিয়ে তিনি ১৫টি গল্প লিখেছেন। হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় লেখা এ গল্পগুলি হল-আদি মানব ও আজাযিল, স্বর্গচ্যুতি, হাবিল ও কাবিল, মহাপ্লাবন, আদ জাতির ধ্বংস, ছামুদ জাতির ধ্বংস, বলদর্পী নমরুদ, হাজেরার নির্বাসন, কোরবানী, কাবা গৃহের প্রতিষ্ঠা, ইউসুফ ও জুলেখা, সাদ্দাদের বেহেশত, পাপাচারী জমজম, কৃপণ কারুন, ফেরাউন ও মূসা ইত্যাদি।
পবিত্র হাদীস হতে ১৪টি কাহিনী নিয়ে তিনি লিখেছেন ১৪টি গল্প। বইয়ের নাম দিয়েছেন-‘হাদীসের গল্প’। এ বইয়ের গল্পগুলি এ রকম-দীন জনে দয়া করো, সত্য নিষ্ঠার পুরস্কার, ক্ষুধাতুরে খাদ্য দাও, স্বল্প কথা, খোড়া শয়তানের বাহাদুরী ইত্যাদি।
তাঁর গল্প লেখার নমুনা এরকম-‘এক দেশের এক রাজা। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে হীরামানিক, তবু রাজার মনে সুখ নেই। রাজার কোন ছেলে পুলে নেই। একটি মেয়েও যদি হতো তবু রাজা-রাণীর মনে সুখ থাকতো।’
অন্যত্র লিখেছেন-
বাঘঃ হালুম-খক খক খেঁকশিয়াল সাহেব। আদাব।
খেঁকশিয়ালঃ মাননীয় বাঘ বাহাদুর যে, আসুন, আসুন, আদাব। আপনি বনের বাদশা, শত কাজ ফেলে সময় করে যে আমার পুত্রের বিবাহে আসতে পেরেছেন-আমার নসিব। আপনার পলাশ ডাংগায় সবাইকে যে দাওয়াত করেছিলুম, তারা এখনো এসে পৌছুলেন না।
বাঘঃ আমি না আসলে তো কউ আগে আসতে পারেন না। ঐ যে আসছেন সবাই। কি হে পন্ডিত এত দেরী যে?
শৃগালঃ ক্যাহুয়া, ক্যাহুয়া। একটু দেরী হুয়া। আসবার পথে একটা রামছাগলের বাচ্চা পেলুম। নাশতাটা না সেরে আসি কি করে? জানিতো বিয়ে বাড়িতে কখন বরাতে জুটবে বলা যায় না। (বিড়ালের প্রবেশ)।
বাঘঃ পন্ডিত রসিক লোক, নাশতা হয়েছে ভালই হয়েছে। এই যে সরকার সাহেব, আদাব।
বিড়ালঃ আদাব, খেঁকশিয়াল সাহেব। আপনার পুত্রকে এই ইদুরের মুক্তা মালা ছড়া আমার আশীর্বাদ দেবেন।
খেঁকশিয়ালঃ এসব আবার কেন? নিমন্ত্রণ পত্রে তো উল্লেখ ছিল, ‘লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়’। তা মালাছড়া যখন এনেছেন-(কুমীরের প্রবেশ)
‘খেঁক শিয়ালের দাওয়াত’ (টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার)।
কার না ভাল লাগে পশুদের এমন চমৎকার সংলাপ? কবি বন্দে আলী মিয়া শিশু কিশোর উপযোগী জীবনী গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন অসম্ভব হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে। তিনি ‘আমাদের নবী’ গ্রন্থে মহানবী(সা) সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। সেই চাঁদের আলোকে চারিদিক পুলকিত। বিবি আমিনা এক ঘরে ছটফট করেছেন। প্রহরের পর প্রহর কাটতে থাকে। নিখিল বিশ্ব স্তব্ধ নীরব। রাতের শেষ প্রহর, চাঁদ আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। বিবি আমিনার আঁধার ঘর আলোকিত করে একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ট হলেন।
………..বাতাস ছুটে এসে খর্জুর বীথি আর আঙ্গুর গুচ্ছকে খোশ আমদেদ জানিয়ে গেল। জাফরানের খুশবু এই খবর নিয়ে ছুটলো মরু আরবের দিগ দিগন্তে।
এসেছে দীনের নবী
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
তাঁহারি রওশানিতে
জাহান হলো উজ্জ্বালা।।
এ প্রাণস্পর্শী বর্ণনা নিঃসন্দেহে বড়দেরও হৃদয় না কেড়ে পারে না।
কবি বন্দে আলী মিয়ার লেখার প্রশংসা করেছেন বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিকপালেরা। এর মধ্যে রয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাকবি কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদ্দীন, কবি সমালোচক আবদুল কাদির প্রমুখ। আর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ওপর জ্ঞানগর্ভ একটি পুরো প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা ব্যাপড় সাড়া ফেলেছিল। কবির কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে শিশু সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান করে। আর ১৯৬৫ সালে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট পুরস্কার।
এই নিরলস শিশু সাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়া ২৮ জুন, ১৯৭৯ সালে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। আমাদের জানামতে তাঁর ২৫ টা অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে যা বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করি। তাঁর রচনাবলীও প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।
\r\n\r\n
রাজপুত্তুর কবি
এই হিং নেবে হিং, কিসমিস, খুবানি, আঙুর, পেস্তা, বাদাম, আখরোটঃ নে-বে। লম্বা পিরহানের জেবে কলসী ভাঙা চাড়া, কড়ি এসব ভরে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে দরাজ গলায় হেঁকে চলেছে এক কিশোর। বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখ। যেন সে দুটি চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে সত্যের দ্যুতি। লম্বা বাঁকানো বাঁশির মত নাক, প্রশস্ক কপাল, ঘাড় অবধি নেমে যাওয়া ঝাঁকড়া চুল-সব মিলিয়ে এক অপরূপ রাজপুত্তুর। কাবুলিওয়ালা সাজার ইচ্ছায় যে রাজপুত্তুর বেশ হাঁক-ডাক করতো।
রাজপুত্তুরটির যেমন ছিল দরাজ গলা, আগুনঝরা চোখ, বাবরীদোলানো চুল, তেমনি ছিল দুরন্ত সাহস। ভয় কখনো তাঁর দিলে বাসা বাঁধেনি। যা সত্য, যা সুন্দর তা সে আজীবনই মেনে চলেছে, সমাজেও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।
তোমরা হয়ত ভাবছ, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের কোন কথা বলছি। না, আসলে তা নয়। এর রাজপুত্তুরটি রাজমহল আমাদের দেশের এক গন্ডগ্রামে। অতীতকালে তাঁর এলাকাটা শাসন করেছে রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা বিক্রমাদিত্য, খান জাহান আলীর মত রাজা বাদশাহরা। হ্যাঁ, দেশটির নাম যশোরাদ্য দেশ। পরে এটা যশোর জেলা নামে পরিচিত হয়। এ জেলারই মাগুরা মহকুমার আওতাধীন মাঝাইল গ্রামে সে রাজমহল। রাজপুত্তুরটির নাম ফররুখ। পুরো নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ।
১৯১৮ সালের ১০ই জুন ফররুখ আহমদ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। মায়ের নাম বেগম রওশন আখতার। মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান তিনি।
গ্রামের স্কুলেই তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এরপর কলকাতার তালতলি মডেল স্কুলে, বালিগঞ্জ হাইস্কুলে, খুলনা জেলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। খুলনা জেলা স্কুল হতে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। বালিগঞ্জ হাই স্কুলে পড়াকালে কবি গোলাম মোস্তফাকে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান। আর খুলনা জেলা স্কুলে পান কবি আবুল হাশিম ও অধ্যাপক আবুল ফজলকে শিক্ষক হিসেবে। কলকাতার রিপন কলেজ হতে ১৯৩৯ সালে তিনি আইএ পাশ করেন। পরে দর্শনে অনার্স নিয়ে বিএ ভর্তি হন। আরো পরে ইংরেজিতে অনার্স নেন। কিন্তু ঐ পর্য্ন্ত যে কোন কারণেই হোক তাঁর আর অনার্স পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।
হ্যাঁ, রাজপুত্তুরটি ছিলেন সত্যি সত্যিই রাজপুত্তুরের মত। যখন হাঁটতেন মনে হত কেশর দুলিয়ে সিংহের বাচ্চা হেঁটে যাচ্ছে। হাঙর কুমিরকে থোড়াই কেয়ার করে দলবল নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি বলতেন, ‘হাঙর কুমির যদি থাকে, আমার ভয়েই তারা পালিয়ে যাবে।’ সারা জীবন এমনই তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, কারো কাছে কোনদিন কোন কারণে মাথা নত করেন নি।
রাজপুত্তুরটি ছিলেন খুবই ভাবুক প্রকৃতির। রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ হেসে উঠতো তখন বিছানা ছেড়ে চলে যেতেন ডাহুক ডাকা বাঁশঝাড়টার কাছে। চুপচাপ শুনতেন ডাহুকের ডাক আর কবিতা লিখেতেন-
রাত্রিভর ডাহুকের ডাক……
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি
কানপেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।
আবার-
তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে আসে পালক মেঘের অন্তরালে
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।
মাঝে মাঝে তিনি বাড়ির পুচকে পুচকে পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেড়াতে বের হতেন্, যেন রাজপুত্তুরের হরিণ শিকার। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন মধুমতির তীরে। পলকহীনভাবে দেখতেন নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার জাহাজের আনাগোনা। শুনতেন মাঝি-মাল্লার দাঁড় ফেলার শব্দ, হাঁক-ডাক। এসব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন। সাথীদেরকে এসময় দিতেন ভূগোলের জ্ঞান। বলতেন, “পাহাড় হতে এসেছে এই নদী। তারপর চলে গেছে দক্ষিণে, সেখানে আছে বঙ্গোপসাগর, তারপর আরব সাগর। নৌকা চড়ে ভেসে যেতে কোনো বাধা নেই, কোনো মানা নেই। কিন্তু সাবধান, হুঁশিয়ার। আসবে ঝড়, উঠবে তুফান, বড় বড় কুমীর আর হাঙর মাতামাতি করবে। আল্লাহ আল্লাহ করে নৌকা ছাড়লে আর কোন ভয় নেই।”
কবি ফররুখ আহমদ চেয়েছিলেন এই ঘূনে ধরা সমাজটাকে ভেঙ্গে একটা সুন্দর সমাজ গড়তে।
তাঁর কথায়-
আল্লাহর দেওয়া বিশ্ববিধান
ইসলামী শরীয়ত
যে বিধানে মোরা গড়িয়া তুলিব
এই পাক হুকুমত।।
তৌহিদে রাখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস
আমরা সৃজিব নয়া ইতিহাস
দেবো আশ্বাস দুনিয়ার বুকে
দেখাব নতুন পথ।।
সারা মুসলিম দুনিয়াকে বেঁধে
একতার জিনজিরে
ফিরায়ে আনাব হারানো সুদিন
নয়া জামানার তীরে।।
আলী, উসমান, উমরের দান
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান
নেব ফেরা মোর আবূ বকরের
সত্য সে খেলাফত।
কবির দৃঢ় বিশ্বাস আগের দিনে যারা জাতির নেতৃত্ব দিয়েছে, তাঁদের ত্রুটির কারণেই আজ মুসলিম জাতি এই খারাপ অবস্থায় পৌছেছে। যেমন-
শুধু গাফলাতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছে তুলে
আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে,
মুসাফির দল বসি,
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের,
সেতারা শশী।
মোদের খেলাধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্ববরী। (পাঞ্জেরী)।
সারা দুনিয়ায় আবার নতুন করে মুসলিম জাগরণ শুরু হয়েছে। আবার যেন নতুন সূর্য্ ওঠার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন-
কেটেছে রঙ্গিন মখমল দিন, নতুন
সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,……….
…………………………………………
নতুন পানিতে সফর এবার এ
মাঝি সিন্দাবাদ। (সিন্দাবাদ)।
কিন্তু আমাদের জাতির নেতারা যখন হতাশ, সাহসহারা তখনো রাজপুত্তুর তার সাহসে ভর দিয়ে বলেছেন-
আজকে তোমায় পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে। (সাত সাগরের মাঝি)।
কবির রাজপুত্তুরটি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এই দৃঢ় প্রত্যয়ী রাজপুত্তুরটি তার জীবনেও ইসলামী অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। কোন ঝড়, কোন বিপদ তাঁকে এপথ হতে চুল পরিমাণও সরাতে পারে নি।
তিনি বিপদ মুসিবতের সময় ভেঙ্গে পড়াকে ঘৃণা করতেন। এই সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাওয়াটাও মোটেই পছন্দ করতেন না। কবি লিখেছেন-
তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে
খোদার মদদ ছাড়া
পরের ওপর ভরসা ছেড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়া।
এমনিভাবে তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে দেশ জাতির মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য অনেক ভাল ভাল বই লিখেছেন। যেমন-‘পাখির বাসা’, ‘হরফের ছড়া’, ‘নতুন লেখা’, ‘ছড়ার আসর’, ‘নয়া জামাত’, ‘চিড়িয়াখানা’ ইত্যাদি। ‘পাখির বাসা’ বইটির জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও কবি পেয়েছেন-বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।
\r\n\r\n
এক সংগ্রামী চেচেন নেতা জওহর দুদায়েভ
সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার এক মুসলিম জনপদের নাম রাশিয়া। সত্যি কথা বলতে কি ১৯৯১ সালের ১লা নভেম্বরের আগে বাংলাদেশের মানুষ জানতো না এই মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ চেচনিয়ার কথা। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ জনগণও এই জনপদটির খবর রাখত না। ১৯৯১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ রাশিয়া ১৫টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন চেচনিয়া স্বাধীনতার ডাক দেয়। রাশিয়ার পনেরটি প্রজাতন্ত্রের বাইরে নব্বইটি স্বায়ত্ত্বশাসিত অঙ্গ প্রজাতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলোর মধ্যে চেচনিয়া একটি।
৬০০০ বর্গমাইল আয়তনের এ ক্ষুদ্র জনপদের লোকসংখ্যা ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত ছিল ১২ লাখ ৮৯ হাজার ৭০০ জন। চেচনিয়ার রাজধানীর নাম গ্রোজনী যার লোকসংখ্যা ছিল ৪ লাখের ওপরে। গ্রোজনী শব্দের অর্থ দুর্দম্য, দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, জাদরেল ইত্যাদি।
বর্তমানে যুদ্ধের কারণে সমগ্র চেচনিয়াতে মাত্র ৪ লাখের মত লোক অবস্থান করছে, বাকীরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে প্রায় ২ লাখের মত চেচেন মারা গিয়েছে বলে জানা যায়। এর আগে ১৯৪৪ সালে স্টালিন সরকার গণহত্যার মাধ্যমে ‘মুসলিম সমস্যা’ সমাধানের লক্ষ্যে জোরপূর্বক ১২ লক্ষ (ঐ সময় চেচনিয়ায় ১২ লক্ষ মুসলমান ছিল) চেচেন মুসলিমকে কাজাখাস্তানে নির্বাসনে পাঠায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ১২ লক্ষ চেচেন মুসলিমদের মধ্যে ৩ লক্ষ পথেই মারা যায়।
ইতিহাস হতে জানা যায়, চেচনিয়ার পার্শ্ববর্তী দাগাস্থানের দ্বারবন্ধ শহরে ৬৪৩ সালে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়। এর আগে ৬৩৯ সালে আরবরা আজরাবাইজান দখল করে নেয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে পুরো দ্বারবন্ধ এলাকায় ইসলাম প্রসার লাভ করে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী চেচনিয়াতে ইসলাম প্রবেশ করতে সময় লাগে। পন্ডিতদের মতে, ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে চেচনিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করে। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে এসে চেচেন মুসলমানদের ওপর রুশ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। ১৫৯৪ সালে মুসলিম বনাম রুশ বাহিনী উত্তর দাগাস্থানের পুলাক নদীর তীরে রুশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। হঠে যায় রুশ বাহিনী। ১৬০৪ সালে রুশ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আঘাত হেনে আবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা রুশ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই বিরাট বিজয় ছিনিয়ে আনে। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর সেই যুদ্ধের শুরু।
জাতীয়তার দিক হতে চেচেনরা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অধিকাংশ জনসংখ্যা তুর্কী বংশোদ্ভুত মুসলমান। জার শাসন ও পরবর্তীকালে সত্তর বছরে কমউনিস্ট শাসনামলে চেচেন মুসলমানদের চেতনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। ইতিহাস সাক্ষী চেচনিয়া কোন কালেই রাশিয়ার অংশ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চেচনিয়াকে জোরপূর্বক রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। বহুকাল ধরে রুশরা বারবার চেচেনদের ওপর হামলা চালিয়েছে কিন্তু চেচেন মুসলমানরা কোনকালেই এই অন্যায় আধিপত্য মেনে নেয় নি। বরং তাদের বিরুদ্ধে ইমাম শেখ মসুর উশুরমা(১৭৩২), শেখ মোহাম্মদ, গাজী মোহাম্মদ, গামজাতবেক, শে হাজী ইসমাঈল, মোল্লা মোহাম্মদ, জামাল উদ্দীন ও ইমাম শামিলরা আপোসহীন জিহাদ পরিচালনা করেছেন। ১৮৫৯ সালের ২৫ শে অগাস্ট ইমাম শামীল রুশ বাহিনীর কাছে সম্মানজনক আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। গুনিব গ্রামের এ যুদ্ধে ইমাম শামিলের সর্বশেষ ৪০০ মুরীদের প্রায় সবাই শহীদ হন। তারপরও ১৮৫৯-৬৪ সালে পর্যন্ত চেচেনরা ককেশাসের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে চেচেনরা জার্মানকে সমর্থন দেয়ায় স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ চেচেনকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে কাজাখস্থানে নির্বাসন দন্ড প্রদান করে। এই নির্বাসন চলাকালে ১৯৪৪ সালের ১৫ এপ্রিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ পিয়ার ভোমায়াস্কা এলাকার ইয়ালখের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা ছিলেন মূসা এবং মাতার নাম ছিল আলেপতিনা কেদোরভনা দুদায়েভ। দুদায়েভের আব্বা ছিলেন জাতিতে চেচেন এবং মা ছিলেন রুশ। মোট ৭ ভাই বোনের মাঝে দুদায়েভ ছিলেন সবার ছোট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়ায় তাঁর আব্বা ও বড় ভাইকে শহীদ করে দেয় স্টালিনবাহিনী।
দুদায়েভ রাডিকাফ কাজে ইলেক্ট্রনিক্স্রের ওপর দু’বছর পড়াশোনার পর সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের রাশিয়ার তাম্বর শহরের বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেনেদ্র তাঁর সামরিক শিক্ষা শুরু হয়। জাতিগতভাবেই রুশরা অন্তর থেকেই চেচেনদের ঘৃণা করে। এরপরও জওহর দুদায়েভ আপন প্রতিভা বলে সমস্ত প্রকার বাধা অতিক্রম করে রাশিয়ার সেরা সামরিক স্কুল ইউরি গ্যাগারিন এয়ারফোর্স একাডেমী, মস্কোতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গতানুগতিক নিয়মে দুদায়েভ ১৯৬৮ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্য্ন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৬-৭৯ পর্যন্ত দুদায়েভ রাশিয়ার এয়ারফোর্স রেজিমেন্ট এর চীফ অব স্টাফ, ১৯৭৯-৯০ কমান্ডার অব ডিভিশন এবং ১৯৯০ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এরপর দুদায়েভ ১৯৯০-৯১ সেশনের জন্য চেচেন জাতির মহাসম্মেলনের নির্বাহী কমিটির প্রধান ছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ ও অলঙ্কৃত করেন।
জওহর দুদায়েভ আল্লা নাম্নী এক রুশ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে ছিল।
দুদায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর মাঝে জাতীয় চেতনা ও অতীত ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে চেচেত জাতির ভেতর তাঁদের পূর্ণ মুসলিমসত্ত্বা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তারা সে বছরেই দুদায়েভের নেতৃত্বে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, যে স্বাধীনতা ছিল চেচেন জাতির আবহমানকালের লালিত স্বপ্ন। ১৯৯৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন যখন তার তিন ডিভিশন সৈন্যকে চেচনিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন তখন দুদায়েভ চেচেন জাতির আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে ওঠেন। চিরসংগ্রামী চেচেন জনগণ তাঁর নেতৃত্বে সুশিক্ষিত বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে মরনপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা যে কোন স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
১৯৯৫ সালে দুদায়েভের বড় ছেলে রুশদের অস্ত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে শহীদ হন এবং ১৯৯৬ সালের গোড়ার দিকে তাঁর জামাতা সালমান রাদুয়েভও শহীদ হন।
দুদায়েভের প্রিয় শখ ছিল কারাতে ও সঙ্গীত। তিনি পুশকিন ও লের মগুভের কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। কারণ ছিল এ দু’জন কবি ককেশাসকে অত্যন্ত ভালবেসেছিলেন এবং ককেশাসের উপর তাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা আছে।
দুদায়েভ কুরআন তিলাওয়াত করতে ও শুনতে ভালবাসতেন। তিনি খুব ফুল প্রিয় লোক ছিলেন। যে কারণে ফুলের বাগান পর্যন্ত করেছেন। দৈহিকভাবে ছোটখাট এ মানুষটি ছিলেন প্রাণোচ্ছ্বল জীবন্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এখনকার কিংবদন্তী।
চেচনিয়াকে নিয়ে ছিল তার সীমাহীন স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন চেচনিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি চেচনিয়ার মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। চেচনিয়াকে তিনি ১৯৯১-১৯৯৪ পর্যন্ত তিন বছরের কিছু বেশি সময় স্বাধীন রাখতে পেরেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি এক দুদায়েভই ছিলেন চেচেন জাতির স্বাধীনতার প্রতীক। দুর্ধর্ষ ককেশীয় চেচেন জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী।
আজাদী পাগল চেচেনরা পাহাড়ী অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ২১শে এপৃল ১৯৯৬ তারিখে চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতোভয় মহানায়ক, চেচেনদের নয়নের মনি, চিরসংগ্রামী নেতা জওহর দুদায়েভ স্যাটেলাইট ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গ্রোজনী হতে ৩০ কিমি দূরে জেখেসু গ্রামের একটি মাঠে শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় তিনি চেচেন সংকট নিরসনের জন্য মধ্যস্থতার ব্যাপারে স্যাটেলাইট টেলিফোনে আলাপ করছিলেন। জানা যায়, কাপুরুষ ইয়েলৎসিন বাহিনী কৌশলে স্যাটেলাইট টেলিফোনের অবস্থান জেনে নিয়ে রুশ বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। ইতিহাস বলে চেচেন মুসলমানরা আজাদী পাগল এক যোদ্ধা জাতি। সত্যিই তারা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। আর যারা মৃত্যুকে ভয় পায় না, বিজয় তাদের অনিবার্য। হতে পারে সেটা সময় সাপেক্ষ। প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ শহীদ হলেও চেচনিয়ার ঘরে ঘরে হাজার হাজার দুদায়েভ এখন তৈরী হবে, জন্ম নেবে।
--- সমাপ্ত ---
সুচীপত্রঃ
ভূমিকা
মহাকবি শেখ সাদী
মহাকবি হাফিজ সিরাজী
হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)
মহাকবি আলাওল
শাহসূফী মুজাদ্দিদে যামান আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.)
হযরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ.)
মহাকবি কায়কোবাদ
মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ
মহাকবি আল্লামা ইকবাল
ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন
গোলাম মোস্তফাঃ একজন মুসলিম কবির প্রতিকৃতি
বিদ্রোহী শাহজাদা
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন
বন্দে আলী মিয়া
রাজপুত্তুর কবি
এক সংগ্রামী চেচেন নেতা জওহর দুদায়েভ
ভূমিকা
মহাকবি শেখ সাদী
মহাকবি হাফিজ সিরাজী
হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)
মহাকবি আলাওল
শাহসূফী মুজাদ্দিদে যামান আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.)
হযরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম(রহ.)
মহাকবি কায়কোবাদ
মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ
মহাকবি আল্লামা ইকবাল
ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন
গোলাম মোস্তফাঃ একজন মুসলিম কবির প্রতিকৃতি
বিদ্রোহী শাহজাদা
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন
বন্দে আলী মিয়া
রাজপুত্তুর কবি
এক সংগ্রামী চেচেন নেতা জওহর দুদায়েভ

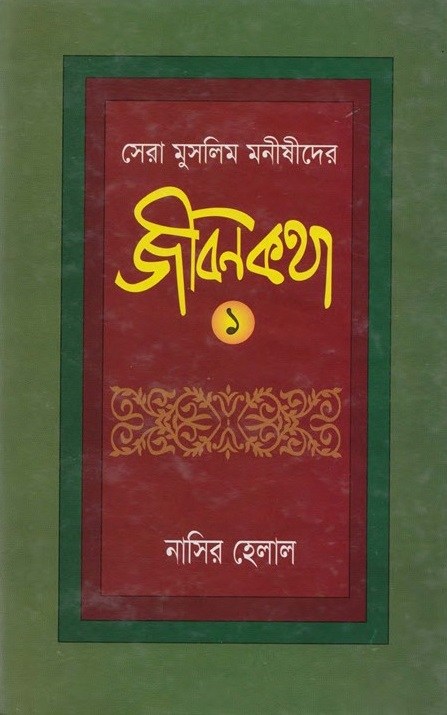 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড