প্রকাশকের কথা
ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান। সর্বশেষ নবী সৃষ্টির মহা পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তিরোধানের পর চার খলিফা ও পঞ্চম খলিফা হিসেবে খ্যাত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাঃ) এর যুগকে ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে এবং সে সময়কার সামগ্রিক কর্মকান্ড যথাঃ খলিফাতুল মুসলিমিনের খোদাভীতি, উন্নত নৈতিক মান, জনসেবা, সরকারী কোষাগার থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক কপর্দকও গ্রহণ না করা, সামাজিক শান্তি, শৃংখলা, সুবিচার, একে অন্যের প্রতি মমত্ববোধ, সহানুভূতি ইত্যাদি সর্বকালের সর্বযুগের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।
বর্তমান এই নব্য জাহেলিয়াতের যুগে মুসলিম মিল্লাতের আমূল পরিবর্তন এবং ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি মুসলমান ইসলামের মূল আবেদন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে এ গ্রন্থ সহায়ক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে উপকৃত হবার তৌফিক দান করুন। আমিন।
ইসলামের মূল প্রাণশক্তি
ইসলামের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে আমরা সেখানে তার মূল প্রাণশক্তিকে সদা সক্রিয় দেখতে পাই।
সত্য দ্বীনকে যে ব্যক্তি জানবার চেষ্টা করবে এবং তার মেজাজ-প্রকৃতি ও ইতিহাসকে অধ্যয়ন করবে সে তার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এই প্রাণশক্তিকে সে ইসলামের আইন-কানুন ও নীতিমালার মধ্যে পূর্ণোদ্যমে কার্যকর দেখতে পাবে। এটা এত প্রভাবশালী যে, যে কোনো মানুষই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। কিন্তু কোনো গভীর অনুভূতি ও মৌলিক চিন্তাধারা যেমন সীমাবদ্ধ ভাষায় বর্ণণা করা যায় না তেমনি এই প্রাণশক্তিরও বর্ণনা দেয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ প্রাণশক্তি আবেগ ও উদ্দীপনায়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এবং রসম-রেওয়াজের মধ্যে সক্রিয় থাকে বটে কিন্তু তাকে ভাষার সীমিত পোষাকে আবৃত করা অত্যন্ত কঠিন।
এই প্রাণশক্তিই সেই সমুন্নত প্রোজ্জ্বল দিক চক্রবালের রূপরেখা নির্দেশ করে, যার অভিমুখে যাত্রা করার জন্য ইসলাম তার অনুসারীদেরকে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং সে জন্য শুধু অপরিহার্য্য্ কর্তব্য ও গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা পালনে ক্ষান্ত না হয়ে, স্বেচ্ছায় সানন্দে আরো বেশি চেষ্টা সাধনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছারপথ অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম আর সেখানে পৌঁছার পর তার ওপর অবিচল থাকা আরো বেশি দুঃসাধ্য। জৈবিক প্রেরণা ও চাহিদা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের প্রবল চাপ অধিকাংশ মানুষের পায়ে জিঞ্জির হয়ে জীবনের মহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছারপথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। আর যদিও-বা আবেগ উদ্দীপনার তীব্রতায় এর সংকল্পের প্রাবল্যে কখনো সেখানে পৌঁছেই যায় তাহলেও তার সেখানকার বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-আপদ অতিক্রম করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এ মহোন্নত স্তরের সাথে জড়িত রয়েছে জান-মাল এবং চিন্তা ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তন্মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর নিজ সত্তা, নিজ সমাজ ও মানব জাতি সম্পর্কে এবং সর্বোপরি তার স্রষ্টার ব্যাপারে যে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর। তার স্রষ্টা যে তার প্রতিটি ছোট বড় কাজ সর্বদা স্বচক্ষে অবলোকন করছেন, তার মনের গভীরে লুকানো গোপন কথা ও তার নিঃ শব্দ কার্যক্রম সম্পর্কেও কার্যক্রম সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল রয়েছেন- এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুভূতি জাগরুক রাখাই হচ্ছে স্রষ্টার সম্পর্কে তার গুরু দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করার জন্য ইসলাম তার বিবেককে করেছে সদা জাগ্রত এবং হুশিয়ার। আর তার চেতনা ও প্রজ্ঞাকে করেছে সুতীক্ষ্ণ ও সুতীব্র।
উচ্চতম লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রার এই জটিলতা এবং লক্ষ্যে উপনীত হবার পর তথায় স্থায়িত্বের এই দুঃসাধ্যতার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম একটা কবিসুলভ কল্পণা অথবা এমন একটা অতি মানবিক ধারণা যাকে জয় করার অভিযোগ পোষণ করা যায় কিন্তু যাকে স্পর্শ করা যায় না। আসল ব্যাপার তা নয়। যে সুমহান ও সুউচ্চ স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে উপনীত হওয়া সকল যুগের সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এটা হচ্ছে একটা লক্ষ্যসীমা মাত্র। মানুষ সর্বদা ওটা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাকবে সে জন্যে তার রূপরেখা নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে। এ চেষ্টা অতীতে যেমন করা হয়েছে, আজ এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকা উচিত। অতীতের মানব সমাজ এ লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা চালিয়েছে- কখনো লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে আবার কখনো বা দূরে সরে গেছে। এটা এমন একটা আদর্শ যাকে শুধু মানুষের বিবেক ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের ওপর গভীর আস্থা দ্বারাই জয় করা সম্ভব। এতে করে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অনাগত ভবিষ্যতে মানুষ সম্পর্কে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। এই সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যের পূর্বেই একটি সুবিশাল প্রান্তর রয়েছে। চেষ্টা সাধনা ও সাফল্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভব সে মাপকাঠির জন্য এ বিশাল প্রন্তর যথেষ্ট। আল্লাহর একটি স্থায়ী নীতি এই যে, তিনি কোনো ব্যাক্তিকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি চেষ্টার জন্য বাধ্য করেন না।
“আল্লাহ্ কোনো মানুষকে তার ক্ষমতার চাইতে বেশি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন না।” (সূরা বাকারা-শেষ আয়াত) ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতি এতো ইনসাফ প্রিয় ও মধ্যমপন্থি যে, সে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে শুধুমাত্র অবশ্য করণীয় কার্যসমূহ গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হয়। কারণঃ
“প্রত্যেকের কাজের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।” বস্তুত অবশ্য করণীয় হিসেবে যে সব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জীবনের সাফল্যের জন্য সেটাই যথেষ্ট। এরপরে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবার জন্য পথ সর্বদা উম্মুক্ত রয়েছে এবং সেদিকে অগ্রসর হবার জন্য উদাত্ত আহবানে ইসলাম সদা সোচ্চার রয়েছে।
যে প্রাণশক্তির কথা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি, তা ইসলামের সমাজ ও সভ্যতাকে বাস্তব রূপদানে পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে ইসলাম শুধু একটা বিশ্বাসের নাম ছিল, তা ব্যাক্তিসমূহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখন আর ইসলাম শুধু মতবাদ ও মতাদর্শের নাম নয় - ওটা নিছক ওয়াজ-নছিহত ও হেদায়েত কিংবা অলীক কল্পনা সমূহের সমষ্টিও মাত্র নয়। ওটা এখন জীবন্ত ও জাগ্রত মানব চরিত্রের রূপ ধারণ করেছে, বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীতে আত্নপ্রকাশ করেছে - সর্বোপরি তা এমন সব সমাজ সংস্থা ও সংস্কারমূলক কীর্তি স্থাপন করেছে- তা কেউ স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকর্ণে শ্রবণ করতে পারে। এসব সমাজ সংস্থা ও সংস্কার কীর্তি গোটা মানক জীবন ও ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুতঃ এ সব ইসলামের সেই মহিমান্বিত ‘প্রাণশক্তির’ই অবদান। এই প্রাণশক্তিই মৃতপ্রায় ব্যাক্তিসমূহের জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। তাতে এক নব চেতনা ও নতুন জীবনী শক্তির সঞ্চার করেছিল।
বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসের সূচনা যুগে এবং তার পরবর্তী যুগে বিস্ময়কর ব্যাক্তি সমূহের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং যাদের জীবনের আলোড়ল সৃষ্টিকারী গৌরবগাথা ইসলামের ইতিহাসে সুরক্ষিত রয়েছে তাদের সম্পর্কে এটাই হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা। যে অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনাবলী শুধু উচ্চতর চিন্তার সৃষ্ট রূপকথার মত মনে হয়, তারও রহস্য এই।
আত্মার পবিত্রতা, বিবেকের নির্ভীকতা, অভাবনীয় ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কোরবানী, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের মরণপণ সংকল্প, চিন্তা ও আত্মার অসাধারণ ও অচিন্তনীয় উচ্চতা এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগের অসামান্য কৃতিত্ব যা পুরোপুরি ভাবে বর্ণনা করা ইতিহাসেরও ক্ষমতা বহির্ভূত-এ সব কিছু ইসলামের এই বিপ্লবী প্রাণশক্তিরই অবদান।
ইতিহাসের পাতায় যে সব অসাধারণ কীর্তি ও ঘটনাবলী ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তার সাথে ইসলামের বিপ্লবী প্রাণশক্তির একটা সুগভীর সম্পর্ক আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। মূলতঃ ইসলামের ইতিহাসে যে শক্তির প্রকাশ দেখা যায় এই অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই তার মূল উৎস।
এ কীর্তি সমূহকে যদি আমরা উক্ত প্রাণশক্তি থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে যাই তাহলে আমাদের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকবে। এই ভ্রান্ত অধ্যয়নের ফলে জীবন ও জগতের ওপর সক্রিয় ভাবে প্রভাবশীল শক্তিসমূহ সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হতে বাধ্য হব। এর ফল দাড়াবে এই যে, প্রত্যেক গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিদের গৌরব ও সম্মানের উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা তার ব্যক্তিগত মাহাত্মকেই প্রাধান্য দেব এবং এ সবের সর্বপ্রথম উদ্দীপক ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কার্যকরণ উক্ত ‘প্রাণশক্তি’কে অগ্রাহ্য করবো। অথচ এই প্রাণশক্তিই সেই মহান ব্যক্তিদের বিবেক ও মনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, আর এরই বলে বলিয়ান হয়ে তারা ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল এবং ঘটনা স্রোতকে নিজেদের ইস্পিত স্রোতে প্রবাহিত করেছিল। এর পর তারা ইতিহাসকে জীবনের এক উদ্দাম, উচ্ছল ও গতিবান স্রোতধারার নিকট সোপর্দ করেছিল। আর সেই স্রোতধারার ওপর ভর করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সব অবিস্মরণীয় বিপ্লবাত্মক কীর্তি।
আমরা যদি গৌরবদীপ্ত মহৎ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব এবং তাদের কীর্তি সমুহের প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে এই বিপ্লবী প্রাণশক্তির অবদান বলে অবিহিত করি তা’হলে সেটা অত্যুক্তি হবে না। আসলে এই প্রাণশক্তি একটা অতীন্দ্রিয় প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা যে সব কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের সাথে এসে মিলিত হয়েছে তা বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন শক্তি হলেও মূলতঃ তা-সবই অতীন্দ্রিয় শক্তি। এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিত্ব উক্ত অতীন্দ্রিয় প্রেরণাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কতদুর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে সেটাই হচ্ছে তার মহত্বের মাপকাঠি। এখন যদি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তকে উক্ত যোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তর বলে মনে করা হয় তা হলে সেটা বিচিত্র কি? আসলে তাঁর সত্তাই অতীন্দ্রিয় প্রেরণাকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করেছিল এবং সারা জীবন ব্যাপী সেই সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।
নবুয়তের স্তরের পর উচ্চ মর্যাদার বহু স্তর রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীরা এবং তাদের পরবর্তী অনুসারীরা এই সব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এই মহান দ্বীনের প্রাণশক্তিকে যে ব্যক্তি যতদূর গ্রহণ করতে পেরেছে, সে সেই অনুযায়ী উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। বস্তুতঃ অত্যন্ত ব্যাপক অধ্যয়নের পরই আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে, এই প্রেরণা মানবাত্মাগুলোকে কতদূর প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে- কিভাবে তাদের ঘুমন্ত প্রাণকে জাগিয়ে তুলেছে- কর্মচঞ্চল ও কর্মক্ষম করে তুলেছে- অপূর্ব ও আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্তসমূহ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সর্বশেষ গোটা মানবেতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে।
এই প্রেরণা ও প্রাণশক্তির প্রভাব আমরা ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা এবং দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনা- উভয়ের মধ্যেই দেখতে পাই। জানা কথা যে, আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের পরিমাণ ইঞ্চি-গজে নির্ণয় করা সম্ভব নয় বরং তার সম্পর্ক হলো গুনাগুণের সাথে। এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় শুধু বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অনুষ্ঠিত ঘটনাপুঞ্জের মাধ্যমে।
আরব উপদ্বীপের মুষ্টিমেয় কতগুলো লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোম ও পারস্যের মত দুটো বিশাল সাম্রাজ্যকে পদানত করে ফেলেছিল। গোটা মানবজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় বিজয়ের অন্য কোনো নজীর পেশ করতে পারবে না। কিন্তু এই গৌরবদীপ্ত ঘটনার গৌরব ও মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ম্লান হবে না যদি আমরা বলি যে কোরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের জবাবে বেলাল (রাঃ) নামক হাবসী ক্রীতদাস একাই যে ধৈর্য্যর পরিচয় দিয়েছিল তাতেও এই একই মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। কোরাইশরা হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)কে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য যে যাতনা দিয়েছিল তা মানুষ মাত্রেরই ধৈর্য ক্ষমতার বহির্ভূত। নীচ থেকে তাকে উত্তপ্ত বালি দগ্ধ করছিল, পেট ও বুকের ওপর পাথরের বোঝা চাপানো ছিল, প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, তদপুরি তাকে প্রচন্ড জোরে প্রহার করা হচ্ছিল। কিন্তু এই অসহনীয় নির্যাতনের মধ্যে তার মুখ দিয়ে যে কথা নিঃসৃত হয় তা ছিল ‘আহাদ’ ‘আহাদ’।
এ প্রেরণাই যখন কোনো পথচারী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তখন স্বৈরাচারী সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়েও সে কড়া কড়া স্পষ্ট কথা বলে এবং আল্লাহর রাহে কারো নিন্দা-সমালোচনাকে ভয় পায় না। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি খলিফায়ে রাশেদ যখন বিনয়, অল্পে তুষ্ট ও আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করেন তখন তার মধ্যেও একই প্রাণশক্তি কার্যকর দেখা যায়। উভয় ব্যক্তি একই উৎস থেকে শক্তি লাভ করেছেন আর সে উৎস হচ্ছে ইসলামের দুর্জয় ও বিপ্লবী প্রাণশক্তি।
রোম ও পারস্য বিজয় প্রসঙ্গে এ কথা বলা প্রয়োজন মনে হচ্ছে যে, এখানে ইসলামের বিজয় মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক মতাদর্শের বিজয় ছিল। এই মতাদর্শ মানুষের অন্তরাত্মাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ ঘটনা ইতিহাসের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণকে সমর্থন করে কেননা এখানে বস্তুগত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বস্তুগত বিশ্লেষণ দ্বারা এই অসাধারণ বিজয়ের হেতু নির্দেশ করা অসম্ভব। নিছক বস্তুগত শক্তি দ্বারা আরবরা অত বড় দু’টো সাম্রাজ্যকে পদানত করতে পারতো না।
সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম আরবদের চিন্তা ও কর্মে, উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে মনস্তাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে তার গুরুত্ব ঐসব দেশের বিজয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশী। এটা ইসলামের প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দেশ জয়ের ঘটনাবলীর চাইতে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। এ কথা সকলেরই জানা যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত ও ইন্তোকালের মাঝামাঝি সময়ে আরব উপদ্বীপে খোদ তাঁর আনীত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া স্বতন্ত্র কোন অর্থনৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়নি- তাই সেখানখার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন কোন মৌলিক পরিবর্তনও সাধিত হয়নি যা আরবদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যকলাপ ও সমাজ ব্যবস্থায় এত বড় বিপ্লব আনতে পারে। বস্তুতঃ এ সমস্ত কীর্তিকলাপ আসলে এই আধ্যাত্মিক মতাদর্শেরই সৃষ্টি।
এখানে আমাদের পক্ষ্যে এই বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। আমরা এর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করবো। এ দৃষ্টান্ত সে যুগের আরবদের একটি বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। এ বিবৃতিটি তারা ইসলামের শত্রুদের সামনে দিয়েছিলেন অথচ তারা এর একটি কথারও প্রতিবাদ করতে পারেননি। এ হচ্ছে আন্দোলনের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। কোরাইশদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করার জন্য মুসলমানরা হিজরত করে হাব্শায় চলে যান। হাব্শায় গিয়ে পাছে তারা শক্তি অর্জন করে ফেলে এই আশংকায় কোরাইশরা রাজা নাজ্জাশীর নিকট দু’জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মোহাজেরদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করানো ব্যবস্থা করা। এই প্রতিনিধিদ্বয় চিল আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়া। তারা গিয়ে বললো,
‘জাহাপনা! আমাদের দেশের কতিপয় অবুঝ তরুণ আপনার দেশে এসে বসবাস করছে। তারা নিজ জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে এক মনগড়া ধর্ম এনেছে- যা আমাদের জন্যও নতুন- আপনার জন্যও নতুন।ওদের বাপ-চাচা, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং আমাদের জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাদেরকে আপনার কাছে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ওদেরকে দেশে ফেরত পাঠাবেন। সে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই তরুণদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তরুণরা যে সব জিনিষের ওপর আপত্তি তোলে এবং যেগুলোকে মন্দ বলে, তা আমাদের নেতারাই ভাল বোঝেন।‘
এই কথা শুনে নাজ্জাশী মুসলিম তরুণদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যার জন্য তোমরা নিজ জাতিকে পরিত্যাগ করে এসেছ এবং আমার ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করনি সে ধর্মটা কি?”
উত্তরে আবু তালেবের পুত্র জাফর (রাঃ) বললেন,
“হে বাদশাহ! আমরা চরম মুর্খতা ও অজ্ঞতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত দেহ আহার করতাম ও ব্যভিচার করতাম। আত্মীয়তার বন্ধনের অবমাননা করা ও প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করা আমাদের নিত্যকার অভ্যাস ছিল। আমাদের মধ্যে যারা সবল ছিল তারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার ও শোষণ চালাতো। এমনি অবস্থায় আমাদেরই একজনকে আল্লাহ নবী বানিয়ে আমাদের নিকট প্রেরণ করলেন। আমরা তার বংশ-মর্যাদা, তার সততা-সত্যবাদীতা, তার বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পের্কে ওয়াকিফহাল। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি আহবান করেন, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা ও কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত-উপাসনা ও আনুগত্য করার শিক্ষা দেন। আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রতিমা ও প্রস্তর মূর্তির পূজা করতাম, তিনি সেগুলোর পূজা ছেড়ে দিতে বলেন। তিনি সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অশ্লীল ও অশালীন কার্যকলাপ, মিথ্যাবাদিতা, ইয়াতিমের ধন আত্মসাৎ ও সতী নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর এবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে, যাকাত দিতে ও রোজা রাখতেও নির্দেশ দিয়েছেন.....।”
কোরাইশদের দু’জন প্রতিনিধিই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিল আমর ইবনুল আস- বাকপটুতা ও কুটনৈতিক দক্ষতায় যার জুড়ি ছিলনা। কিন্তু জাফর (রাঃ) প্রাগৈসলামিক আরবের পরিস্থিতির যে ছবি এঁকেছেন এবং রাসুলুল্লাহ’র আনীত জীবন-বিধানের যে পরিচয় পেশ করেছেন দু’জনের কেউ তার প্রতিবাদ করেনি। এটা প্রমাণ করেছে যে আরবের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।
এ হচ্ছে শুধু আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য। আধুনিক যুগের একজন অমুসলিম সে সময়কার সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে এ ধরনেরই একটি সাক্ষ্য দিয়েছেন। জে. এইচ. ডেনিসন (J.H. Denison) তার পুস্তকে সভ্যতার ভিত্তি হিসাবে ভাবাবেগ-এ (Emotion as the basis of civilization)লিখেছেন,
“পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য জগত নৈরাজ্যের এক সাংঘাতিক বিপজ্জনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছেল। এরূপ মনে হচ্ছিল যে, চার হাজার বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনার ফলে গড়ে ওঠা বিরাট সভ্যতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে চাচ্ছে এবং মানবতা অসভ্যতা ও বর্বরতার আদিম যুগে ফিরে যেতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। গোত্রে গোত্রে ভয়াবহ দাংগা ও কোন্দল লেগে ছিল। কোন আইন-শৃংখলার পরিবর্তে বিভেদ ও বিশৃংখলার জন্ম দিচ্ছিল। যেন একটি বিরাট বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ডালপালা সমগ্র পৃথিবীকে নিজের ছায়াতলে আবৃত করতে চায়। কিন্তু ভেতর থেকে তার কান্ডকে মূল পর্যন্ত এমনভাবে ঘুনে খেয়ে দিয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে বৃক্ষটি ভুমিস্মাৎ হতে পারে। তখনকার সভ্যতা ঠিক এমনি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল। এহেন সর্বাত্মক ধ্বংসের চিহ্ন যখন পরিস্ফুট ঠিক তখনি সেই ব্যক্তি জন্মলাভ করলেন যিনি সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবব্ধ করলেন।” [মওলানা মুহাম্মদ আলী প্রণীত ও ওস্তাদ আহমদ জাওয়াদুছাছানুহার কর্তৃক আরবীতে অনুদিত Islam and New World order থেকে গৃহীত। ] যাহোক আমরা এখন এই ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করবো।
বিবেকের সচেতনতার দৃষ্টান্ত
দৃষ্টান্তগুলো পেশ করার আগে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ইসলামের ইস্পিত বিবেকের ওপর আলোকপাতকারী কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। কেননা এই বিবেকের ওপরই ইসলামের গোটা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আগেই বলেছি যে, ইসলাম ব্যক্তির বিবেককে সদা জাগ্রত থাকার এবং তার চেতনা ও অনুভূতিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও তীব্র করার শিক্ষা দেয়। ইসলামের ইতিহাস এই বিবেকের সচেতনতা ও অনুভূতি তীব্রতার এত অধিক দৃষ্টান্ত সংরক্ষণ করেছে যে তা আমাদের এ সীমাবদ্ধ গ্রন্থে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখানে অনেকগুলো নমুনার স্থলে বিবিধ রকমের মাত্র কয়েকটি নমুনা পেশ করা যাচ্ছে।
হযরত বারিদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,
“মাগের ইবনে মালেক (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে হাজির হয়ে বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।” রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বললেন, “তোমার সুমতি হোক, যাও, আল্লাহর নিকট তওবা কর গিয়ে”। মাগের কিছুদুর পর্যন্ত চলে যায়- অতঃপর আবার রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে ফিরে এসে বলে, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন”। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আগের মতই জবাব দেন, তিনবার এরূপ হলো। চতুর্থবার রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বললেন, “আমি তোমাকে কিসের থেকে পবিত্র করবো?” মাগের বললো, “ব্যভিচার থেকে”। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তি মাতাল নয় তো?” সকলে জানালো যে সে মাতাল না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “ও কি মদ খেয়েছে”। এক ব্যক্তি গিয়ে মাগেরের মুখ শুঁকলো। দেখা গেল সে মদ খায়নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি সত্যই ব্যভিচার করেছ?” মাগের বলেলো, “হ্যাঁ”। এরপর তিঁনি শাস্তির হুকুম দিলেন এবং তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে শাস্তি কার্যকরী করা হলো”।
এ ঘটনার দুই তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “তোমরা মাগেরের জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর। সে এরূপ তওবা করেছে তা একটি গোটা জাতির মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে”।
এরপর তাঁর নিকট আজ্দ গোত্রের এক মহিলা এল। সে বললো, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন”। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “তোমার সুমতি হোক, যাও, আল্লাহর নিকট তওবা কর গিয়ে।? সে বললো,
“আপনি কি আমাকে মাগেরের মত ফিরিয়ে দিতে চান? আমি যে ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি”। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “তুমি কি সত্যই ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী?” সে বললো, “হ্যাঁ”। তিঁনি তাকে বললেন, “সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর”। অতঃপর তিনি উক্ত মহিলাকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত জনৈক আনসারীর তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর উক্ত আনসারী এসে রাসূলুল্লাহকে জানালেন যে, মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বললেন, “ আমি তাকে মৃত্যুদন্ড দেব আর শিশুকে দুধ পান করানোর কেউ থাকবে না- এমন কাজ আমি করবো না”। এতে এক আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শিশুর দুধ পান করানোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি”। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার ওপর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করলেন।
অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে বললেন, “তুমি যাও, সন্তান প্রসব করার পর এসো”। সন্তান প্রসবের পর সে এলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “যাও দুধ পান করাও গিয়ে। দুধ ছাড়লে তখন এসো”।এরপর শিশু দুধ ছেড়ে দিলে সে শিশুকে কোলে নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে এলো। শিশুর হাতে এক টুকরো রুটি ছিলো। সে বললো, “রাসূলে খোদা! আমি শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি। এখন সে রুটি ইত্যাদি খেতে শিখেছে”। তখন তিনি শিশুকে একজন মুসলমানের হাতে সোপর্দ করলেন এবং মহিলার মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দিলেন। তার বুক পর্যন্ত গভীর গর্ত খোড়া হলো, অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশে লোকেরা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেললো। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) একটু সামনে অগ্রসর হয়ে একটা পাথর তার মাথার নিক্ষেপ করলেন। এর দরুন খানিকটা রক্ত ছিটে এসে খালেদের মুখমন্ডলে লাগলো। এতে খালেদ মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে কটুক্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনতে পেয়ে বললেন, “খালেদ! মুখ সামলে কথা বলো। খোদার শপথ করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, অন্যায়ভাবে আদায়কারীও যদি সেরূপ তওবা করতো তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হতো”। অতঃপর তাঁর নির্দেশে মহিলার জানাজার নামাজ পড়া হলো এবং তাকে যথারীতি দাফন করা হলো। (মুসলিম, নাসায়ী)।
মাগের ইবনে মালেক ও উক্ত মহিলার চরিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। এদের কারো ব্যভিচারের কঠিন শাস্তির কথা অজানা ছিলনা। তাদেরকে কেউ পাপ কাজ করতে দেখেনি এবং তা প্রমাণ করার উপায়ও ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে পিড়াপিড়ি করলো্ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হৃদয়ের কোমলতা ও ইসলামের ন্যায়-নীতিমূলক প্রকৃতির তাগিদে সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের শাস্তি ক্ষমা করতে চাইলেন। কিন্তু তা এত বেশি পিড়াপিড়ি করলো যে তাদের মুক্তির সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মহিলাটি তো খানিকটা শক্ত কথাই বলে ফেললো যে, তিনি কি তাকে মাগেরের মত ফিরিয়ে দিতে চান? যেন সে ইসলামের বিধানের অকাট্য বিধানের ব্যাপারে শৈথিল্য ও উদারতা প্রদর্শনের অভিযোগ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওপর আরোপ করতে চাচ্ছে।
এসব কেন?.........তাদের এরূপ কথা বলা যে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন” তাদের মধ্যে এমন এক জীবন্ত ও উদগ্র প্রেরণার অস্তিস্ত নির্দেশ করে যা স্বয়ং বেঁচে থাকার আকাংখার চেয়েও প্রবল ও প্রাণবন্ত। এই প্রেরণা বিবেকের সচেতনতা ও অনুশোচনার তীব্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে পাপের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না তা থেকে পবিত্র হবার সুতীব্র বাসনা এবং অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে এই অনুভূতি থেকে সৃষ্ট প্রচন্ড লজ্জা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিল।
এই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম। অপরাধীর মনে সুতীব্র অনুশোচনা আর নবীর মনে প্রথমে দয়া ও সহানুভূতি এবং পরে অপরাধ প্রমানিত হওয়ার পর অপরাধীর তওবা ও স্বীকারোক্তির মাহাত্মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দন্ড কার্যকরী করার মত দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা এই ইসলামেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা ইসলাম তার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক ও তার গৌরব অম্লান থাকুক- এটাই ছিল অপরাধী ও শাসক উভয়ের নিকট সবচেয়ে কাম্য বস্তু।
দন্ড বিধির ক্ষেত্রে যখন মুসলিম বিবেকের এই অবস্থা তখন যে সব সামাজিক কাজে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে হয় তাতে তার ভূমিকা কিরূপ হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।
এ প্রসঙ্গে সিরিয়ার সেনাবাহীনির নেতৃত্ব থেকে খালেদ ইবনে ওলীদকে অপসারিত করে আবু ওবায়দাকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। খালিদ হলেন সেই গৌরবদীপ্ত সেনাপতি, যিনি তখন পর্যন্ত কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেননি। সৈনিকসুলভ স্বভাব ও দক্ষতা তার মেরু মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও তিনি ছিলেন একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। এহেন খালেদকে সেনাপতিত্ব থেকে অপসারিত করা হয় অথচ তিনি অসহযোগিতাও করেননি, বিদ্বেষও পোষণ করেননি। লজ্জা কিংবা সম্ভ্রমবোধ তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে উদ্বুদ্ধ করেনি। বিদ্রোহ করার কোন চিন্তার তো প্রশ্নই ওঠেনা। তিনি একাই যুদ্ধের ময়দানে সমান আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের বিজয়ের প্রেরণায় ও শাহাদাতের কামনায় উজ্জীবিত হয়ে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ সময়ে তিনি তার মনে কোনো প্রকার কু-চিন্তা ও কু-প্ররোচনার প্রশ্রয় দেননি। কেননা সচেতন মুসলিম বিবেক এ ধরনের চিন্তার বহু উর্দ্ধে। এসব চিন্তার কোনই গুরুত্ব নেই তার কাছে।
ঘটনার অপর দিকটিও অর্থপূর্ণ। হযরত ওমরের খালেদকে অপসারিত করাও একই চেতনা ও প্রেরণা থেকে উদ্ভুত ছিল। তিনি হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে খালেদ ইবনে ওলিদের মধ্যে এমন কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করেন যা ওমরের বিবেককে প্রকম্পিত করে তোলে। একটি ছিল এই যে, খালেদ মালেক ইবনে নোয়াইরাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন এবং অব্যবহিত পরে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এর পর তিনি আবার অনুরূপ একটা ত্রুটি লক্ষ্য করেন। সেটা হচ্ছে এই যে, মুসাইলেমায়ে কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেদিন বারশত শীর্ষস্থানীয় সাহাবী শহীদ হন, তার অব্যবহিত পরের দিন প্রত্যুষে খলেদ মাজ্জায়ার মেয়ে বিয়ে করেন।
এসব কার্যকলাপের সামনে যা আমার ধারণা ত্রুটিপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল খলিফা খালেদের বীরত্বের এবং যুদ্ধ জয়ের কোনোই গুরুত্ব দেননি। নিঃসন্দেহে খালেদ সবচেয়ে বড় সেনাপতি ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যুদ্ধ জয় করেছিলেন। তদুপরি মুসলিম জাতি সিরিয়া ও ইরাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের মুখোমুখি ছিল। সেখানে খালেদের মত অপরাজেয় সেনাপতির সমর দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু খালেদের মারাত্মক ত্রুটিসমূহ ওমর (রাঃ) এর বিবেকে যে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার সৃস্টি করেছিল, খালেদের এই সব গুণাগুণের কোনোটাই তা দমন করতে সক্ষম হয়নি। এর কোনটাই খালেদকে সেনাপতিত্ব থেকে এবং পরে খোদ সেনাবাহিনী থেকেও অপসারিত করার স্বপক্ষে তাঁর অভিমতকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। আরো একটি কারণ ছিল এই যে, খালেদ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে দায়িত্ব পালন করতেন আর এটা ছিল হযরত ওমরের মেজাজের পরিপন্থি। তাঁর দায়িত্ববোধ তাঁকে খুটিনাটি ব্যাপারেও নজর রাখতে হস্তক্ষেপ করতে উদ্বুদ্ধ করতো।(সাদেক উরজুন কৃত গ্রন্থ ‘খালেদ ইবনে ওলিদ’ থেকে)।
কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, খালেদ যদি এত বড় ভুল করে থাকেন, তাহলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? আসল ব্যাপার এই যে, খালেদ বিন ওলিদ সম্পর্কে হযরত আবু বকরের মতামত ওমরের মত গুরুতর ছিলনা। তিনি মনে করতেন যে, খালেদের বুদ্ধির ভুল হয়েছে এবং তিনি পরিকল্পিতভাবে কোন ত্রুটি বা গুনাহর কাজ করেননি। এ কারনে তিনি তার ওপর রুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় ঘটনাটিকে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ঘোর আপত্তির দৃষ্টিতে দেখেন এবং তিনি এক ক্রোধাপ্তি চিঠি লিখে পাঠান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খালেদের ভুল-ভ্রান্তিকে তিনি ক্ষমার যোগ্য মনে করতেন এবং তা শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেও দেন।
এই যুগে মুসলিম গণ-বিবেক যে সু-উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, তার সাথে ঘটনার উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু ডাঃ হাইকেলের মত ব্যক্তি খালেদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও ওমরের নীতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমাকে রীতিমত বিস্মিত করেছে। হাইকেলের এই ব্যাখ্যা ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই। অবশ্য এটা এ যুগের নোংরা রাজনীতির সাথে যথার্থভাবে সংগতিশীল। ‘আস-সিদ্দিকু আবু বকর’ নামক গ্রন্থের ১৫০ থেকে ১৫২ পৃষ্ঠায় ডাঃ হাইকেল লিখেছেনঃ
“মালেক ইবনে নোয়াইরার ব্যাপারে আবু বকর ও ওমরের মধ্যে মতভেদ কত দুর গিয়ে পৌছেছিল তা পাঠক নিষ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন্ তার দু’জনেই যে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন, সেটা সন্দেহাতীত ব্যাপার। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, খালেদের ভুল কি একজনের নিকট অতীব বিরাট এবং অপর জনের নিকট অতীব ক্ষুদ্র ছিল, না ব্যাপক বিদ্রোহ ও ধর্ম ত্যাগের সমস্যা জর্জরিত আরব উপদ্বীপের মুসলিম জীবনের নাজুক পরিস্থিতিতে সঠিক নীতি নির্ধারণ নিয়েই আসল মতভেদের উদ্ভব হয়েছিল?”
আমার মতে আসল মতভেদ ছিল নীতি নির্ধারণ নিয়ে। উভয় খলিফার প্রকৃতিতে যে পার্থক্য ছিল সে অনুসারে এই মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ওমর (রাঃ) ছিলেন আপোষহীন ন্যায় বিচারের প্রতীক। তার দৃষ্টিতে খালেদ জনৈক মুসলমানের ওপর অবিচার করেছিলেন। তাই তিনি যাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ ন্যাক্কারজনক ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী কাজ করার সুযোগ না পান সে জন্য তাকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা প্রয়োজন ছিল। মালেকের ব্যাপারে খালেদের বুদ্ধি ও বিবেচনাই ভুল হয়েছে একথা মেনে নিয়ে তাকে ক্ষমা করা গেলেও- যদিও হযরত ওমর (রাঃ) তা মানতে পারতেন না- মালেকের স্ত্রী লায়লার সাথে অশালীন আচরণের শাস্তি না দেয়া কিছুতেই শোভন হতো না। [যদি সত্যিই হযরত ওমরের অভিমত এত কঠিন ও চরম ভাবাপন্ন হতো তাহলে নিজের খেলাফতকালে তাকে অবশ্যিই ব্যাভিচারের শাস্তি দিতেন-গ্রন্থকার।] ‘তিনি একজন অজেয় সেনাপতি’ ‘তিনি খোদার তলোয়ার’ এ সব কথা তাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য যথেষ্ট হতো না। কেননা তার মানে দাঁড়াতো খালেদের মত লোকদের জন্য হারামকে হালাল করে দেয়া। আর এরূপ করা হলে মুসলমানদের সামনে আল্লাহর বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিকৃষ্টতর নজীর স্থাপন করা হতো। নিজের এই মতামতের কারণে ওমর (রাঃ) বার বার আবু বকর (রাঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) খালেদকে (রাঃ) ডেকে তার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।
অপরদিকে আবু বকরের (রাঃ) দৃষ্টিতে পরিস্থিতি এত বেশি নাজুক ছিল যে, এ ধরনের ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না। সে সময়ে গোটা দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আরবের চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমনি পরিস্থিতিতে ভুলবশতঃ কিংবা ইচ্ছাবশতঃ এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করার কি গুরুত্ব থাকতে পারে? যে সেনাপতিকে ত্রুটিপূর্ণ কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল তিনি সেই ভয়াবহ বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম ছিলেন। কোন স্ত্রীকে ইদ্দতের পূর্বে বিয়ে করা আরবদের প্রচলিত আদত-অভ্যাসের পরিপন্থি ছিল না, বিশেষতঃ কোনো বিজয়ী সেনাপতির পক্ষে। কারণ যুদ্ধের কারণেই সে যুদ্ধবন্দী মেয়েদের মালিকানা অধিকার লাভ করে থাকে। [ইসলামী শরিয়তের ক খ-ও জানে না - এমন লোকের পক্ষে এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব। যদি সত্যি সত্যিই খালেদ কোন মুসলমানের স্ত্রীর ওপর বলৎকার করে থাকেন তাহলে তার ওপর ব্যাভিচারের দন্ড কার্যকরী করা অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া মালেক যখন মুসলমান তখন তার স্ত্রীকে বাঁদী বানানোর প্রশ্নই ওঠেনা।] খালেদের মত অসাধারণ মানুষের ব্যাপারে আইনের কড়াকড়ি আরোপ করা অপরিহার্য ছিলনা। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে যখন এমন কাজ রাস্ট্রের স্বার্থের বিরোধী ছিল এবং তার অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারতো। এ সময়ে মুসলমানদের জন্য খালেদের তরবারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যেদিন আবু বকর (রাঃ) তাকে ডেকে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন সেদিনই মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল খালেদের। খালেদের (রাঃ) অবস্থানস্থল আল-বাত্তাহের সন্নিকত এমামাতে মোসায়লেমা বনু হানিফার চল্লিশ হাজার নওজোয়ানকে নিয়ে যুদ্ধের সাজে সেজে ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ছিল সবচাইতে সাংঘাতিক বিদ্রোহ। মুসলমানদের সেনাপতিদের মধ্যে থেকে ইকরামা (রাঃ) কে সে আটক করে ফেলেছিল এবং তখন বিজয়ের সমস্ত আশা-আকাংখা খালেদের তরবারীর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। এমতাবস্থায় মালেক ইবনে নোয়াইরাকে হত্যা করার কারণে অথবা খালেদকে বিমুগ্ধকারিণী অপরূপ সুন্দরী লায়লার কারণে খালেদ (রাঃ)কে অপসারণ করা এবং মুসলিম বিহিনীকে মুসাইলেমার হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার অবকাশ সৃষ্টি করা কি করে উচিত হতো? এভাবে আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদে ফেলে দেয়া হতো নয় কি? খালেদ খোদার পতাকা ছিলেন-খোদার তরবারী ছিলেন- তাই আবু বকর (রাঃ) তাকে ডেকে নিয়ে শুধু তিরস্কার করে ক্ষান্ত হওয়া এবং তৎক্ষনাৎ এমামাতে গিয়ে মোসালেমার মোকাবেলা করতে নির্দেশ দেয়াই সবচেয়ে সংগত কর্মপন্থা বলে বিবেচনা করেছিলেন।
এই হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে খালেদ ইবনে ওলিদের ব্যাপারে আবু বকর ও ওমরের নীতির পার্থক্যের আসল চিত্র। বনি হানিফার মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার যখন ইকরামা (রাঃ) কে গ্রেফতার করে তখন আবু বকর (রাঃ) খালেদকে তার মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মদিনাবাসী এবং ওমরের মতের সমর্থকরা এতে করে বুঝতে পারবে যে- খালেদ ইসলামের দুর্যোগ মূহূর্তের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এ নির্দেশ দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, খালেদ হয় যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হবে- তখন সেটা হবে মালেক ও তার স্ত্রীর প্রতি অবিচারের চেয়ে উত্তম শাস্তি আর না হয় তিনি বিজয়ী হবেন এবং সে বিজয় তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হলেন এবং বিপুল গণিমতের সম্পদ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এত বড় বিপদ থেকে মুক্ত করলেন। সে বিপদের সামনে আল বাত্তাহে অবস্থানকালে তার পক্ষ থেকে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয় - সেটার কোন গুরুত্বই ছিলনা।
এই হচ্ছে ডাঃ হাইকেলের দৃষ্টিতে পরিস্থিতির রূপ। আমার দেখে বিস্ময় জাগে যে, এক ব্যক্তি কিভাবে তার কল্পনার ডানা মেলে ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে প্রবেশ করে এবং সেই জাগ্রত ও সচেতন বিবেক সমূহের ছায়তলে বসে লেখনি পরিচালনা করে। অথচ তার নিজের বিবেক ও মন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দানের ব্যাপারে আধুনিক জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উর্দ্ধে ওঠা তো দূরের কথা তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে ইসলামের মূল প্রাণশক্তি এবং সেই বিশেষ যুগের বাস্তব ইতিহাসের কোনই সম্পর্ক নেই। এটা তো বর্তমান যুগের রাজনীতি। এই রাজনীতির দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট লক্ষ্যের জন্য নিকৃষ্ট কর্মপন্থা ও উপায় উপকরনের আশ্রয় গ্রহণ সম্পূর্ণ বৈধ। এ রাজনীতি মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে গোলাম বানিয়ে দেয় আর একে উচ্চতর ‘ডিপ্লোমেসী’ এবং উচ্চাঙ্গের কর্মদক্ষতা ও কর্মকুশলতার নামে অভিহিত করে।
যে চিত্র ডাঃ হাইকেল তুলে ধরেছেন এবং যাকে তিনি একমাত্র বিশুদ্ধ চিত্র বলে দাবী করেছেন- তাতে হযরত আবু বকরের (রাঃ) ব্যক্তিত্বকে কত নীচ ও হীন করে দেখানো হয়েছে তা যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যাক্তি দেখতে পারে।
সৌভাগ্য যে, আজকের নিকৃষ্ট ও অধঃপতিত সমাজের মানুষ যে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখতে অভ্যস্ত আবু বকরের ব্যক্তিত্ত তার অনেক উর্দ্ধে। এ দূরবীক্ষণ দ্বারা মানবতার সেই সু-উন্নত স্তরকে পর্যবেক্ষণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ পর্যবেক্ষক যদি ইসলামী শরিয়তের সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে তাহলে ব্যাপার আরো ঘোলাটে হয়ে যায়।
স্বীয় পুস্তক ‘আল-ফারুক-উমর’-এ ডাঃ হাইকেল পুনরায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি খালেদকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে হযরত ওমরের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। সেখানেও পুনরায় তাকে আধুনিক অধঃপতিত সভ্যতা প্রভাবিত করেছে। যে দল-নেতার সামনে আপাতঃ কল্যাণ ও আঞ্চলিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কিছুর গুরুত্ব থাকে না-ইসলামের প্রাণশক্তি যার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়- সেই নেতার চরিত্রই লেখকের মন মানসে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ৯৯ ও ১০০ পৃঃ তিনি লিখেছেনঃ
“বুঝে আসে না যে, হযরত ওমর (রাঃ) খালেদের (রাঃ) অপসারণের মত বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত কেন নিলেন। অথচ সিরিয়ায় মুসলমানদের সমগ্র সামরিক শক্তি খালেদের অধীন ছিল। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সেটা ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ মুহুর্ত। তারা রোমক সৈন্যদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধও হচিছল না- আবার দু’পক্ষের কেউ কাউকে হার মানাতে পারছিল না। ইরাক থেকে খালেদের আগমনের পূর্বে যে পরিস্থিতি ছিল তার আগমনের পরও সে পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। উভয় পক্ষ আক্রমন চালাবার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করছিল। খলিফার এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিল যে, খালেদকে পদচুত করলে মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়বে এবং পরিস্থিতি আরো অধিক বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ খালেদ যতক্ষনে না মুসলমানদের উক্ত বিপজ্জনক মুহূর্ত অতিক্রম করিয়ে না নেন ততক্ষণ খলিফার অপেক্ষা করাই উচিত ছিল এবং এরপর যা খুশী নির্দেশ তিনি জারী করতে পারতেন”।
“যুদ্ধের উত্থান-পতনে এ ব্যাপারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আবু ওবাইদা (রাঃ) খলিফার অসন্তোষ ও অমতকে অগ্রাহ্য করে এ সব ব্যাপারের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু ওমর ব্যাপারটা দেখেছেন অন্য দিক থেকে। তিনি যদি খালেদকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী রাখতেন তাহলে তার নীতি ক্ষুন্ন হতো এবং ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়তো। জানা কথা যে, যুদ্ধে মুসলমানদের হয় জয় হতো না হয় পরাজয় হতো। যদি পরাজয় হতো তাহলে খালেদকে পদচ্যুত করেও লাভ হতো না। কিন্তু যদি খালেদের নেতৃত্বে মুসলমানরা জয় লাভ করতো তাহলে হযরত ওমরের পক্ষে তাকে বিজয় ও সাফল্যের গৌরব থেকে নীচে নামিয়ে পদচ্যুত করা সম্ভব হতো না। এরূপ করা অত্যন্ত ভুল কাজ হতো।
“ওমর (রাঃ) মোটের ওপর চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, সিরিয়ায় অথবা অন্য কোথাও খালেদকে সেনাপতি পদে বহাল রাখবেন না। এ কারণেই তিনি পদচ্যুতির হুকুম জারী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন। এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তার যুক্তি এ ছিল যে খালেদ (রাঃ) হযরত আবু বকররের (রাঃ) নির্দেশাবলী যথাযতরূপে পালন করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল, তাই কেউ ওমরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারতো না। তিনি যা ভাল বুঝেছেন তা-ই করেছেন। খালেদও এমন পর্যায়ে ছিলেন যে, তাকে পদচ্যুতকারীরর ওপর কোনো অবিচারের অভিযোগ আরোপ করা যেতো না”।
এ হলো বিংশ শতাব্দীর হাইকেল ‘পাশা’র চিন্তাধারা- যা তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর ওমর ফারুকের ওপর চাপাতে চাচ্ছেন। ইতিপূর্বে তিনি হযরত আবু বকরের ব্যাপারেও এরূপ করেছেন। যার আত্মা আবু বকর (রাঃ) ও ওমরের আত্মাকে স্পর্শও করতে পারেনি, যে ইসলামের পরিবেশে কিছুদিন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও এক মুহুর্তের জন্যও বিংশ শতাব্দির মলিনতা ও কদর্যতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি- সেরূপ লোকের পক্ষেই এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করা সম্ভব। আধুনিক সভ্যতার নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বিবেক, সত্যবাদিতা ও ধর্ম- সব কিছুকে উপেক্ষাকারী সুবিধাবাদ যে লেখকের পিছু ছাড়েনি- তা অত্যন্ত স্পষ্ট। অধিকন্তু এ যুগের মিথ্যাচার ও প্রতারণা দর্শন তার চিন্তা ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
জিজ্ঞাস্য এই যে, হাইকেল সাহেব ওমর ফারুক (রাঃ) কে কি ভেবেছেন? যদি পরিস্থিতি অন্যরকম হতো এবং এরূপ সুযোগ না থাকতো তাহলে কি ওমর (রাঃ) খালেদ (রাঃ)কে ছেড়ে দিতেন? অথচ স্বয়ং হাইকেল পাশার বর্ণনা অনুসারে হযরত ওমরের বিবেক এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে, মালেক ইবনে নোয়াইরার ব্যাপারে এবং আল্লাহ ও তার দ্বীনের ব্যাপারে খালেদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল।
যে ওমর (রাঃ) পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারতেন কিন্তু নিজে নীতিচ্যুত হতেন না, যে ওমরের ঈমান ঝড়ের গতিবেগ ঘুরিয়ে দিত, কিন্তু নিজে বিচলিত হতেন না- সেই ওমর (রাঃ) কি করে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন?
এ ধরনের কাজ করতো উমাইয়া ও আব্বাসীয় বাদশাহরা। মানুষ তাদের এসব কাজকে ‘ডিপ্লোমেসী’ ও ‘চতুরতা’ বলে আখ্যায়িত করতো। কিন্তু ওমর (রাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এসব থেকে বহু উর্ধ্বে। এখন কেউ যদি তাঁদের সম্পর্কেও এই রূপ চিন্তা করা শুরু করে থাকেন তাহলে সেটা হচ্ছে বর্তমান যুগের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি ও নিম্ন মানের মূল্যবোধের প্রভাব।
আমি এই চিন্তাধারার উপস্থাপনা এবং তার ভ্রান্তি স্পষ্ট করার ব্যাপারে খানিকটা বিস্তারিত বিবরণের সাহায্য নিয়েছি। কারণ এ ছাড়া আধুনিক যুগের ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তি থেকে আক্রান্ত মন-মানসকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রাণশক্তির চরমোৎকর্ষের যুগে যে চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কেউ কেউ সেই চিন্তা পদ্ধতির ব্যাখ্যা বর্তমান জড়বাদী চিন্তা-পদ্ধতির আলোকে দিতে চান। অথচ আজকের এ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত তখনকার আত্মিক চেতনা ও জাগরণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। আমি এই বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যার অপনোদন করতে চাই। কারণ মানবীয় বিবেক এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের এ দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
অবশ্য আমি প্রথম শতকের লোকদের কোনো কৃত্রিম পোষাকে আবৃত করে পেশ করতে চাই না অথবা তাদেরকে যাবতীয় মানব-সুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত দেখাতেও ইচ্ছুক নই। আমি শুধু চাই মানুষ পুনরায় বিবেকের ওপর নির্ভর করতে শিখুক। এই উদ্দেশ্যে আমি মুসলমানদের জীবনের সঠিক পরিচয় পেশ করতে চাই। এতে করে যেসব বিবেকের মধ্যে উক্ত উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তারা সেই পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।
এখন আমি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম শতকের মুসলমানরা যেরূপ বিবেক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত পুনরায় পেশ করবো।
একদিন দেখা গেল, আমিরু মুমেনীন ওমর ইবনুল খাত্তার (রাঃ) পানির মশক ঘাড়ে করে নিয়ে আসছেন। তার পুত্র বিক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি এরূপ করছেন কেন?” তিনি জবাব দেন, “আমার মন অহংকার ও আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়েছিল, তাই ওকে আমি অপদস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি”। চেতনার তীব্রতা দেখুন! এই ব্যক্তির মনের কোনো এক কোনে ক্ষণিকের জন্য খেলাফত, রাজ্য জয় এবং অনাগত কালের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সামান্যতম আত্মম্ভরিতা মাথা তুলেছিল। তিনি এটা বরদাশত করলেন না এবং তৎক্ষণাৎ সকলের সামনে প্রবৃত্তিকে জব্দ করা শুরু করে দিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ভেবে দেখলেন না যে, তিনি কত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক, যার মধ্যে আরব উপদ্বীপ ছাড়াও রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ দেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
আর একদিন দেখা গেল, আলী ইবনে তালেব প্রচন্ড শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। তার গায়ে শীত নিবারনের উপযুক্ত পোষাক নেই। ‘বায়তুল মাল’ তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তাঁর বিবেক সচেতনতা তাঁকে একটি কপর্দকও স্পর্শ করতে দিচ্ছে না।
আবু ওবায়দা (রাঃ) ‘আমওয়াসে’ নিজ বাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেছেন। ‘আমওয়াসে’ ভয়াবহ মহামারী দেখা দিল। হযরত ওমর (রাঃ) শংকিত হলেন পাছে ‘আমিনুল উম্মতের’(আবু ওবায়দা) কোনো অনিষ্ট না হয়। তিনি তাঁকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চিঠি লিখে নিজের কাছে ডাকেন। চিঠিতে তিনি লিখেনঃ
“সালাম বাদ, একটা জরুরী কাজে তোমার আমার সামনা-সামনি কথা বলা প্রয়োজন। আমি খুব জোর দিয়ে বলছি, এই চিঠি পড়ার পর চিঠি রাখার আগেই আমার কাছে রওয়ানা হও”। আবু ওবায়দা (রাঃ) চিঠি পড়া মাত্রই আসল উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই খলিফা একটা পথ খুঁজে বের করেছেন। সংগে সংগে বলে ওঠেনঃ “আল্লাহ! আমিরুল মুমেনীনকে ক্ষমা করুন”। তিনি হযরত ওমরকে চিঠির নিম্নরূপ জবাব লিখে পাঠানঃ
“আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে দিয়ে আপনার প্রয়োজনটা কি, এ সময়ে মুসলমানদের গোটা বাহিনী আমার সাথে রয়েছে। আমি মুসলিম জোয়ানদের নিকট থেকে পৃথক হতে চাই না। আল্লাহ যতক্ষণ আমার ও তাদের ভাগ্যের লিখন পূর্ণ না করেন ততক্ষণ আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে পারি না। আমিরুল মুমেনীন, এই সব কারণে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমাকে এই নির্দেশ পালনে বাধ্য করবেন না। আমাকে আমার জোয়ানদের সাথে থাকতে দিন”।
হযরত ওমর (রাঃ) চিঠিটা পড়ে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করেন, “আবু ওবায়দা কি ইন্তেকাল করেছেন?” তিনি বাষ্পরুদ্ধ কন্ঠে জবাব দেন, “না”।
বস্তুতঃ তাকদীরের ওপর অটল বিশ্বাস এবং আল্লাহর পথের প্রতিটি সৈনিকের নিজের সমান মর্যাদা দান- এ দুটো কার্যকারণই আবু ওবায়দা (রাঃ) কে মৃত্যুর মুখে অবিচল থাকতে বাধ্য করেছিল।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুয়াজ্জিন হজরত বেলাল বিন রাবাহের ইসলামী ভাই আবু রুয়াইহা খাশ্য়ামী তার বিয়ের জন্য ইয়ামনের কতিপয় লোকের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য বেলালের কাছে আবদার ধরেন। হজরত বেলাল সেই লোকদেরকে বলেন, “আমি বেলাল বিন রাবাহ। আর এ হচ্ছে আমার ভাই আবু রুয়াইহা। এর ধর্ম ও চরিত্র দুটোই খারাপ। তোমাদের ইচ্ছা হয় তার সাথে আত্মীয়তা কর, না হয় করো না”।
একদম পরিস্কার কথা বলে দেন। নিজের ভাই এর দোষ গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেননি।
তিনি একটা বিয়ের কথা-বার্তার মাধ্যম হচ্ছেন- এ অনুভূতি তাঁকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি থেকে বিস্মৃত করে দেয়নি। ইয়ামনবাসীরা তাঁর সত্যবাদীতায় মুগ্ধ হয়ে সম্বন্ধ স্থাপনে রাজী হন। এত বড় সত্যবাদী তাদের মেয়ের জন্য বিয়ের পয়গাম এনেছে এটুকুই তাদের জন্য যথেষ্ট গৌরবের ব্যাপার ছিল।
ইমাম আবু হানিফার চরিত্র লক্ষ্যনীয়ঃ তিনি নিজের শরীক ব্যবসায়ী হাফ্স ইবনে আবদুর রহমানের কাছে কিছু কাপড় বিক্রীর জন্য পাঠান। তিনি তাঁকে বলে দেন যে, একখানা কাপড়ে কিছু খুঁত আছে তা ক্রেতাকে জানিয়ে দিতে হবে। হাফ্স সেই কাপড় বিক্রী করে দেন কিন্তু খুঁতের কথা বলতে ভুলে যান। খুঁতপূর্ণ কাপড়ের বিনিময়ে তিনি পুরো দাম আদায় করেন। এই চালানের দাম ছিল ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম। আবু হানিফা (রঃ) তাঁর শরীককে ক্রেতার সন্ধান নিতে বলেন কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর তিনি তাঁর শরীক থেকে পৃথক হন এবং গোটা চালানের দাম আল্লাহর পথে দান করে দেন। নিজের পবিত্র সম্পত্তি সাথে তিনি সেটা মিশাতেও চাননি। [আবদুল হালিম আল-জুনদীর গ্রন্থ- ‘আবু হানিফা বাতলুল হুররিয়াতি অত্-তাছামুহি ফিল ইসলাম’ থেকে গৃহীত।]
বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত ইমাম ইউনুছ বিন ওবায়েদের নিকট বিভিন্ন মূল্যের কাপড় বিক্রীর জন্য রক্ষিত ছিল। এক রকমের কাপড়ের প্রতি জোড়ার দাম ছিল চারশো দিরহাম। অপর এক ধরনের কাপড়ের প্রতি জোড়ার দাম ছিল দু’শো দিরহাম। তিনি নিজের ভ্রাতুস্পুত্রকে দোকানে রেখে নামাজ পড়তে যান। এ সময় একজন লোক আসে এবং চারশো দিরহাম মূল্যের জোড়া চায়। ছেলেটি তাকে দু’শো দিরহাম মূল্যের জোড়া দেখায়। সেটা তার পছন্দ হয় এবং সন্তুষ্ট চিত্তে খরিদ করে নিয়ে যায়। সে উক্ত কাপড় নিয়ে বাড়ী যাওয়ার সময় পথে ইউনুছের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ইউনুছ তার কাপড় চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে ওটা কত দামে খরিদ করেছে? সে জবাব দেয় যে, চারশো দিরহাম। তিনি বলেন, এটা তো দু’শো দিরহাম মূল্যের কাপড়। যাও ওটা ফেরত দিয়ে এস। সে জবাব দিল, এ কাপড় আমাদের দেশে পাঁচশো দিরহাম মূল্যে পাওয়া যায়। তাই আমি ওটা সন্তুষ্ট চিত্তেই খরিদ করেছি।ইউনুস বললেন, তোমাকে ফেরত নিতেই হবে। কারণ ইসলামের ব্যাপারে হীত কামনার চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে না। এই বলে তিনি তাকে দোকানে নিয়ে যান এবং দু’শো দিরহাম ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই বলে তিরস্কার করেনঃ “তোর লজ্জা করলো না? তোর মনে খোদার ভয়ের সৃষ্টি হলো না? শতকরা একশো ভাগ লাভ করিস্ আর মুসলমানদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিস না?” ছেলেটি শপথ করে বললো যে, ক্রেতা খুশী হয়েই কাপড় কিনেছিল। এতে তিনি বললেন, “তুই নিজের জন্য যা পছন্দ করিস- তা অপরের জন্যও পছন্দ করতে হয়, একথা ভুলে গেলি কেন?”
মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার ভৃত্য এক ব্যাক্তির নিকট পাঁচ দিরহাম দামের কাপড় দশ দিরহামে বিক্রী করে। তিনি জানতে পেরে সারাদিন উক্ত ক্রেতার সন্ধান করেন। শেষে তাকে পেয়ে বললেন, ভৃত্য ভুল করে তোমার কাছে পাচঁ দিরহামের কাপড় দশ দিরহামে বিক্রী করেছে। সে আশ্চর্য হয়ে বললো, “আমিতো খুশী হয়েই এ দাম দিয়েছি”। তিনি জবাব দিলেন, “তুমি হাজার খুশী হও। আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তা তোমার জন্যও পছন্দ করবো”। এই বলে তিনি তাকে পাঁচ দিরহাম ফিরিয়ে দেন। (আর রিসালাতুল খালেদাঃ আবদুর রহমান আজ্জাম)
এ তিনটি ঘটনার রহস্য উদঘাটনের সবচেয়ে শক্তিশালী চাবিকাঠি হচ্ছে ইউনুস ইবনে ওবায়েদের এই উক্তি যেঃ “তোর লজ্জা করলো না?” নিঃসন্দেহে নিজের বিবেকের কাছে লজ্জিত হওয়া ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়াই হচেছ এই সমস্ত ঘটনার পেছনে সক্রিয় একমাত্র শক্তি। মানুষের বিবেক, প্রকৃতি ও মন-মানস যখন ইসলামের প্রাণশক্তিকে গ্রহণ করে এবং সেই প্রাণশক্তি তার মেরু-মজ্জায় মিশে যায় তখন ইসলাম পূর্ণ শক্তি সহকারে তার মধ্যে এরূপ চরিত্রের সৃষ্টি করে।
এই কয়টি দৃষ্টান্ত ছাড়া আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু মানুষের বিবেকের পরিশুদ্ধির জন্য ইসলাম যে সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে, তার দিকে পথ-নির্দেশের জন্য এই দৃষ্টান্ত কয়টিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইসলাম মানুষের বিবেককে যাবতীয় বস্তুগত প্রয়োজন, সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং জানমাল ও পদ-মর্যাদার আকর্ষণ থেকে উর্ধ্বে তুলতে চায়। সে মানুষকে সদা সচেতন, বিবেকবান ও তীব্র অনুভূতি সহকারে জীবনের সকল দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে চায়।
সাম্যের উদাহরণ
ইসলাম মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ সাম্যের বাণী নিয়ে এসেছিল। যত মূল্যবোধ সাম্যের পথে অন্তরায় সৃ্ষ্টি করেছে তার শৃংখল থেকে সে মানুষকে মুক্ত করতে এসেছিল। এবার আমরা দেখতে চাই এই মতবাদকে বাস্তব জীবনে কিভাবে রূপায়িত করা হয়েছে।
সে সময়ে সারা দুনিয়ার দাস-শ্রেণী স্বাধীন মানব জাতি থেকে পৃথক একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বিদ্যমান ছিল। আরব উপদ্বীপেরও ছিল একই অবস্থা। এ ব্যাপারে আমরা যখন হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যাবলী বিবেচনা করি তখন দেখতে পাই যে তিনি নিজের ফুফাতো বোন এবং কোরাইশ বংশীয় হাশেমী গোত্রের মেয়ে জয়নবকে নিজের আজাদ করা গোলাম জায়েদের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ে একটা অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার, এতে উভয় পক্ষের সমতা অন্য সকল প্রশ্নের চাইতে গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।
মহানবী (সাঃ) ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো শক্তির পক্ষে এত বড় অসাধারণ কাজ করা সম্ভব ছিল না- এমন কি আজও মুসলিম জাহান ব্যতীত অন্য কোথাও সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসবৃত্তি বে-আইনী বটে কিন্তু কোনো নিগ্রোর পক্ষে কোন শ্বেতাংগিনীকে-তা সে যতই নিকৃষ্ট হোক- বিয়ে করা আইনানুগভাবে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, বরং কোনো নিগ্রোর পক্ষে বাসে বা অন্য কোন যানে-রেস্তোঁরায় থিয়েটারে অথবা অন্য কোন স্থানে কোন শ্বেতাঙ্গের পাশাপাশি উপবেশন করাও আজ পর্যন্ত নিষিদ্ধ।
হিজরতের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন তখন তার স্বাধীনকৃত গোলাম জায়েদ এবং তার চাচা হামজা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন, হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং খারেজা ইবনে জায়েদ ভাই ভাই বন্ধনে আবদ্ধ হন। খালেদ ইবনে রুয়াইছা খাশ্য়ানী এবং বিলাল ইবনে আবি রাবাহের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। এই ভ্রাতৃত্ব শুধু কথার মধ্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি- বরং রক্ত সম্পর্কের মত মজবুত ও পাকাপোক্ত সম্পর্কের রূপ ধারণ করে। জান-মাল ও জীবনের সকল ব্যাপারে তাদের মধ্যে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।
এরপরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জায়েদকে মুতা যুদ্ধে সেনাপতি বানিয়ে পাঠান। অতঃপর তার ছেলে উসামা (রাঃ)-কে রোমের যুদ্ধে এমন এক বাহিনীর সেনাপতি করেন-যার মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন মুহাজের ও আনসার। এই সেনাবাহিনীতে হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং ওমন (রাঃ)ও ছিলেন- যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকটতম সাথী ও উজীর এবং পরে পূর্ণ ঐক্যমত সহকারে খলিফা নির্বাচিত হন। উসামার নেতৃত্বে পরিচালিত এই সেনাবাহিনীতে রাসূলুল্লার (সাঃ) ঘনিষ্ট আত্মীয় সা’দ ইবনে আবি আক্কাসও ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মাতুল গোষ্ঠি-বনু জোহরা গোত্রের লোক। তাছাড়া কোরাইশদের যে সব ব্যক্তি নবুয়তের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন- তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। আল্লাহতায়ালা তাকে মাত্র সতের বছরে ইসলাম গ্রহণের তওফিক দেন। তিনি বিরাট বিত্তশালী ও মর্যাদা সম্পন্ন লোকি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ সমর-কুশলীও ছিলেন এবং সেই সাথে জেহাদী প্রেরণায়ও উদ্বুদ্ধ ছিলেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর হজরত আবু বকর (রাঃ) যখন উসামার বাহিনীকে পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিযুক্ত সেনাপতিকেও বহাল রাখেন। তিনি যখন সেনাপতিকে বিদায় দেয়ার জন্য মদিনার বাইরে আসেন- তখন উসামা সওয়ারীতে চড়ে যাচ্ছিলেন, আর খলিফাতুল মুসলেমীন চলছিলেন পায়ে হেঁটে। উসামা এতে অত্যন্ত কুন্ঠা বোধ করেন। নিজে সওয়ার হয়ে সওয়ারীতে চড়বেন, আর বৃদ্ধ খলিফা পায়ে হেঁটে চলবেন- এটা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাই উসামা বললেন, “খলিফাতুর রাসূল! আপনিও সওয়ারীতে আরোহন করুন-নইলে আমি নেমে আসবো”। খলিফা শপথ করে বলেন, “খোদার কছম! তুমি নীচে নেমনা। খোদার কছম! নীচে নেমনা। খোদার কছম! আমি সওয়ারীতে আরোহন করবো না। আমি কিছুক্ষণ আল্লাহর রাহে হেঁটে চললে আমার কোনোই ক্ষতি হবে না”। এরপর হজরত আবু বকরের (রাঃ) হঠাৎ মনে পড়ে যে, হজরত ওমরের তাঁর প্রয়োজন পড়তে পারে। অসুবিধা ছিল এই যে, ওমর (রাঃ) উসামার বাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। যেহেতু সে বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন উসামা, তাই ওমর (রাঃ) কে রাখতে হলে উসামার অনুমতি প্রয়োজন।খলিফা বলেন, “যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক ওমরকে আমার সাহায্যের জন্য রেখে যান”।
এখানে এসে বিস্ময়ে ইতিহাসের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। “যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক ওমরকে (রাঃ) আমার সাহায্যের জন্য রেখে যান”। একথা কত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে খলিফা তার মামুলী সেনাপতিকে বলতে পারেন তা বুঝিয়ে বলার উপযুক্ত ভাষা আমাদের নেই।
ইতিহাস আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়। আমরা দেখতে পাই, ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ)কে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অথচ তিনিও দাস শ্রেণী-উদ্ভুত ছিলেন। আমাদের কল্পনার চোখ আরো বিস্তারিত হয় যখনি আমরা দেখি যে, আমর ইবনে হিশামের পুত্র সোহায়েল, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং অন্যান্য কোরাইশ সর্দার দাঁড়ানো থাকতে হজরত ওমর দু’জন প্রাক্তন গোলাম সোহায়েব (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ)কে আগে ডেকে নেন। কেননা তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবী ও বদর যুদ্ধের সিপাহী। এ অগ্রাধিকারে আবু সুফিয়ান অস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে জাহেলিয়াতের উক্তি করে ফেলেনঃ “এমন কান্ড কখনো দেখিনি। আমাদেরকে দরজায় দাঁড় করিয়ে গোলামগুলোকে ভেতরে ডেকে নেয়া হলো”।
হজরত ওমর (রাঃ) একদিন মক্কা শরীফের কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখেন যে চাকর-নফররা মুনিবদের সাথে খেতে বসেনি বরং একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে মুনিবদের উদ্দেশ্যে বলেন, “ব্যাপার কি! নিজেদের ভৃত্যদের সাথে এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে কেন?” অতঃপর তিনি ওই ভৃত্যদেরকে ডেকে জোর পূর্বক মনিবদের সাথে ভোজনে বসিয়ে দেন।
হযরত ওমর (রাঃ) নাফে ইবনুল হারেসকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার সাথে উসফানে খলিফার সাক্ষাত হলে জিজ্ঞাসা করেন, “কি সংবাদ, কাকে স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ?” নাফে জবাব দেন, “ইবনে আবজাকে স্থালাভিষিক্ত করে এসেছি। তিনি আমাদের আজাদকৃত গোলামদের অন্যতম”। ওমর (রাঃ) বললেন, “সে কি! একজন আজাদকৃত গোলামকে মক্কাবাসীদের ওপর নিজের স্থলাভিষিক্ত করে এলে?” জবাব এলো, “তিনি কোরআনে অভিজ্ঞ, শরিয়তে সুপন্ডিত এবং সুবিচারক”। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, “হবেই তো! আমাদের নবী (সাঃ) বলে গেছেন যে, আল্লাহতায়ালা এই কিতাব দ্বারা অনেককে ওপরে তুলবেন, অনেককে নীচে নামাবেন”।
------------এরাবিক টেক্সট-------
বলা বাহুল্য, হযরত ওমর (রাঃ) আপত্তি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নয়- বরং ইবনে আবজার পরিচয় জানবার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন। নইলে এই ওমরই নিজের পরবর্তী খলিফা নির্বাচনকারী ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিষদকে অছিয়ত করার সময় বলতেন না যে, “হোজাইফার গোলাম সালেম জীবিত থাকলে আমি তাঁকে খলিফা নিয়োগ করে যেতাম”। এ থেকে বুঝা যায়, তিনি তাকে পরিষদের ছয়জন সদস্যের প্রত্যেকের চেয়ে উত্তম মনে করতেন। এই ছয়জন ছিলেন, ওসমান, আলী, তালহা, জোবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা’দ ইবনে আবি আক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)।
একবার জনৈক আজাদকৃত গোলাম অন্য একজন কোরাইশ বংশীয় ব্যক্তির নিকট তার বোনের পাণি গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করে এবং তার বোনকে প্রচুর অর্থ দিতে চায়। কিন্তু সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ওমর (রাঃ) যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোন কারণে তার সাথে তোমার বোন বিয়ে দিতে চাওনি? সে অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং সে তোমার বোনকে অনেক অর্থ সম্পদও দিতে চেয়েছে”। লোকটা বললো, “আমরা উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। কিন্তু সে আমার বোনের সম-পর্যায়ভুক্ত নয়”। ওমর (রাঃ) বললেন, “এই ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, দুনিয়ায় সম্ভ্রান্ত এই জন্যে যে, সে প্রচুর বিত্তবান আখেরাতে সম্ভ্রান্ত এই জন্য যে, সে খোদাভীরু ও সৎকর্মশীল। যদি মেয়ে রাজী থাকে তবে তাকে এই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও”। লোকটি তার বোনের মতামত গ্রহণ করে দেখে যে সে সম্মত। অতঃপর তার সাথে তার বোনকে বিয়ে দিয়ে দেয়।
গোলামদের যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা, উচ্চ থেকে উচ্চতর পদমর্যাদায় উন্নীত হবার অবাধ সুযোগ ছিল। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে তার গোলাম ইকরাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে তার গোলাম নাফে, আনাস ইবনে মালিকের সাথে তার গোলাম ইবনে শিরীন এবং আবু হোরাইরার সাথে তার গোলাম ইবনে হরমুজ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বসরায় হাসান বসরী এবং মক্কায় মুজাহেদ ইবনে জুবায়ের, আতা ইবনে আবি রাবাহ এবং তাউস ইবনে কাইসান খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন দাস বংশোদ্ভুত। অনুরূপভাবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সময়কার মিশরের মুফতি ইয়াজিদ ইবনে আবু যিব দিনকালার আসওয়াদ নামক ব্যক্তির গোলাম ছিলেন। (আবু হানিফাঃ আবদুল হালিম জুন্দী)।
শ্রমজীবীদের ব্যাপারেও মুসলমানদের নীতি অনুরূপ ছিল। গায়ে খেটে জীবিকা উপার্জনকারীরা মুসলমানদের সমাজ জীবনে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিল। স্বয়ং শ্রমের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। তাই শ্রমিক মাত্রই- তা সে যে পেশার সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক- সমান শ্রদ্ধা লাভ করতো। কোনো শ্রমজীবীর পেশা তাকে জ্ঞানার্জনে বাধা দিতে পারতো না- এমনকি বড় বিদ্বান ও ওস্তাদে পরিনত হবার পথেও কোনো বাধা ছিল না।
ইমাম আবু হানিফা কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন, আর তার পরবর্তী বহু বিখ্যাত মনীষি ব্যবসায়ী অথবা কারিগর ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে আমর ছিলেন জুতা প্রস্তুতকারী। তার পিতা ছিলেন ইমাম আবু হানিফার সহচর মুহাম্মদ ও হাসানের শিষ্য। ইনি একদিকে জুতা তৈরী করে জীবিকা উপার্জন করতেন, আবার অপরদিকে খলিফা মুহতাদী বিল্লাহর জন্য ‘কিতাবুল খারাজ’ বা ‘ইসলামের রাজস্ব-নীতি’ প্রণয়ন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ফেকাহ শাস্ত্রের ওপর নিজের মূল্যবান গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করতেন। কাফ্ফালের হাতে তালা বানানোর দাগ পরিদৃষ্ট হতো, ইবনে কাত্তান্দুবাগা দর্জ্জীগিরী করতেন, খ্যাতনামা ইমাম জাসসাস ছিলেন কাঁচপাত্র র্নিমাতা। এমনিভাবে ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দিতে আমাদের সামনে আসেন পিতলের পাত্র বিক্রেতা (সাফ্ফার), আতর বিক্রেতা (সায়দালানী), হালুয়া বিক্রেতার পুত্র (হালওয়ারী), আটা বিক্রেতা (দাক্কাক), সাবান বিক্রেতা (সাজুনী), জুতা প্রস্তুতকারী (নায়ালী), তরকারী বিক্রেতা (বাক্কালী) এবং হাড়ী বিক্রেতা (কুদূরী) প্রমুখ।
ইসলামী সভ্যতার প্রাতঃকালেই অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানরা যা করে দেখান, বহু শতাব্দীব্যাপী চেষ্টা করেও পাশ্চাত্য জগত তা করতে পারেনি- অর্থাৎ কিনা কোন পেশাই মূলতঃ নীচ কিংবা সম্ভ্রান্ত নয়, আসলে মানুষই উচ্চতর গুণাবলীর অধিকারী হয় অথবা তা থেকে বঞ্চিত হয়। (আবু হানিফাঃ জুন্দী)
ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা
মানবিক সাম্যের এই সু-উচ্চ মর্যাদার পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব হবে না যতক্ষন আমরা উচ্চ পদস্থ লোকদের ব্যাপারে ইসলামী সমাজের নীতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ওয়াকিফহাল না হবো। বড়রা যখন ছোটদের সাথে এক সারিতে দাঁড়াবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের একমাত্র ভিত্তি হবে- বংশ-মর্যাদা, পদ-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ নয় বরং চরিত্র- কেবলমাত্র তখনি প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কেবলমাত্র ছোটদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।
ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) তদীয় ‘কিতাবুল খারাজে’ লিখেছেনঃ ‘একবার হযরত ওমর (রাঃ) তার কর্মচারীদের হজ্জের সময় তার সাথে সাক্ষাত করার নির্দেশ পাঠান। যথাসময়ে তারা উপস্থিত হলে হযরত ওমর (রাঃ) তাদের ও সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেনঃ
“ভাইসব! সততার সাথে তোমাদের তত্ত্বাবধান ও সেবার জন্যই আমি এসব কর্মচারী নিয়োগ করেছি। তোমাদের জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য আমি এদেরকে নিযুক্ত করিনি। সুতরাং কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে তোমাদের কারো কোন অভিযোগ থাকলে তার দাঁড়িয়ে সে কথা বলা উচিত। সেদিন মাত্র এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, “আমিরুল মুমেনীন! আপনার অমুক কর্মচারী আমাকে অন্যায়ভাবে একশো কোড়া মেরেছে”।
হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমিও কি তাকে প্রহার করতে চাও? এস, প্রতিশোধ গ্রহণ কর”। তখন আমর ইবনুল আস দাঁড়িয়ে বললেন, “আমিরুল মুমেনীন! আপনি কর্মচারীদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা শুরু করলে তা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। এটা একটা স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনার পরবর্তী লোকেরাও তদনুসারে কাজ করবে”।
হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ “তাই বলে কি আমি এই ব্যক্তিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না? অথচ আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নিজের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখেছি। (লোকটিকে লক্ষ্য করে) এস, প্রতিশোধ গ্রহণ কর”। আমর ইবনুল আস বললেন, “আমাদেরকে লোকটিকে সন্তুষ্ট করার সুযোগ দিন”।
হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি দিলেন। তখন তারা লোকটিকে দু’শো দিনার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। প্রতিটি কোড়ার বিনিময়ে দুই দিনার দিতে হলো। আমর ইবনুল আস অন্য কর্মচারীর ওপর থেকে বিপদ অপসারণ করলেন সত্য, কিন্তু স্বয়ং তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে যখন জনৈক মিশরীয় ছেলেকে প্রহার করার অভিযোগ এল তখন ওমর (রাঃ) তাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে ছাড়েন এবং আমরকে কোন উচ্চ-বাচ্চ করতে দেননি। প্রতিশোধ গ্রহণ করানোর সময়ে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, “এই বড়লোকের ছেলেকে প্রহার কর”। আমর ইবনুল আসেরও শাস্তি ভোগ করা অবধারিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মিশরীয় লোকটি ক্ষমা করে দেয় এবং প্রহার থেকে বিরত থাকে।
আর একদিন হযরত ওমর (রাঃ) বসে মুসলমানদের মধ্যে কিছু অর্থ বন্টন করছিলেন। সমবেত লোকদের ভীড় প্রবল হয়ে ওঠে। সা’দ ইবনে আবি আক্কাস সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং অন্যান্য লোককে ঠেলে হযরত ওমরের নিকট পৌঁছে যান। এই সাহাবী বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের সন্তান। হযরত ওমর (রাঃ) এই বলে তাঁকে এক দোররা কষে দিলেন, “তুমি পৃথিবীর ওপরে আল্লাহর হুকুমতের প্রতাপ মান না কিন্তু আল্লাহর হুকুমাতের দৃষ্টিতে যে তোমার প্রভাব প্রতিপত্তির কানা-কড়িও মূল্য নেই তা তোমাকে দেখিয়ে দেয়া আমি প্রয়োজন বোধ করলাম”।
কেউ বলতে পারে যে, তিনিতো ছিলেন খলিফা। তার সাথে কার তুলনা? এই জন্য আমরা এবার দেখবো যে খলিফা ও বাদশাহদের সামনে তাদের প্রজারা মত প্রকাশ ও সমালোচনার ব্যাপারে কতখানি স্বাধীনচেতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। মতামত প্রকাশে এই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীকতার আসল উৎস হচ্ছে ইসলাম প্রদত্ত বিবেক ও প্রজ্ঞার স্বাধীনতা এবং কথায় ও কাজে বাস্তবায়িত পূর্ণ সাম্য।
খলিফা হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, “যদি তোমরা আমার মধ্যে কোন বক্রতা দেখ তবে আমাকে সোজা করে দিও”। সমবেত মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠেন, “তোমার মধ্যে কোন বক্রতা দেখলে আমরা তোমাকে তীক্ষ্ণধার তরবারী দিয়ে সোজা করে দেব”। একথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, “আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি ওমরের খেলাফতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও সৃষ্টি করেছেন যে তাকে তীক্ষ্ণধার তরবারী দিয়ে সোজা করতে পারে”। একবার মুসলমানরা গণিমতে কতগুলো ইয়ামেনী চাদর লাভ করেন। সকল মুসলমানের মত হযরত ওমরও একটা চাদর পান এবং তার পুত্র আব্দুল্লাহকেও একটা চাদর দেন। যেহেতু খলিফার জামার দরকার ছিল তাই আব্দুল্লাহ নিজের অংশের চাদরটা খলিফাকে দিয়ে দেন যাতে দু’টো মিলে একটা জামা হতে পারে। এ জামা গায়ে দিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) বক্তৃতা দিতে ওঠেন এবং বলেন, “তোমরা আমার কথা শোন এবং মেনে চল”।তৎক্ষনাৎ সালমান উঠে বললেন, “আপনার কথা আর শুনবোও না মানবোও না”। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন?” সালমান বললেন, “আগে আপনি জবাব দিন, এ জামা কি করে তৈরী করলেন? নিশ্চয়ই আপনিও একটা চাদরই পেয়েছেন, আর আপনি খুবই লম্বা মানুষ”। তিনি বললেন, “তাড়াহুড়া করে ফায়সালা করে ফেল না”। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডেকে বললেন, “আমি তোমাকে খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি বল, যে চাদর দিয়ে আমি জামা বানিয়েছি তা তোমার চাদর কি-না? তিনি বললেন, “হ্যাঁ”। তখন সালমান বললেন, “এবার বলুন আপনি, কি হুকুম। আমরা শুনবো এবং মানবোও”।
কেউ বলতে পারে যে, এটা তো ওমরের (রাঃ) ব্যাপার। তার সাথে কার তুলনা?
আবু জাফর মনসুরের উদাহরণ নিন। তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তার আইনের ভিত্তি শরিয়তের ওপর নয় বরং আমাদের পরিভাষা অনুসারে সামাজিক রসম-রেওয়াজ ও রীতি-প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফিয়ান সওরী তার নিকট গিয়ে বলেন, “আমিরুল মুমেনীন! আপনি আল্লাহ ও মুসলমানদের ধন-সম্পদ তাদের ইচ্ছা ও সম্মতি ছাড়াই ব্যয় করছেন। বলুন এর কি জবাব আছে আপনার কাছে?” হযরত ওমর (রাঃ) একবার সরকারী খরচে হজ্জ করেছিলেন, তাতে তার এবং তার সংগী-সাথীদের ওপর সর্বমোট ষোল দিনার ব্যয়িত হয়েছিল। তথাপি ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, আমার মনে হয় আমরা বাইতুল মালের ওপর বিরাট বোঝা চাপিয়েছি। আপনি নিশ্চই জানেন, মনসুর ইবনে আম্মার আমাদেরকে কি হাদীস শুনিয়েছিলেন। কারণ সেই মজলিসে আপনিও ছিলেন এবং সর্বপ্রথম আপনিই হাদীসটা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের সম্পদে নিজের খেয়াল খুশী মত হস্তক্ষেপ করবে তার জন্য দোজখের আগুন অবধারিত রয়েছে”। এতে বাদশাহর ঝানু চাটুকার আবু ওবায়দা নামক কেরানী বলে উঠলো, “কি! আমিরুল মুমেনীনের সাথে এ ধরনের আলাপ!” সুফিয়ান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ হতভাগা! হামান ও ফেরাউন এই ভাবেই চাটুকারীতা করে পরস্পরকে ধ্বংশ করেছিল।” এই বলেই দরকার থেকে নিস্ক্রান্ত হন।
স্বৈরাচারী শাসকদের স্বৈরাচার যতই প্রবল হোক, যার হৃদয় জোর্তিময় ছিল এবং যে বস্তুগত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর বিধানের নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করেছে- তেমন ব্যক্তির ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।
ওয়াসেকও ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। তার কাছে একবার জনৈক মুসলিম দার্শনিক আগমন করেন। তিনি ওয়াসেককে সালাম করেন কিন্তু তার জবাবে ওয়াসেক বলেন- “লা সাল্লামাল্লাহ আলায়কা” (অর্থাৎ আল্লাহ যেন তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত না করেন)”। এ কথা শোনা মাত্রই তিনি ওয়াসেককে ধমক দিয়ে বলেন, “তোমার শিক্ষকরা তোমাকে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ শিখিয়েছে”। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ
“যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম কর অথবা সেটার মতই জবাব দাও”। অথচ তুমি আমাকে উত্তম সালাম করা দূরে থাক সমান সমান জবাবও দাওনি। (আবু হানিফা-জুন্দী)।
বিচারপতি আবু ইউসুফ আদালতের অধিবেশনে বসেছেন। এক ব্যক্তি তার নিকট মোকদ্দমা নিয়ে এলো। আব্বাসী বাদশাহ হাদীর সাথে একটি বাগানের ব্যাপারে তার কোন্দল। আবু ইউসুফ মত পোষণ করেন যে, বাগান ওই লোকটিরই প্রাপ্য। কিন্তু অসুবিধা এই যে, বাদশাহের সাক্ষী ছিল। তিনি বললেন, “বাদী দাবি করছেন যে, বাদশাহর সাক্ষীরা সত্যবাদী এ মর্মে বাদশাহকে শপথ করতে হবে”। হাদী শপথ করাকে নিজের অবমাননা মনে করায় তা অস্বীকার করেন এবং বাগান তার মালিককে ফেরত দেন। অপর একটি মামলায় তিনি হারুনুর রশীদকে শপথমূলক বিবৃতি দিতে বাধ্য করেন। ফজল ইবনুর রবী হারুনুর রশীদের পক্ষে সাক্ষী হয়ে এলে তিনি তার সাক্ষ্য নাকচ করে দেন। খলিফা বিক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, “ফজলের সাক্ষ্য নাকচ হবার কারণ কি?” জবাবে আবু ইউসুফ বলেন, “আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, আমি আপনার গোলাম”। যদি তার কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় আর যদি সে মিথ্যুক হয়ে থাকে তাহলে মিথ্যুকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না”।(আবু হানিফা-জুন্দী)
ইসলাম যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রদীপ মানুষের বিবেক-মনে প্রজ্জ্বলিত করেছিল, তা ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগেও অনির্বাণ ছিল। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে বিবেকের এহেন গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতার প্রচুর উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়।
মিসরে আহমদ ইবনে তুলুন, বাক্কার ইবনে কাতিবা নামক হানাফী কাজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আহমদ তাকে আব্বাসী যুবরাজ মুয়াফ্ফাকের ওপর অভিসম্পাত করার অনুরোধ জানালে তিনি ক্ষণিক থেকে বললেনঃ
----এরাবিক টেকস্ট----
“সাবধান! অত্যাচারীদের ওপর অভিসম্পাত”। এতে এক ব্যক্তি আহমদ ইবনে তুলুনকে বলেন যে, বাক্কার আপনাকে (আহমদকে) লক্ষ্য করেই অভিসম্পাত করেছে। এর ফলে ইবনে তুলুন তাকে প্রদত্ত যাবতীয় উপঢৌকন ফেরত চান। এ জিনিসগুলো তিনি যেরূপ সিলমোহর করা অবস্থায় দিয়েছিলেন সে অবস্থায়ই ফেরত পান। অতঃপর ইবনে তুলুন বাক্কারকে একটি ভাড়াটিয়া ঘরে অন্তরীণ করেন। বহুলোক তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ইবনে তুলুনের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসতো। বাক্কার তাদের সাথে জানালার মধ্য দিয়ে আলাপ করতেন, এরপর ইবনে তুলুন এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যে, তার জীবনের কোন আশাই থাকলো না। তখন তিনি বাক্কারের মুক্তির নির্দেশ দেন। যে দূত মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিল তাকে তিনি বলেছেন, “ইবনে তুলুনকে বল, আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছি আর উনি রোগাক্রান্ত। এখন শীগগীরই আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমাদের মাঝে শুধু আল্লাহ ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন”। ইবনে তুলুন মারা গেলে বাক্কার বলতেন, “আহা! বেচারা মারা গেছে!” (আবু হানিফা-জুন্দী)
এই “বেচারা মারা গেছে!” উক্তিটির মধ্য দিয়ে তার এ অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, ইবনে তুলুন ক্ষমতাসীন ছিল সত্য, কিন্তু সে ছিল তার চেয়ে নীচ এবং অসহায়।
আইয়ুবী শাসনামলে মিশরের বাদশাহ ইসমাইল ক্রুসেড-যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করেন। ইংরেজরা তাকে সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে-এই মর্মে আশ্বাস পেয়ে সায়দাসহ কতিপয় এলাকা তিনি ইংরেজদের নিকট হস্তান্তর করেন।কিন্তু আজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুল সালাম এর কঠোর প্রতিবাদ জানালে বাদশাহ রুষ্ট হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর তিনি দূত পাঠিয়ে আজ্জুদ্দীনকে ভীতি ও লোভে প্রদর্শন করেন। দূত তাকে বলে, “আপনি বাদশাহর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করলে আপনাকে সাবেক পদে বহাল করা হবে এবং আপনার আরো পদোন্নতি হবে”। আজ্জুদ্দীন জবাব দেন, “খোদার শপথ! বাদশাহ এসে আমার হাত চুম্বন করুক-তাও আমি বরদাশত করবো না। আসলে তোমরা এক জগতের লোক আর আমি অন্য জগতের লোক”। (আবু হানিফা-আব্দুল হালিম জুন্দী)
জাহির বেবরিসের শাসনামলে শেষ মহিউদ্দিন নবভী দামেস্ক অবস্থান করতেন। তিনি জাহিরকে প্রায়ই সদুপদেশ দিতেন। তিনি কখনো চিঠি দ্বারা কখনো মৌখিক উপদেশ দিতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী তার প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘হুনসুল মহাজারা’তে বাদশাহর নিকট লিখিত তার বহু চিঠি উদ্বৃত করেছেন।এর অধিকাংশ চিঠিতে জনগনের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে কর মওকুফ করার দাবি জানানো হয়েছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “এ বছর যথোপযুক্ত বৃষ্টি হয়নি। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য দ্রব্যের তীব্র অভাব, গবাদি পশুর মড়ক প্রভৃতি কারণে সিরিয়াবাসীরা শোচনীয় অবস্থায় পতিত। এমতাবস্থায় দরিদ্র জনগনের ওপর আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শণ করা উচিত। আপনার এবং জনগনের কল্যাণের জন্যই এ কথা বলা। কেননা কল্যাণ কামনাই হচ্ছে ইসলামের মূল কথা”।
বাদশাহ এ উপদেশ শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, অধিকন্তু তার প্রতি আলেম সমাজের অসহযোগীতায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, “তাতারীরা যখন দেশের ওপর হামলা করে লুটতরাজ চালাচ্ছিল-তখন এই হুজুররা কোথায় ছিলেন?” শেখ মহিউদ্দীন তার এ টিটকারীর কঠোর জবাব দিয়েছিলেন। তিনি নিজের মতামত এবং পূর্বোক্ত উপদেশের পূনরাবৃত্তি করে বলেন, “অমুসলিম হানাদারদের ব্যাপার আর দেশের মুসলিম শাসকদের ব্যাপার সমান হতে পারে না। সেই বিদ্রোহী কাফেররা যখন আমাদের দ্বীনের ওপর বিন্দুমাত্র ঈমান রাখতো না- তখন তাদেরকে আমরা কি উপদেশ দিতে পারতাম এবং তাতে কি লাভ হতো? আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাকে সত্য কথা বলা এবং সদুপদেশ দেয়া থেকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এটা আমার এবং আমার মত অন্যান্যদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে বিপদেরই সম্মুখীন হতে হোক না কেন, সেটা আল্লাহর নিকট মহাকল্যাণের কারণ এবং মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। আমি পুরোপুরিভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি। আল্লাহ তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে সত্য কথা বলা সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখতে এবং এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদ গ্রাহ্য না করতে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা বাদশাহকে সর্বাবস্থায় ভালবাসি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার কল্যাণ কামনা করি”।
শেখ সাহেব এমনি হীত কামনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখতে থাকেন। কিন্তু জাহির তার উপদেশ কর্ণপাত না করে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির অজুহাতে কর আদায় করা অব্যাহত রাখেন। বাদশাহ নিজের মতামতের পক্ষে আলেমদের ফতোয়া জমা করে রেখেছিলেন। এই সব আলেম তার নির্দেশ অনুসারে ফতোয়া দিয়েছিল। তিনি শেখকে ডেকে অন্যান্য আলেমদের ফতোয়ায় স্বাক্ষর দিতে বলেন। শেখ এতে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, “আমি জানি, তুমি কয়েদী ক্রীতদাস ছিলে। তুমি ছিলে দেউলে। এরপর আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং তোমাকে বাদশাহর মর্যাদায় উন্নীত করেন। আমি জানি, তোমার কাছে জরিদার কাপড় পরিহিত এক হাজার ক্রীতদাস এবং আপদমস্তক স্বর্ণালংকারে মন্ডিত একশো দাসী আছে। এখন তুমি যদি ক্রীতদাসের এই জরিদার কাপড়গুলো এবং দাসীদের অলংকারগুলো খরচ করে দাও তাহলে আমি ফতোয়া দেব যে, তোমার জন্য প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করা বৈধ”।
জাহির একথা শুনে প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং তাকে তৎক্ষনাৎ দামেস্ক থেকে বহিস্কার করেন। শেখ সিরিয়ার নাভা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। পরে সমস্ত আলেমগণ ও ফকীহগণ বাদশাহকে বলেন যে, “ইনি আমাদের সর্বজনমান্য ও সবার সেরা আলেম। তাকে দামেস্কে ফিরিয়ে আনুন”। এতে বাদশাহ তাকে দামেস্কে ফিরে আসার অনুমতি দেন, কিন্তু শেখ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “যতদিন জাহির ওখানে থাকবে ততদিন আমি আসবো না”। এর একমাস পর জাহির মৃত্যুমুখে পতিত হন। (অধ্যাপক আবু জুহরা কৃত ‘ইবনে তাইমিয়া’ থেকে)।
সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসেও এ ধরনের মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমি শুধু দু’টো ঘটনার উল্লেখ করবো।
ইসমাইলের শাসনামলে একবার সুলতান আব্দুল আজীজ মিসরে আগমন করেন। ইসমাইল তার আগমনের প্রতীক্ষার দিন গুনছিলেন, কারণ তার খদেভ উপাধি লাভের ব্যাপারে তার আগমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তা ছাড়া সুলতানের সফরের ফলে মিসরের বহু রাজনৈতিক সুবিধাদি পাওয়ার বহু সম্ভাবনা ছিল। এই সময়ে সুলতান কর্তৃক আলেমদের সাক্ষাত দানে এক কর্মসূচী তৈরী
করা হয়। এই সাক্ষাত দানের অনুষ্ঠানে বহু ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ পালিত হয়। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, আগমনকারীর নতজানু হয়ে ভূমির সাথে মাথা ঠুকে তুর্কী কায়দায় কুর্ণিশ করতে হতো। রাজ প্রাসাদের ব্যবস্থাপকদের ওপর আগত আলেমদেরকে এ সব রসম-রেওয়াজের অনুশীলন দানের দায়িত্ব ছিল, পাছে তারা সুলতানের সামনে ভুল না করে বসেন।
অতঃপর সাক্ষাত অনুষ্ঠান সময় ঘনিয়ে এল, আলেমগণ একে একে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং নিছক পার্থিব স্বার্থের লোভে নিজেরই মত সৃষ্ট জীবের সামনে কুর্ণিশ করে যেতে লাগলেন। তারপর শিখানো পদ্ধতিতে সুলতানের দিকে মুখ করে পেছনের দিকে অগ্রসর হতে হতে বেরিয়ে এলেন। এই ঘৃণ্য কাজ থেকে মাত্র একজন আলেম রক্ষা পেলেন। তিনি হচ্ছেন শেখ হাসানুল আদাদী। তিনি তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেন এবং আল্লাহর হাতে সমস্ত শক্তি নিহিত এই অনুভূতি জাগ্রত রাখেন। তিনি স্বাধীন মানুষের মত মাথা উচু করে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সুলতানের সামনে এসে ইসলামী রীতি অনুসারে “আসসালামু আলাইকুম” বলে সালাম করেন। অতঃপর (শাসকের সাথে সাক্ষাত করার সময় কোন আলেমের যেমন করা উচিত) তিনি তাকে আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের সাথে সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দেন। তারপর কথা শেষ করে আবার সালাম করেন এবং নির্ভীক স্বাধীন মানুষের মত আবার মাথা উচু করে বাইরে চলে যান।
এসব দেখে দরবারের ব্যবস্থাপক এবং স্বয়ং খদেভের চেতনা বিলোপের উপক্রম হলো। তারা ভাবলেন পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে এবং সুলতানের বোধহয় ক্রোধের কোন সীমা থাকবেনা। তাদের সযত্ন অনুশীলন ব্যর্থ হওয়ায় তারা হতাশায় ভেংগে পড়লো।
কিন্তু সত্য কথার প্রভাব কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। ওটা যে শক্তি ও প্রতাপ নিয়ে মন থেকে বেরিয়ে আসে সেই শক্তি ও প্রতাপ নিয়ে অন্যান্যদের মনে উপ্ত হয়। এখানেও তাই হলো। সুলতান বে-ইখতিয়ার বলে ফেললেন যে, তোমাদের এখানে শুধু এই একজনই আলেম রয়েছে। সুলতান শুধু তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং অন্য সবাইকে বঞ্চিত রাখলেন।
দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে খদেভ তওফিক পাশা ও শেখ হাসানুওভীলের মাঝে ‘দারুল উলুমে’।
শেখ হাসানুওভীল ছিলেন দারুল উলুমের অধ্যাপক। তিনি সস্তা মূল্যের মামলী ধরণের জামা (জালবাব) পরিধান করতেন। একদিন দারুল উলুমের অধ্যক্ষ জানতে পারলেন যে, খাদেভ শীগ্গিরই মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে আসবেন। তিনি তৎক্ষনাৎ মাদ্রসা পরিস্কার করা ও সাজ শয্যা শুরু করে দিলেন। শেখ হাসানুওভীলকে পোষাক পরিবর্তন করে কাফতান ও জুব্বা (অপেক্ষাকৃত অভিজাত পোষাক) পরিধান করে আসতে বলা হলো। শেখ ইঙ্গিতে এ অনুরোধ মেনে নিলেন।
নির্ধারিত দিনে শেখ তার পুরনো পোষাক পরিধান করেই এলেন। তবে তার হাতে একটা রুমালে একটা কিছু পুটুলির মত বাধা ছিল। তাকে পুরনো পোষাকে দেখে অধ্যক্ষের মুখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। খানিকটা ক্রোধমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “শেখ! জুব্বা ও কাফতান কোথায়? তিনি রুমালের দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে দিলেন যে এখানে আছে। অধ্যক্ষ ভাবলেন যে মেহমানের আগমন আসন্ন হলেই হয়তো উনি পোষাক পরিবর্তন করে নেবে।
কিছুক্ষণ পর প্রতিক্ষিত মেহমান এলেন। সমগ্র মাদ্রাসায় একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। এর পরক্ষণেই এক অপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হলো। শেখ হাসানুওভীল হাতের পুটুলীটি নিয়ে খদেভের সামনে হাজির হলেন এবং সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে বলেলেন, “ আমাকে লোকেরা বলেছে যে আমাকে অবশ্যই জুব্বা ও কাফতান পরে আসতে হবে। যদি আপনার জুব্বা-কাফতানই চাই তাহলে এই রইলো জুব্বা-কাফতান, আর যদি আপনার হাসানুওভীলকে চাই তাহলে এই যে, হাসানুওভীল উপস্থিত”।
স্বাভাবিকভাবেই খদেভ জবাব দিলেন যে, তার হাসানুওভীলকে চাই।
এ হচ্ছে মুমিনদের প্রকৃত অবস্থা। তাদের ইসলামের সম্মান ছাড়া অন্য কোন সম্মানের আকাংখা থাকে না। তাদের মন-মানস ও বিবেক তুচ্ছ ও অসার মূল্যবোধ এবং ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে এবং তাকে পুরোপুরিভাবে জীবনে কার্যকরী করে। তারা ইসলামের দুর্জয় প্রাণশক্তি অর্জন করার পর কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন বোধ করে না। বস্তুতঃ এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম।
বিজিত দেশসমূহের সাথে ব্যবহার
বিজিত দেশসমূহের অধিবাসী এবং মুসলিম দেশসমূহের অমুসলিম জাতি সমূহের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, এবার আমরা সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করবো। কারণ সাম্য, সুবিচার ও বিবেকের স্বাধীনতার সাথে এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম প্রবর্তিত এই সাম্য ও সুবিচার ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও ইসলামের পরিধি ছাড়িয়ে সমগ্র মানবতার সাথে যুক্ত হয়েছে।
বিজিত দেশসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেশ জয়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যকারণের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই এসে পড়ে। এটা একটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আমরা এ সম্পর্কে শুধু যতটুকু অপরিহার্য এবং ইসলামের বিশ্বজনীন সামাজিক ন্যায়-নীতির সাথে সম্পৃক্ত ততটুকুই আলোচনা করবো।
ইসলামী দাওয়াত মানুষের বিবেক ও মন-মগজকে আবেদন জানায়। এতে বল প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতার অবকাশ নেই। এমনকি পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে অলৌকিক ঘটনাবলীর আকারে যে মনস্তাত্মিক বল প্রয়োগ প্রচলিত ছিল ইসলাম তাকেও প্রশ্রয় দেয়নি। ইসলামই একমাত্র বিধান, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে, তাকে অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজার মাধ্যমে সম্মোহিত করা এবং মনস্তাত্মিক উপায়ে প্রলুব্ধ করার পরিবর্তে তাকে সাদাসিদে ভাষায় সম্বোধন করে ক্ষান্ত হয়েছে। তরবারীর শক্তি দ্বারা মানতে বাধ্য করার পন্থা সে কখনো অবলম্বন করেনি।
------------এরাবিক টেক্সট------
“জীবন বিধানের ব্যাপারে বল প্রয়োগের অবকাশ নেই”।
------------এরাবিক টেক্সট------
“সদুপদেশ ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথে আহবান জানাও আর উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর”।
কিন্তু কোরাইশরা প্রথম দিন থেকেই বস্তুগত শক্তি দ্বারা এই নতুন জীবন বিধানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আল্লাহতায়ালা যাকেই ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, তার ওপর তার অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। কিছু সংখ্যক মুসলমানকে তারা তাদের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তাদেরকে পর্বতের গুহায় আটক রেখে সামাজিক ‘বয়কট’ করে অনাহারে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। মোট কথা, মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য বস্তুগত শক্তি ব্যবহারের কোনো পন্থাই তারা বাদ রাখেনি।
এমতাবস্তায় ইসলামের অনুসারীদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না-
------------এরাবিক টেক্সট------
“যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে অস্ত্র ধারনের অনুমতি দেয়া গেল। কেননা তার মজলুম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম”।
------------এরাবিক টেক্সট------
“যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অবশ্য বাড়াবাড়ি করো না। কারণ সেটা আল্লাহ পছন্দ করেন না”।
এরপর এক সময়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। দেশ জয়ের ধারাবাহিকতা আরবের বাইরে পদার্পণ করে। প্রশ্ন জাগে যে, এই দেশ জয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল?
আগেই বলেছি, ইসলাম আপনাকে একটা আন্তর্জাতিক মতাদর্শ ও বিশ্বজনীন জীবন বিধান পেশ করেছে। সে নিজেকে কোন বিশেষ উদ্দীপনার চতুর্সীমায় আবদ্ধ করতে পারে না। নিজের কল্যাণ ধারাকে সে বিশ্বের প্রতিটি কোণে এবং সমগ্র মানব জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দিতে চায়। কিন্তু পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় রোম ও পারস্যের দুই বিশাল সাম্রাজ্য। তারা তাকে ধ্বংস করার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে। এই শক্তি ইসলামী আন্দোলনের নিশানবাহীদেরকে পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে লোকদের নিকট ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। এমতাবস্থায় খোদায়ী বিধান ও সাধারণ মানুষের মাঝে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা অপসারণ করা ছাড়া ইসলামের গত্যন্তর ছিল না। এই বাধা অপসারনের পর সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা এবং মানুষের আনুগত্য ও গোলামী থেকে মুক্ত হবার সুযোগ দেয়। বাতিল ব্যবস্থার স্থলে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হবার এ হচ্ছে মর্মার্থ। এতে মানুষ অবাধ বাক-স্বাধীনতা লাভ করে। রাষ্ট্রীয় শক্তির বাধা অপসারিত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানের বিজয়ের পর আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে। এরপর যার ইচ্ছা হবে স্বেচ্ছায়-সানন্দে ও পূর্ণ অধিকার নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা হবে না- গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব নীতি নিজেরই নির্ধারণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কোরআনের নিম্নোক্ত ঘোষনায় দ্বীন বা আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার এটাই মর্মার্থ-
------------এরাবিক টেক্সট------
“এই কাফেরদের সাথে সংগ্রাম কর যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্য পুরোপুরিভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে না যায়”। এখানে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ মানুষের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধীন হবে। অতঃপর কোন বাধা বিপত্তি ও জোর-জবরদস্তি ছাড়াই নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস নিজেরাই নির্বাচন করে নেবে।
এই ব্যাখ্যার আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ইসলামের দেশ জয়মূলক ঘটনাবলী শক্তিমদমত্ত জাতি সমূহের শোষণ-নিষ্পেষণের উদ্দেশ্য বিজাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এ যুদ্ধসমূহের তাৎপর্য শুধু এই যে, এগুলো ছিল ইসলামের আনীত নতুন আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের মধ্যে ও অন্য জাতিগুলোর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রীয় শক্তি অপসারনের সংগ্রাম। এটা জাতিগুলোর জন্য ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, আর তাদের ওপর বস্তুগত শক্তির সাহায্যে খোদা হয়ে সওয়ার থাকা রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বন্তুগত ও সশস্ত্র সংগ্রাম।
ইসলাম নিজেকে গোটা মানব জাতির বিধান মনে করে এবং নিজের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে বস্তুগত শক্তি প্রয়োগ করে না। নিজের এই মূলনীতি অনুসারে সে বিশ্বের সমস্ত জাতির সামনে তিনটে পথ রেখেছে। প্রত্যেক জাতিকে তার একটা না একটা গ্রহণ করতে হবে- ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া দেয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা ও আনুগত্য প্রকাশ অথবা যুদ্ধ।
বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্য তার “ইসলাম গ্রহণের” আহ্বান নিঃসন্দেহে ন্যায় সংগত। কারণ এটাই হল একমাত্র হেদায়েতের পথ। এটা খোদা, মানুষ, জীবন ও জগত সম্পর্কে সর্বাধুনিক ও পরিপূর্ণতম মতবাদ। এটা সেই সিংহদ্বার- যেখান দিয়ে প্রবেশ করার পর একজন অমুসলিম সমস্ত মুসলিমানের ভাই হয়ে যায়, মুসলমানদের মতই তার অধিকার এবং মুসলমানদের মতই তার কর্তব্য স্থির হয়। বর্ণে, বংশে, ধনে, মানে- কোন দিক দিয়ে অন্য কোন মুসলমান এই নতুন মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না।
জিজিয়ার আহ্বানও অনুরূপ। দেশ রক্ষার জন্য মুসলমানদের জান পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা যাকাতও দেয়। একজন অমুসলিমও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক এবং অন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা উপভোগ করার ব্যাপারে সে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য সকলের সাথে সমান অংশীদার। বার্ধক্যে কিংবা অক্ষমতায় সে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুবিধাও উপভোগ করতে পারে। এমতাবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির দাবী এই যে, এ সব কাজে তারও নিজ অর্থ দ্বারা শরীক হওয়া উচিত। যাকাতে যেহেতু আর্থিক করের চেয়ে ইবাদতের বৈশিষ্ট্যই অধিকতর বিরাজমান, তাই ইসলাম তাদেরকে এই ইবাদাত পালনে বাধ্য করে না। কেননা ইসলামকে যারা গ্রহণ করেনি তাদের আবেগ অনুভূতিকেও ইসলাম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্য সে তাদের নিকট থেকে যাকাতের পরিবর্তে জিজিয়ার আকারে কর আদায় করে। জিজিয়া ধার্য করার সময় এ কথা লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন হলে সেটা শুধু মুসলমানরাই করে থাকে। এছাড়া জিজিয়া আনুগত্য ও আত্মসমর্পনেরও নিদর্শন। এ থেকে বোঝা যায় যে, জিজিয়া দানকারীরা শক্তির মাধ্যমে ইসলামের পথে বাধার সৃষ্টি করবে না এবং জনগণের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেয়ার পথে কেউ অন্তরায় হবে না। এটাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য।
সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ। ইসলাম এবং জিজিয়া- এ দুটোই প্রত্যাখ্যান করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে (অর্থাৎ অমুসলিম) ইসলাম ও সাধারণ মানুষের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে প্রদর্শিত এ স্পর্ধাকে মুক্তি দিয়েই খতম করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা এ ছাড়া এর আর কোন ওষুধ নেই।
ইসলাম বিজিত দেশগুলোতে নিজের মানবিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচীকে যথাযথরূপে বাস্তবায়িত করেছে। ইসলাম গ্রহণ করলে সে সেই অধিবাসীদেরকে সকল ব্যাপারে মুসলমানদের সমান অধিকার দিয়েছে। জিজিয়া দিলেও তাদেরকে সব উচ্চতর মানবাধিকারে সমৃদ্ধ করেছে। এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও সে তাদের সাথে ব্যবহারে ইনসাফ ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
কোন বিজিত দেশের শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম যথারীতি তাদেরকে সেখানকার শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রেখেছে। পারস্য বংশোদ্ভূত ‘বাজান’ কে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখেন। এমনিভাবে সানার শাসনকর্তা পারসিক ফিরোজকে তার পদে নিয়োজিত রাখেন। আরব বংশোদ্ভূত কায়েস ইবনে আবদে ইয়াগুস যখন ফিরোজকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে তখন আবু বকর (রাঃ) আরবী মুসলমানের বিরুদ্ধে পারসিক মুসলমানের সাহায্য করেন এবং তাকে পুনরায় সেখানে এনে পূর্বপদে বহাল করেন। এমনিভাবে মুসলমানরা অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে এবং আমীরের নিম্নপদস্থ অমুসলিম কর্মকর্তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখেন।
যারা ইসলামও গ্রহণ করে না- এবং জিজিয়াও দিতে স্বীকৃত হয় না বরং যুদ্ধের পথ বেছে নেয়- সেই সব বিদ্রোহীর যাবতীয় ধনসম্পদ বিজেতা কর্তৃক করায়ত্ব করা ইসলামী আইন অনুসারে সম্পূর্ণ বৈধ। এ সত্ত্বেও হযরত ওমরের (রাঃ) যুগে যখন পারস্য বিজিত হয়, তখন তিনি ইসলামের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের দাবিতে অন্য এক নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ভূমির ওপর যথারীতি ভূমি মালিকদের স্বত্বাধিকার স্বীকার করেন, তবে তার ওপর খাজনা ধার্য করেন। তিনি একাধারে দুটো স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। একটি হলো স্বয়ং বিজিত দেশগুলোর স্বার্থ, যদিও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল; তথাপি তিনি তাদের জীবিকার উপায় হরণ করতে চাননি। দ্বিতীয় স্বার্থ ছিল মুসলমানদের পরবর্তী বংশধরদের। সমস্ত ভূমি বর্তমান বিজেতাদেরকে দিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ বংশধররা তার ফল থেকে বঞ্চিত হতো।তাই তিনি মনে করলেন ভুমি থেকে খাজনা গ্রহণ করার পন্থাই উত্তম। এতে করে লব্ধ অর্থ সব সময় জনকল্যাণে ব্যয় করা যাবে এবং ভবিষ্যতের বংশধররাও তা থেকে যুক্তিসঙ্গত অংশ পেতে থাকবে।
এটা একটা সর্ববাদী সম্মত সত্য কথা যে, বিজিত দেশগুলোর সাথে ইসলাম সর্বদা অতি উন্নতমানের মানবিক আচরণ করেছে। মানুষকে সে তার সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকর গুণাবলী দ্বারা উপকৃত হওয়ার অবাধ ও শর্তহীন সুযোগ দিয়েছে। অধিকন্তু এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য সে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বানও জানিয়েছে। প্রত্যেককে সমাজ কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার সুযোগ দিয়েছে। ইসলামের একটা বিশেষ বিভাগে অর্থাৎ আইন ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিজিত দেশের অধিবাসীরা ও দাস শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল। গণজীবনের কোন একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগেও আরবদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল না। এমনকি আমীর ও শাসনকর্তার পদেও এমন সব লোক নিযুক্ত করা হতো, যারা সংশ্লিষ্ট দেশের অতিরিক্ত রাজস্ব প্রথমে সে দেশের কল্যাণ খাতে ব্যয় করতো এবং এর শুধু অবশিষ্টাংশই কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা করতো। বিজিত দেশগুলো উপনিবেশের পর্যায়ভুক্ত ছিল না এবং বিজেতাদের জন্য দেশবাসীর জানমাল নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যাবহার করার অবকাশও ছিল না। ঠিক অনুরূপ ভাবে ইসলাম বিজিত দেশগুলোর অধিবাসীদেরকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের অতুলনীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। তাদের ইবাদতখানা, খানকা, গির্জা এবং আলেমদের ও ধর্মযাজকদের সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলাম স্ব-হস্তে গ্রহণ করেছে। সে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিগুলো এমন সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে যার কোন নজির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ইতিহাসে মেলা দুষ্কর। আজও এ ব্যাপারে ইসলামের প্রবর্তিত রীতিই বহাল রয়েছে।
আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা হতভাগ্য উপনিবেশগুলোর সাথে যে ব্যাবহার করে, তার সাথে যখন আমরা ইসলামের তুলনা করি, তখন ইসলামকে তার ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে পবিত্র আদর্শ হিসেবে উজ্জ্বল ও ভাস্বর দেখতে পাই। আজ আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ বৈশিষ্ট্য থেকে ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যাতে যত দীর্ঘদিন সম্ভব তাদেরকে দুধের গাভীর মত দোহন করা যেতে পারে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে মানবীয় মান-সম্মান ও ভদ্র রীতি-নীতিকে জলাঞ্জলি দেয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে নৈতিক নৈরাজ্য বিস্তার করা, গোষ্ঠীগত ও দলগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ও তা সম্প্রসারিত করা এবং অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন চালানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
পাশ্চাত্যবাসীরা আজ ধর্মীয় স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়ান বটে কিন্তু তাদের পূর্বতন ইতিহাস স্পেনের তথাকথিত আদালতগুলোর পাশবিক শাস্তি এবং প্রাচ্যে ক্রুসেড যুদ্ধের নৃশংসতা দ্বারা কলংকিত। আজও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিছক একটি প্রদর্শনী মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ সুদানে খ্রিস্টান মিশনারীদের সকল সুযোগ সুবিধা থাকলেও মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গত মহাযুদ্ধে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি এ্যালেন বী (Allen by) বায়তুল মুক্ককাদাসে প্রবেশ করার সময়ে ইউরোপের প্রতিটি মানুষের মানসিকতার রূপ এই বলে তুলে ধরেন যে “প্রকৃতপক্ষে ‘ক্রুসেড যুদ্ধ’ আজ শেষ হল।” ফরাসি জেনারেল কাট্টো ১৯৪০ শালে দামেস্কে বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর সেখানে দাঁড়িয়ে বলেন, “আমরা ক্রুসেড যোদ্ধাদের বংশধর। আমাদের সরকার যাদের পছন্দ না হয়, তারা এখান থেকে চলে যেতে পারে।” ঠিক এই ধরনেরই কথা তার এক সম-মতাবলম্বী ১৯৪৫ সালে আলজিরিয়াতে বলেছিলেন।
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবস্থা আরও সাংঘাতিক। সেখানে মুসলমানদেরকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চলছে। মাত্র সিকি শতাব্দীতে রাশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা চার কোটি দু’লাখ থেকে কমে দু’কোটি ছ’লাখে এসে দাঁড়িয়েছে। যে রেশন কার্ড ছাড়া সেখানে জীবনযাপনের উপায় উপকরণ মেলা সম্ভব নয় তা থেকেও আজকাল মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের বলা হয়, “তোমাদের যখন খুশি নামাজ পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সরকার তোমাদেরকে খাদ্য দিতে পারবে না। তোমরা তোমাদের খোদার কাছে খাদ্য চাও।” এমনি ব্যবহার তাদের সাথে যুগোস্লাভিয়া এবং অন্যান্য দেশেও করা হয়।
ইসলাম চিরদিনই সর্বাত্মক ও সার্বজনীন সামাজিক সুবিচারের এমন উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে- যার ধারে কাছেও ইউরোপীয় সভ্যতা যেতে পারেনি। আর কোনদিন পারবেও না, কেননা ওটা হচ্ছে নিছক জড়বাদী ও বস্তুবাদী সভ্যতা। নরহত্যা, লুটতারাজ, রক্তপাত, হিংস্রতা ও নৃশংসতার ওপরই ওর ভিত্তি প্রথিষ্ঠিত। [এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থকারের “আসসালামুল আলমী আল-ইসলাম (বিশ্বশান্তি ও ইসলাম) এবং “দিরাসাতুন ইসলামিয়া’র ‘ইসলামের দেশ জয়ের প্রকৃতি ও তাৎপর্য’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]
পারষ্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
সবল ও দুর্বল, ধনী ও নির্ধন, ব্যক্তি ও সমাজ, শাসক ও শাসিত এবং এমনিভাবে সকল মানব মণ্ডলীর মধ্যে দয়া, সহানুভূতি, হীতকামনা ও পারষ্পরিক সহযোগিতার যে গুণাবলী ইসলামের কাম্য সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকে কতিপয় বাস্তব উদাহরন পেশ করবো। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ মালায় পরিপূর্ণ।
ইসলাম গ্রহণের সময় আবু বকর (রাঃ) এর নিকট ব্যবসায়ের মুনাফালব্ধ চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ব্যাবসা করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু যেদিন তার মহান বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ সাঃ এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন সেদিন তার এত পুঁজির মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। নিজের অবশিষ্ট সমস্ত পুঁজি তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলিম গোলামদের স্বাধীন করার জন্য ব্যয় করেন, এ সম্পদ থেকে তিনি দরিদ্র সর্বহারাদেরকে সাহায্য করতেন।
হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। খয়বরে তিনি এক টুকরো ভূমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট এসে বলেন, “আমি খয়বরে খানিকটা জমি পেয়েছি। এত মূল্যবান সম্পত্তি আমি কোন দিন পাইনি। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন “যদি তোমার মনে চায় তবে আসল জমি নিজের অধিকারে রেখে তার লভ্যাংশ দান করে দিও।”
হযরত ওমর (রাঃ) সেটা গরিব-দুঃখী, অভাবী আত্নীয়-স্বজনের জন্য, গোলামদেরকে স্বাধীন করার জন্য এবং দুর্বল-অক্ষম লোকদের সাহায্যে ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এভাবে তিনি নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে দান করে কোরআনের এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করেনঃ
------------এরাবিক টেক্সট------
“তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হবে না।”
খেলাফতের পূর্বে হযরত ওসমানের নিকট সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য বহর আসে। এই বহরে গম,জয়তুনের তেল ও মোনাক্কাবাহী এক হাজার উট ছিল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষের দরুন মুসলমানগণ শোচনীয় দুর্দশায় পতিত ছিলেন। বহু ব্যবসায়ী তার কাছে এসে বলে, “দেশে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা কত তীব্র তাতো আপনি ভাল করেই জানেন। এই দ্রব্য সম্ভার আমাদের নিকট বিক্রি করে দিন।” হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, “স্বাচ্ছন্দে বিক্রি করতে পারি কিন্তু আমাকে কত মুনাফা দেবে তাই বল।” ব্যাবসায়ীরা বললো, “দ্বিগুণ মূল্য দেব।” হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, “আমাকে তো এর চেয়ে অনেক বেশী মুনাফা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।” তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার বাণিজ্য বহর এইমাত্র এলো, আর ওটা পৌঁছানো মাত্রই আমরা মদিনার সমস্ত ব্যাবসায়ী হাজির হয়েছি। অন্য কেউ তো আপনার সাথে আমাদের পূর্বে সাক্ষাত করেনি। তা হলে কোন ব্যক্তি আপনাকে এত মুনাফা দিতে চেয়েছে?” হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, “আল্লাহ তায়ালা আমাকে দশগুণ মুনাফা দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তোমরা কি আমাকে এর চেয়ে বেশী দিতে পার?” তারা বললো, “না”। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) আল্লাহকে সাক্ষী করে ঘোষণা করলেন যে, “এই বাণিজ্যে বহরের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্য দরিদ্র ও মিসকিনদের জন্য সদ্কা করে দিলাম।”
হযরত আলীর (রাঃ) পরিবারে একদিন মাত্র তিনটে জবের রুটি ছিল। এই রুটি কয়টি তিনি একজন ইয়াতিম, একজন মিসকিন, ও একজন কয়েদীকে দান করে দিলেন। তিনি তাদেরকে তৃপ্তির সাথে খাইয়ে নিজে সপরিবারে অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রা গেলেন।
হরত হোসাইনের ওপর ঋণের ছাপ বেড়ে গেছে। আবি নাইজারের নির্ঝরিণী তার মালিকাধিন, ইচ্ছা করলে সেটা বিক্রি করে তিনি ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু গরীব মুসলমানরা তা থেকে সেচ কার্য সম্পন্ন করে, সে জন্য তিনি তা বিক্রী করলেন না। অথচ বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠ পরিবারের সন্তান হয়ে ঋণের বোঝা বয়ে বেরাতে লাগলেন।
মদিনায় আনসাররা মুহাজেরদেরকে নিজ নিজ সম্পত্তি, ঘরবাড়ী সকল জিনিসেরই অংশীদার করেন। তাদেরকে নিজেদের ভাই বলে গ্রহণ করেন। তাদের পক্ষ থেকে দিয়াত(অনিচ্ছাকৃত হত্যা বা জখমের আর্থিক ক্ষতিপূরণ) দিয়ে দেন, তাদের কয়েদিদেরকে ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করেন। এক কথায় তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আপন করে নেন। কোরআনের ভাষায়ঃ
------------এরাবিক টেক্সট------
“তারা যা কিছু মুহাজেরদেরকে দেয় সে সম্পর্কে মনে কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ করে না। তারা নিজ স্বার্থের ওপর অপরের স্বার্থকে অগ্রগণ্য মনে করে, এমনকি যদি তাদেরকে অভুক্তও থাকতে হয়।”
বস্তুতঃ যতদিন মুসলিম দেশগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবমুক্ত থাকে ততদিন তাদের সমাজ জীবনে এই প্রাণশক্তি সক্রিয় থাকে। জনাব আবদুর রহমান আযযাম তার গ্রন্থ “আর রিসালাতুল খালিদা”য় লিখেছেনঃ
“আমি উত্তর আফ্রিকার তাওয়ারেক গোত্রকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে দেখেছি। তাদের গোত্রে কোন ব্যক্তিই শুধু নিজের জন্য নয় বরং গোটা সমাজের জন্য জীবন ধারণ করে। তারা যে কাজ সমাজের জন্য করে তাতেই তারা সবচেয়ে বেশী গর্ব অনুভব করে। একটা অপূর্ব ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জনৈক শহরবাসী ফরাসিদের এলাকা থেকে হিজরত করে তাওয়ারেকদের নিকট ‘ফাজানে’ বসবাস এবং তাদের কৃপাদৃষ্টির ওপর জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। অতঃপর সে জীবিকার সন্ধানে বের হয়। সে তাদের দানের প্রতিদান দিতেও সংকল্পবদ্ধ ছিল। সে তার পরিবার পরিজনকে ঐ মুসলিম গোত্রের তত্তাবাধানে রেখে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কোন চাকরির সন্ধান পেলো না। সে আমাদের নিকট ‘মিসরাতা’ নামক স্থানে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এলো। আমরা তাকে, যাতে সে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারে সেই পরিমাণ সাহায্য করলাম। কিন্তু সে প্রায় এক বছর পর আবার আমাদের নিকট ফিরে এলো। আমরা মনে করলাম যে, সে তার পরিবারবর্গের নিকট থেকে ফিরে আসছে। কিন্তু সে আমাদের ধারণা খণ্ডন করে বলে যে, সে এখন নিজ পরিবারবর্গের নিকট যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, “কিভাবে?” সে বললো, “গত সাক্ষাতের সময় আমি যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে ব্যাবসা করেছি। এখন আমার নিকট যে টাকা সঞ্চিত হয়েছে তা নিয়ে আমি তাওয়ারেকদের নিকট যেতে পারবো।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি নিজের পরিবারের নিকট যাবে- না তাওয়ারাকদের নিকট?” সে বললো, “আমি প্রথমে তাওয়ারাকেদের নিকট যাব, কেননা তারা আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করেছে। এখন আমি গিয়ে তাদের মধ্যে যারা নিজ পরিবার থেকে অনুপস্থিত রয়েছে তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চালাবো এবং নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের এবং প্রতিবেশীদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বণ্টন করে দেব।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমাদের সমাজে কি প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি এরূপই?” সে বলল, “হাঁ, আমারা সকলে সুখে-দুঃখে পরস্পরের অংশীদার হই। আমারা বিদেশ থেকে খালি হাতে বাড়ি যেতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করি। কারণ আমাদের প্রতিবেশীরাও ঠিক আমাদের পরিবারবর্গের মতই আমাদের পথ চেয়ে থাকে।
এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঘটনার অত্যন্ত নির্ভুল ব্যাখ্যা দেনঃ
“সমাজ জীবনের এ বিচিত্র পদ্ধতি শুধু তাওয়ারেক গোত্র কিংবা বেদুঈন যাযাবরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা তাদের গোত্রবাদেরও ফল নয়। এটাই হচ্ছে আসল ইসলামী পদ্ধতি। আধুনিক জড়বাদী ও বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে যারা বহু দূরে অবস্থিত- সে সমস্ত গোত্রের মধ্যেই এ সমাজ ব্যবস্থার অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। আমি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু শহর বন্দরকে ইসলামী ভাবাপন্ন দেখেছি এবং শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ও আরব-অনারব নির্বিশেষে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ সমাজ পদ্ধতির প্রচলন দেখেছি। আমি বহু জায়গায় আজও মুসলমানদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সুখী জীবন-যাপন করতে দেখেছি। তারা নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য জড়বাদীর সভ্যতার পূজারী কোটি কোটি মানুষের তুলনায় অধিক সুখী ও সমৃদ্ধশালী। তারা আজও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কায়েম করা সমাজ ব্যবস্থার খুবই নিকটবর্তী। পাশ্চাত্য পূজারী মানুষ সমাজের বিরাট ক্ষতি ও বিপর্যয়ের বিনিময়েও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী। নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রয়োজন হলে তারা নিজ পরিবারেরও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, প্রতিবেশীর স্বার্থে সদ্বব্যবহারের তো প্রশ্নই ওঠে না।”
প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পারস্পারিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ইসলামের প্রাণশক্তিরই সৃষ্টি। কিন্তু এটাকে শুধু ব্যক্তির ও সমাজের বিবেকের বা দয়া-মায়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। সরকারও এটা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতো। হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক ‘বাইতুল মাল’ থেকে মাতৃদুগ্ধত্যাগী শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করা এর প্রকৃষ্ট উদাহরন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যয়ের খাতগুলো যাকাতের সুপরিচিত ব্যয়ের খাত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। স্বীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ খাতকে ‘সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা’ (Social security) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় চুরির শাস্তি রহিত করেছিলেন। কেননা হয়তোবা তীব্র ক্ষুধা কাউকে চুরি করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। ইসলামে সন্দেহের ভিত্তিতে দণ্ডবিধি মওকুফ করা হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত ঘটনা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং এ থেকে ব্যক্তি মালিকানার প্রকৃত সরূপ ও সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
বর্ণিত আছে যে, আব্দুর রহমান ইবনে হাতেব বালতায়ার কতিপয় গোলাম মোজাইনা গোত্রের একটি উট চুরি করে। তাদেরকে ধরে হযরত ওমরের (রাঃ) দরবারে নেয়া হলে তারা চুরির কথা স্বীকার করে। হযরত ওমর (রাঃ) কাছির ইবনুচ্চালতকে নির্দেশ দেন তাদের হাত কেটে দিতে। সে যখন হুকুম তামিল করতে এগিয়ে গেল, ওমর (রাঃ) তাকে থামলেন এবং বললেন, “শোন আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা ঐ গোলামদের থেকে প্রচুর পরিশ্রম নিয়ে থাক অথচ তাদেরকে অভুক্ত রাখ? এমনকি তাদের ক্ষুধা এতো তীব্র হয় যে তারা হারাম জিনিস খেলেও তা বৈধ হয়। আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, এটা জানতে না পারলে আমি ওদের হাত কেটে দিতাম।” অতঃপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেব ইবনে আবি বালতায়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন “আমি ওদের হাত কাটলাম না সত্য, তবে আমি তোমার ওপর এমন জরিমানা ধার্য করবো যে তুমি মজা টের পাবে।” তিনি মোজাইনা গোত্রীয় লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার উটের দাম কত?” সে বললো, “চারশো দিরহাম”। ওমর (রাঃ) ইবনে হাতেবকে বললেন, “যাও ওকে আটশো দিরহাম দিয়ে যাও।” তিনি গোলামদের চুরির শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন। কেননা তাদের মনিব তাদেরকে অভুক্ত রেখে চুরি করতে বাধ্য করেছিল।
ইসলামের ইতিহাসে সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মর্যাদা অন্য এক দিক দিয়েও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। সে দিকটি হচ্ছে তার সার্বজনীনতা। কেননা ইসলামের গণ্ডি পেরিয়েও এ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকে।
একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক অন্ধ বৃদ্ধকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখেন। জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন যে, সে ইহুদি। তিনি তার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি ভিক্ষা করছ কেন?” সে বলল, “জিজিয়া, অভাব ও বার্ধক্য- এই তিনে মিলে আমাকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করেছে।” হযরত ওমর (রাঃ) তাকে হাত ধরে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ দিলেন। অতঃপর বায়তুল মালের তত্তাবাধায়ককে বলে পাঠালেন, এই ব্যক্তি এবং এর মত অন্যান্য লোকদের খোঁজ নাও। খোদার শপথ, এটা আদৌ ইনসাফের কথা নয় যে, যৌবনে আমরা তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবো আর বার্ধক্যে তাকে অবজ্ঞাভরে তাড়িয়ে দেব। যাকাত দরিদ্র ও সর্বহারাদের প্রাপ্য। আর এ লোকটি আহলে কিতাবের একজন সর্বহারা। তিনি তার এবং তার মত অন্যান্য লোকদের জিজিয়া মওকুফ করে দেন।
দামেষ্ক সফরের সময়ে তিনি একটি গ্রামের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তিনি জানতে পারেন যে, সেখানে কতিপয় খ্রিষ্টান কুষ্ঠরোগী বাস করে। তিনি তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে সাহায্য দান এবং তাদের জন্য রেশনে খাদ্য সরবারাহ করার নির্দেশ দেন।
তেরশো বছরেরও বেশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাণশক্তি ওমরকে মানবতার সেই সুমহান স্তরে অধিষ্ঠিত করেছিল, যেখান থেকে তিনি সামাজিক নিরাপত্তাকে একটি সার্বজনীন মানবাধিকারের মর্যাদা দান করেন। এই অধিকার অর্জনের জন্য কোন বিশেষ ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের শর্ত ছিল না- কোন শরিয়ত এবং কি আকিদার অনুসারী তাও দেখার প্রয়োজন ছিলা না।
এটা হচ্ছে সেই সু-উচ্চ স্তর যেখানে পোঁছাতে মানবতার পদদ্বয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং সে এখনো তা থেকে বহু দূরে রয়েছে।
রাজনৈতিক ব্যবস্থা
ইতিহাস সাক্ষী যে, একটি সু-সংহত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে ইসলামের একটি দুর্লভ ও আদর্শ যুগ অতিবাহিত হয়েছে। নিদারুন পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলামের এ যুগ বেশী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। আগামীতে আমরা এর প্রকৃত কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করবো। কোন কোন ব্যক্তির ধারণা এই যে, এই কারণ স্বয়ং ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কারণ তার অভ্যন্তরেই নিহিত না বাইরে- তা আমরা পরে আলোচনা করবো। প্রথমে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো। কেননা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবসময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন এবং তার প্রকৃতির অনুসারী হয়ে থাকে।
নবী করিম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামাজের ইমামতী করার নির্দেশ দিলেন। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই যুক্তি দেখিয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করেন যে, আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয় অত্যন্ত কোমল। তাই নামাজের ইমামতি করলে লোকেরা তার আওয়াজ শুনতে পাবে না, তাঁকে তার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেন। এতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রেগে যান এবং আবু বকর (রাঃ)-কে ইমামতী করার জন্য ডেকে আনার ওপর জোর দেন।
প্রশ্ন এই যে, এর অর্থ কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খলিফা নিযুক্ত করে গেছেন? মুসলমানরা কি এ দ্বারা স্পষ্টতঃ তাই বুঝেছিলেন?
আমাদের মতে এ দু’টোই নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যদি খলিফা নিযুক্ত করে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করতেন এবং ইসলামে যদি খলিফা মনোনীত করার বিধানই থাকতো তাহলে তিনি যেমন ইসলামের অন্যান্য বিধি ও নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, এটাও সেরূপ করতেন। আর মুসলমানরাও যদি স্পষ্ট বুঝে থাকতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু বকরকে খলিফা নিযুক্ত করে গেছেন- তাহলে সাকিফা নামক স্থানে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে খলিফা নিয়ে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তার প্রশ্নই উঠতো না। কারন আনাসাররা কখনো রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সিদ্ধান্তে আপত্তি করার মত লোক ছিলেন না।
প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের গোটা ব্যাপারটাকেই মুসলামানদের পারস্পরিক পরামর্শের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়ছে। লোকেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্মতির সাথে খেলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন করবে- এটাই ছিল উদ্দেশ্য। সাকিফায় অনুষ্ঠিত আলোচনার পর যদি এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যে, খলিফা মুহাজেরদের মধ্যে থেকে হবে- তাহলে সেটা ইসলামের কোন নির্দিষ্ট বিধান ছিল না বরং মুসলমানদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটা সিদ্ধান্ত। আনসাররা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তাতে কেউ আপত্তি করতে পারতো না। কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছিল তাহলো এই যে, আনসাররা হযরত আবু বকরের খেলাফতে সম্মত হয়ে যান। কেননা তিনি অন্য সকলের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য মদিনায় আওস ও খাযরাজ গোত্র আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ উস্কিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা ঘোলাটে করতে চেয়েছিল কিন্তু আনসাররা সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন।
এ ক্ষেত্রে খলিফা মোহাজেরদের মধ্য থেকে হবে, এ সিদ্ধান্তের অর্থ এই নয় যে খলিফা কোরেশ বংশের মধ্য থেকেই হতে হবে, যদি তাই হতো তাহলে হযরত ওমর রাঃ পরামর্শ পরিষদ নিযুক্ত করার সময় বলতেন না যে, “হোজায়ফার গোলাম সালেম জীবিত থাকলে আমি তাকে খলিফা নিযুক্ত করতাম।” জানা কথা যে, সালেম (রাঃ) কোরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তাছাড়া ইসলামের মূলনীতি অনুসারেও কোন কোরেশীকে শুধু ‘কোরেশী’ এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ-
-------এরাবিক টেক্সট------
“যার কার্যকালাপ তাঁকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ-মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না।”
হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কে খলিফা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি মুসলমানদেরকে বাধ্য করে গিয়েছিলেন। তার এই নিয়োগকে রদ করার পূর্ণ অধিকার তাদের ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) আবুবকরের নিয়োগের ফলে নয় বরং লোকদের নির্বাচনের ফলেই খলিফা হয়েছিলেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদকে নিজেদের মধ্য হতে একজনকে খলিফা নির্বাচনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু মুসলমানদের ওপর সেই ছয়জনের একজনকে খলিফা মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না। তার সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে নির্বাচিত করেন। কারন প্রকৃতপক্ষে তখনকার মুসলিম উম্মতের মধ্যে ঐ ছয় জনই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাক্তি ছিলেন।
হযরত আলীর রাঃ নির্বাচনের সময় মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদের দরুন প্রথম বারের মত মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এর পরিণামেই একে একে এমন সব হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয় যে, ইসলামের প্রাণশক্তি, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূলনীতি এবং জীবনের অন্যান্য বিভাগে তার প্রবর্তিত চিন্তাধারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের আসল মতাদর্শ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেটা হচ্ছে এই যে,কেবলমাত্র মুসলমানদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতেই কোন ব্যাক্তি শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচাত ভাই, তার জামাতা, তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। এসব জেনে বুঝেও মুসলমানরা তাঁকে অনেক বিলম্বে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হয়তো বা হযরত আলীকে এরূপ বিলম্বিত করা বিশেষতঃ হযরত ওমরের পর-তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করারই নামান্তর। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই বিলম্ব দ্বারাই ইসলামের শাসন পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা নিখুঁত মূল্যায়ণ সম্ভব হয়েছে। এতে করে এই বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়েছে যে উত্তারাধিকারের ধারণা খেলাফতের আসনের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। কারণ এ ধারণা ইসলামের প্রাণসত্তা ও তার মূলনীতিসমূহ থেকে সবচেয়ে দূরত্বে অবস্থিত। হযরত আলীর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে একটু অবিচার হলেও এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ন যে তার চেয়েও গুরুতর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
এরপরে এল বনু উমাইয়ার যুগ। তারা ইসলামী খেলাফতকে বনু উমাইয়ার বংশের মধ্যে সীমিতই শুধু করলো না বরং এক স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় রূপান্তরিত করলো। এটা ইসলামের শিক্ষার ফল ছিল না বরং এটা ছিল “জাহেলিয়াতের” প্রভাব। জাহেলিয়াতের এই প্রভাব ইসলামের প্রাণশক্তিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।
এখানে ইয়াজিদের নিয়োগ ও বাইয়াত কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল সে সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত পেশ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
সিরিয়ায় ইয়াজিদের পক্ষে ‘বাইয়াত’ (প্রস্তাবিত অথবা মনোনীত খলিফার প্রতি জনগণের আনুগত্য বা সমর্থন ও সম্মতিকে বাইয়াত বলা হয়) গ্রহণের পর মুয়াবিয়া সাইদ ইবনুল আসকে যে প্রকারেই হোক হেজাজবাসীদের সমর্থন আদায় করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু সাইদ ব্যর্থ হন। অতঃপর মুয়াবিয়া স্বয়ং বিপুল সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে মক্কায় যান এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলমানদেরকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ
“দেখ, তোমাদের সাথে আমি যেরূপ ব্যবহার করেছি এবং তোমাদের আত্নীয়তা ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের যেরূপ মর্যাদা রক্ষা করেছি তা তোমরা ভালভাবেই অবগত আছো। ইয়াজিদ তোমাদেরই ভাই-তোমাদের চাচার ছেলে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা ইয়াজিদকে নামে মাত্র খলিফা মেনে নাও। যাবতীয় নিয়োগ-বদলি, রাজস্ব আদায় ও বণ্টন প্রভৃতি কাজ তোমরাই করবে।”
আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) জবাব দিলেন, আপনার জন্য দু’টো পন্থার একটা অনুসরণ করা উচিত, হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন নিজের বংশ বহির্ভূত এক ব্যাক্তির পক্ষে অছিয়ত করেছিলেন তাই করুন, নচেৎ হযরত ওমর (রাঃ) যেমন কোন নিকট আত্নীয় নয় এমন ছয় ব্যাক্তির সমন্বয়ে যে পরিষদ গঠন করেন সেরূপ একটি নিরপেক্ষ পরিষদ গঠন করুন।”
মুয়াবিয়া (রাঃ) ক্রোধে যেন জ্বলে উঠলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কাছে তৃতীয় কোন পন্থা নেই?” ইবনে জোবায়ের বললেন, “না।” মুয়াবিয়া অন্যান্য লোকদের দিকে ফিরে বললেন, “তোমাদের মতামত কি?” সকলে একযোগে বললেন, “ইবনে জোবায়ের যা বলেছেন আমাদের বক্তব্যও তাই।” তখন মুয়াবিয়া (রাঃ) তাদেরকে হুমকি দিয়ে বললেন, “কোন চরম পন্থা অবলম্বন করার আগে হুশিয়ারী সংকেত দিলে পরে আর আপত্তির অবকাশ থাকে না। আমি তোমাদের সামনে ভাষণ দিলাম সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের একজন দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমার কথার প্রতিবাদ করলো। আমি এটা বরদাশ্ত করলাম এবং ক্ষমা করে দিলাম।
কিন্তু এখন আমি একটি চূড়ান্ত কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমি হুশিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের কেউ যদি এর জবাবে একটি কোথাও বলে, তবে দ্বিতীয় কোন কথা কর্ণগোচর হবার আগেই তরবারী তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলবে। এখন প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করার চিন্তা করা উচিত।
এরপর মোয়াবিয়ার দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ইয়াজিদের মননোয়নের বিরোধী হেজাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগনের মস্তকোপরি উলঙ্গ তরবারীধারী দুজন করে লোক নিযুক্ত করে মুয়াবিয়া অধিনায়ককে নির্দেশ দেন যে ওদের কেউ যদি আমার ঘোষণার সমর্থনে অথবা প্রতিবাদে একটি বাক্যও উচ্চারণ করে তবে উভয় যেন একযোগে তরবারি দিয়ে আঘাত করে।
এই ব্যবস্থা করার পর মুয়াবিয়া মিম্বারে আরোহণপূর্বক বললেন, “এই ব্যক্তিগণ হচ্ছেন মুসলমানদের নেতা এবং তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, এদের মতামত ছাড়া কোন কিছু করা উচিত নয়। এরা ইয়াজিদের খেলাফতে সম্মত হয়ে ‘বাইয়াত’ করেছেন তোমরাও আল্লাহর নাম নিয়ে বাইয়াত কর। সংগে সংগে লোকেরা ‘বাইয়াত’ করলো। [ইবনুল আমীর, হাওয়াদেস হিঃ ৫৬। আমরা এই বর্ণনাতে সত্য বলে গ্রহণ করার ব্যাপারে বেশী জোর দেয়া পছন্দ করি না। কিন্তু ইসলামের মূলনীতিকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটুকু নিশ্চয়ই বলবো যে, এই রেওয়ায়েত যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ ধরণের কাজ ইসলামের মূল প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। কোন যুক্তি কিংবা ওজর আপত্তি এ কাজকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারে না। - গ্রন্থকার]
এই হচ্ছে ইয়াজিদ সরকারের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে ইসলাম কখনো মেনে নিতে পারে না। আর স্বয়ং ইয়াজিদ কি ধরনের লোক ছিল? তার সম্পর্কে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালার (রাঃ) বিবরণ লক্ষ্যণীয়।
“খোদার শপথ! আমরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে তখন আন্দোলন শুরু করি যখন আমাদের আশংকা হয় যে আমাদের ওপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি হবে। এই ব্যক্তি মা ও কন্যা এবং একাধিক বোনকে এক সাথে বিয়ে করে, মদ পান করে, নামাজ পরিত্যাগ করে। খোদার শপথ! অন্য কোন লোক আমার সাথী না হলেও আমি একাই আল্লাহর পথে কোরবানী দিতাম।”
হয়তো বা এটা ইয়াজিদের একজন দুশমনের অতিরঞ্জিত কথা। কিন্তু পরে ইয়াজিদ যে সব জঘন্য কাজ করেছিল যথাঃ হযরত হোসাইন (রাঃ) কে এমন নিকৃষ্ট পন্থায় হত্যা করা, কাবা শরীফ ঘেরাও এবং তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে ইয়াজিদের দুশমনেরা আদৌ অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেয়নি। প্রকৃত অবস্থা যাই থাক না কেন মুসলমানদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেইনদের উপস্থিতি সত্ত্বেও ইয়াজিদই খেলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল- এ কথা দাবি করার ধৃষ্ঠতা কেউ দেখাতে পারে না। মূলতঃ এ সবের লক্ষ্য ছিল সরকারকে শুধু উমাইয়া বংশের মধ্যে সীমিত করা এবং তাকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। এ প্রবণতা ইসলাম ও ইসলামী বিধানের বুকে ছুরিকাঘাতের সমতুল্য ছিল।
এ তথ্যগুলো আমাদের পরিবেশন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তির নিন্দা করা নয়, বরং ইসলামে যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন শরিয়ত সম্মত সনদ ছাড়াই শুরু করা হয়, তার সাথে ইসলামের প্রাণশক্তি ও মূলনীতির যে কোনই সম্পর্ক নেই, তা স্পষ্ট করে দেখানো। ইসলামকে ও ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত ও আসল স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য আমাদের এ আলোচনার অবতারণা।
শাসন পদ্ধতির কতিপয় নমুনা
এই সত্যের সঠিক উপলব্ধির ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য আমরা খেলাফতে রাশেদার বিভিন্ন যুগ যথাঃ হযরত আবু বকর ও ওমরের যুগ, হযরত ওসমান ও মারওয়ানের যুগ, অতঃপর হযরত আলীর যুগ এবং এমনিভাবে আব্বাসী ও উমাইয়া যুগ থেকে শাসন পদ্ধতির কতপয় বাস্তব নমুনা পেশ করার চেষ্টা করবো।
যখন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খেলাফতের আসনে অভিষিক্ত করেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতে মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়তকে বাস্তবায়িত করা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। এ ধরনের কোন চিন্তা তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি যে, ইতিপূর্বে সাধারণ নাগরিক হিসেবে তার ওপর যে সব কাজ হারাম ছিল এখন তা এ পদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। অথবা আগে যে সব অধিকার ছিল না, তেমন কোন নতুন অধিকার তিনি পাচ্ছেন কিংবা তার ওপর যে সব দায়েত্ব ও কর্তব্য এতদিন ছিল, এখন তা থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।
সাকিফায় যখন তার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তখন তিনি নিম্নরূপ ভঅষণ দেন, “আমি যদি আমার দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালন করি তাহলে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আর যদি আমি বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করি তাহলে তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে। সত্যবাদিতা হচ্ছে বিশ্বস্ততা আর মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে দুর্বল, সে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সবল– যাবত আমি তাকে তার অধিকার না দিয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, সে আমার নিকট সবচেয়ে দুর্বল– যাবত আমি তার নিকট থেকে রাষ্ট্রের অধিকার আদায় করি। মনে রেখো, কোন জাতি যখনি জেহাদ থেকে পিছপা হয়, তখনই আল্লাহ তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন। যখনি কোন জাতি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই আল্লাহ তায়ালা সকলের ওপর পাইকারীভাবে আজাব নাজিল করেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করতে থাকবো, ততক্ষণ তোমরা আমার আদেশ মান্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হই, তখন তোমাদের ওপর আমার আদেশ পালনের দায়িত্ব থাকবে না।”
হযরত আবু বকরের বাড়ী মদিনার পার্শ্ববর্তী “সানহে” অবস্থিত ছিল। একটা ক্ষুদ্র মামুলী ধরণের বাড়ী। খলিফা হবার পরও তিনি সে বাড়ী মেরামতও করাননি। সেই বাড়ী থেকে মদিনা পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে পদব্রজে আসা-যাওয়া করতেন। কখনো কখনো একটা ঘোড়া ব্যবহার করতেন কিন্তু সেটা বাইতুল মালের ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত। পরে কাজের চাপ বেড়ে গেলে তিনি মদিনায় চলে আসেন।
তিনি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলিফা নির্বাচিত হবার পরের দিন যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন, তখন মুসলমানরা তাকে থামিয়ে বললেন, “খেলাফতের দায়িত্ব ব্যাবসা-বানিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পালন করা যাবে না।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি যখন জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন পন্থা জানি না তখন আমার চলবে কি করে?” সবাই তার বিষয় বিবেচনা করলেন এবং তার ব্যবসায় করতে না পারা ও খেলাফতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে ‘বাইতুল মাল’ থেকে তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান বেতন নির্ধারণ করেন।
এ সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুকালে অছিয়ত করেন যে তিনি ‘বাইতুল মাল’ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা যেন হিসাব করে তার জমি-জমা ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে গ্রহণ করে বাইতুল মালে জমা দেয়া হয়।
ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিবেক ও মন-মগজে যে চেতনা ও দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলে তারই প্রভাবাধীনে উজ্জীবিত হয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিটি প্রজার অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী মনে করতেন। তিনি সানহে অবস্থানকালে তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল ও অসহায় প্রতিবেশীদের ছাগলের দুধ প্রতিদিন দুইয়ে দিতেন। যখন তিনি খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর প্রতিবেশীর একটি শিশু মেয়ে তাকে বলে, “এখনতো আপনি আর আমাদের ছাগল দুইয়ে দেবেন না, তাই না?” আবু বকর (রাঃ) বলেন, “কেন দেব না? নিশ্চয় দুইয়ে দেব।” তিনি যথার্থই তাদের দুধ দুইয়ে দেয়া অব্যহত রাখলেন। কখনো কখনো ছাগলের মালিক বালিকাকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, ‘খালি দুধ দুইয়ে দেব, না মাখনও বের করবো?” কখনো সে বলতো, “মাখন বের করে দাও।” আবার কখনো বলতো, “খালি দুধ রেখে দাও।” মোট কথা সে যা বলতো, তিনি তাই করতেন।
হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে হযরত ওমর (রাঃ) মদিনায় একটি অন্ধ মহিলার তত্বাবধান করতেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখেন, তিনি যাওয়ার আগেই কে এসে মহিলাটির কাজ করে দিয়ে যায়। এরূপ প্রতিদিন হতে লাগলো। একদিন গোপনে লুকিয়ে বসে থাকেন। দেখেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে মহিলাটির সব কাজ করে দিয়ে যান। খেলাফত এবং তার গুরুদায়িত্ব তাকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। তাকে দেখামাত্র হযরত ওমর (রাঃ) চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ “নিশ্চয়ই আপনি। খোদার শপথ আপনিই (প্রতিদিন এই কাজ করে থাকেন)।”
এটা হল হযরত আবু বকরের শাসন নীতির কয়েকটা সাধারণ নমুনা! তার স্থলে যখন হযরত ওমর এলেন তখনও এই নীতি অক্ষুন্ন ছিল। ওমর (রাঃ) কখনো খেলাফতকে নিজের একটা বাড়তি অধিকার হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে বাড়তি দায়িত্ব অবশ্যই মনে করেছেন। বলা বাহুল্য সে দায়িত্ব আল্লাহর আইন জারী করা ছাড়া আর কিছু নয়।
‘বাইয়াত’ অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে বলেন, “ভাই সব! আমি তোমাদেরই একজন। তার চেয়ে বেশী কিছু নই। যদি খলিফাতুর রসূলের (হযরত আবু বকর) অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সংগত হতো তাহলে আমি কিছুতেই তোমাদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না।”
অপর এক ভাষণে তিনি বলেন, “আমার ওপর তোমাদের সম্পর্কে কতিপয় দায়িত্ব অর্পিত আছে সেগুলো আমি উল্লেখ করছি। ওগুলো সম্পর্কে তোমরা সব সময় আমার কাছে হিসাব চাইবে। তোমাদের খাজনা ও কর আদায় করা আমার দায়িত্ব। আমি তোমাদের মধ্যে সততার সাথে ধন বন্টন করবো, তোমাদেরকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করবো না, বেশীদিন সীমন্ত রাখবো না এবং যুদ্ধের জন্যে বিদেশে থাকাকালে তোমাদের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করবো।”
তিনি বলতেন, “আমি আল্লাহর মালকে নিজের পক্ষে ইয়াতিমের মালের সমতুল্য মনে করি। প্রয়োজন না হলে স্পর্শ করবো না আর প্রয়োজন হলে সততার সাথে গ্রহণ করবো।”
একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, “আল্লাহর মাল থেকে আপনি কতটুকু গ্রহণ করা নিজের পক্ষে বৈধ মনে করেন?” তিনি উত্তরে বলেন, “শীত ও গ্রীষ্মের জন্য দু’খানা কাপড়, হজ্জ-ওমরার জন্যে সওয়ারীর জন্তু এবং কোরেশের কোন মাঝারী পরিবারের সমমানের খাদ্য আমার পরিবারবর্গের জন্য। এর পরে আমি সাধারণ মুসলমানের মতই একজন মুসলমান। তারা যা পাবে আমিও তাই পাব।”
সাধারণত তিনি এভাবেই জীবন যাপন করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি নিজের জন্য যা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তার ব্যাপারেও অসাধারণ কঠোরতা প্রয়োগ করতেন। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য মধু ব্যবহার করতে বলা হল।
বাইতুল মালে প্রচুর মধু ছিল। তিনি মিম্বরে আরোহন করে বললেন : “তোমরা অনুমতি দিলে মধু ব্যবহার করতে পারি নইলে এটা আমার জন্য হারাম।” তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সবাই অনুমতি দিয়ে দিল।
মুসলমানরা হযরত ওমরের এই কঠোরতা দেখে তাঁর কন্যা উম্মুল মোমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট গিয়ে বললেন, “ওমর (রাঃ) নিজের ব্যাপারে কৃচ্ছতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। বর্তমান সময়ে আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছলতা দান করেছেন। যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে তাঁর ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত গ্রহণ করা উচিত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের এরূপ করার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে।” হযরত হাফসা (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ) কে এ কথা বললেন তখন তিনি জবাব দিলেন, “হাফসা, তুমি তোমার জাতির পক্ষপাতিত্ব করেছ আর নিজের পিতার সাথে অহিতাকাঙ্খী সুলভ আচরণ করেছ। আমার পরিবারভুক্ত লোকদের আমার জান ও মালে অধিকার রয়েছে, কিন্তু আমার ধর্ম ও আমানতদারীতে কোন অধিকার নেই।”
তিনি নিজের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে সাম্যের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। যখন বিখ্যাত আমুর রামাদা’র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তখন হযরত ওমর (রাঃ) শপথ করেন যে যতদিন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন তিনি ঘি ও গোশত স্পর্শ করবেন না। তিনি এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ফলে তেল খেতে খেতে তার শরীরের চামড়া শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর বাজার দুটো পাত্রে দুধ ও ঘি বিক্রি হতে দেখা গেল। হযরত ওমরের জনৈক ভৃত্য চল্লিশ দিরহাম দ্বারা তা কিনে নিয়ে এল। সে এসে তাকে বললো, এখন আল্লাহ আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দিয়েছেন। বাজারে দুধ ও ঘি বিক্রির জন্য এসেছে, আমি তা কিনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যখন তিনি তার দাম জানতে পারলেন তখন বললেন, “খুব চড়া দামে কিনেছ দু’টোই সদকা করে দাও। আমি অপব্যয় করে খাওয়া পছন্দ করি না।” মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতপঃর বললেন, “জনগণের যে দুরবস্থা হয় তা যদি আমারও না হয় তাহলে তাদের সমস্যার গুরুত্ব আমি কি করে বুঝবো।”
ওমর (রাঃ) এর মত ছিল যে জিনিস থেকে প্রজারা বঞ্চিত তা থেকে তার নিজেরও বঞ্চিত হওয়া উচিত। যেমন তিনি নিজেই বলেছিলেন, তার মনের কোন কোণেও এরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল না যে, খেলাফতের পদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি কোনরূপ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে এ ব্যাপারে তিনি যদি সাম্য ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হন তাহলে জনগণের আনুগত্য লাভের কোন অধিকারই তার থাকবে না। এ থেকে ইসলামের রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা যায়। তা হচ্ছে এই যে, কোন শাসক আল্লাহর আইন কার্যকর করা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজের বিচার ফায়সালায় ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি রক্ষা না করলে আনুগত্য লাভের যোগ্য হতে পারে না। হযরত ওমর (রাঃ) এর মনে ইসলামের এই মূলনীতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল এবং এ সম্পর্কে অনুভুতি সবসময় জাগরূক থাকত।
একবার তিনি এক ব্যক্তির সাথে একটি ঘোড়ার দরদস্তুর করেন। এরপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সেটায় সওয়ার হয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন। ইত্যবসরে ঘোড়া ঠোকর খেয়ে পড়ে যায় এবং আহত হয়। তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মালিক ঘোড়া ফেরত নিতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে মোকদ্দমা নিয়ে বিচারপতি শোরাইহের আদালতে গিয়ে হাজির হলেন। শোরাইহ উভয় পক্ষের বিবৃতি শ্রবণের পর বললেন, “আমিরুল মোমিনীন! আপনি যে জিনিস কিনেছেন তা নিয়ে নিন। নচেৎ ওটা যে অবস্থায় নিয়েছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিন।” ওমর বে-ইখতিয়ার বলে ওঠলেন, “একেই বলে ন্যায় বিচার।” অতঃপর তিনি শোরাইহকে তার ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে কুফার বিচারপতি নিযুক্ত করেন।
যখন হযরত ওমরের নীতি নিজের ব্যাপারে এতটাই কঠিন ছিল তখন খলিফার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য নাগরিকের বেলায় কোন বৈষম্যমূলক আচরণের তো প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণ স্বরূপ, যখন তার পুত্র আব্দুর রহমান মদ পান করেন তখন তার ওপর ইসলামী দন্ড কার্যকর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে তার ঘটনা সর্বজন বিদিত। এমনিভাবে আমর ইবনুল আসের পুত্র জনৈক মিশরীয় বালকের ওপর অত্যাচার করলে তাকে শরীয়তের দন্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়।
কর্মচারীদের ব্যাপারে তার নীতি ছিল, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের নিকট যে অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যেত, সে সম্পর্কে তাদের জবাবদিহী করতে হতো। মুসলমানদের ক্ষতি করে কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঐ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে পুংখানুপুংখরূপে তদন্ত করা হতো। “সম্পদ কিভাবে অর্জিত হলো?” – এটা ছিল একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং এ অনুসারে তিনি যখনই কোন কর্মচারীর মধ্যে দুর্নীতির সন্দেহ বোধ করেছেন তখনই কৈফিয়ত তলব করেছেন। মিশরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আসের অর্ধেক সম্পত্তি এই অনুসারেই বাজেয়াপ্ত করে বাইতুল মালে জমা করা হয়। কুফাস্থ প্রতিনিধি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথেও তিনি এ নীতি অবলম্বন করেন। এমনিভাবে বাহরাইনের শাসনকর্তা হযরত আবু হোরাইরার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।
হযরত ওমরের রাজনীতির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, প্রজার ইসলামের চতুর্সীমার মধ্যে থেকে সরকারের আনুগত্য ও হিত কামনা করবে, আর সরকার করবে ন্যায় বিচার ও সর্বাঙ্গীন জনকল্যাণ। এ জন্যই তিনি তার একজন সাধারণ প্রজার এ উক্তি স্বীকার করেন যে, “যদি তোমার মধ্যে আমরা গোমরাহী দেখি তবে আমরা তরবারী দ্বারা সোজা করে দেব।” অর্থাৎ তিনি মেনে নিলেন যে প্রজাদের শাসকের সমালোচনা ও সংশোধনের অধিকার রয়েছে। একদিন তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “তোমাদের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের ওপর অযথা হস্তক্ষেপের জন্যে আমি কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করিনি। তাদেরকে নিয়োগ করেছি তোমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব শিক্ষাদানের জন্য। যদি কোন কর্মচারী কারও ওপর জুলুম অত্যাচার করে তবে আমি তা কিছুতেই বরদাশ্ত করবো না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তার সম্পর্কে আমার নিকট অভিযোগ আনা উচিত।” এ ভাবে তিনি কর্মচারীদের জন্য তাদের ক্ষমতার সীমারেখা নির্দেশ করেন এবং তা লংঘন করতে নিষেধ করে দেন।
শাসকের এহেন গুরুদায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি খাত্তাবের বংশধরদের মধ্য থেকে দ্বিতীয় কোন খলিফা নির্বাচিত হওয়া পছন্দ করেননি। তিনি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে যান যে আব্দুল্লাহকে যেন খলিফা নির্বাচিত করা না হয়। অবশ্য তিনি তাকে পরামর্শ পরিষদে শামিল করেন। এ সময় তিনি যে উক্তি করেন, তা খেলাফত সম্পর্কে তার ধারণার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি বলেন,
“আমরা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করার আদৌ কোন অভিলাষ পোষণ করি না। আমি নিজেও এটা করে সুখী হইনি। তাই আমার বংশধরের মধ্যে আর কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক তাও আমি চাই না। এটা যদি সত্যই ভালভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা সকলে তার নায্য অংশ পেয়েছি। অন্যথায় সমগ্র বংশের মধ্যে একলা ওমরের জবাবদিহী করাই যথেষ্ট।”
হযরত ওসমানের শাসন পদ্ধতি
সন্দেহ নেই, শাসন পদ্ধতি সম্পর্কিত এ ধারণা হযরত ওসমানের (রাঃ) আমলে খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ পরিবর্তন সত্ত্বেও সেটা সামগ্রিকভাবে ইসলামের আওতাভূক্ত থাকে।
হযরত ওসমান (রাঃ) যখন অশীতিপর বৃদ্ধ তখন তার ওপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। মারওয়ান তার বার্ধক্যের সুযোগ গ্রহণ করে বহু বিষয়ে ইসলামের পরিপন্থী নীতি অবলম্বন করে। ওদিকে হযরত ওসমানের কোমলচিত্ততা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার অস্বাভাবিক প্রীতি ও স্নেহ এই দু’টোর কারণে এমন কতিপয় পদক্ষেপ গৃহীত হয় যা সাহাবাদের নিকট বিশেষ আপত্তিজনক বলে মনে হয়। এই পদক্ষেপগুলোর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে ভয়াবহ গোলযোগ ও বিশৃংখলা দেখা দেয় তা ইসলামকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
হযরত ওসমান (রাঃ) এর স্বীয় জামাতা হারেস ইবনে হাকামকে তার বিয়ের দিন বাইতুল মাল থেকে দু’লাখ দিরহাম দান করেন। পরদিন প্রাতে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বিষন্ন বদনে অশ্রুসজল নয়নে খলিফার নিকট এসে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিতে অনুরোধ করেন। তিনি তার নিকট কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে মুসলমানদের ধনাগার থেকে তার জামাতাকে দান করার কারণেই তিনি ইস্তফা দিতে চান। হযরত ওসমান (রাঃ) বিস্ময়ের সাথে বললেন, “ইবনে আরকাম। আমি আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করেছি এজন্য তুমি কাঁদছো? ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে সুতীব্র অনুভূতির অধিকারী সেই ব্যক্তি এ প্রশ্নের উত্তরে যে জবাব দিলেন তা হলো, “না, আমীরুল মুমিনীন! কথা সেটা নয়, আমি এ চিন্তা করে কাঁদছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশায় মুসলমানদের জন্য যে বিপুল অর্থ দান করতেন তারই প্রতিদান হিসেবে এ অর্থ গ্রহণ করলেন না তো? খোদার শপথ করে বলছি, আপনি তাকে একশো দিরহাম দিলেও তা বেশী হতো। খলিফার আত্মীয়-স্বজনের জন্য একশো দিরহাম ব্যয় করাকেও যার বিবেক সংগত মনে করতো না- সেই ব্যক্তির ওপর হযরত ওসমান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং বলেন, “ইবনে আরকাম! তুমি চাবি রেখে যাও। আমি অন্য লোক অবশ্যই পাব।”
এই ধরনের দৃষ্টান্ত হযরত ওসমানের মধ্যে বহু দেখা যায়। একবার তিনি জুবায়েরকে ছ’লাখ, তালহাকে দু’লাখ এবং মারওয়ান ইবনে হাকামকে আফ্রিকার এক পঞ্চমাংশ প্রদান করেন। এতে হযরত আলীর নেতৃত্বাধীন সাহাবাদের একটি দল প্রবল আপত্তি তুললে খলিফা জবাব দেন, “আমার অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে এবং তাদের সাথে আমার সহৃদয় ব্যবহার করা উচিত।” লোকেরা এই জবাবকে আরো আপত্তিকর আখ্যায়িত করে প্রশ্ন করলেন “হযরত আবু বকর ও ওমরের কি আত্মীয়-স্বজন ছিল না?” হযরত ওসমান (রাঃ) জবাব দিলেন, “আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চিত করে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করতেন আর আমি তাদেরকে দান করে পূণ্য অর্জন করতে চাই।” এতে তারা রাগান্বিত হয়ে উঠে চলে এলেন এবং বললেন, “খোদার শপথ! যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেই দু’জনের নীতিই আমাদের নিকট আপনার নীতির চেয়ে অধিক প্রিয়।”
ধন-সম্পদ ছাড়া পদ ও চাকুরীর অবস্থা ছিল এই যে, ওসমানের (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনের ওপর তা বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়েছিল। এদেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া। ওসমান (রাঃ) মুয়াবিয়ার রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে ফিলিস্তিন ও হেমসকেও তার অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাকে সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বানিয়ে দেন এবং তিনি যাতে সমগ্র আর্থিক ও সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে হযরত আলীর মোকাবিলায় খেলাফতের দাবীদার হয়ে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য তার পথ খোলাসা করে দেন। চাকুরীর সুবিধা লাভকারী এই সব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রত্যাখ্যাত হাকাম ইবনে আস, তার পুত্র মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং তার দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবিচ্ছারাহ অন্যতম ছিলেন। মারওয়ানকে তিনি নিজের প্রধান উজীরের পদে অধিষ্ঠিত করেন।
সাহাবারা এই সব কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিনতির কথা চিন্তা করে বারবার মদিনায় ছুটে আসতেন এবং ইসলামী রীতি-নীতিকে বিকৃতির হাত থেকে এবং খলিফাতুল মুসলেমীনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু খলিফার অবস্থা এই যে, বার্ধক্য ও দুর্বলতার দরুন মারওয়ানের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ কথা ঠিক যে হযরত ওসমান (রাঃ) এর মধ্যে ইসলামী ভাবধারার অবস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ অথবা কোন অভিযোগ আরোপ করার অবকাশ নেই। কিন্তু সংগে সংগে তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলাও কঠিন। ভুল-ভ্রান্তির কারণ আমাদের মতে মারওয়ানের ওজারত এবং হযরত ওসমানের বার্ধক্যজনিত মানসিক অস্বাভাবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।
একবার জনগণ সমবেত হয়ে হযরত আলীকে হযরত ওসমানের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে বলেনঃ
“আমি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। তারা আমার নিকট আপনার সম্পর্কে নানা কথা বলেছে। কিন্তু আমি আপনাকে কি বলব তা বুঝতেই পারছি না। আমি যা জানি তা আপনার অজানা নয়। আপনাকে কোন কথা বুঝানোরও সাধ্য আমার নেই। কেননা আপনি নিজেই সব কিছু বুঝতে পারেন। আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমাদের কারও নেই। ইসলাম সম্পর্কে আপনার আগে আমরা কোন জ্ঞান অর্জন করিনি। এমন কোন তথ্য নেই যা শুধু আমরা জানি এবং আপনার নিকট তা এখন পৌঁছানোর প্রয়োজন হতে পারে। কোন কথাই আপনার কাছ থেকে গোপন করে আমাদেরকে শিখানো হয়নি। আপনি রাসূল (সাঃ) কে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তার সাহচর্যে অবস্থান করেছেন এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আপনার চাইতে বেশী কল্যাণের নিকটবর্তীয় ছিল না। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়েও যেমন, আবার শ্বশুর জামাতা সম্পর্কেও তেমন- আপনি তাদের উভয়ের চাইতে রাসূলুল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। তাদের কেউ এ ব্যাপারে আপনার চাইতে অগ্রগামী ছিল না। সুতরাং নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনা কিংবা অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে আনার কোনই প্রয়োজন নেই। সঠিক পথ সম্পূর্ণ উজ্জল ও স্পষ্ট। ইসলামের নিদর্শন সমূহ এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওসমান! জেনে রাখুন! যে ন্যায়পরায়ণ শাসক নিজেও সুপথে থাকে, অপরকেও পরিচালিত করে, সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত এবং বেদা’তকে বিলুপ্ত করে- সেই হলো আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি। খোদার শপথ! সব কিছুই স্পষ্ট। আল্লাহর নীতি এখনো প্রতিষ্ঠিত এবং তার পতাকা এখনো উড্ডীন। আল্লাহর নিকট সবচাইতে অধম ব্যক্তি হচ্ছে সেই, যে সুন্নাতকে বিলুপ্ত এবং বেদা’তকে প্রচলিত করে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন জালেম শাসককে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় হাজির করা হবে। তার ওজর-আপত্তি শ্রবণ করা হবে না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” (তাবারী)
হযরত ওসমান (রাঃ) জবাব দিলেন, “আমি জানি, তুমি যা বলেছ লোকেরাও তাই বলে থাকে। শোন! খোদার শপথ করে বলছি, যদি তোমার স্থলে আমি হতাম তাহলে আমি তোমার নিন্দা বা সমালোচনা করতাম না এবং তোমাকে সমালোচনার মুখে অসহায় ছেড়ে দিতাম না। আমি এ আপত্তি তুলতাম না যে, তুমি আত্নীয়-স্বজনের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করলে কেন? গরীব-দুঃখীর সাহায্য করলে কেন? ওমর (রাঃ) যাদেরকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করতেন- তাদেরকে নিয়োগ করলে কেন? আলী! আমি খোদার শপথ দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না- মুগিরা ইবনে শো’বা সেই পদে নিযুক্ত আছে।”
তিনি বললেনঃ “হ্যাঁ জানি।”
ওসমানঃ “জান, তাঁকে হযরত ওমর (রাঃ) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন?”
আলিঃ “হ্যাঁ।”
ওসমানঃ তাহলে আমি যদি আত্মীয়তার জন্য ইবনে আমেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে থাকি তাহলে তোমরা সে জন্য আমাকে সমালোচনা কর কেন?
আলীঃ “আমি আপনাকে আসল ব্যপার বলছি। ওমর (রাঃ) যাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন, ওমরের জুতা তার মস্তকোপরি থাকতো। তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি শুনলেও তৎক্ষণাৎ তাকে হাজির হতে বলতেন এবং তার শেষ মীমাংসা করে তবে ক্ষান্ত হতেন। এই কাজটাই আপনি করেন না। আপনি নিজে দুর্বল হয়ে পরেছেন এবং আত্নীয়-স্বজনের সাথে নম্র ব্যবহার শুরু করেছেন।
ওসমানঃ “আর তোমার আত্মীয়দের সাথেও তো করি।”
আলীঃ “সন্দেহ নেই, তাঁদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ আত্নীয়তা রয়েছে কিন্তু অন্য লোক তাঁদের চেয়ে উত্তম।”
ওসমানঃ “তুমি নিশ্চয় জান, ওমর (রাঃ) তার খেলাফতের গোটা যুগ ধরেই মুয়াবিয়াকে শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। আমিও তো তাকে শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রেখেছি।”
আলীঃ “আমি আপনাকে খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন না যে, ওমরকে গোলাম ‘ইয়ারফা’ যত ভয় করতো, মুয়াবিয়া তার চাইতেও বেশি ভয় করতেন?”
ওসমানঃ “হ্যাঁ”
আলীঃ “কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, মুয়াবিয়া আপনার মতামত না নিয়েই সিদ্ধান্ত করতে থাকেন অথচ আপনি তার খবরও রাখেন না। তিনি নিজের হুকুম কে লোকদের মধ্যে ওসমানের হুকুম বলে চালিয়ে দেন। এ সব ব্যাপার আপনার নিকট পৌঁছায়, কিন্তু আপনি মুয়াবিয়ার উক্তির প্রতিবাদ করেন না”।
শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে এক ভায়াবহ অভ্যুত্থান শুরু হলো- এর মধ্যে সত্য ও অসত্য, ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কার্যকারণ মিশ্রিত ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, এই অভ্যুত্থান মোটামুটিভাবে ইসলামী ভাবধারার একটি গণবিস্ফোরণ ছিল। অবশ্য এই মত প্রকাশ করার সময় আমরা এ সত্য অগ্রাহ্য করছি না যে, এই বিস্ফোরণের পিছনে অভিশপ্ত ইহুদী সন্ত্রাসবাদী নেতা ইবনে সাবারও গোপন হাত সক্রিয় ছিল।
হযরত ওসমানের ওজর হিসেবে আমরা এ কথা পেশ করতে চাই যে, খেলাফতের দায়িত্ব তার ওপর তার শেষ বয়সে এসে অর্পিত হয়। তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ আর উমাইয়া গোত্রের লোকেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছেল। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আলী রা. সবচেয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি যদি ঘরে বসে থাকি তবে তিনি (ওসমান) বলবেন যে, তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ- আমার অধিকার ও সম্পর্ক অগ্রাহ্য করেছো। আর যদি তার সাথে আলাপ-আলোচনা করি, তাহলেও তিনি নিজের খেয়াল-খুশি অনুসারেই কাজ করেন। মারওয়ান তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করায়। রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহচর্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও বার্ধক্যের কারণে তিনি পুরোপুরিভাবে তাদের খপ্পরে পড়ে গেছেন। তারা তাকে যেদিকে ইচ্ছা করে- সেদিকে চালিত করে।’’
বস্তুতঃ তৃতীয় খলিফার বার্ধক্যের সময় এই গতিশীল জীবন ব্যবস্থাটি উমাইয়া চক্রের মুষ্ঠির মধ্যে চলে যাওয়ায় তার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা এর বাস্তব রীতি-পদ্ধতিকে এর আদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার সময় আর দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়নি।
তাঁর দীর্ঘ খেলাফত যুগে উমাইয়া চক্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও মজবুত হয়। তারা সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে ক্ষমতা সু-সংহত করার সুযোগ লাভ করে। তা ছাড়া হযরত ওসমানের অনুসৃত নীতির স্বাভাবিক ফল হিসেবে সম্পদের কেন্দ্রায়ন অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। ফলে তার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান মুসলিম উম্মাতের ভিত্তিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই দুর্বল করে দেয়।
এ যুগের ইতিহাস একদিকে সত্য দ্বীনের কতিপয় দুর্লভ গুণাগুণের স্বাক্ষর বহন করে। অপরদিকে তার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার সম্পর্কে এক প্রবল চিন্তাগত বিপ্লবেরও নিদর্শন বহন করে। অবশ্য যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার বিপজ্জনক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবও কম গুরুতর নয়।
হজরত ওসমানের পর
হজরত ওসমারন রা. যখন ইন্তেকাল করেন তখন কার্যতঃ উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। খলিফা নিজেই তাদেরকে এ সুযোগ সরবরাহ করেন। সারাদেশে বিশেষতঃ সিরিয়ায় তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং অন্যান্য যাবতীয় সম্পদকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে। তারা সৌভ্রাতৃত্ব, অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি কাজকে উপেক্ষা করতে থাকে। আর এ সবই হজরত ওসমানের খেলাফতের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হতে থাকে। এর কারণে মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের প্রণশক্তি ও ভাবধারা অত্যন্ত দুর্বল ও ম্লান হয়ে পড়ে।
খলিফার কতিপয় পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ জনগণের মনে কখনো স্বাভাবিকভাবে আর কখনো অযৌক্তিকভাবে এক তীব্র ও তিক্ত ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা অভিযোগ মুখর হয়ে ওঠে যে, খলিফা নিজের আত্মীয়-স্বজনের সংগে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন এবং তাদের লাখ লাখ দিরহাম উপঢৌকন দেন। তিনি রাসূলুল্লাহর সা. দুশমনদেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করার জন্য তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে অপসারিত করেন এবং আবু জরের রা. মত উন্নত চরিত্রের সাহাবীর ওপর শুধু এ জন্য নির্যাতন চালান যে, তিনি সম্পদের কেন্দ্রায়ন ও উঁচু তলার লোকদের বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের বাড়াবাড়ির বিরোধিতা করেছিলেন। আবু জর রা. দানশীলতা ও সৎপথে ব্যয়ের প্রচলন এবং শালীনতা ও পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছিলেন।
এ সব কার্যকলাপ মুসলমানদেরকে মর্মাহত ও বিচলিত করে তোলে। এ ধরণের প্রবণতা যখন ব্যাপকভঅবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কিছু লোকের মধ্যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আবার কিছু লোকের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। যাদের মনে ইসলামী আদর্শ বদ্ধমূল ছিল তাঁরা এ সব কার্যকলাপ দেখে নীরবতা অবলম্বন করাকে পাপ মনে করতে থাকেন। তাঁদের মনে সৃষ্ট এ ভাবধারা তাঁদেরকে বিদ্রোহ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর যারা ইসলামকে শুধু লেবেল হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের পার্থিব লোভ লালসা তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে, যারা সব সময় বাতাসের দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেন, তাদের চরিত্র উচ্ছৃংখল এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। এহেন পরিস্থিতিই হজরত ওসমানের খেলাফতের অবসান ঘটায়।
হজরত আলী রা. যখন খেলাফতের মসনদে আসীন হলেন, তখন পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা সহজসাধ্য ছিল না। ওসমানের রা. যুগে যারা অবৈধ মুনাফাখোরীতের লিপ্ত ছিল বিশেষতঃ বনু উমাইয়া ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে হজরত আলী রা. তাদের ব্যাপারে নীরব থাকবেন না। এ সব চিন্তা করে তারা নিজ নিজ কল্যাণের খাতিরে মুয়াবিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।
হজরত আলী রা. এই লক্ষ্য নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন যে তিনি জনগণ ও সরকারকে পুনরায় ইসলামের আসল রাজনৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তাঁর স্ত্রী স্ব-হস্তে গম পিষতেন এবং তা-ই তিনি আহার করতেন। একবার তিনি নিজের এক বস্তা গমের ওপর বায়তুল মালে জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী সিল মোহর অংকিত করছিলেন। বললেন, ‘‘আমি নিজের পেটে শুধু তাই প্রবেশ করাতে চাই যার হালাল হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।’’ কখনো কখনো এমন অবস্থা হয়েছে যে, তাঁকে খাদ্য বস্ত্র খরিদ করার জন্য নিজের তরবারী পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। কুফায় তিনি শ্বেত–প্রসাদে অবস্থান করতেন, তিনি কি ধরণের জীবন যাপন করতেন সে সম্পর্কে নজরে ইবনে মানসুরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ
‘‘আমি হজরত আলীর নিকট গিয়ে দেখি, তাঁর সামনে দুর্গন্ধযুক্ত টক দুধ এবং শুকনো রুটি রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনি কি এসব জিনিস খান?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সা. এর চেয়ে শুকনো রুটি এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। আমি যদি তাঁর নীতি অনুসরণ করে না চলি তাহলে আমার আশংকা হয় যে, হয়তো রাসূলুল্লাহর সা. সংগী হতে পারবো না।’’
এমনিভাবে হারুন ইবনে আনতারা বর্ণনা করেছেন যে, আমি খাওরানাক নামক স্থানে হজরত আলীর সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তখন ছিল শীতকাল। হজরত আলীর রা. গায়ে একটা ছিন্ন পুরনো চাদর ছিল এবং তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। আমি বললাম, ‘‘আমিরুল মি’মিনীন! আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের জন্য এই সম্পদে আল্লাহ কিছু অধিকার নির্ধারিত করেছের। তা সত্ত্বেও আপনি নিজের প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করছেন।’’ আলী রা. বললেন, ‘‘খোদার শপথ! আমি তোমাদের হক নষ্ট করব না। এটা আমার সেই চাদর যা আমি মদিনা থেকে এনেছিলাম।’’
অবশ্য হজরত আলী রা. নিজের ও নিজের পরিবার বর্গের ব্যাপারে এরূপ নীতি অবলম্বন করার সময় এ কথা নিশ্চয়ই জানতেন যে, ইসলাম তাকে এর চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণের অনুমতি দেয়। ইসলাম কাউকে সর্ব রকমের আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে নিতান্ত সংসার বিরাগীর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করে না। তিনি জানতেন যে, তখনো একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাইতুল মালের ধন-সম্পদে তার যা প্রাপ্য ছিল তার চাইতে তিনি অনেক কম গ্রহণ করছিলেন। তা ছাড়া জনগণের কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত শাসক হিসেবে তার প্রাপ্য আরো বেশী ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে অন্ততঃ হজরত ওমর রা. বিভিন্ন দেশের শাসন কর্তাদের যেরূপ বেতন নির্ধারণ করতেন সেই পরিমাণ বেতন গ্রহণ করতে পারতেন। হজরত ওমর রা. কুফার শাসনকর্তা আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং তার সহকারীদের জন্য মাসিক ছ’শ দিরহাম বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। আর সাধারণ লোকদের মত যে সব দানের অংশ পেতেন সেটা এ থেকে স্বতন্ত্র। তাছাড়া তিনি দৈনিক একটি ছাগলের অর্ধাংশ ও আধা বস্তা আটা পেতেন। এমনিভাবে কুফার জনগণকে ইসলামের শিক্ষাদানের এবং বাইতুল মালের দেখাশুনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে নিয়োগ করেন এবং তাঁর জন্য মাসিক একশো দিরহাম এবং দৈনিক একটি ছাগলের এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন। ওসমান ইবনে হানিফের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার দিরহাম বৃত্তি, দৈনিক একটি ছাগলের এক চতুর্থাংশ ও মাসিক দেড়শো দিরহাম বেতন নির্ধারণ করেন।
হজরত আলী রা. নিজের জন্য যে কঠিন পথ অবলম্বন করেন, তা এ সব ব্যাপার না জেনে করেননি। তিনি যে দৃষ্টিভংগী অনুসারে এ নীতি অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, শাসক সব সময়ই জনসাধারণের জন্য আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকে এবং তার ওপর সন্দেহের প্রচুর অবকাশ থাকে। যেহেতু সরকারী কোষাগার তার অধীন থাকে, তাই আত্মসাতের সন্দেহও সৃষ্টি হতে পারে। সেটা জনসাধারণ ও নিজের অধীনস্থ রাজ-কর্মচারীদের জন্য সততা ও সংযমের আদর্শ হয়ে থাকে। এ কারণে তিনি নিজেকে হজরত আবু বকর ও ওমরের রা. সংযমের নীতির অনুসারী করে তোলেন। যে সব ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাদের জন্য এই উন্নত মাপকাঠিই সর্বাপেক্ষা সংগত ছিল।
হজরত আলী রা. গোটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নবী সা. ও তার পরবর্তী খলিফাদ্বয়ের আদর্শের অনুসারী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান।
একবার তিনি স্বীয় বর্ম জনৈক খৃস্টানের নিকটে পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে বিচারপতি শোরাইহের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন এবং একজন সাধারণ নাগরিকের মত তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তিনি দাবী করেন যে, ওই বর্ম তার। শোরাইহ খৃস্টানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমিরুল মু’মিনীনের দাবী সম্পর্কে তার বক্তব্য কী? খৃস্টান বললো, ‘বর্ম নিশ্চয়ই আমার, তবে আমিরুল মু’মিনীনকেও আমি মিথ্যুক বলতে চাই না।’’ শোরাইহ বললেন, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে কী?’’ হজরত আলী রা. হেসে বললেন, ‘‘আমার কাছে প্রমাণ নেই।’’ শোরাইহ রায় দিলেন যে, বর্ম খ্রীস্টানকে দিতে হবে। সে বর্ম নিয়ে রওয়ানা দিল আর আমিরুল মু’মিনীন অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকলেন। কয়েক পা গিয়ে সে ফিরে এল এবং বলতে লাগলো ‘‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে ধর্মের খলিফা স্বয়ং আমাকে বিচারকের নিকট পেশ করে এবং বিচারক তার বিরুদ্ধে রায় দেন; নিঃসন্দেহে তা সত্য ধর্ম।’’ এ বলেই সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো। অতঃপর সে বললো, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! খোদার শপথ করে বলছি, এ বর্ম আপনার। আপনি যখন সিফ্ফিন অভিমুখে যাত্রা করেন তখন আমি সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে চলছিলাম। এ বর্ম আপনার বাদামী রং-এর উটের ওপর থেকে পড়ে গেছে।’’ হজরত আলী রা. বললেন, ‘‘তুমি যখন ঈমান এনেছ তখন এটা তোমাকেই উপহার দিলাম।’’ (আবকারিয়া ইমাম- উস্তাদ আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ)
তিনি যে শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার রূপরেখা তিনি তার অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণেই নির্দেশ করেনঃ
‘‘ভাইসব! আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমাদের যা অধিকার আমারও তাই। তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা আমার ওপরও অর্পিত হয়। আমি তোমাদের নবীর নীতি অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবো এবং তারই আইন চালু করবে। শোনো! ওসমান রা. যাকে যত জায়গা-জমি এবং আল্লাহর ধন থেকে যাকে যা কিছু দিয়েছেন তা বাইতুল মালে ফেরত নেয়া হবে। কেননা, বাস্তবকে কোন জিনিস পরিবর্তিত করতে পারে না। এমনকি যদি আমি দেখি যে, এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিয়ে কিংবা বাঁদী খরিদ করার কাজে ব্যয়িত হয়েছে অথবা তা বিদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তবুও আমি তা ফেরত আনবো। কারণ, ন্যায়-নীতি যার পক্ষে দুঃসহ হবে, জুলুম ও অত্যাচার তার পক্ষে আরো বেশী দুঃসহ হবে।’’
‘‘ভাইসব! হুশিয়ার হয়ে যাও! কিছুদিন আগে যাদের ওপর দুনিয়ার স্বার্থ প্রবল হয়ে পড়েছিল এবং তারা বড় বড় দালান-কোঠা, উট-ঘোড়া, দাস-দাসী ও চাকর-নফরের মালিক হয়েছিল- তাদেরকে যখন আমি এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত করবো এবং তাদের আসল অধিকারের আওতায় ফিরিয়ে আনবো- তখন যেন তারা বলতে আরম্ভ না করে থাকে যে, আবু তালেবের বেটা আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহর সাহাবী, মুহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে কেউ যদি এরূপ মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের দরুণ অন্যান্যদের ওপর তার অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তাহলে তার জানা উচিত যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি শুধু আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে এবং সেখানেই এর উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়া যাবে। জেনে রাখ! যে ব্যক্তি খোদা ও রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দেবে, আমাদের জাতীয়তাকে গ্রহণ করবে, আমাদের সত্য দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং আমাদের কেবলামুখী হবে, সে ইসলামের দেয়া যাবতীয় অধিকার লাভ করবে এবং তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য হবে। তোমরা সকলে আল্লাহর দাস এবং এ সম্পদ আল্লাহর সম্পদ। এটা তোমাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। এ ব্যাপারে কাউকে কারো ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে না। খোদাভীরু লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে।’’
মুনাফাখোর, বৈষম্যপ্রিয়, স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী মহল হযরত আলীর সমবণ্টন নীতিতে খুশী হতে পারেনি এবং তা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই এই মেহল শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী উমাইয়া শিবিরে গিয়ে মিলিত হয়। এই শিবিরে গিয়ে তারা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থের শেষ রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠে।
যাদের দৃষ্টিতে মুয়াবিয়ার মধ্যে হযরত আলীর চাইতে বেশী চাতুর্য, বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও দ্ক্ষতা ধরা পড়ে এবং যারা এই কারণে শেষ পর্যন্ত মুয়াবিয়া বিজয়ী হয়েছেন বলে মনে করেন, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ভুল করেন এবং হযরত আলীর প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ ও তার আসল কর্তব্য পালন সম্পর্কে সঠিক মতামত স্থাপনে ব্যর্থ হন। হযরত আলীর সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ কর্তব্য ছিল ইসলামী ঐতিহ্যকে তার প্রকৃত শক্তিতে পুনর্বহাল করা এবং সত্য দ্বীনের নির্জীব-প্রায় দেহে পুনরায় জীবনীশক্তির সঞ্চার করা। হযরত ওসমানের রা. দুর্বলতা ও বার্ধক্যের সুযোগে উমাইয়া বংশীয় কু-চক্রীদের যে মলীনতা ও কদর্যতা ইসলামের প্রাণশক্তিকে কলুষিত করে তোলে তা থেকে তাকে মুক্ত করাই ছিল হযরত আলীর অন্যতম মিশন।
এই মিশন সফল করার সংগ্রামে তিনি যদি মুয়াবিয়ার রা. মত কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর মিশনই ব্যর্থ হয়ে যেত। এর অর্থ এই দাঁড়াতো যে, তিনি খেলাফত অর্জনের সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করেছেন। এরূপ হলে তাঁর সংগ্রামের কোন মূল্যই থাকতো না। আলী ‘আলী’ হয়েই থাকতে হবে, নচেৎ ‘খেলাফত এবং সেই সাথে তার প্রাণও যদি তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে তার আপত্তি নেই’- এই ছিল হযরত আলী রা. এর সংকল্প। এ সংকল্প তার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্য স্থলিত হতো না। এক বর্ণনা অনুসারে (অবশ্য যদি এটা সত্য হয়) হযরত আলী রা. বলতেন, ‘‘খোদার শপথ, মুয়াবিয়া আমার চাইতে ধূর্ত নয়, কিন্তু সে ধোকাবাজ। সে প্রকাশ্যে নাফরমানি করে। আমি যদি ধোঁকা ও প্রতারণা পছন্দ করতাম তাহলে আমি সবচাইতে ধূর্ত হতাম।’’
হযরত আলীর ইন্তেকালের পর বনু উমাইয়ার যুগ আসে। উমাইয়াদের সামনে হযরত ওসমানের রা. ঈমান, তার খোদাভীরুতা এবং তার হৃদয়ের কোমলতা একটা প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল। কিন্ত সেটা তো আগেই অপসারিত হয়েছিল। এবার হযরত আলীর ইন্তিকালে সর্বশেষ বাধাও দূর হয়ে গেল এবং উচ্ছৃংখলতার পথ উন্মুক্ত হলো।
এরপরও ইসলাম পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু ইসলামের প্রাণশক্তি যে মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল সে ব্যাপারে কো দ্বি-মতের অবকাশ নেই। যদি স্বয়ং ইসলামের প্রকৃতিতে একটি প্রবল শক্তি লুকানো না থাকতো এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তিতে গতিশীলতার যোগ্যতা না থাকতো তাহলে উমাইয়া যুগই তাকে তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার প্রাণশক্তি অবিরাম সংগ্রাম করতে এবং শক্তি অর্জন করতে থাকে। আজও তার মধ্যে সংগ্রামের ও বিজয়ের গোপন শক্তি নিহিত রয়েছে।
উমাইয়া যুগ থেকে মুসলমানদের কোষাগার অতিমাত্রায় উদার হয়ে পড়ে এবং তা বদাশাহ, তাদের চাটুকার ও তল্পিবাহীদের লুটের মালে পরিণত হয়। ইসলামী সুবিচার-ন্যায়নীতির ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। শাসকরা বিশেষ সুবিধাভোগী আর তাদের চাটুকাররা উপঢৌকন-ভোগীতে পরিণত হয়। মোটকথা খেলাফত রূপান্তরিত হয় রাজতন্ত্রে, আর তাও নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে। এই স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সা. ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। এর পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, আমাদের গায়ক কবি ও চাটুকারদেরকে পুরস্কার দেয়ার বহু কাহিনী শ্রবণ করতে হলো। মাবাদ নামক কবিকে জনৈক উমাইয়া বাদশাহ ১২ হাজার দিনার পুরস্কার দেন এবং আব্বাসী বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইসমাইল ইবনে জামে নামক গায়ককে শুধুমাত্র একটি গানের জন্য চার হাজার দিনার দান করেন, সেই সাথে একটা সুন্দর কারুকার্য খচিত মনোরম বাড়ীও দেন। কালের স্রোতধারা এভাবেই চলতে থাকে। কখনো অল্প সময়ের জন্যে এতে বিরতি দেখা দেয়, অতঃপর আবার পূর্ণ গতিবেগে ছুটে চলে।
ওমর ইবনে আবদুল আজিজ
এবারে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের যুগের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ যুগটা ছিল খেলাফতে রাশেদারই পরিশিষ্ট। এটা ছিল একটা তীব্র আলোকচ্ছটা যা গোটা পথকে আলোকিত করে তুলেছিল। অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত শাসন ক্ষমতাকে তার আসল মালিক মুসলিম জাতির নিকট ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তিনি তার খেলাফত যুগের উদ্বোধন করেন। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার গঠনের একমাত্র বৈধ পন্থা হচ্ছে এই যে, মুসলিম জাতি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় শাসক নির্বাচিত করবে, সামরিক শক্তি দ্বারা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেনঃ
‘‘ভাই সব! আমাকে আমার নিজের এবং জাতির মতামত ছাড়াই এ কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমার আনুগত্যের যে বোঝা তোমাদের ওপর চেপে রয়েছে তা আমি নিজেই দূরে নিক্ষেপ করছি। তোমরা নিজেরাই কাউকে নির্বাচন কর।’’
জনতা চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আমরা আপনাকেই নির্বাচন করছি। আপনার নেতৃত্বের ওপর আমরা পূর্ণ আস্থাশীল।’’
এভাবে তিনি শাসক নির্বাচনের আসল পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কেননা জাতির সম্মতি ও পরামর্শ ব্যতিত কেউ শাসক নিযুক্ত হতে পারে না।
অতঃপর তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন,
‘‘বন্ধুগণ! আমার আগে কিছু সংখ্যক শাসক অতিবাহিত হয়ে গেছে। তারা ছিল জালেম। তোমরা কেবল তাদের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছ। মনে রেখ! স্রষ্টার না-ফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না। যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তার আনুগত্য স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে আল্লাহ্র না-ফরমানী করে তার আনুগত্য স্বীকার করা উচিত নয়। যতক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করবো ততক্ষণ তোমরাও আমার নির্দেশ মেনে চলবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহর না-ফরমানী করি তাহলে আমার নির্দেশ পালন করা তোমাদের জন্য জরুরী নয়।’’
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ প্রত্যর্পণ করা শুরু করেন। এ কাজ তিনি নিজের সম্পদ থেকেই শুরু করেন। তিনি নিজের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির উপার্জন সূত্র অনুসন্ধান করে দেখতে পান যে, তার সবই অবৈধভাবে অর্জিত। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই সব সস্পদ ফিরিয়ে দেন। এমনকি তার হাতে একটা অংগুরী ছিল। সেটার দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘এটা আমাকে পশ্চিমাঞ্চল থেকে আদায়কৃত অর্থ সম্ভার থেকে ওলিদ অন্যায়ভাবে দিয়েছিল।’’ তিনি সেটা তৎক্ষণাৎ বায়তুল মালে জমা দেন। তার নিকট যত জায়গীর ছিল তা তিনি ফিরিয়ে দেন। এমামার কতিপয় জায়গীর, ইয়ামনে মুকাইদিস, জাবালুল অরস ও ফিদিক তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল- এর সব ক’টি তিনি পরিত্যাগ করেন এবং মুসলমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন, শুধুমাত্র সুয়াইদা নামক স্থানে একটি নির্ঝরিনী তিনি নিজের অধিকারে রাখেন। এটি তিনি নিজের অর্থে খোদাই করেছিলেন। এর মুনাফা প্রতি বছর তার হাতে আসতো এবং তা প্রায় দেড়শো দিনার হতো।
যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যা কিছু তার অধিকারভুক্ত রয়েছে, তার সবই তিনি মুসলমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করবেন তখন অন্যায়ভাবে অধিকারভুক্ত মুসলমানদের সকল অধিকার প্রত্যর্পণ করতে হবে এই বলে জনগণকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দিলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেনঃ
‘‘নাগরিকবৃন্দ আমাদেরকে বহু জিনিস দিয়েছিলেন, সেগুলো আমাদের গ্রহণ করাও উচিত ছিল না, কাউকে দান করাও উচিত ছিল না। এর সব সম্পদ আমার হস্তগত হয়েছিল। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার নিকট হিসাব চাইতে পারতো না। তোমরা শুনে নাও, আমি এ ধরণের সমস্ত ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করেছি। তবে এ কাজ আমি আমার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ থেকেই শুরু করছি।
মুহাজেম! তুমি পড়তে আরম্ভ কর।’’
এর আগে একটি থলিতে করে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র আনা হয়েছিল। মুহাজেম এক একটি করে দলিল পড়তে আরম্ভ করলেন। এক একটি পড়া শেষ হলে ওমর সেটি নিয়ে নিতেন, তার হাতে ছিল এক কাঁচি, তা দিয়ে তিনি দলিলগুলো কেটে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত কোন একটি দলিল তার কাট-ছাটের হাত থেকে রক্ষা পেলো না। এর পর তিনি স্বীয়-মহিষী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেকের মামলা হাতে নিলেন। তিনি তাকে বললেন, ‘‘তুমি তোমার গহনা বাইতুল মালে দাখিল করে দাও নতুবা আমাকে তোমার থেকে পৃথক হবার অনুমতি দাও। দু’টোর একটা গ্রহণ কর। আমার পক্ষে ওগুলোর সাথে ঘরে বসবাস করা সম্ভব নয়।’’ ফাতিমা বললেন, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আমি আপনাকেই গ্রহণ করবো। একটি হীরকের কিইবা মূল্য। ওর চাইতে হাজার গুণ মূল্যবান জিনিস হলেও আমি তার মোকাবেলায় আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম।’’ এরপর তার নির্দেশে ওটা বাইতুলমালে জমা করা হলো। যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইন্তেকাল করেন এবং ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তিনি তাঁর বোন ফাতিমাকে বলেন যে, তুমি যদি চাও তবে তোমার হীরক তোমাকে ফেরত দেয়া যেতে পারে।’’ তিনি জবাবে বলেন, ‘‘আমি ওটা ওমরের জীবদ্দশায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিয়েছিলাম, আজ তার ইন্তেকালের পর আমি তা কিছুতেই গ্রহণ করবো না।’’
ওমর ইবনে আবদুল আজিজ শুধু অবৈধ সম্পদ ফেরত দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিজের জন্য ‘বাইতুল মাল’ থেকেও কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। অথচ হজরত ওমর ফারুক রা. ‘ফায়’ লব্ধ সম্পদ থেকে নিজের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দূল আজীজকে হযরত ওমর ফারুকের সমান গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তার জবাবে বলেন, ‘‘ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট ব্যক্তিগত সম্পত্তি মোটেই ছিল না- এদিকে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা আছে তাদের আমার বেশ চলে যায়।’’
তিনি মারওয়ান বংশধরকে অর্ধেক সম্পত্তি আসল মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণে উদ্বুদ্ধ করেন। বর্ণিত আছে যে, হেমসের একজন অমুসলিম এসে বলেছিল, ‘‘আমিরুল মুমিনীন! আমার অনুরোধ আল্লাহর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করে দিন।’’ তিনি বললেন, ‘‘কি ব্যাপারে?’’ সে বললো, ‘‘আব্বাস ইবনে ওলিদ ইবনে আব্দুল মালেক আমার ভূমি কেড়ে নিয়েছে।’’ আব্বাস সেখানেই বসা ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আব্বাস, কি বলতে চাও?’’ আব্বাস বললো, ‘‘ওটা আমাকে (পিতা) ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে লিখিত দলিলও দিয়েছেন।’’ তিনি আগন্তুককে বললেন, ‘‘এখন তোমার বক্তব্য কি?’’ সে বললো, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দিন।’’ ওমর বললেন, ‘‘হ্যা, ওলিদ ইবনে আব্দুল মালেকের দলিলের চাইতে আল্লাহর ফরমানই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তুমি এর জমি ফিরিয়ে দাও।’’ তৎক্ষণাৎ সে তার জমি ফিরিয়ে দিল।
রওহ নামে ওলিদের এক ছেলে ছিল। সে আশৈশব গ্রামে লালিত পালিত হওয়ার দরুন দেখতে সম্পূর্ণ গ্রাম্য বলে মনে হতো। কতিপয় ব্যক্তি ওমরের নিকট হেমসে অবস্থিত কয়েকটি দোকান সম্পর্কে মোকদ্দমা রুজু করে। আসলে এই দোকানগুলো ছিল অভিযোগকারীদের, কিন্তু ওলিদ তা রওহের নামে লিখিয়ে দেন। ওমর রওহকে ডেকে তাদের দোকান প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেন। রওহ জবাব দেয় যে, দোকান ওলিদের লিখিত দলিল অনুসারে তার মালিকানাভুক্ত। তিনি জবাব দেন, ওলিদের দলিল দিয়ে তোমার কোন কাজ হবে না। দোকান ওদের এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। তুমি ফিরিয়ে দাও।’’ তখন রওহ এবং হেমসের এক ব্যক্তি উঠে দরবার থেকে ফিরে আসতে লাগলো। পথে রওহ হেমসবাসীকে হুমকি দিল। হেমসবাসী ফিরে গিয়ে ওমরের কাছে উপস্থিত হয়ে রওহের হুমকির কথা জানালো। ওমর তার দেহরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি কাব ইবনে হামেদকে নির্দেশ দিলেন, ‘‘রওহের নিকট গিয়ে বল যে, সে যেন দোকান তার মালিকদের ফিরিয়ে দেয়। যদি ফিরিয়ে দেয় উত্তম, নচেৎ তার মস্তক ছেদন করে আমার কাছে হাজির কর।’’ একথা শুনে রওহের এক শুভাকাংখী দরবার থেকে বেরিয়ে এল এবং আমিরুল মু’মিনীনের নির্দেশের কথা ব্যক্ত করলো। শুনে রওহের চৈতন্য বিলুপ্ত হবার উপক্রম হলো। কাব তার নিকট অর্ধোন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে উপনীত হলো। কাব বলা মাত্রই সে গিয়ে দোকান খালি করে দিল।
জনগণ অবিশ্রান্তভাবে জুলুম, বল প্রয়োগ ও হয়রানির নালিশ নিয়ে তার দরবারে হাজির হতে থাকে। অবৈধভাবে ছিনিয়ে নেয়া সব সম্পত্তির মামলাই তার নিকট পেশ করা হয় এবং তিনি তার সব গুলোই প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করেন, তা তার অধিকারভুক্ত থাকুক বা অন্য কারো। তিনি বনু মারওয়ানের নিকট থেকেও বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নেয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন এবং তার আসল মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। তিনি অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াও এ ধরণের জুলুমের প্রতিকার করতেন, এ ব্যাপারে তিনি সামান্য প্রমাণকেও যথেষ্ট মনে করতেন, যখনই তার নিকট কোন সম্পত্তির ব্যাপারে জুলুম করা হয়েছে বলে অনুমিত হতো অমনি তিনি সে সম্পত্তির মালিকানা প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, পূর্বতন শাসকরা জনগণের সাথে অবিচার করতো। বর্ণিত আছে যে, জুলুমের মাধ্যমে গৃহীত ধন-দৌলত ফেরত দিতে দিতে তিনি ইরাকের ‘বাইতুল মাল’ শূণ্য করে দেন। ফলে সিরিয়া থেকে সেখানে সম্পদ স্থানান্তরিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক উমাইয়া বংশোদ্ভূত আম্বাসা ইবনে সাইদ ইবনুল আসকে ২০ হাজার দিনার উপহার দেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ঘুরে নির্দেশনাটি মোহরের দপ্তরে এসে উপনীত হয় এবং কেবল টাকা গ্রহণ করা বাকী থাকতেই সুলাইমানের মৃত্যু হয়। আম্বাসা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের বন্ধু ছিলেন। ভোর হতেই তিনি ওমরের নিকট উক্ত উপহারটির ব্যাপারে আলাপ করার জন্য রওনা হন। এসে দেখেন, তার দুয়ারে বনু উমাইয়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে। তারাও নিজ নিজ ব্যাপারে কথা বলার জন্য সাক্ষাতপ্রার্থী। আম্বাসাকে দেখে তারা ভাবলেন যে, আমরা নিজেরা আলাপ-আলোচনা করার পূর্বে এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয় তা-ই দেখে নেয়া যাক। আম্বাসা তার নিকট গিয়ে বললেন, ‘আামিরুল ম’মিনীন! সুলাইমান আমাকে ২০ হাজার দিনার দেয়ার নির্দেশ জারী করেছিলেন। এই নির্দেশ মোহরের দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং কেবল ওটা গ্রহণ করা বাকী ছিল। এমন সময় তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস আপনি এই মহানুভবতার কাজটি সম্পূর্ণ করে দেবেন। কেননা সুলাইমানের চেয়ওে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।’’ ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘কত টাকা?’’ তিনি বললেন, ‘’২০ হাজার দিনার।’’ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বললেন, ‘’২০ হাজার দিনার তো মুসলমানদের চার হাজার পরিবারের জন্য যথেষ্ট। এতটা অর্থ আমি কি করে এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে পারি? আমি তা কিছুতেই পারবো না।’’ আম্বাসা বলেন, এ কথা শুনে আমি সেই দলিলটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেই- যাতে অর্থের কথা লিখিত ছিল। ওমর বললেন, ‘‘দলিল তুমি নিজের কাছেও রাখতে পার। কারণ আমার পরে এমন লোকও ক্ষমতাসীন হতে পারে, যে এই সরকারী অর্থের ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী দুঃসাহসী হবে এবং এই দলিলে লিখিত টাকা তোমাকে হয়তো দিয়ে দেবে।’’ এ কথা শুনে আমি দলিলটি তুলে নিলাম এবং বাইরে এসে বনু উমাইয়ার লোকদেরকে আমার সাথে খলিফার আচরণের কথা খুলে বললাম। তারা বলে উঠলো, ‘‘এর পরে আর আমাদের কোনো আশা নেই। তুমি গিয়ে খলিফার নিকট আবেদন কর যেন আমাদেরকে অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার অনুমতি দেন।’’ আমি তার নিকট পুনরায় গিয়ে বললাম, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনার বংশের লোকেরা আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আগে তাদেরকে যে সব বৃত্তি দেয়া হতো তা এখনও জারী রাখার আবেদন জানাচ্ছে।’’ ওমর জবাব দিলেন, ‘‘খোদার শপথ! এ অর্থ আমার নয় আর আমি এ ধরণের দান করার অবকাশও দেখি না।’’ আমি বললাম, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! তাহলে তারা অন্য অঞ্চলে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুমতি চাচ্ছে।’’ তিনি বললেন, ‘‘তারা যা করতে চায়, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে।’’ আমিও বললাম, ‘‘আমিও যেতে চাই।’’ তিনি বললেন, ‘‘হা, তোমাকেও অনুমতি দিচ্ছি। তবে আমার মতে তোমার এখানে থাকাই উত্তম। তোমার কাছে যথেষ্ট পুঁজি রয়েছে। এদিকে আমি সুলাইমানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রি করবো। দেখা যেতে পারে, তুমি সেখান থেকে এমন কিছু কিনতে পার কিনা-যার লভ্যাংশ দ্বারা তোমার এই ক্ষতিপূরণ হতে পারে। আম্বাসা বলেন, ‘‘আমি সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং সুলাইমানের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক লাখ দিনারের জিনিসপত্র কিনে তা ইরাকে নিয়ে দু’লাখ দিনারে বিক্রি করলাম। আমি সেই দলিলও সংরক্ষণ করেছিলাম। ওমরের ইন্তেকালের পর ইয়াজীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট উক্ত দলিল নিয়ে উপনীত হই এবং তিনি সেই ২০ হাজার দিনার আমাকে দিয়ে দেন।’’
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ মারওয়ানের বংশধরকে ডেকে বলেন যে, ‘‘তোমাদেরকে আল্লাহ বিপুযল ধন-ঐশ্বর্য দান করেছেন। আমার ধারণা মতে উম্মতের সামগ্রিক সম্পদের অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ তোমাদের কুক্ষিগত রয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের যা কিছু প্রাপ্য তোমাদের নিকট রয়েছে তা তাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করো না।’’ কিন্তু কেউ এ কথার জবাব দিল না। তিনি বললেন যে, ‘তোমরা আমার কথার জবাব দাও।’’ তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ‘‘আমরা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমরা এভাবে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নিঃস্ব বানিয়ে দিতে এবং পিতৃপুরুষদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারবো না, তা আমাদের মস্তক ছেদন করাই হোক না কেন।’’ ওমর বললেন, ‘‘খোদার শপথ! যদি আমি আশংকা না করতাম যে, যে জনগণের অধিকারের জন্য আমি এই চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত রয়েছি, তাদেরকেই তোমরা দলে ভিড়িয়ে ফেলবে- তাহলে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাদেরকে জব্দ করে ছাড়তাম। কিন্তু আমার গোলযোগের আশংকা রয়েছে। যাদি আল্লাহ আমাকে আরো কিছু দিন জীবিত রাখেন, তাহলে আমি প্রত্যেক নাগরিককে তার ন্যায্য অীধকার দিয়ে তবে ক্ষান্ত হব।’’ (ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ, আহম্মদ, জাকি, সফওয়াত)।
কিন্তু তিনি নিজ বাসনা অনুসারে এতটা আয়ু লাভ করতে পারেননি যাতে সকলের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া যায়। তার পরবর্তী শাসকরা তার প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে উমাইয়াদের পথে চলতে থাকে। এরপর আব্বাসীয়রাও এল বাদশাহ হয়ে। তারা যখন এল, তখন দেশে বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, দেশবাসী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। কেননা উমাইয়া শাসকরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামী জীবনপদ্ধতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বস্তুতঃ আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসনের চাইতে উত্তম ছিল না। সেটাও ছিল একই ধরণের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন।
রাজতন্ত্র
আমরা যেহেতু এখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন পদ্ধতি নয়- বরং শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে ইসলামী প্রাণশক্তির ইতিহাস আলোচনা করতে চাচ্ছি- তাই আমরা সেই প্রাণশক্তির বিকৃতি করণ ও তাতে মলিনতার স্পর্শের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করার জন্য রাজততান্ত্রিক শাসনামলের তিনটি ভাষণ পেশ করেই ক্ষান্ত হব। খেলাফতে রাশেদার যুগে যে তিনটি ভাষণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এ তিনটির তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
সন্ধির পর মুয়াবিয়া কুফায় জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘কুফাবাসীগণ! তোমরা কি মনে করেছ যে আমি নামাজ, জাকা, ও হজ্জ্বের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি? আমিতো ভাল করেই জানি যে, তোমরা নামাজ, জাকাত ও হজ্জ্ব যথারীতি পালন করে থাক। আসলে আমি যুদ্ধ করেছি তোমাদের গর্দানের ওপর আমার শাসন চালাবার জন্য। তোমাদের অসম্মতি সত্ত্বেও আল্লাহ আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। জেনে রেখ, এই হাংগামায় যত জান-মালেরই ক্ষতি হয়ে থাক না কেন তার কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। আর আমি যত প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে না কেন তা সব এই যে আমার পায়ের তলে পিষ্ট করে দিলাম।’’ এমনিভাবে তিনি মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ
‘‘খোদার শপথ! আমার যতদূর জানা আছে, আমি তোমাদের প্রীতি-ভালবাসার পরিণতিতে ক্ষমতা লাভ করিনি। তোমরা এতে খুশী হওনি- তাও আমি জানি। আমি এই তরবারীর সাহায্যে সংগ্রাম করেছি। তোমাদের ব্যাপারে আমি আবু বকর ও ওমরের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনকে সম্মত করতে পারলাম না। সুতরাং আমি নিজেকে এমন এক পথে চালিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে আমার ও তোমাদের- উভয় পক্ষেরই কল্যাণ সাধিত হবে। সকলকে সুচারুরূপে মিলেমিশে পানাহার করতে হবে। তোমরা যদি আমাকে শাসক হিসেবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে মনে না কর, তথাপি আমি তোমাদের জন্য উত্তম শাসক।’’
মনসুর আব্বাসী উমাইয়া শাসন ধারাকে চরম বিকৃতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান এবং রাজত্ব ও বাদশাহীকে একটি ঐশী ও খোদার পক্ষ থেকে সঠিক ও সত্য ব্যাপার বলে গণ-মানসে ধারণার সৃষ্টি করে দেন। অথচ ইসলামের নিকট এ ধারণা সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরূপ অপকীর্তি সাধনের পর মনসুর নিম্নরূপ ভাষণ দেনঃ
‘‘দেশবাসী! আমি আল্লাহর জমীনে তার স্থলাভিষিক্ত। তারই সাহায্য সহায়তায় তোমাদের ওপর শাসন চালাবো। আমি তার ধন-সম্পদের ওপর তার পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রহরী। তার ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে আমি তা ব্যয় করি অথবা কাউকে দান করি। আল্লাহ আমাকে জাতীয় কোষাগারের তালা স্বরূপ বানিয়েছেন। তিনি যদি আমাকে খুলতে চান তাহলে তোমাদের মধ্যে খাদ্য বণ্টন অথবা দান করার জন্য খোলেন আর যদি বন্ধ করতে চান তাহলে বন্ধ করে দেন।’’
এরপর শাসন ব্যবস্থা ইসলাম ও তার মূলনীতির আওতা থেকে একেবারেই বাইরে নিক্ষিপ্ত হলো।
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
স্বর্ণযুগে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন ছিল। শাসকবৃন্দ শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার সম্পর্কে যে ধরণের চিন্তা করতেন, তাদের অর্থনীতিও সেই ধরণের ছিল। হযরত মুহাম্মাদ সা., হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা. এবং হযরত আলী রা. এর যুগে ইসলামী আদর্শ সক্রিয় ছিল অর্থাৎ এই নীতি প্রচলিত ছিল যে, সরকারী অর্থ-সম্পদ সবই জাতির এবং জনতার সম্পদ। শাসক তা থেকে কেবলমাত্র নিজের অথবা নিজের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রমাণ করেই কিছু গ্রহণ করতে পারে। এমনিভাবে শাসক প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেবলমাত্র তার সত্যিকার প্রাপ্য যতটুকু ততটুকুই দিতে বাধ্য। কেননা এ ব্যাপারে শাসক ও অন্যান্যরা সমান। হযরত ওসমান রা.-এর যুগে এ নীতিতে সামান্য বিকৃতি দেখা দিয়েছিল, তখনও জনগণ নিজেদের পূর্ণ অধিকার অর্জন করতো। তবে সম্ভবতঃ সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ লোকদের নির্ধারিত বৃত্তি ইত্যাদি দেয়ার পরেও বিপুল অর্থ বেঁচে থাকতো। খলিফার ধারণা ছিল এই যে, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও তার ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য লোকদের দান করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরপর যখন শাসন ক্ষমতা চলে গেল স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে, তখন সমস্ত বিধি-নিষেধ অপসারিত হলো এবং শাসকরা জনগণকে দান কিংবা বঞ্চনার হিড়িক চলতে থাকলো। মুসলমানদের সম্পদে শাসকদের, তাদের সন্তান-সন্ততির, তাদের তল্পিবাহী ও চাটুকারদের জন্য অবাধ ভোগের দ্বার উন্মুক্ত হলো। তারা এ ব্যাপারে ইসলামের সমস্ত সীমরেখা অতিক্রম করে চলতে থাকলো।
এ হলো পরিস্থিতির একটা মোটামুটি বিবরণ। এবারে আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করবো।
রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগ থেকে বাইতুল মালের আয়ের যে সব পন্থা চলে আসছিল তা হচ্ছেঃ
প্রথমতঃ যাকাত- এটা মুসলমানদের বিভিন্ন রকমের সম্পদের ওপর ধার্য করা হয়। যেমনঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, কৃষি উৎপাদন, ফলমূল, গবাদিপশু, বাণিজ্য পণ্য, খনিজ ও প্রোথিত ধন প্রভৃতি। সাধারণভাবে যাকাতের গড় হার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এটা ৮টি প্রসিদ্ধ খাতে ব্যয় করা হয়।
দ্বিতীয়তঃ জিজিয়া- এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের বসবাসের জন্য রাষ্ট্রকে প্রদত্ত কর বিশেষ। এটা মুসলমানদের যাকাত এবং কায়িক ত্যাগ কুরবানীর সমপর্যায়ভুক্ত।
তৃতীয়তঃ ‘ফায়’- এটা হচ্ছে সেই অর্থ-সম্পদ যা মোশরেকদের নিকট থেকে যুদ্ধ ছাড়াই আদৌ পরিশ্রম না করেই পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান অনুসারে এই অর্থ সম্পদের সমগ্রটাই আল্লাহ, তাঁর রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও প্রবাসীদের প্রাপ্য।
চতুর্থতঃ গণিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ- এর চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের আর বাকীটুকু ‘ফায়’-এর অনুরূপ এবং ঐ সব খাতেই ব্যয়িত হবে।
অথবা, গণিমতের স্থলে ‘খারাজ’- মোশরেকদের যে সব জমি যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের হস্তগত হয়; যেমন হযরত ওমর রা. পারস্যের জমির ব্যাপারে করেছিলেন- সেই সব জমির ওপর ধার্যকৃত কর বিশেষ।
রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে বাইতুল মালের আয় পর্যাপ্ত ছিল না। মুহাজেররা নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে মদিনায় এসেছিলেন এবং আনসারগণ তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের ধন সম্পত্তিতে অংশীদার করে ভাই বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। যুদ্ধের আগে মুসলমানদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল ইচ্ছাকৃত দান।
যখন যুদ্ধাভিযানের ধারাবাহিকতা শুরু হলো এবং হিজরতের দ্বিতীয় বছর যাকাত ফরজ হলো তখন আসল আয়ের উৎস অর্থাৎ যাকাতের সাথে আরেকটা উৎস গণিমতের মাল যুক্ত হলো। এর এক পঞ্চমাংশ দেয়া হতো যোদ্ধাদেরকে। রাসূলুল্লাহ সা. পদাতিককে একাংশ এবং অশ্বারোহীকে দুই অংশ অন্য এক রেওয়ায়েত তিন অংশ দিতেন। এভাবে তিনি এই নীতি নির্ধারিত করে দিলেন যে, ‘‘প্রত্যেকের অংশ তার ত্যাগ ও কুরবানী অনুপাতে।’’ তিনি অবিবাহিতকে একাংশ এবং বিবাহিতকে দুই অংশ দিতেন। এমনিভাবে তিনি দ্বিতীয় নীতি এই নির্ধারণ করেন যে, ‘‘প্রত্যেকের অংশ তার প্রয়োজন অনুপাতে।’’ গণিমতের অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ ব্যায়ের খাত ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
অতঃপর একটা নতুন ব্যাপার ঘটলো। বনু নজীর অভিযানে প্রথম বারের মত ‘ফায়’ অর্জিত হলো। এটিকে রাসূলুল্লাহ সা. মুহাজেরদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। আনসারদের মধ্য থেকে মাত্র দু’জন দরিদ্র ব্যক্তিকে এ থেকে অংশ দেয়া হয়। এরপর কোরআনের এক আয়াতে এই মূলনীতি ঘোষণা করা হয় যে,
‘তোমাদের ধনিকদের মধ্যে যেন সম্পদের আবর্তন সীমিত হয়ে না থাকে।’
অপ্রতিহত গতিতে দেশ জয় ও ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাইতুল মালের আয় বর্ধিত হতে থাকে। সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে মুসলমানগণ ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে। কারণ ইসলামের নির্ধারিত অংশ অনুসারে তারা সকলেই বাইতুল মালের অর্থের সমান অংশীদার।
যখন রাসূলুল্লাহ সা. ইন্তেকাল করেন এবং কিছু লোক ইসলাম-ত্যাগী হয়ে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তখন আবু বকর রা. যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা ইতিহাসের অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ
‘‘খোদার শপথ! (যাকাতের) উট ও অন্যান্য গবাদি পশু বাঁধার এক গাছি রশিও যদি তারা দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।’’ এ ব্যাপারে তিনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের অভিমতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে হযরত ওমরও হযরত আবু বকরের অভিমত সমর্থন করেন ও নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথমদিকে তার মত ছিল এই যে, তারা ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) স্বীকার করে বলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। তার মতভেদ এতটা তীব্র ছিল যে, তিনি খানিকটা চড়া স্বরে বলে ওঠেন, ‘‘আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করে অস্ত্র ধারণ করি’’ যখন রাসূলুল্লাহ সা. বলে গেছেনঃ
‘‘মানুষ যতক্ষণ না বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ‘ইলাহ’ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ রাসূল, ততক্ষণ আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এটা বলবে, তার ধন ও প্রাণ আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। অবশ্য ইসলামী বিধান অনুসারে তাতে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হলে সে কথা স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আয়ত্তাধীন।’’ এতে হযরত আবু বকর রা. পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন যে, ‘‘খোদার শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতে প্রভেদ করবে আমি তার সাথে যদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হলো ধন-সম্পদের ওপর ধার্য অধিকার বিশেষ।’’ সংগে সংগে হযরত ওমর রা. বলে উঠলেন, ‘‘খোদার শপথ! আমি অনুভব করতে পেরেছি যে, আল্লাহ আবু বকরের বক্ষকে যুদ্ধের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এখন আমিও বুঝতে পেরেছি যে, এটাই সঠিক পন্থা।
এই মহান যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ইতিহাসে ইসলামের একটি মূলনীতিকে কার্যকরী করে দেখিয়ে দিলেন। তিনি সপ্রমাণ করলেন যে, আল্লাহ ধন-সম্পদে সমাজের জন্য যে হারে ও যে নিয়মে অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা আদায় করার জন্য যুদ্ধ করাও ন্যায়সংগত।
হযরত আবু বকর রা. যাকাত, গণিমত ও ‘ফায়’ প্রভৃতির তহবিল নির্ধারিত খাতে ব্যায় করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. এর পদানুসরণ করতে থাকেন। তিনি নিজেদের জন্য মুসলমান জনসাধারণের নির্ধারিত মামুলী বৃত্তি গ্রহণ করতেন আর সেটা ছিল দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম। এর পর তিনি জনগণকে নির্ধারিত বৃত্তি প্রদান করতেন। অতঃপর অবশিষ্ট অর্থ তিনি সামরিক খাতে ব্যয় করতেন।
হযরত আবু বকরের যুগে অপর একটি ব্যাপারেও হযরত ওমরের সাথে তাঁর মতভেদ ঘটে। হযরত আবু বকরের অভিমত ছিল, ধন বণ্টনের ব্যাপারে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং পরবর্তী যুগে ইসলাম গ্রহণকারী, স্বাধীন ও গোলাম, নারী ও পুরুষ সকলকে সমান অংশ দেওয়া উচিত। কিন্তু হযরত ওমর রা. ও সাহাবাদের একটি দল ইসলামের প্রতি প্রথম অগ্রসর ব্যক্তিদের পর্যায়ক্রমে অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। হযরত আবু বকর রা. তাদের লক্ষ্য করে বলেন, ‘‘তোমরা যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের কথা বলছ, সে সম্পর্কে আমি উত্তম রূপে ওয়াকিবহাল। কিন্তু আসলে ওটা এমন একটা ব্যাপার, যার সওয়াব আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে প্রদান করবেন। পক্ষান্তরে এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যাপার। এখানে অগ্রাধিকারের চাইতে সমাধিকারের নীতিই উত্তম।’’
বস্তুতঃ এই সমাধিকারের নীতি অনুসরণই অব্যাহত থাকে এবং আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ যতই বাড়তে থাকে ততই সমান হারে মুসলমানদেরকে স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে থাকে। অবশেষে ওমর ইবনে খাত্তাবের রা. যুগ এলো। তিনি তখনো একই অভিমত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, ‘‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সা. বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাকে আমি রাসূলুল্লাহর সা. পক্ষে যুদ্ধকারীর সম-মর্যাদা দিতে পারি না।’’
একদিন বাহরাইনের শাসনকর্তা আবু হোরাইরা রা. বহু অর্থ-সম্পদ নিয়ে খলিফার দরবারে উপনীত হন। তাঁর ভাষায়, ‘‘পাঁচ লাখ দিরহাম নিয়ে আমি সন্ধ্যা বেলায় ওমরের সাথে সাক্ষাত করি। আমি বললাম, ‘আমিরুল মু’মিনীন! এই নিন টাকা।’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কত টাকা?’ আমি বললাম, ‘পাঁচ লাখ দিরহাম।’ তিনি বললেন, ‘জান, পাঁচ লাখে কত হয়।’ আমি বললাম, ‘জি হাঁ, পাঁচশো হাজার।’ কিন্ত তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন, ‘মনে হচ্ছে তোমার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। যাও রাত্রে আরাম কর গিয়ে। সকালে এস।’ আমি সারারাত বিশ্রাম করে ভোরে আবার এসে বললাম, ‘আমিরুল মু’মিনীন! টাকা নিন।’ তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ টাকা ন্যায়সঙ্গত পন্থায় অর্জিত হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘যতদূর আমার জানা আছে, ন্যায়সঙ্গত পন্থায়ই অর্জিত হয়েছে।’ তখন হজরত ওমর রা. উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘ভাই সব! আমাদের কাছে বহু অর্থ এসেছে। তোমরা মেপে-গুণে অথবা ওজন করে যেভাবে ইচ্ছা বন্টন করে নিতে পার।’ এক ব্যক্তি উঠে বললোঃ ‘আমিরুল মু’মিনীন। আপনি যথারীতি হিসাবের খাতা তৈরী করে নিন এবং সেই হিসাবের বিবরণ অনুসারে লোকদের মধ্যে বণ্টন করুন। হযরত ওমর রা. এ প্রস্তাব পছন্দ করেন। তিনি মুহাজেরদের জন্য মাথা প্রতি ৫ হাজার, আনসারদের জন্য মাথা প্রতি ৩ হাজার এবং নবীর সা. মহিষীদের জন্য মাথা প্রতি ১২ হাজার দিরহাম ধার্য করেন।
এখানে আমরা এ রেওয়ায়েত এই জন্য উদ্ধৃত করেছি যাতে অগ্রাধিকার দান সম্পর্কে হযরত ওমরের রা. নীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এ দ্বারা সেই সময়কার প্রাচুর্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। অর্ধ মিলিয়ন দিরহাম তখন এমন একটা স্বপ্ন বলে মনে হতো যেন এ কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারে না। অবশ্য পরবর্তী যুগে বড় বড় বিজয়ের ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তার কিতাবুল খারাজে লিখেন, ‘‘হযরত ওমর রা. বলেছেন, ‘খোদার শপথ! এই ধন-সম্পদে (বাইতুল মালের ধনসম্পদে) প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে। এতে কারো অধিকার অপরের চেয়ে বেশী নয়। এ ধরণের ব্যাপারে আমিও তোমাদেরই মত একজন। তবে আমাদের মর্যাদার তারতম্য আল্লাহর কিতাবের আলোকে এবং রাসূলুল্লাহর সা. সাহচার্য অনুপাতে নির্ধারিত হবে। ইসলামের জন্য কে কি পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং কে কত আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা বিবেচনা করতে হবে, মুসলমান অবস্থায় স্বচ্ছলতা অথবা দারিদ্রের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হবে। খোদার শপথ! আমি যদি বেঁচে থাকি তবে সানার পাহাড়ে মেষচারণকারী রাখালও বিনা পরিশ্রমে নিজের জায়গায় বসেই ধন-সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য অংশ লাভ করতে পারবে।’’
‘‘তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক ৫ হাজার দিরহাম, ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং হাবশায় হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক ৪ হাজার দিরহাম এবং বদর-যোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের মাথা প্রতি ২ হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করেন। হযরত হাসান রা. ও হযরত হোসেনের রা. জন্য বার্ষিক ৫ হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারিত করেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য তিনি বার্ষিক ৩ হাজার দিরহাম এবং মক্কা বিজয়ের পর ঈমান আনয়নকারীদের জন্য মাথা প্রতি ২ হাজার দিরহাম এবং আনসার ও মোহাজেরদের তরুণ পুত্রদের জন্যও অনুরূপ বৃত্তি নির্ধারণ করেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণে তিনি তাদের সামাজিক মর্যাদা, কোরআনের জ্ঞান এবং ইসলামের পথে জেহাদকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সবাইকে তিনি এক সারিতে রাখেন। যে কোন মুসলমান মদিনায় এসে অবস্থান করলে তার জন্য ২৫ দিনার বৃত্তি ধার্য করা হতো। সিরিয়া ও ইরাকের মতই ইয়ামেনবাসীদের জন্যেও দুই হাজার, এক হাজার, নয়শো, পাচশো’ এবং তিনশ’ দিরহাম করে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। তিনশ’র চেয়ে কম কারো ছিল না। তিনি বলতেন যে, সম্পদ যদি আরো বর্ধিত হয় তাহলে আমি প্রত্যেকের জন্য চার হাজার দিরহাম ধার্য করবো- এক হাজার তার সফরের জন্য, এক হাজার অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য, এক হাজার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়ার জন্য এবং এক হাজার তার ঘোড়া ও খচ্চরের জন্য।’’ (আল-ফারুক ওমর, দ্বিতীয় খণ্ড; ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হাইকেল)
বৃত্তি ধার্য করার ব্যাপারে হযরত ওমর রা. যে নীতি নির্ধারণ করেন কোন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে তা অনুসরণ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। এই সব ব্যক্তিকে তিনি তারই সমপর্যায়ের অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক বৃত্তি দেন।
ওমর ইবনে আবি ছালমার জন্য তিনি ৪ হাজার দিরহাম ধার্য করেন। ইনি হলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমার পুত্র। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস এতে আপত্তি জ্ঞাপন করে আমিরুল মুমিনীনকে বলেন, ‘‘আপনি ওমরকে কিসের ভিত্তিতে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন? তার পিতার মত আমাদের পিতারাওতো হিযরত এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।’’ আমিরুল মুমিনীন তাকে জবাব দেন, ‘‘আমি তাকে, রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট তার মর্যাদা ছিল ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার নিকট আপত্তি করছে সে উম্মে সালমার মত মা নিয়ে আসুক, আমি তার কথা মেনে নেব।’’ তিনি উসামা ইবনে জায়েদের জন্য চার হাজার দিরহাম ধার্য করেন। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, ‘‘আপনি আমার জন্য তিন হাজার ধার্য করলেন। আর উসামার জন্য চার হাজার ধার্য করলেন। অথচ আমি এমন বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি যাতে উসামা অংশগ্রহণ করেননি।?’’ হযরত ওমর রা. তাকে জবাব দিলেনঃ ‘‘আমি তাকে এ জন্য বেশি দিয়েছি যে, সে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। তার পিতাও রাসূলুল্লাহর সা. নিকট তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন।’’ তিনি হযরত আবু বকরের রা. স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের জন্য এক হাজার দিরহাম, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার জন্য এক হাজার দিরহাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মায়ের জন্য এক হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। এই সব মহিলাকে তিনি তাদেরই সমপর্যায়ের অন্যান্য মহিলার চেয়ে বেশি দেন, কেননা তারা যে সব পুরুষের স্ত্রী কিংবা মা ছিলেন, তাদের অন্যান্য পুরুষের ওপর অগ্রাধিকার ছিল।’’ (আল-ফারুক ওমর, দ্বিতীয় খণ্ড, হাইকেল)
এখানে ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে আবু বকর ও ওমরের দুটো পৃথক অভিমত দেখা যাচ্ছে। ওমরের অভিমতের ভিত্তি ছিল, ‘‘যারা রাসূলুল্লাহর সা. বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তাদেরকে আমি তাঁর পক্ষে যোদ্ধাদের সমপর্যায়ে গণ্য করতে পারবো না।’’ এছাড়া ইসলামের পথে দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরদাশত করাকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করার জন্যও ইসলামে ভিত্তি রয়েছে। সেই ভিত্তি হচ্ছে শ্রম ও শ্রমের মজুরীর মধ্যে সমতার নীতি। এমনিভাবে আবু বকরের রা. অভিমতেরও ভিত্তি রয়েছে, ‘‘লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং তার প্রতিদানও তার হাতে নিবদ্ধ। তিনি কেয়ামতের দিন এর পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। দুনিয়ায় কারো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের চেয়ে বেশী অধিকার নেই।’’
কিন্তু আমরা কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ ছাড়াই হযরত আবু বকরের মতকে অগ্রাধিকার দেব। কারণ এটা মুসলমানদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। আর জানা কথা এই যে, সাম্য হচ্ছে ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ নীতি সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারেও অধিক সহায়ক- যা এই বৈষম্য নীতি গ্রহণ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। এক শ্রেণীর লোকের সম্পদ বর্ধিত হয়ে গিয়েছিল এবং বছরের পর বছর মুনাফার দ্বারা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল। ধন-বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, মুনাফার মাধ্যমে সম্পদ যত বাড়ে, তা মূলধনের বৃদ্ধি অনুপাতে অনেক বেশী। স্বীয় অনুসৃত নীতির এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে হযরত ওমর রা. তার জীবনের শেষ ভাগে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পরবর্তী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকলে সকলের বৃত্তি সমান করে দেবেন। এই সময়ে তার এ উক্তি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেঃ
‘‘যে সব সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছি তা পুনরায় করার সুযোগ পেলে ধনিকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতাম।’’
কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। বৈষম্যমূলক বণ্টন নীতির যে সব কুফল দেখা দেয় তা গোটা ইসলামী সমাজের ভারসাম্য ব্যাহত করে। এরপর যখন মারওয়ানের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপ শুরু হয় এবং হযরত ওসমান রা. তা বরদাশত করতে থাকেন তখন সমাজ মারাত্মক বিপর্যয়ের কবলে পতিত হয়।
মর্যাদার পার্থক্য অনুসারে ধন-বণ্টনের কুফল দেখে হযরত ওমর রা. নিজের মত পরিত্যাগ এবং হযরত আবু বকরের রা. মত গ্রহণ করেন। হযরত আলীর রা. মতও ছিল প্রথম খলিফার ন্যায়।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা হযরত আলীর খেলাফতকে প্রথম দুই খলিফার খেলাফতেরই স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বলে মনে করি। আর হযরত ওসমানের যুগকে মনে করি একটি শূণ্যতা, যা আলী ও পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের মাঝে বিভেদের দেয়াল টেনে দিয়েছিল। কারণ এ সময়ে মারওয়ানই ছিল আসল শাসন পরিচালক। এ জন্য এখন আমরা হযরত আলী রা. সম্পর্কে আলোচনা করবো, এর পর আলোচনা করবো হযরত ওসমানের রা. যুগ সম্পর্কে।
হযরত আলী বৃত্তি বণ্টনের ব্যাপারে সাম্যের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম ভাষণেই স্পষ্ট করে বলেনঃ
‘‘শোনো! রাসূলুল্লাহর সা. সাহাবীদের মধ্যে আনসার কিংবা মোহাজের-যেই মনে করে যে, রাসূলুল্লাহর সা. সাহচর্যের কারণে অন্যান্যদের ওপর তার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার রয়েছে, তার জানা উচিত যে, এই অগ্রাধিকার সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট লাভ করবে এবং তার প্রতিদানও সেখানে পাবে। ভালো করে বুঝে নাও! যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়, আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেয়, আমাদের জীবন-বিধান গ্রহণ করে এবং আমাদের কেবলা অভিমুখী হয়- ইসলামের যাবতীয় অধিকার ও কর্তব্য তার ওপর অর্পিত হয়। তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা, আর এ সমস্ত সম্পদ আল্লাহর। এটা সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। এ ব্যাপারে কেউ অপর কারো ওপর অগ্রাধিকার পাবে না। অবশ্য খোদাভীরু লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’’
এটাই প্রকৃত ইসলামী বিধান, ইসলামের সাম্যের আদর্শের সাথে এর পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। এটা ইসলামী সমাজে ভারসাম্য রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় এবং এতে কেবল কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনা দ্বারাই সম্পদ বাড়ানো যায়। এই নীতি কাউকে লাভজনক কাজের জন্য অপরের চেয়ে বেশী অর্থ সরবরাহ করে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেয়ার অবকাশ রাখে না।
হযরত ওমর রা. জীবনের শেষ ভাগে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সময় পাননি। আকস্মিক শাহাদাতের ফলে তিনি তাঁর দু’টো ইচ্ছা সফল করতে পারেননি। একটা হলো তিনি চেয়েছিলেন যে, ধনিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবেন। কেননা এই অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল শুধুমাত্র সরকারী অর্থের অসম বণ্টনের ফলে। দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল তিনি ধনবন্টনের ব্যাপারে সম-অধিকার নীতি প্রবর্তন করবেন।
হযরত ওসমান রা. যখন খলিফা হলেন তখন তিনি এই দু’টো সিদ্ধান্তের একটিও কার্যকরী করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি বাড়তি অর্থ তার মালিকের হাতেই ছেড়ে দেন এবং বৃত্তি বন্টনেও বৈষম্য বহাল রাখেন। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে মুক্ত হাতে আরো উপঢৌকনাদি দিতে থাকেন। এর ফল দাঁড়াল এই যে, ধনীরা আরো বেশি ধনী এবং গরীবরা আরো গরীব হয়ে পড়ে। অবশ্য গরীবরাও কখনো কখনো স্বচ্ছলতা বোধ করতো। যাদের ধন-দৌলতের কোন অভাব ছিল না তিনি তাদেরকেও বড় বড় অংকের অর্থ সাহায্য করেন। কোরেশদেরকে তিনি সারা দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অবাধ সুযোগ দেন। তিনি বড় বড় ধনীদেরকে সাওয়াদ অঞ্চলে অথবা বিদেশে দালান কোঠা ও জায়গা-জমি খরিদ করারও সুযোগ দেন। এর পরিণতি স্বরূপ তাঁর খেলাফতের শেষের দিকে সমগ্র মুসলিম সমাজে ধন-বণ্টনে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাঁর ওপর অনুগ্রহ করুন।
হযরত আবু বকর রা. ও তার পর হযরত ওমর রা. এই নীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে কার্যকরী করতেন যে, কোরাইশ প্রধানদের একটি উল্লেখযোগ্য দলকে মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য করতেন। তাই আবু বকর রা. ও ওমর রা. তাদেরকে বিজিত দেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দিতেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা, ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং জেহাদে তাদের অগ্রসরতার দরুণ জনগণ বিশেষভাবে তাদের ভক্ত ও অনুরক্ত হতে পারে এবং তখন এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধন-সম্পদ, দক্ষতা ও পদের লিপ্সা জন্মাতে পারে। এটাকে অবশ্য ইসলামের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ বলা যেতে পারে না। কেননা ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের শর্তের সাথে জড়িত। যখন হযরত ওসমানের যুগ এলো, কখন তিনি তাদেরকে সর্বত্র অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা দান করলেন। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে বিজিত দেশ সমূহে ঘর-বাড়ী ও জায়গা-জমি ক্রয় করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করলেন। আর এটা করলেন তখনি- যখন তিনি তাদেরকে লাখ লাখ দিরহাম দিয়ে ফেলেছেন।
নিঃসন্দেহে মুসলমানদের এবং বিশেষতঃ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে উদার ও সদয় ব্যবহার হিসেবেই এ সব করা হয়েছিল। কিন্তু এই নীতির অত্যন্ত মারাত্মক কুফল দেখা দেয়। সে কুফল আবু বকর রা. ও ওমরের রা. দৃষ্টি থেকে গোপন ছিল না। এর ফলে মুসলমানদের সমাজে বিপুল আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজে একটি অলস ও নিষ্ক্রীয় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। চরম নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও তাদের ধন সম্পদের অন্ত ছিল না। বিনা চেষ্টায় বসে বসে তারা পরম তৃপ্তিকর জীবন যাপন করতো।
এভাবে বিলাসিতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। অথচ এই বিলাসিতার বিরুদ্ধে ইসলাম তার আইন-কানুন ও নীতিমালা উভয়ের মাধ্যমেই অবিরাম যুদ্ধ ঘোষণা করে আসছিল। হযরত ওসমানের পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং এটা যাতে কোনক্রমেই মাথা তুলতে না পারে তার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয় তখন কতিপয় লোকের মধ্যে ইসলামী প্রাণশক্তির বিষ্ফোরণ ঘটে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত আবু জর। তিনি ছিলেন সবচেয়ে স্পষ্টবাদী ও বিপ্লবী।
দুঃখের বিষয়, হযরত আবু জরের নীতিকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে মিশরের দারুল ইফতা সম্প্রতি এক ফতোয়া দিয়ে আবু জরের চেয়ে বেশি ইসলাম বুঝার দাবী ফলাতে চেষ্টা করেছেন। খোদার দ্বীন তাদের নিকট যেন ব্যবসা-পণ্যে পরিণত হয়েছে।
আবু জর রা. মুসলিম সমাজের উঁচু তলার লোকদের বিলাসিতাকে পূর্ণোদ্যমে চ্যালেঞ্জ করেন। কেননা ওটা ছিল ইসলামের একেবারেই পরিপন্থী। এই বিলাসিতার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বনু উমাইয়া ও হযরত মুয়াবিয়ার সমালোচনা করেন। কেননা তার এ নীতির দরুন ধনিকদের ধন এবং বিলাসীদের বিলাসিতাই কেবল বেড়ে চলছিল।
আবু জর রা. জানতে পারলেন যে, হযরত ওসমান রা. মারওয়ানকে আফ্রিকার রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ, হারেসকে দুই লাখ দিরহাম এবং জায়েদ ইবনে ছাবেতকে এক লাখ দিরহাম দান করেছেন। এটা তার বিবেকের পক্ষে অসহনীয় ছিল। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করে এক জনসভায় নিম্নরূপ বক্তৃতা দেনঃ
‘‘আজকাল এমন সব কাজ করা হচ্ছে যা আমার বুদ্ধির অগম্য। খোদার শপথ! এ সব কাজের পেছনে আল্লাহর কোরআনে কিংবা রসূলের হাদীসে কোথাও কোনো ভিত্তি নেই। খোদার শপথ! আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সত্য পদদলিত হচ্ছে, বাতিলকে পুনরায় জীবন্ত করে তোলা হচ্ছে, সত্যবাদী লোকদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করা হচ্ছে এবং ‘তাকওয়া’ ও খোদাভীতি ছাড়াই লোকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। হে ধনিক সমাজ! তোমরা গরীবদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার কর। যারা টাকা-পয়সা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে জানিয়ে দাও যে তাদের কপালে, পিঠে ও পার্শ্বে আগুন দিয়ে দাগানো হবে। হে পুঁজিপতিরা! জেনে রাখ, ধন-সম্পদে তিনজন অংশীদার রয়েছেঃ প্রথমতঃ অদৃষ্ট। এটা যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে তোমাদের বিনা-অনুমতিতে তোমাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকারী। সে সব সময় অপেক্ষা করছে, কখন তোমার চোখ মুদিত হবে এবং সে তোমার ধন-সম্পদ কুক্খিগত করবে। তৃতীয়তঃ তোমার অধিকার। যদি তুমি এই তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশীদার না হতে চাও তবে সে জন্য অবশ্যই চেষ্টা কর। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
‘‘তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয়তম সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে না।’’ বন্ধুগণ! তোমরা এখন রেশমী পর্দা এবং মখমলের বালিশ ব্যবহার করা শুরু করেছে। আজকাল আজার বাইজানের গদিতে শয়ন করা তোমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. শুধু চাটাই-এর ওপর শয়ন করতেন। তোমরা আজ রকমারী খাদ্য খাও অথচ রাসূলুল্লাহ সা. পেট ভরে জবের রুটিও পেতেন না।’’
মালেক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বর্ণনা করেন যে, একবার আবু জর রা. হযরত ওসমানের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকলে আবু জর রা. একখানা লাঠি হাতে করে দরবারে উপস্থিত হন। এই সময়ে হযরত ওসমান রা. কা’ব নামক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ‘‘কা’ব, আবদুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বহু টাকা রেখে গেছেন। সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?’’ কা’ব বললেন, ‘‘তিনি যদি তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করে থাকেন তাহলে আর তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করা যায় না।’’ এ কথা শোনামাত্র আবু জর রা. তার লাঠি উত্তোলন করলেন এবং কা’বকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যেঃ
‘‘যদি আমার কাছে এই পর্বতের সমান সোনা থাকতো এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম ও তা আল্লাহ গ্রহণ করতে থাকতেন তবে আমি তা থেকে ছয় উকিয়া পরিমাণ স্বর্ণও রেখে যাওয়া পছন্দ করতাম না।’’ এই হাদীস বর্ণনা করে তিনি হযরত ওসমানকে তিনবার খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আপনি কি এ হাদীস শুনেছেন?’’ তিনি বললেন, ‘‘হাঁ!’’ (৪৫৩ নম্বর হাদীস- মুসনাদে আহমদ)
এ ধরণের আহ্বান বরদাশত করা মারওয়ান ও মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা অবিরাম হযরত ওসমানকে তার বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবু জরকে উপযুক্ত শরিয়ত সম্মত অপরাধ ছাড়াই দেশান্তরিত হয়ে ‘রবজা’য় চলে যেতে হয়।
দেশে সম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও অর্থলিপ্সা যাকে পর্যদস্ত করতে পারেনি সেই জাগ্রত বিবেকের পক্ষ থেকেই এই উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছিল। তখন সম্পদের কেন্দ্রায়ণ এমন প্রকট হয় যে, ইসলামী সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ইসলামের প্রধান প্রধান মূলনীতিগুলো অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। আমরা এই সময়কার আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে মাসউদী বর্ণিত কতিপয় নমুনা পেশ করছি। তিনি বর্ণনা করেনঃ
‘‘ওসমানের রা. আমলে সাহাবারা বিপুল ধন-সম্পদ উপার্জন করেন। যেদিন ওসমান রা. শাহাদাত বরণ করেন, সেদিন তার কোষাধ্যক্ষের নিকট তার দেড় লাখ দিনার ও দশ লাখ দিরহাম নগদ জমা ছিল। ওয়াদিল কুরা ও হোনাইন প্রভৃতি স্থানে তাঁর যে ভূ-সম্পত্তি ছিল তার দাম ছিল এক লাখ দিনার। এ ছাড়াও তিনি বহু সংখ্যক ঘোড়া ও উট রেখে যান। জোবায়ের রা. এর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত একটি ভূ-সম্পত্তির মূল্যই ছিল ৫০ হাজার দিনার। তা ছাড়া তিনি এক হাজার ঘোড়া ও এক হাজার বাঁদী রেখে যান। তালহার রা. ইরাক থেকে দৈনিক এক হাজার দিনার এবং সারাত থেকে এর চেয়েও বেশী আয় হতো। আবদুর রহমান ইবনে আওফের আস্তাবলে এক হাজার ঘোড়া ছিল, তার এক হাজার উট এবং দশ হাজার ছাগল-ভেড়াও ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের মূল্য দাঁড়ায় ৮৪ হাজার দিরহাম। জায়েদ ইবনে ছাবেত এত বেশী সোনা রূপা রেখে যান যে, তা কুড়াল দিয়ে কাটতো হতো। যে সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তিনি রেখে যান তা এ থেকে পৃথক। জোবায়ের বসরায়, মিশরে, কুফায় ও আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি করে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এমনভিাবে তালহা রা. কুফায় একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মদিনায়ও তিনি সেগুনের কাঠ ও চুন-সুরকী দিয়ে একটি বিরাট কোঠা নির্মাণ করেন। সা’দ ইবনে আবি আক্কাস আকিকে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গন গম্বুজসহ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মিকদাদ মদিনার ভিতরে ও বাইরে কারুকার্যখচিত এক মনোরম প্রাসাদ তৈরী করেন। ইয়ালা ইবনে মুম্বা ৫০ হাজার দিনার নগদ এবং তিন লাখ দিরহাম মূল্যের ভূ-সম্পত্তি রেখে যান।’’ (ওসমান- উস্তাদ ছাদেক উরজুন)
ওমরের রা. আমলে ধন বণ্টনে মর্যাদার তারতম্য করার অনিবার্য ফল হিসাবে সম্পদের এই ভারসাম্যহীন প্রাচুর্যের উৎপত্তি হয়। হযরত ওমর রা. এ নীতি ও এর ফলাফলের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এটার অবসান করেই ছাড়তেন যদি তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ না হতো। তার শাহাদাতের পর এ প্রাচুর্য ক্রমশঃ বেড়েই যেতে থাকে। হযরত ওসমান রা. সে নীতি অব্যাহত রাখেন এবং তার ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। হযরত ওসমান রা. অসম বণ্টন ছাড়াও যে সব উপহার-উপঢৌকনাদি এবং জায়গীর ইত্যাদি প্রদান করেন সেগুলোও মুসলিম সমাজে ধনবাদী প্রবণতা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে সহায়তা করে। এরপর এমন কতগুলো কার্যকারণ আত্মপ্রকাশ করে যার দরুণ ধন-সম্পদের ভারসাম্যহীন প্রাচুর্য অস্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করে। বিশেষতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একত্রিকরণ এবং লাভজনক কারবারের উপায়-উপকরণ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজে পুঁজিবাদী প্রবণতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। আবু জরের মন থেকে যে গভীর ও আন্তরিকতা পূর্ণ আবেদন বহির্গত হয়েছিল তার বিরোধিতা ও উপেক্ষার কারণেও পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। যদি তার আবেদন সফলকাম হতো এবং রাষ্ট্র প্রধানকে তিনি স্ব-মতে দীক্ষিত করতে পারতেন তাহলে তার মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার যোগ্যতা ছিল। এতে করে ধনিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা সম্পর্কিত হযরত ওমরের শেষ সংকল্প পূর্ণ হতো। জাতিকে পুজিবাদী অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের এরূপ করা সম্পূর্ণ বৈধই শুধু ছিল না বরং বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের খাতিরে অবশ্য কর্তব্যও ছিল।
একদিকে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবারের সদস্যদের জীবনে প্রাচুর্যের বান ডেকেছিল। অপরদিকে ঠিক তেমনি তীব্রতা ও প্রাবল্য নিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র ও হাহাকার আঘাত হানছিল সাধারণ মানুষের জীবনে। এতে স্বভাবতই বিদ্বেষ ও ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। এই সমস্ত কার্যকারণ অব্যাহত গতিতে পুঞ্জিভূত হতে থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত এক বিভীষিকাময় সহিংস অভ্যুত্থানের সূচনা করে ছাড়ে। এই অভ্যুত্থানে ইসলামের শত্রুদেরই উপকার সাধিত হয় এবং তা হযরত ওসমানের প্রাণ সংহার করে। সেই সাথে মুসলিম উম্মতের শান্তি ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয় এবং তাকে বিশৃংখলা ও উত্তেজনার গভীরতম আবর্তে নিক্ষেপ করে। যতক্ষণ স্বয়ং ইসলামের প্রাণশক্তি এই বিশৃংখলার আগুনে ধূমায়িত না হয় এবং উম্মত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের হিংস্র থাবায় আক্রান্ত না হয় ততক্ষণ এ বিশৃংখলার আগুন নির্বাপিত হয়নি।
ওসমানের রা. পর আলী রা. সাম্য ও ন্যায় বিচারের যে নীতি গ্রহণ করেন, তাতে পুঁজিবাদী মহল এবং যারা সম্পদের অসম-বণ্টন দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হয়েছিল তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; এটা আদৌ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল না। তারা হযরত আলীকে এ নীতি পরিহার করার পরামর্শ দেয় এবং আশংকা প্রকাশ করে যে, এতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। তাঁর জাগ্রত বিবেকে ইসলামের যে দীপশিক্ষা প্রজ্জ্বলিত ছিল তদনুসারে তার এই জবাব দেয়াই স্বাভাবিক ছিল যে, ‘‘তোমরা কি আমাকে আমার দেশবাসীর ওপর জুলুম করে অন্য কারো সাহায্যে গ্রহণের পরামর্শ দিতে চাচ্ছ? এ ধন-সম্পদ যদি আমার হতো তথাপি আমি এর বণ্টনে সাম্য অবলম্বন করতাম। আর এটা যখন আল্লাহর সম্পদ, তখন আমি কি করে বে-ইনসাফী করতে পারি? জেনে রাখ, সম্পদ অন্যায়ভাবে কাউকে দেয়া অপব্যায়ের আওতায় পড়ে। সন্দেহ নেই যে, এতে করে দানকারী দুনিয়ায় খানিকটা মর্যাদাশীল হতে পারে, কিন্তু আখেরাতে এরূপ নীতি তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।’’
বনু উমাইয়া অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপারে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। অবশেষে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগ এলে তিনি অন্যায়ভাবে অর্জিত ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণ এবং অপব্যয় রোধ করার কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। এই সময়ে বনু উমাইয়ার লোকেরা বাইতুল মালের অর্থ সম্পদের ব্যাপারে অন্যান্য প্রজাদের সমানাধিকার পায়। তখন আর চাটুকার, স্তুতিবাদী কবি ও গায়কদের কোনো অংশ তাতে ছিল না। তিনি কবিদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বাইতুল মাল থেকে তাদের পুরস্কার দেয়ার নীতি রহিত করেন।
একবার কবি জারির তার প্রশংসা করে এক কবিতা পাঠ করেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাকে বলেন, ‘‘জারির! তুমি কি মোহাজেরদের সন্তান, যে তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তা তোমাকেও দেব? তুমি কি আনসারদের সন্তান, যে তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তা তোমাকেও দেব? না তুমি কোন গরীব লোক, যে তোমাকে তোমার জাতির ছদকা ও জাকাতের তহবিল থেকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দেব?’’
সে জবাব দিল, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আমি এর কোনোটি নই। বরং আমি সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। আমাকে সাবেক শাসকরা এর পুরস্কার হিসাবে চার হাজার দিরহাম ও তার সাথে মূল্যবান কাপড়-চোপড় ও সওয়ারীর জন্তু দিতেন। ওগুলো গ্রহণ করার আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাই আপনার কাছে আমি সেই পুরস্কার চাই।’’
ওমর জবাব দিলেন, ‘‘প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের প্রতিফল আল্লাহর কাছে পাবে। তবে আমার যতদূর জানা আছে, আল্লাহর সম্পদে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) তোমার কোন প্রাপ্য নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত ভাতা লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি হিসাব করে দেখবো যে, আমার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য সারা বছরে কত লাগে। যত লাগে ততটা আমি রেখে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তোমাকে দিয়ে দেব।’’ জারির বললো, ‘‘না আমার দরকার নেই। আল্লাহ আমিরুল মু’মিনীনকে আরো বেশী দান করুক এবং তার আরো বেশী প্রশংসা করা হোক এই কামনা করি। আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট মনে বিদায় হচ্ছি।’’ তিনি বললেন, ‘‘এটাই আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা।’’ জারির সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে ওমর ভাবলেন, ও আবার নিন্দাবাদও করতে পারে। এর একটা প্রতি-বিধান করা উচিত। এই ভেবে তিনি তাকে পুনরায় ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। জারির এলে তিনি বললেন, ‘‘আমার কাছে চল্লিশটি দিনার ও দুই জোড়া কাপড় আছে। এর এক জোড়া ধুয়ে অপর জোড়া পরি। আমি এই জিনিসগুলোর অর্ধেক তোমাকে দিতে পারি। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী আছেন যে, তোমার চাইতে ওমরের এই জিনিসগুলোর বেশী প্রয়োজন।’’ জারির বললো, ‘‘আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে আরো বেশী দিন। খোদার শপথ! আমি সন্তুষ্টচিত্তেই যাচ্ছি। এগুলোর আমার কোনো দরকার নেই।’’ তিনি বেললেন, ‘‘বেশ! তাহলে তুমি যখন শপথ করে বললে, তখন আমি তোমাকে বলতে চাই যে, তুমি এই প্রার্থনা ও পুরস্কার গ্রহণ না করে আমাদেরকে যে অনটন থেকে অব্যাহতি দান করলে সেটা আমাকে তোমার কবিতা ও স্তুতিবাদের চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। এখন তুমি আমার বন্ধু হয়ে যাও।’’
মুসলমানদের সম্পদকে যখন এভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং তাকে তার আসল পাওনাদারদের নিকট পৌঁছানো হয়েছে তখন আর বর্ণনাকারীদের এ বর্ণনায় বিস্ময়ের কিছু থাকে না যে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগে লোকেরা এত স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিল যে, যাকাত নেয়ার লোক পাওয়া যেত না, কেননা তারা তাদের অন্যায্য ন্যায্য পাওনা পেয়ে যাকাতের দিক থেকে অভাব শূণ্য হয়ে গিয়েছিল।
ইয়াহিয়া ইবনে সা’দ বর্ণনা করেন, ‘‘আমাকে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ যাকাত ও ছদ্কা সংগ্রহের জন্য আফ্রিকায় পাঠান। আমি সেখানকার যাকাত ও ছদ্কা সংগ্রহ করে তা বিতরণ করার জন্য গরীব লোকদের সন্ধান করি। কিন্তু কোনো গরীব লোক আমি সেখানে পাইনি। কোনো ব্যক্তিই সেখানে অর্থ গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। কারণ ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাদের সকলকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে আমি সেই অর্থ দ্বারা গোলাম ক্রয় করে স্বাধীন করে দেই।’’
আসল ব্যাপার হলো, দারিদ্র ও অভাব শুধুমাত্র সম্পদের কেন্দ্রীকরণেরই সৃষ্টি। প্রত্যেক যুগে গরীব লোকেরা বৃহৎ পুঁজিপতিদের জুলুম-উৎপীড়ন ও শোষণের শিকার হয়ে থাকে, আর এই বৃহৎ পুঁজিপতিরা আত্মপ্রকাশ করে বড় বড় দান, উপঢৌকন, পুরস্কার, জায়গীর, শোষণ, জুলুম ও মুনাফাখুরীর বলে।
উমাইয়া ও তার পরবর্তী আব্বাসীয় শাসনামলে সরকারী কোষাগার বাদশাহদের জন্য নিজের সম্পদের মতই ‘‘হালাল’’ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে দু’টো পৃথক পৃথক কোষাগার স্থাপন করা হয়। একটি সাধারণ কোষাগার- অপরটি বিশেষ কোষাগার। শোষোক্তটি সম্পর্কে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ওটার আয় ও ব্যয় বাদশাহর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এরূপ বহু দেখা যেত যে, কোনো সাধারণ খাতের অর্থ বিশেষ কোষাগারে দাখিল করা হয় আবার কোনো বিশেষ ব্যয় সাধারণ কোষাগার থেকে সম্পন্ন করা হয়।
অধ্যাপক আদম মেজ (Adam Mez) স্বীয় পুস্তক ‘ইসলামী সভ্যতা চতুর্থ শতাব্দী’-তে বলেনঃ
ভাতা ও রাজধানী সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের জন্য সাধারণ কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণ করা হতো। আমাদের কাছে চতুর্থ শতকের প্রথম দিকের একটি ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে যাতে বিশেষ কোষাগারের উপার্জন খাত সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ
১. সন্তান-সন্ততির জন্য পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদঃ কথিত আছে যে, সবচেয়ে বেশী সম্পদ রেখে যান হারুনুর রশীদ অর্থাৎ ৪ কোটি ৮ লাখ দিনার। মুতাজিদ (হিঃ ২৭৯-২৮৯) নিজ শাসনামলে প্রতি বছর সকল ব্যয়-বরাদ্দের পর বিশেষ উপার্জন খাত থেকে দশ লাখ দিনার সঞ্চয় করতেন। এভাবে তার কাছে ৯০ লাখ দিনার সঞ্চিত হয়। তিনি আশা পোষণ করতেন যে এক কোটি দিনার হলে তা গলিয়ে বড় একটা পিন্ড তৈরী করবেন এবং তাঁর কাছে এক কোটি দিরহাম আছে তাই তার আর কোনো অর্থের লোভ নেই এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি সেই পিন্ড প্রকাশ্য দরবারে ঝুলিয়ে রাখবেন বলেও স্থির করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, এক কোটি দিরহাম সঞ্চিত হলে তিনি এক বছরের জন্য জনগণের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা মওকুফ করে দেবেন। কিন্তু এ বাসনা পূর্ণ হবার আগেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।
মুতাজিদের পর মুকতাফির (২৮৯-২৯৫) যুগ আসে। তিনি কোষাগারের উপার্জন এক কোটি চল্লিশ লাখে উন্নীত করেন।
২. পারস্য ও কিরমান থেকে বার্ষিক গড়ে (ব্যয়ের খাত কেটে রাখার পর) হিঃ ২৯৯-৩২০ পর্যন্ত ২ কোটি ৩০ লাখ দিনার কর ও সরকারী সম্পত্তি লব্ধ অর্থ। এ থেকে চল্লিশ লাখ সাধারণ কোষাগারে ও অবশিষ্ট এক কোটি ৯০ লাখ বিশেষ কোষাগারে দাখিল করা হতো। অবশ্য এ থেকে সেই সব দেশের জরুরী প্রয়োজনের খাত সমূহে ব্যয়িত অর্থ বাদ দেয়া আবশ্যক মনে করা হতো। যেমন হিঃ ৩০৩ সালে (৯১৫ খৃঃ) এই দেশগুলো জয় করতে তিনি ৭০ লাখের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করেন।
৩. মিসর ও সিরিয়া থেকে অর্জিত অর্থঃ যেমন অমুসলিমদের ‘জিজিয়া’ সংগ্রহ করে জনসাধারণের কোষাগারে দাখিল করার পরিবর্তে খলিফার কোষাগারে জমা করা হতো। কেননা আমিরুল মুমিনীন হবার কারণে নীতিগত ভাবে ওটা তার ন্যায্য অধিকার ছিল।
৪. পদচ্যুত উজীর, সচিব ও সরকারী কর্মচারীদের উপার্জিত অর্থ, তাদের বাজেয়াফ্ত করা সম্পত্তিঃ তাছাড়া খলিফা নিজের নিঃসন্তান ভৃত্যদের এবং রাজ পরিবারের নিঃসন্তান গোলামদের উপার্জিত অর্থের মালিক হতেন। যেহেতু তারা সাধারণতঃ উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী ছিল, তাই এ উপায়ে খলিফার কোষাগারে বিপুল অর্থের সমাগম হতো।
৫. সাওয়াদ, আওয়াজ এবং অন্যান্য পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত ও সরকারী সম্পত্তি লব্ধ অর্থঃ এটাও বিশেষ কোষাগারে দাখিল করা হতো।
৬. খলিফারা যে অর্থ সঞ্চয় করতেনঃ যেমন হিঃ তৃতীয় শতকের দু’জন শেষ খলিফা মুতাজিদ ও মুকাতাফী বার্ষিক ১০ লাখ দিনার সঞ্চয় করতেন। মুকতাদিরও অনুরূপ সঞ্চয় করতেন। এভাবে পনেরো বছরে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াতো এক কোটি পঞ্চাশ লাখ অর্থাৎ প্রায় খলিফা হারুনুর রশীদের অর্থের অর্ধেক।
এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ‘খলিফা’ নামধারী এই বাদশাহরা মুসলিম জনগণের ধন-সম্পদের ওপর কিভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামো ইসলামী মূলনীতি থেকে কতখানি ভিন্ন ধরণের হয়ে পড়েছিল।
একদিকে ধনের প্রাচুর্য, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা চরমে উঠেছিল অপরদিকে তারই পাশাপাশি বঞ্চনা, ক্ষুধা ও দারিদ্রের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। ইসলামী সমাজ ইসলামী রীতি-নীতি থেকে দূরীভূত ও ইসলামী মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ফলে অবনতির সর্বনিম্নস্তর উপনীত হয়েছিল।
কতিপয় মূলনীতি
কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ইসলামের বাস্তব কর্মধারা অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপারে অনেকগুলো মূলনীতি নির্ধারিত করে দিয়েছে। মানবতার একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, উমাইয়া শাসকদের কারণে ইসলামকে তার প্রথম যুগেই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তথাপি ইসলামী ইতিহাস ইসলামের অনেকগুলো মতাদর্শকে বাস্তব রূপদান করে দেখিয়ে দিয়েছে।
বাস্তব ইতিহাস এ কথা চূড়ান্তরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেঃ
১. ইসলামে অগ্রসর ব্যক্তিদের চেয়ে দরিদ্র লোকেরা বাইতুল মালের অর্থের অধিক হকদার। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘‘আদি ইবনে হাতেম বর্ণনা করেছেন, আমি স্বীয় গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট গমন করি। তিনি তাই গোত্রের কয়েক ব্যক্তির জন্য দু’হাজার করে ভাতা নির্ধারণ করছিলেন। আদি বলেন, আমি পুনরায় তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তথাপি তিনি আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমি পুনরায় তার সামনে এসে দাঁড়ালাম এখনো তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, ‘‘আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন?’’ হযরত ওমর রা. খিল খিল করে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, খোদার শপথ! আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি। সকলে যখন কুফরির ওপর অবিচল ছিল তুমি তখন ঈমান এনেছিলে। অন্যের যখন পশ্চাদপসরণ করছিল তুমি তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলে। অনেকেই যখন প্রতারণা করছিল তুমি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলে। আমার ভালভাবেই মনে পড়ে যাকাতের যে প্রথম অর্থ দেখে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবা রা. দের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সেটা ছিল তাই গোত্রের যাকাতের টাকা। আমিই সে টাকা রাসূলুল্লাহ সা. এর দরবারে আনয়ন করেছিলাম।’’ অতপর হযরত ওমর রা. এই বলে ওজর পেশ করতে আরম্ভ করেন যে, আমি এই অর্থ থেকে শুধুমাত্র সেই সব লোকের ভাতা নির্ধারণ করেছি যারা নিজ নিজ পোষ্যদের খাদ্য না দিতে পেরে অনাহারে কষ্ট ভোগ করছে। কেননা তারা হচ্ছে গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।’’
যে ওমর রা. ইসলামের ব্যাপারে অগ্রসর লোকদের অগ্রাধিকার দানের পক্ষপাতি ছিলেন, সেই ওমরের রা. পক্ষ থেকে এ উক্তি অত্যন্ত অর্থবহ এবং এ থেকে অনেক কিছু প্রমাণিত হয়। আসলে ইসলামী সমাজে ‘প্রয়োজন’ হচ্ছে অধিকারের সর্বপ্রথম ভিত্তি। এই মূলনীতি থেকেই বুঝা যায় যে ইসলাম দারিদ্র ও অভাবের কত বড় দুশমন এবং এগুলো মোচনের চেষ্টাকে সে অন্য সকল চেষ্টার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়।
২. সমাজের এক শ্রেণী সীমাহীন প্রাচুর্যের উদ্দাম স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে আর অপর শ্রেণী থাকবে বঞ্চিত-নিঃস্ব-সর্বহারা, ইসলাম কিছুতেই এটা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। এ ধরণের অবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসলাম সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে। এটা এমন একটা মূলনীতি যা ঐতিহাসিক ভাবে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে প্রমাণিত। তিনি বনু নজীর থেকে সংগ্রহীত ‘ফায়’ এর সমগ্র অর্থই শুধুমাত্র দরিদ্র মোহাজেরদের মধ্যে বিতরণ করেন- যাতে প্রথম সুযোগেই ইসলামী সমাজে খানিকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র দু’জন দরিদ্র আনসারকে তিনি তাদের সাথে শামিল করেন। অতঃপর কোরআন এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসেঃ
‘‘যাতে করে ধন-সম্পদ শুধুমাত্র তোমাদের ধার্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবর্তনশীল না থাকে।’’
এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এর আলোকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী শাসনকারী মুসলমান শাসন মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাইতুল মাল থেকে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য করার সর্বদাই ক্ষমতা রাখে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের মধ্যে যাতে সাধারণ ভারসাম্য ব্যাহতকারী বৈষম্য বিরাজিত না থাকে এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।
৩. ক্ষমতা ও অক্ষমতা অনুপাতে করের হারে তারতম্য করা অপরিহার্য। অমুসলিমদের ওপর জিজিয়া ধার্য করার সময়ে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের ওপর নিম্নলিখিত হারে কর ধার্য করা হয়ঃ
ক. বিত্তশালী শ্রেণী- মাথা প্রতি বার্ষিক ৪৮ দিরহাম।
খ. মধ্যম শ্রেণী- মাথা প্রতি বার্ষিক ২৪ দিরহাম।
গ. দরিদ্র শ্রমজীবি- মাথা প্রতি বার্ষিক ১২ দিরহাম।
সম্পূর্ণ নিঃস্ব, দেউলে, শ্রমে অক্ষয় এবং শারীরিক অথবা মানসিক দিক থেকে পঙ্গু ব্যক্তিদের জিজিয়া মওকুফ। কেবলমাত্র স্বাধীন সুস্থমনা পুরুষদের জিজিয়া দিতে হতো। মহিলা কিংবা শিশুদের জিজিয়া দিতে হতো না।
দুর্ভিক্ষের বছর হযরত ওমর রা. জাকাত সংগ্রহ করার জন্য কর্মচারী পাঠাননি- বরং দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া পর্যন্ত জাকাত আদায় স্থগিত রেখেছিলেন। দুর্ভিক্ষ শেষে তিনি আদায়কারী পাঠান এবং সক্ষম লোকদের নিকট দ্বিগুণ জাকাত দাবি করেন। একটি দুর্ভিক্ষের বছরের দ্বিতীয়টি চলতি বছরের। অক্ষম লোকদের তিনি ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দেন যে আদায়কারী যেন তার সংগৃহীত দ্বিগুণ অর্থের এক ভাগ উক্ত অক্ষম লোকদেরকে দিয়ে আসে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ রাজধানীতে নিয়ে আসে।
৪. বল প্রয়োগ করা অথবা জীবনের প্রয়োজনীয় অর্থ থেকে কাউকে বঞ্চিত করে কর আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল। হযরত আলী রা. তার জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ দেন ‘‘তুমি যখন তাদের নিকট যাবে তখন কর আদায় করার জন্যে তাদের গ্রীষ্ম কিংবা শীতের বস্ত্র-খাদ্য-দ্রব্য ও সওয়ারীর জন্তু বিক্রি করবে না, কাউকে একটা বেত্রাঘাতও করবে না, কাউকে এক পায়েও দাঁড় করাবে না যতই খাজনা বা কর বাকী থাকুক না কেন। কেননা আমাদেরকে শুধু জন-সাধারণের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
৫. ‘‘প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ত্যাগের অনুপাতে’’ এই নীতির পাশাপাশি ‘‘প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুপাতে’’ নীতিও কার্যকরী করা অপরিহার্য। নবী করীম সা. গণিমত লব্ধ অর্থ থেকে অবিবাহিতদের জন্য এক অংশ এবং বিবাহিতদের জন্য দুই অংশ নির্ধারিত করেন। এ থেকে এ কথাই প্রামণিত হয় যে ভাতা নির্ধারণে পরিশ্রমের সাথে সাথে প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নইলে এটা জানা কথা যে, জেহাদে বিবাহিত এবং অবিবাহিতকে সমান পরিশ্রম করতে হয়। কেবল বিবাহিতের প্রয়োজন দ্বিগুণ বলে তাকে দ্বিগুণ ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে শুধুমাত্র ‘প্রয়োজন’ ও ইসলামে মালিকানা অর্জনের একটা পৃথক মাধ্যম হতে পারে। ‘সামাজিক নিরাপত্তা’র ব্যাপারে এ মূলনীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৬. প্রত্যেক অক্ষম ও অভাবী ব্যক্তির জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিধান। হযরত ওমর রা. প্রত্যেক নবজাতকদের জন্য একশো দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। শিশু একটু বড় হলে দু’শো দিরহাম এবং সাবালক হবার পর তাকে আরো বেশী দেয়া হতো। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর জন্য একশো দিরহাম এবং তাকে লালন-পালনকারীর জন্য অতিরিক্ত ভাতা দেয়া হতো, শিশুর দুধ পান করানো ও অন্যান্য ব্যয়ভার ‘বাইতুল মাল’ থেকে বহন করা হতো, আর সে বড় হলে অন্যান্য বালকদের সমান ভাতা পেত।
হযরত ওমরের এই উদারতা আসলে ইসলামের উদারতারই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ, কেননা পথে পড়া শিশু নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। সে তার অপরাধী মা-বাপের পাপের জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নয়। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত ওমর রা. অন্ধ ইহুদী ও খৃষ্টান কুষ্ঠ রোগীদের জন্য ‘বাইতুল মাল’ থেকে সাহায্য বরাদ্দ করেছিলেন। ওমরের রা. প্রকৃতিতেও উদারতা সকল মানুষের জন্য ছিল, শুধু মাসলমানদের জন্য নয়। এটা হচ্ছে অভাব, অক্ষমতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।
৭. ‘‘সম্পদ কোত্থেকে অর্জিত হয়েছে?’’ এ মৌলিক প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাসকের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা আসলে জাতির সম্পদ না তার নিজস্ব এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার মুসলিম সমাজের রয়েছে, এ ব্যাপারে জনগণের হিসাব গ্রহণের হাত থেকে তার অব্যাহতি লাভের কোনো উপায় নেই। এ হিসাব গ্রহণের নীতি নির্ধারিত হওয়ার ফলে জাতীয় কোষাগার প্রশাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। এ ধরণের কোনো কিছু করার পূর্বে শাসককে একাধিকবার চিন্তা করতে হয়। হযরত ওমর রা. তার সকল শাসনকর্তাদের সাথে এরূপ করেছেন। হযরত আলীও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ নীতি অবলম্বন করেছেন।
৮. যাকাত ব্যবস্থা ইতিহাসের সেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগেও স্থগিত হয়নিঃ যদিও সে যুগ ইসলামের প্রাণশক্তি থেকে বহু দুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। হযরত আবু বকর রা. এর যুগের প্রারম্ভে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ যাবত কোনো এক ব্যক্তিও মৌখিক অথবা কার্যতঃ যাকাত অস্বীকার করেনি। কেবল আমাদের যুগে এসে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ীর আসনের অধিষ্ঠিত হলো। তখন তারই পরিণামে ইসলামী মূলনীতি সমূহের সর্বশেষটি যাকাতও মুসলমান সমাজের বাস্তব জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।
৯. সাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক জনপদের লোকদেরকে সেখানে অনাহারে মৃত্যুবরণকারী যে কোনো ব্যক্তির জন্যে দায়ী করা হয়। ফৌজদারী বিধি অনুসারে তাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়। এই ভাবে মৃত্যুবরণকারী লোকের জন্য সংশ্লিষ্ট জনপদের সবাইকে পাইকারীভাবে জরিমানা তথা ‘দিয়াত’ দিতে হয়। কারণ সমাজের সকলে সেই ব্যক্তির হত্যাকারী সাব্যস্ত হয় যে তাদেরই মধ্যে থেকে অনাহারে ধুকে ধুকে মরেছে।
এই বিধান শরিয়াতের অপর একটি বিধান দ্বারাও সমর্থিত হয়। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন ক্ষুধা-পিপাসা জর্জরিত ব্যক্তি ক্ষুধা-পিপাসায় মৃত্যু বরণ করার আশংকা বোধ করলে তাকে খাদ্য অথবা পানীয়ধারী ব্যক্তির সাথে সবশেষ পন্থা হিসাবে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তিকে সে হত্যা করলে তার দুনিয়ায়ও কোনো শাস্তি জরিমানা হবে না এবং আখেরাতেও আযাব ভোগ করতে হবে না।
১০. সুদ বিলোপ এবং দারিদ্রাবস্থায় ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির নীতিঃ আধুনিক সভ্যতা সুদকে হালাল ঘোষণা করার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম সমাজে সুদ যথারীতি নিষিদ্ধই ছিল। ফরাসী আইন এই অভিশাপ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং একে আমাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনের একটা অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করে। অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটা শুধু এই জন্যে প্রচলিত হয় যে আমাদের বাস্তব জীবন থেকে নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব মুছে গিয়েছিল এবং মানুষের মন থেকে সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ ইসলাম এই মনোভাবকে সমাজে ও পারস্পরিক লেন-দেনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।
এ বিষয়গুলি ছাড়াও পারস্পরিক সহানুভূতি ও সামাজিক নিরাপত্তা জনিত বহুনীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে যা আইনের শক্তি দ্বারা কার্যকরী করার বস্তু নয়। স্বয়ং আমাদের নিকট অতীত ও মুসলিম সমাজের ওপর ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। এ যুগ আমাদের দাদারা নয় বরং পিতারাই স্বচক্ষে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে অবলোকন করেছেন। মুসলিম জাহানের ওপর পাশ্চাত্যে বস্তুবাদী সভ্যতার সর্বাত্মক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও আজও এই প্রভাব অনেকটা অম্লান রয়েছে। সেখানে এই মূল্যবোধ কার্যকরী করার ব্যাপারে আইন ও বল প্রয়োগের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আজ কালকার সরকার সমূহের মধ্যে যে সব ওয়াক্ফ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়- যাকে আজ তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যাকে বিভিন্ন শোষক শ্রেণী নানা নামে ও নানা দলে কুক্ষিগত করে রেখেছে এ সব প্রকৃতপক্ষে দূর ও নিকট অতীতের মুসলমানদের হৃদয়ে অবস্থিত দয়া, সহানুভূতি, সৎকর্মশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পবিত্র মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে। পাশ্চাত্যের নৃশংসতা, মৃত চেতনা ও স্থবির জড়বাদী সভ্যতা তাদের অন্তরাত্মাকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়নি।
আমাদের স্বর্ণযুগে দুর্বলের প্রতি সামাজিক নিরাপত্তা দানের মনোভাব এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, শুধু মানুষই নয় জন্তু-জানোয়ারও তা থেকে উপকৃত হয়েছে, বহু স্থানে দুর্বল পশুদের আশ্রয় স্থল তৈরী করার জন্য কোনো কোনো স্থান ওয়াক্ফ করা হয়েছে যাতে তারা সেখানে এসে ক্ষুধা ও দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।
প্রাথমিক স্তরে শাসন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক কার্যধারায় কিছুটা বিকৃতি দেখা দেয়ায় সে সুদূর প্রসারী ক্ষতি হয়েছে তা সত্ত্বেও এটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম।
ইতিহাসের বাস্তব মঞ্চে এই হচ্ছে ইসলামের ভূমিকা যা বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর সাধারণ মূলনীতিগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা চলে যে, নবতর পরিস্থিতির দাবি পূরণ এবং নতুন সমস্যাবলীর সমাধান করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা তার রয়েছে, ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে। আগামী দিনে যে সমাজ ইসলামের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যেখানে ইসলামী শরিয়তকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দান করা হবে সেখানে ইসলাম, সেই সমাজের যাবতীয় দাবী ও প্রয়োজন অত্যন্ত ব্যাপকতা ও ভারসাম্য সহকারে পূরণ করতে সক্ষম হবে। আজকের মানব সমাজ যেভাবে মতবাদ সমূহ ও মানবীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরন্তর এক চরম সীমা থেকে অপর চরম সীমায় গিয়ে আঘাত খাচ্ছে, আর এই ঘাত-প্রতিঘাতে মানব জাতি যেরূপ তার বহু মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দিচ্ছে- ইসলাম তাকে এই অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি থেকে চিরতরে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করবে। [গ্রন্থকারের ‘‘আল ইসলাম ওয়া মুসকিলাতুল হাজারা’’ (ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার সংকট) গ্রন্থের ‘‘উজতেরাব ওয়া ইনতেমার’’ (উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি) অধ্যায় দ্রষ্টব্য]
........ সমাপ্ত ........
', 'ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a3-%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be-2', '', '', '2019-10-26 16:56:44', '2019-10-26 10:56:44', '
ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি
মূল-সাইয়েদ কুতুব
অনুবাদ-আকরাম ফারুক
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
প্রকাশকের কথা
ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান। সর্বশেষ নবী সৃষ্টির মহা পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তিরোধানের পর চার খলিফা ও পঞ্চম খলিফা হিসেবে খ্যাত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাঃ) এর যুগকে ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে এবং সে সময়কার সামগ্রিক কর্মকান্ড যথাঃ খলিফাতুল মুসলিমিনের খোদাভীতি, উন্নত নৈতিক মান, জনসেবা, সরকারী কোষাগার থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক কপর্দকও গ্রহণ না করা, সামাজিক শান্তি, শৃংখলা, সুবিচার, একে অন্যের প্রতি মমত্ববোধ, সহানুভূতি ইত্যাদি সর্বকালের সর্বযুগের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।
বর্তমান এই নব্য জাহেলিয়াতের যুগে মুসলিম মিল্লাতের আমূল পরিবর্তন এবং ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি মুসলমান ইসলামের মূল আবেদন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে এ গ্রন্থ সহায়ক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে উপকৃত হবার তৌফিক দান করুন। আমিন।
ইসলামের মূল প্রাণশক্তি
ইসলামের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে আমরা সেখানে তার মূল প্রাণশক্তিকে সদা সক্রিয় দেখতে পাই।
সত্য দ্বীনকে যে ব্যক্তি জানবার চেষ্টা করবে এবং তার মেজাজ-প্রকৃতি ও ইতিহাসকে অধ্যয়ন করবে সে তার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এই প্রাণশক্তিকে সে ইসলামের আইন-কানুন ও নীতিমালার মধ্যে পূর্ণোদ্যমে কার্যকর দেখতে পাবে। এটা এত প্রভাবশালী যে, যে কোনো মানুষই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। কিন্তু কোনো গভীর অনুভূতি ও মৌলিক চিন্তাধারা যেমন সীমাবদ্ধ ভাষায় বর্ণণা করা যায় না তেমনি এই প্রাণশক্তিরও বর্ণনা দেয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ প্রাণশক্তি আবেগ ও উদ্দীপনায়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এবং রসম-রেওয়াজের মধ্যে সক্রিয় থাকে বটে কিন্তু তাকে ভাষার সীমিত পোষাকে আবৃত করা অত্যন্ত কঠিন।
এই প্রাণশক্তিই সেই সমুন্নত প্রোজ্জ্বল দিক চক্রবালের রূপরেখা নির্দেশ করে, যার অভিমুখে যাত্রা করার জন্য ইসলাম তার অনুসারীদেরকে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং সে জন্য শুধু অপরিহার্য্য্ কর্তব্য ও গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা পালনে ক্ষান্ত না হয়ে, স্বেচ্ছায় সানন্দে আরো বেশি চেষ্টা সাধনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছারপথ অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম আর সেখানে পৌঁছার পর তার ওপর অবিচল থাকা আরো বেশি দুঃসাধ্য। জৈবিক প্রেরণা ও চাহিদা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের প্রবল চাপ অধিকাংশ মানুষের পায়ে জিঞ্জির হয়ে জীবনের মহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছারপথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। আর যদিও-বা আবেগ উদ্দীপনার তীব্রতায় এর সংকল্পের প্রাবল্যে কখনো সেখানে পৌঁছেই যায় তাহলেও তার সেখানকার বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-আপদ অতিক্রম করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এ মহোন্নত স্তরের সাথে জড়িত রয়েছে জান-মাল এবং চিন্তা ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তন্মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর নিজ সত্তা, নিজ সমাজ ও মানব জাতি সম্পর্কে এবং সর্বোপরি তার স্রষ্টার ব্যাপারে যে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর। তার স্রষ্টা যে তার প্রতিটি ছোট বড় কাজ সর্বদা স্বচক্ষে অবলোকন করছেন, তার মনের গভীরে লুকানো গোপন কথা ও তার নিঃ শব্দ কার্যক্রম সম্পর্কেও কার্যক্রম সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল রয়েছেন- এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুভূতি জাগরুক রাখাই হচ্ছে স্রষ্টার সম্পর্কে তার গুরু দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করার জন্য ইসলাম তার বিবেককে করেছে সদা জাগ্রত এবং হুশিয়ার। আর তার চেতনা ও প্রজ্ঞাকে করেছে সুতীক্ষ্ণ ও সুতীব্র।
উচ্চতম লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রার এই জটিলতা এবং লক্ষ্যে উপনীত হবার পর তথায় স্থায়িত্বের এই দুঃসাধ্যতার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম একটা কবিসুলভ কল্পণা অথবা এমন একটা অতি মানবিক ধারণা যাকে জয় করার অভিযোগ পোষণ করা যায় কিন্তু যাকে স্পর্শ করা যায় না। আসল ব্যাপার তা নয়। যে সুমহান ও সুউচ্চ স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে উপনীত হওয়া সকল যুগের সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এটা হচ্ছে একটা লক্ষ্যসীমা মাত্র। মানুষ সর্বদা ওটা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাকবে সে জন্যে তার রূপরেখা নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে। এ চেষ্টা অতীতে যেমন করা হয়েছে, আজ এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকা উচিত। অতীতের মানব সমাজ এ লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা চালিয়েছে- কখনো লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে আবার কখনো বা দূরে সরে গেছে। এটা এমন একটা আদর্শ যাকে শুধু মানুষের বিবেক ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের ওপর গভীর আস্থা দ্বারাই জয় করা সম্ভব। এতে করে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অনাগত ভবিষ্যতে মানুষ সম্পর্কে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। এই সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যের পূর্বেই একটি সুবিশাল প্রান্তর রয়েছে। চেষ্টা সাধনা ও সাফল্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভব সে মাপকাঠির জন্য এ বিশাল প্রন্তর যথেষ্ট। আল্লাহর একটি স্থায়ী নীতি এই যে, তিনি কোনো ব্যাক্তিকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি চেষ্টার জন্য বাধ্য করেন না।
“আল্লাহ্ কোনো মানুষকে তার ক্ষমতার চাইতে বেশি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন না।” (সূরা বাকারা-শেষ আয়াত) ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতি এতো ইনসাফ প্রিয় ও মধ্যমপন্থি যে, সে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে শুধুমাত্র অবশ্য করণীয় কার্যসমূহ গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হয়। কারণঃ
“প্রত্যেকের কাজের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।” বস্তুত অবশ্য করণীয় হিসেবে যে সব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জীবনের সাফল্যের জন্য সেটাই যথেষ্ট। এরপরে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবার জন্য পথ সর্বদা উম্মুক্ত রয়েছে এবং সেদিকে অগ্রসর হবার জন্য উদাত্ত আহবানে ইসলাম সদা সোচ্চার রয়েছে।
যে প্রাণশক্তির কথা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি, তা ইসলামের সমাজ ও সভ্যতাকে বাস্তব রূপদানে পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে ইসলাম শুধু একটা বিশ্বাসের নাম ছিল, তা ব্যাক্তিসমূহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখন আর ইসলাম শুধু মতবাদ ও মতাদর্শের নাম নয় - ওটা নিছক ওয়াজ-নছিহত ও হেদায়েত কিংবা অলীক কল্পনা সমূহের সমষ্টিও মাত্র নয়। ওটা এখন জীবন্ত ও জাগ্রত মানব চরিত্রের রূপ ধারণ করেছে, বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীতে আত্নপ্রকাশ করেছে - সর্বোপরি তা এমন সব সমাজ সংস্থা ও সংস্কারমূলক কীর্তি স্থাপন করেছে- তা কেউ স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকর্ণে শ্রবণ করতে পারে। এসব সমাজ সংস্থা ও সংস্কার কীর্তি গোটা মানক জীবন ও ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুতঃ এ সব ইসলামের সেই মহিমান্বিত ‘প্রাণশক্তির’ই অবদান। এই প্রাণশক্তিই মৃতপ্রায় ব্যাক্তিসমূহের জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। তাতে এক নব চেতনা ও নতুন জীবনী শক্তির সঞ্চার করেছিল।
বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসের সূচনা যুগে এবং তার পরবর্তী যুগে বিস্ময়কর ব্যাক্তি সমূহের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং যাদের জীবনের আলোড়ল সৃষ্টিকারী গৌরবগাথা ইসলামের ইতিহাসে সুরক্ষিত রয়েছে তাদের সম্পর্কে এটাই হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা। যে অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনাবলী শুধু উচ্চতর চিন্তার সৃষ্ট রূপকথার মত মনে হয়, তারও রহস্য এই।
আত্মার পবিত্রতা, বিবেকের নির্ভীকতা, অভাবনীয় ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কোরবানী, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের মরণপণ সংকল্প, চিন্তা ও আত্মার অসাধারণ ও অচিন্তনীয় উচ্চতা এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগের অসামান্য কৃতিত্ব যা পুরোপুরি ভাবে বর্ণনা করা ইতিহাসেরও ক্ষমতা বহির্ভূত-এ সব কিছু ইসলামের এই বিপ্লবী প্রাণশক্তিরই অবদান।
ইতিহাসের পাতায় যে সব অসাধারণ কীর্তি ও ঘটনাবলী ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তার সাথে ইসলামের বিপ্লবী প্রাণশক্তির একটা সুগভীর সম্পর্ক আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। মূলতঃ ইসলামের ইতিহাসে যে শক্তির প্রকাশ দেখা যায় এই অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই তার মূল উৎস।
এ কীর্তি সমূহকে যদি আমরা উক্ত প্রাণশক্তি থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে যাই তাহলে আমাদের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকবে। এই ভ্রান্ত অধ্যয়নের ফলে জীবন ও জগতের ওপর সক্রিয় ভাবে প্রভাবশীল শক্তিসমূহ সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হতে বাধ্য হব। এর ফল দাড়াবে এই যে, প্রত্যেক গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিদের গৌরব ও সম্মানের উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা তার ব্যক্তিগত মাহাত্মকেই প্রাধান্য দেব এবং এ সবের সর্বপ্রথম উদ্দীপক ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কার্যকরণ উক্ত ‘প্রাণশক্তি’কে অগ্রাহ্য করবো। অথচ এই প্রাণশক্তিই সেই মহান ব্যক্তিদের বিবেক ও মনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, আর এরই বলে বলিয়ান হয়ে তারা ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল এবং ঘটনা স্রোতকে নিজেদের ইস্পিত স্রোতে প্রবাহিত করেছিল। এর পর তারা ইতিহাসকে জীবনের এক উদ্দাম, উচ্ছল ও গতিবান স্রোতধারার নিকট সোপর্দ করেছিল। আর সেই স্রোতধারার ওপর ভর করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সব অবিস্মরণীয় বিপ্লবাত্মক কীর্তি।
আমরা যদি গৌরবদীপ্ত মহৎ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব এবং তাদের কীর্তি সমুহের প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে এই বিপ্লবী প্রাণশক্তির অবদান বলে অবিহিত করি তা’হলে সেটা অত্যুক্তি হবে না। আসলে এই প্রাণশক্তি একটা অতীন্দ্রিয় প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা যে সব কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের সাথে এসে মিলিত হয়েছে তা বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন শক্তি হলেও মূলতঃ তা-সবই অতীন্দ্রিয় শক্তি। এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিত্ব উক্ত অতীন্দ্রিয় প্রেরণাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কতদুর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে সেটাই হচ্ছে তার মহত্বের মাপকাঠি। এখন যদি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তকে উক্ত যোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তর বলে মনে করা হয় তা হলে সেটা বিচিত্র কি? আসলে তাঁর সত্তাই অতীন্দ্রিয় প্রেরণাকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করেছিল এবং সারা জীবন ব্যাপী সেই সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।
নবুয়তের স্তরের পর উচ্চ মর্যাদার বহু স্তর রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীরা এবং তাদের পরবর্তী অনুসারীরা এই সব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এই মহান দ্বীনের প্রাণশক্তিকে যে ব্যক্তি যতদূর গ্রহণ করতে পেরেছে, সে সেই অনুযায়ী উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। বস্তুতঃ অত্যন্ত ব্যাপক অধ্যয়নের পরই আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে, এই প্রেরণা মানবাত্মাগুলোকে কতদূর প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে- কিভাবে তাদের ঘুমন্ত প্রাণকে জাগিয়ে তুলেছে- কর্মচঞ্চল ও কর্মক্ষম করে তুলেছে- অপূর্ব ও আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্তসমূহ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সর্বশেষ গোটা মানবেতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে।
এই প্রেরণা ও প্রাণশক্তির প্রভাব আমরা ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা এবং দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনা- উভয়ের মধ্যেই দেখতে পাই। জানা কথা যে, আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের পরিমাণ ইঞ্চি-গজে নির্ণয় করা সম্ভব নয় বরং তার সম্পর্ক হলো গুনাগুণের সাথে। এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় শুধু বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অনুষ্ঠিত ঘটনাপুঞ্জের মাধ্যমে।
আরব উপদ্বীপের মুষ্টিমেয় কতগুলো লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোম ও পারস্যের মত দুটো বিশাল সাম্রাজ্যকে পদানত করে ফেলেছিল। গোটা মানবজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় বিজয়ের অন্য কোনো নজীর পেশ করতে পারবে না। কিন্তু এই গৌরবদীপ্ত ঘটনার গৌরব ও মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ম্লান হবে না যদি আমরা বলি যে কোরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের জবাবে বেলাল (রাঃ) নামক হাবসী ক্রীতদাস একাই যে ধৈর্য্যর পরিচয় দিয়েছিল তাতেও এই একই মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। কোরাইশরা হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)কে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য যে যাতনা দিয়েছিল তা মানুষ মাত্রেরই ধৈর্য ক্ষমতার বহির্ভূত। নীচ থেকে তাকে উত্তপ্ত বালি দগ্ধ করছিল, পেট ও বুকের ওপর পাথরের বোঝা চাপানো ছিল, প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, তদপুরি তাকে প্রচন্ড জোরে প্রহার করা হচ্ছিল। কিন্তু এই অসহনীয় নির্যাতনের মধ্যে তার মুখ দিয়ে যে কথা নিঃসৃত হয় তা ছিল ‘আহাদ’ ‘আহাদ’।
এ প্রেরণাই যখন কোনো পথচারী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তখন স্বৈরাচারী সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়েও সে কড়া কড়া স্পষ্ট কথা বলে এবং আল্লাহর রাহে কারো নিন্দা-সমালোচনাকে ভয় পায় না। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি খলিফায়ে রাশেদ যখন বিনয়, অল্পে তুষ্ট ও আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করেন তখন তার মধ্যেও একই প্রাণশক্তি কার্যকর দেখা যায়। উভয় ব্যক্তি একই উৎস থেকে শক্তি লাভ করেছেন আর সে উৎস হচ্ছে ইসলামের দুর্জয় ও বিপ্লবী প্রাণশক্তি।
রোম ও পারস্য বিজয় প্রসঙ্গে এ কথা বলা প্রয়োজন মনে হচ্ছে যে, এখানে ইসলামের বিজয় মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক মতাদর্শের বিজয় ছিল। এই মতাদর্শ মানুষের অন্তরাত্মাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ ঘটনা ইতিহাসের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণকে সমর্থন করে কেননা এখানে বস্তুগত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বস্তুগত বিশ্লেষণ দ্বারা এই অসাধারণ বিজয়ের হেতু নির্দেশ করা অসম্ভব। নিছক বস্তুগত শক্তি দ্বারা আরবরা অত বড় দু’টো সাম্রাজ্যকে পদানত করতে পারতো না।
সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম আরবদের চিন্তা ও কর্মে, উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে মনস্তাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে তার গুরুত্ব ঐসব দেশের বিজয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশী। এটা ইসলামের প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দেশ জয়ের ঘটনাবলীর চাইতে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। এ কথা সকলেরই জানা যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত ও ইন্তোকালের মাঝামাঝি সময়ে আরব উপদ্বীপে খোদ তাঁর আনীত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া স্বতন্ত্র কোন অর্থনৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়নি- তাই সেখানখার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন কোন মৌলিক পরিবর্তনও সাধিত হয়নি যা আরবদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যকলাপ ও সমাজ ব্যবস্থায় এত বড় বিপ্লব আনতে পারে। বস্তুতঃ এ সমস্ত কীর্তিকলাপ আসলে এই আধ্যাত্মিক মতাদর্শেরই সৃষ্টি।
এখানে আমাদের পক্ষ্যে এই বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। আমরা এর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করবো। এ দৃষ্টান্ত সে যুগের আরবদের একটি বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। এ বিবৃতিটি তারা ইসলামের শত্রুদের সামনে দিয়েছিলেন অথচ তারা এর একটি কথারও প্রতিবাদ করতে পারেননি। এ হচ্ছে আন্দোলনের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। কোরাইশদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করার জন্য মুসলমানরা হিজরত করে হাব্শায় চলে যান। হাব্শায় গিয়ে পাছে তারা শক্তি অর্জন করে ফেলে এই আশংকায় কোরাইশরা রাজা নাজ্জাশীর নিকট দু’জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মোহাজেরদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করানো ব্যবস্থা করা। এই প্রতিনিধিদ্বয় চিল আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়া। তারা গিয়ে বললো,
‘জাহাপনা! আমাদের দেশের কতিপয় অবুঝ তরুণ আপনার দেশে এসে বসবাস করছে। তারা নিজ জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে এক মনগড়া ধর্ম এনেছে- যা আমাদের জন্যও নতুন- আপনার জন্যও নতুন।ওদের বাপ-চাচা, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং আমাদের জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাদেরকে আপনার কাছে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ওদেরকে দেশে ফেরত পাঠাবেন। সে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই তরুণদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তরুণরা যে সব জিনিষের ওপর আপত্তি তোলে এবং যেগুলোকে মন্দ বলে, তা আমাদের নেতারাই ভাল বোঝেন।‘
এই কথা শুনে নাজ্জাশী মুসলিম তরুণদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যার জন্য তোমরা নিজ জাতিকে পরিত্যাগ করে এসেছ এবং আমার ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করনি সে ধর্মটা কি?”
উত্তরে আবু তালেবের পুত্র জাফর (রাঃ) বললেন,
“হে বাদশাহ! আমরা চরম মুর্খতা ও অজ্ঞতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত দেহ আহার করতাম ও ব্যভিচার করতাম। আত্মীয়তার বন্ধনের অবমাননা করা ও প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করা আমাদের নিত্যকার অভ্যাস ছিল। আমাদের মধ্যে যারা সবল ছিল তারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার ও শোষণ চালাতো। এমনি অবস্থায় আমাদেরই একজনকে আল্লাহ নবী বানিয়ে আমাদের নিকট প্রেরণ করলেন। আমরা তার বংশ-মর্যাদা, তার সততা-সত্যবাদীতা, তার বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পের্কে ওয়াকিফহাল। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি আহবান করেন, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা ও কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত-উপাসনা ও আনুগত্য করার শিক্ষা দেন। আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রতিমা ও প্রস্তর মূর্তির পূজা করতাম, তিনি সেগুলোর পূজা ছেড়ে দিতে বলেন। তিনি সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অশ্লীল ও অশালীন কার্যকলাপ, মিথ্যাবাদিতা, ইয়াতিমের ধন আত্মসাৎ ও সতী নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর এবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে, যাকাত দিতে ও রোজা রাখতেও নির্দেশ দিয়েছেন.....।”
কোরাইশদের দু’জন প্রতিনিধিই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিল আমর ইবনুল আস- বাকপটুতা ও কুটনৈতিক দক্ষতায় যার জুড়ি ছিলনা। কিন্তু জাফর (রাঃ) প্রাগৈসলামিক আরবের পরিস্থিতির যে ছবি এঁকেছেন এবং রাসুলুল্লাহ’র আনীত জীবন-বিধানের যে পরিচয় পেশ করেছেন দু’জনের কেউ তার প্রতিবাদ করেনি। এটা প্রমাণ করেছে যে আরবের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।
এ হচ্ছে শুধু আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য। আধুনিক যুগের একজন অমুসলিম সে সময়কার সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে এ ধরনেরই একটি সাক্ষ্য দিয়েছেন। জে. এইচ. ডেনিসন (J.H. Denison) তার পুস্তকে সভ্যতার ভিত্তি হিসাবে ভাবাবেগ-এ (Emotion as the basis of civilization)লিখেছেন,
“পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য জগত নৈরাজ্যের এক সাংঘাতিক বিপজ্জনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছেল। এরূপ মনে হচ্ছিল যে, চার হাজার বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনার ফলে গড়ে ওঠা বিরাট সভ্যতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে চাচ্ছে এবং মানবতা অসভ্যতা ও বর্বরতার আদিম যুগে ফিরে যেতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। গোত্রে গোত্রে ভয়াবহ দাংগা ও কোন্দল লেগে ছিল। কোন আইন-শৃংখলার পরিবর্তে বিভেদ ও বিশৃংখলার জন্ম দিচ্ছিল। যেন একটি বিরাট বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ডালপালা সমগ্র পৃথিবীকে নিজের ছায়াতলে আবৃত করতে চায়। কিন্তু ভেতর থেকে তার কান্ডকে মূল পর্যন্ত এমনভাবে ঘুনে খেয়ে দিয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে বৃক্ষটি ভুমিস্মাৎ হতে পারে। তখনকার সভ্যতা ঠিক এমনি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল। এহেন সর্বাত্মক ধ্বংসের চিহ্ন যখন পরিস্ফুট ঠিক তখনি সেই ব্যক্তি জন্মলাভ করলেন যিনি সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবব্ধ করলেন।” [মওলানা মুহাম্মদ আলী প্রণীত ও ওস্তাদ আহমদ জাওয়াদুছাছানুহার কর্তৃক আরবীতে অনুদিত Islam and New World order থেকে গৃহীত। ] যাহোক আমরা এখন এই ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করবো।
বিবেকের সচেতনতার দৃষ্টান্ত
দৃষ্টান্তগুলো পেশ করার আগে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ইসলামের ইস্পিত বিবেকের ওপর আলোকপাতকারী কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। কেননা এই বিবেকের ওপরই ইসলামের গোটা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আগেই বলেছি যে, ইসলাম ব্যক্তির বিবেককে সদা জাগ্রত থাকার এবং তার চেতনা ও অনুভূতিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও তীব্র করার শিক্ষা দেয়। ইসলামের ইতিহাস এই বিবেকের সচেতনতা ও অনুভূতি তীব্রতার এত অধিক দৃষ্টান্ত সংরক্ষণ করেছে যে তা আমাদের এ সীমাবদ্ধ গ্রন্থে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখানে অনেকগুলো নমুনার স্থলে বিবিধ রকমের মাত্র কয়েকটি নমুনা পেশ করা যাচ্ছে।
হযরত বারিদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,
“মাগের ইবনে মালেক (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে হাজির হয়ে বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।” রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বললেন, “তোমার সুমতি হোক, যাও, আল্লাহর নিকট তওবা কর গিয়ে”। মাগের কিছুদুর পর্যন্ত চলে যায়- অতঃপর আবার রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে ফিরে এসে বলে, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন”। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আগের মতই জবাব দেন, তিনবার এরূপ হলো। চতুর্থবার রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বললেন, “আমি তোমাকে কিসের থেকে পবিত্র করবো?” মাগের বললো, “ব্যভিচার থেকে”। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তি মাতাল নয় তো?” সকলে জানালো যে সে মাতাল না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “ও কি মদ খেয়েছে”। এক ব্যক্তি গিয়ে মাগেরের মুখ শুঁকলো। দেখা গেল সে মদ খায়নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি সত্যই ব্যভিচার করেছ?” মাগের বলেলো, “হ্যাঁ”। এরপর তিঁনি শাস্তির হুকুম দিলেন এবং তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে শাস্তি কার্যকরী করা হলো”।
এ ঘটনার দুই তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “তোমরা মাগেরের জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর। সে এরূপ তওবা করেছে তা একটি গোটা জাতির মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে”।
এরপর তাঁর নিকট আজ্দ গোত্রের এক মহিলা এল। সে বললো, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন”। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “তোমার সুমতি হোক, যাও, আল্লাহর নিকট তওবা কর গিয়ে।? সে বললো,
“আপনি কি আমাকে মাগেরের মত ফিরিয়ে দিতে চান? আমি যে ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি”। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “তুমি কি সত্যই ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী?” সে বললো, “হ্যাঁ”। তিঁনি তাকে বললেন, “সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর”। অতঃপর তিনি উক্ত মহিলাকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত জনৈক আনসারীর তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর উক্ত আনসারী এসে রাসূলুল্লাহকে জানালেন যে, মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বললেন, “ আমি তাকে মৃত্যুদন্ড দেব আর শিশুকে দুধ পান করানোর কেউ থাকবে না- এমন কাজ আমি করবো না”। এতে এক আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শিশুর দুধ পান করানোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি”। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার ওপর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করলেন।
অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে বললেন, “তুমি যাও, সন্তান প্রসব করার পর এসো”। সন্তান প্রসবের পর সে এলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “যাও দুধ পান করাও গিয়ে। দুধ ছাড়লে তখন এসো”।এরপর শিশু দুধ ছেড়ে দিলে সে শিশুকে কোলে নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে এলো। শিশুর হাতে এক টুকরো রুটি ছিলো। সে বললো, “রাসূলে খোদা! আমি শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি। এখন সে রুটি ইত্যাদি খেতে শিখেছে”। তখন তিনি শিশুকে একজন মুসলমানের হাতে সোপর্দ করলেন এবং মহিলার মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দিলেন। তার বুক পর্যন্ত গভীর গর্ত খোড়া হলো, অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশে লোকেরা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেললো। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) একটু সামনে অগ্রসর হয়ে একটা পাথর তার মাথার নিক্ষেপ করলেন। এর দরুন খানিকটা রক্ত ছিটে এসে খালেদের মুখমন্ডলে লাগলো। এতে খালেদ মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে কটুক্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনতে পেয়ে বললেন, “খালেদ! মুখ সামলে কথা বলো। খোদার শপথ করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, অন্যায়ভাবে আদায়কারীও যদি সেরূপ তওবা করতো তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হতো”। অতঃপর তাঁর নির্দেশে মহিলার জানাজার নামাজ পড়া হলো এবং তাকে যথারীতি দাফন করা হলো। (মুসলিম, নাসায়ী)।
মাগের ইবনে মালেক ও উক্ত মহিলার চরিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। এদের কারো ব্যভিচারের কঠিন শাস্তির কথা অজানা ছিলনা। তাদেরকে কেউ পাপ কাজ করতে দেখেনি এবং তা প্রমাণ করার উপায়ও ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে পিড়াপিড়ি করলো্ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হৃদয়ের কোমলতা ও ইসলামের ন্যায়-নীতিমূলক প্রকৃতির তাগিদে সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের শাস্তি ক্ষমা করতে চাইলেন। কিন্তু তা এত বেশি পিড়াপিড়ি করলো যে তাদের মুক্তির সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মহিলাটি তো খানিকটা শক্ত কথাই বলে ফেললো যে, তিনি কি তাকে মাগেরের মত ফিরিয়ে দিতে চান? যেন সে ইসলামের বিধানের অকাট্য বিধানের ব্যাপারে শৈথিল্য ও উদারতা প্রদর্শনের অভিযোগ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওপর আরোপ করতে চাচ্ছে।
এসব কেন?.........তাদের এরূপ কথা বলা যে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন” তাদের মধ্যে এমন এক জীবন্ত ও উদগ্র প্রেরণার অস্তিস্ত নির্দেশ করে যা স্বয়ং বেঁচে থাকার আকাংখার চেয়েও প্রবল ও প্রাণবন্ত। এই প্রেরণা বিবেকের সচেতনতা ও অনুশোচনার তীব্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে পাপের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না তা থেকে পবিত্র হবার সুতীব্র বাসনা এবং অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে এই অনুভূতি থেকে সৃষ্ট প্রচন্ড লজ্জা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিল।
এই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম। অপরাধীর মনে সুতীব্র অনুশোচনা আর নবীর মনে প্রথমে দয়া ও সহানুভূতি এবং পরে অপরাধ প্রমানিত হওয়ার পর অপরাধীর তওবা ও স্বীকারোক্তির মাহাত্মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দন্ড কার্যকরী করার মত দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা এই ইসলামেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা ইসলাম তার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক ও তার গৌরব অম্লান থাকুক- এটাই ছিল অপরাধী ও শাসক উভয়ের নিকট সবচেয়ে কাম্য বস্তু।
দন্ড বিধির ক্ষেত্রে যখন মুসলিম বিবেকের এই অবস্থা তখন যে সব সামাজিক কাজে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে হয় তাতে তার ভূমিকা কিরূপ হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।
এ প্রসঙ্গে সিরিয়ার সেনাবাহীনির নেতৃত্ব থেকে খালেদ ইবনে ওলীদকে অপসারিত করে আবু ওবায়দাকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। খালিদ হলেন সেই গৌরবদীপ্ত সেনাপতি, যিনি তখন পর্যন্ত কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেননি। সৈনিকসুলভ স্বভাব ও দক্ষতা তার মেরু মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও তিনি ছিলেন একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। এহেন খালেদকে সেনাপতিত্ব থেকে অপসারিত করা হয় অথচ তিনি অসহযোগিতাও করেননি, বিদ্বেষও পোষণ করেননি। লজ্জা কিংবা সম্ভ্রমবোধ তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে উদ্বুদ্ধ করেনি। বিদ্রোহ করার কোন চিন্তার তো প্রশ্নই ওঠেনা। তিনি একাই যুদ্ধের ময়দানে সমান আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের বিজয়ের প্রেরণায় ও শাহাদাতের কামনায় উজ্জীবিত হয়ে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ সময়ে তিনি তার মনে কোনো প্রকার কু-চিন্তা ও কু-প্ররোচনার প্রশ্রয় দেননি। কেননা সচেতন মুসলিম বিবেক এ ধরনের চিন্তার বহু উর্দ্ধে। এসব চিন্তার কোনই গুরুত্ব নেই তার কাছে।
ঘটনার অপর দিকটিও অর্থপূর্ণ। হযরত ওমরের খালেদকে অপসারিত করাও একই চেতনা ও প্রেরণা থেকে উদ্ভুত ছিল। তিনি হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে খালেদ ইবনে ওলিদের মধ্যে এমন কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করেন যা ওমরের বিবেককে প্রকম্পিত করে তোলে। একটি ছিল এই যে, খালেদ মালেক ইবনে নোয়াইরাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন এবং অব্যবহিত পরে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এর পর তিনি আবার অনুরূপ একটা ত্রুটি লক্ষ্য করেন। সেটা হচ্ছে এই যে, মুসাইলেমায়ে কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেদিন বারশত শীর্ষস্থানীয় সাহাবী শহীদ হন, তার অব্যবহিত পরের দিন প্রত্যুষে খলেদ মাজ্জায়ার মেয়ে বিয়ে করেন।
এসব কার্যকলাপের সামনে যা আমার ধারণা ত্রুটিপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল খলিফা খালেদের বীরত্বের এবং যুদ্ধ জয়ের কোনোই গুরুত্ব দেননি। নিঃসন্দেহে খালেদ সবচেয়ে বড় সেনাপতি ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যুদ্ধ জয় করেছিলেন। তদুপরি মুসলিম জাতি সিরিয়া ও ইরাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের মুখোমুখি ছিল। সেখানে খালেদের মত অপরাজেয় সেনাপতির সমর দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু খালেদের মারাত্মক ত্রুটিসমূহ ওমর (রাঃ) এর বিবেকে যে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার সৃস্টি করেছিল, খালেদের এই সব গুণাগুণের কোনোটাই তা দমন করতে সক্ষম হয়নি। এর কোনটাই খালেদকে সেনাপতিত্ব থেকে এবং পরে খোদ সেনাবাহিনী থেকেও অপসারিত করার স্বপক্ষে তাঁর অভিমতকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। আরো একটি কারণ ছিল এই যে, খালেদ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে দায়িত্ব পালন করতেন আর এটা ছিল হযরত ওমরের মেজাজের পরিপন্থি। তাঁর দায়িত্ববোধ তাঁকে খুটিনাটি ব্যাপারেও নজর রাখতে হস্তক্ষেপ করতে উদ্বুদ্ধ করতো।(সাদেক উরজুন কৃত গ্রন্থ ‘খালেদ ইবনে ওলিদ’ থেকে)।
কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, খালেদ যদি এত বড় ভুল করে থাকেন, তাহলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? আসল ব্যাপার এই যে, খালেদ বিন ওলিদ সম্পর্কে হযরত আবু বকরের মতামত ওমরের মত গুরুতর ছিলনা। তিনি মনে করতেন যে, খালেদের বুদ্ধির ভুল হয়েছে এবং তিনি পরিকল্পিতভাবে কোন ত্রুটি বা গুনাহর কাজ করেননি। এ কারনে তিনি তার ওপর রুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় ঘটনাটিকে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ঘোর আপত্তির দৃষ্টিতে দেখেন এবং তিনি এক ক্রোধাপ্তি চিঠি লিখে পাঠান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খালেদের ভুল-ভ্রান্তিকে তিনি ক্ষমার যোগ্য মনে করতেন এবং তা শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেও দেন।
এই যুগে মুসলিম গণ-বিবেক যে সু-উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, তার সাথে ঘটনার উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু ডাঃ হাইকেলের মত ব্যক্তি খালেদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও ওমরের নীতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমাকে রীতিমত বিস্মিত করেছে। হাইকেলের এই ব্যাখ্যা ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই। অবশ্য এটা এ যুগের নোংরা রাজনীতির সাথে যথার্থভাবে সংগতিশীল। ‘আস-সিদ্দিকু আবু বকর’ নামক গ্রন্থের ১৫০ থেকে ১৫২ পৃষ্ঠায় ডাঃ হাইকেল লিখেছেনঃ
“মালেক ইবনে নোয়াইরার ব্যাপারে আবু বকর ও ওমরের মধ্যে মতভেদ কত দুর গিয়ে পৌছেছিল তা পাঠক নিষ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন্ তার দু’জনেই যে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন, সেটা সন্দেহাতীত ব্যাপার। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, খালেদের ভুল কি একজনের নিকট অতীব বিরাট এবং অপর জনের নিকট অতীব ক্ষুদ্র ছিল, না ব্যাপক বিদ্রোহ ও ধর্ম ত্যাগের সমস্যা জর্জরিত আরব উপদ্বীপের মুসলিম জীবনের নাজুক পরিস্থিতিতে সঠিক নীতি নির্ধারণ নিয়েই আসল মতভেদের উদ্ভব হয়েছিল?”
আমার মতে আসল মতভেদ ছিল নীতি নির্ধারণ নিয়ে। উভয় খলিফার প্রকৃতিতে যে পার্থক্য ছিল সে অনুসারে এই মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ওমর (রাঃ) ছিলেন আপোষহীন ন্যায় বিচারের প্রতীক। তার দৃষ্টিতে খালেদ জনৈক মুসলমানের ওপর অবিচার করেছিলেন। তাই তিনি যাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ ন্যাক্কারজনক ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী কাজ করার সুযোগ না পান সে জন্য তাকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা প্রয়োজন ছিল। মালেকের ব্যাপারে খালেদের বুদ্ধি ও বিবেচনাই ভুল হয়েছে একথা মেনে নিয়ে তাকে ক্ষমা করা গেলেও- যদিও হযরত ওমর (রাঃ) তা মানতে পারতেন না- মালেকের স্ত্রী লায়লার সাথে অশালীন আচরণের শাস্তি না দেয়া কিছুতেই শোভন হতো না। [যদি সত্যিই হযরত ওমরের অভিমত এত কঠিন ও চরম ভাবাপন্ন হতো তাহলে নিজের খেলাফতকালে তাকে অবশ্যিই ব্যাভিচারের শাস্তি দিতেন-গ্রন্থকার।] ‘তিনি একজন অজেয় সেনাপতি’ ‘তিনি খোদার তলোয়ার’ এ সব কথা তাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য যথেষ্ট হতো না। কেননা তার মানে দাঁড়াতো খালেদের মত লোকদের জন্য হারামকে হালাল করে দেয়া। আর এরূপ করা হলে মুসলমানদের সামনে আল্লাহর বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিকৃষ্টতর নজীর স্থাপন করা হতো। নিজের এই মতামতের কারণে ওমর (রাঃ) বার বার আবু বকর (রাঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) খালেদকে (রাঃ) ডেকে তার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।
অপরদিকে আবু বকরের (রাঃ) দৃষ্টিতে পরিস্থিতি এত বেশি নাজুক ছিল যে, এ ধরনের ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না। সে সময়ে গোটা দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আরবের চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমনি পরিস্থিতিতে ভুলবশতঃ কিংবা ইচ্ছাবশতঃ এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করার কি গুরুত্ব থাকতে পারে? যে সেনাপতিকে ত্রুটিপূর্ণ কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল তিনি সেই ভয়াবহ বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম ছিলেন। কোন স্ত্রীকে ইদ্দতের পূর্বে বিয়ে করা আরবদের প্রচলিত আদত-অভ্যাসের পরিপন্থি ছিল না, বিশেষতঃ কোনো বিজয়ী সেনাপতির পক্ষে। কারণ যুদ্ধের কারণেই সে যুদ্ধবন্দী মেয়েদের মালিকানা অধিকার লাভ করে থাকে। [ইসলামী শরিয়তের ক খ-ও জানে না - এমন লোকের পক্ষে এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব। যদি সত্যি সত্যিই খালেদ কোন মুসলমানের স্ত্রীর ওপর বলৎকার করে থাকেন তাহলে তার ওপর ব্যাভিচারের দন্ড কার্যকরী করা অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া মালেক যখন মুসলমান তখন তার স্ত্রীকে বাঁদী বানানোর প্রশ্নই ওঠেনা।] খালেদের মত অসাধারণ মানুষের ব্যাপারে আইনের কড়াকড়ি আরোপ করা অপরিহার্য ছিলনা। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে যখন এমন কাজ রাস্ট্রের স্বার্থের বিরোধী ছিল এবং তার অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারতো। এ সময়ে মুসলমানদের জন্য খালেদের তরবারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যেদিন আবু বকর (রাঃ) তাকে ডেকে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন সেদিনই মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল খালেদের। খালেদের (রাঃ) অবস্থানস্থল আল-বাত্তাহের সন্নিকত এমামাতে মোসায়লেমা বনু হানিফার চল্লিশ হাজার নওজোয়ানকে নিয়ে যুদ্ধের সাজে সেজে ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ছিল সবচাইতে সাংঘাতিক বিদ্রোহ। মুসলমানদের সেনাপতিদের মধ্যে থেকে ইকরামা (রাঃ) কে সে আটক করে ফেলেছিল এবং তখন বিজয়ের সমস্ত আশা-আকাংখা খালেদের তরবারীর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। এমতাবস্থায় মালেক ইবনে নোয়াইরাকে হত্যা করার কারণে অথবা খালেদকে বিমুগ্ধকারিণী অপরূপ সুন্দরী লায়লার কারণে খালেদ (রাঃ)কে অপসারণ করা এবং মুসলিম বিহিনীকে মুসাইলেমার হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার অবকাশ সৃষ্টি করা কি করে উচিত হতো? এভাবে আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদে ফেলে দেয়া হতো নয় কি? খালেদ খোদার পতাকা ছিলেন-খোদার তরবারী ছিলেন- তাই আবু বকর (রাঃ) তাকে ডেকে নিয়ে শুধু তিরস্কার করে ক্ষান্ত হওয়া এবং তৎক্ষনাৎ এমামাতে গিয়ে মোসালেমার মোকাবেলা করতে নির্দেশ দেয়াই সবচেয়ে সংগত কর্মপন্থা বলে বিবেচনা করেছিলেন।
এই হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে খালেদ ইবনে ওলিদের ব্যাপারে আবু বকর ও ওমরের নীতির পার্থক্যের আসল চিত্র। বনি হানিফার মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার যখন ইকরামা (রাঃ) কে গ্রেফতার করে তখন আবু বকর (রাঃ) খালেদকে তার মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মদিনাবাসী এবং ওমরের মতের সমর্থকরা এতে করে বুঝতে পারবে যে- খালেদ ইসলামের দুর্যোগ মূহূর্তের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এ নির্দেশ দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, খালেদ হয় যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হবে- তখন সেটা হবে মালেক ও তার স্ত্রীর প্রতি অবিচারের চেয়ে উত্তম শাস্তি আর না হয় তিনি বিজয়ী হবেন এবং সে বিজয় তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হলেন এবং বিপুল গণিমতের সম্পদ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এত বড় বিপদ থেকে মুক্ত করলেন। সে বিপদের সামনে আল বাত্তাহে অবস্থানকালে তার পক্ষ থেকে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয় - সেটার কোন গুরুত্বই ছিলনা।
এই হচ্ছে ডাঃ হাইকেলের দৃষ্টিতে পরিস্থিতির রূপ। আমার দেখে বিস্ময় জাগে যে, এক ব্যক্তি কিভাবে তার কল্পনার ডানা মেলে ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে প্রবেশ করে এবং সেই জাগ্রত ও সচেতন বিবেক সমূহের ছায়তলে বসে লেখনি পরিচালনা করে। অথচ তার নিজের বিবেক ও মন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দানের ব্যাপারে আধুনিক জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উর্দ্ধে ওঠা তো দূরের কথা তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে ইসলামের মূল প্রাণশক্তি এবং সেই বিশেষ যুগের বাস্তব ইতিহাসের কোনই সম্পর্ক নেই। এটা তো বর্তমান যুগের রাজনীতি। এই রাজনীতির দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট লক্ষ্যের জন্য নিকৃষ্ট কর্মপন্থা ও উপায় উপকরনের আশ্রয় গ্রহণ সম্পূর্ণ বৈধ। এ রাজনীতি মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে গোলাম বানিয়ে দেয় আর একে উচ্চতর ‘ডিপ্লোমেসী’ এবং উচ্চাঙ্গের কর্মদক্ষতা ও কর্মকুশলতার নামে অভিহিত করে।
যে চিত্র ডাঃ হাইকেল তুলে ধরেছেন এবং যাকে তিনি একমাত্র বিশুদ্ধ চিত্র বলে দাবী করেছেন- তাতে হযরত আবু বকরের (রাঃ) ব্যক্তিত্বকে কত নীচ ও হীন করে দেখানো হয়েছে তা যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যাক্তি দেখতে পারে।
সৌভাগ্য যে, আজকের নিকৃষ্ট ও অধঃপতিত সমাজের মানুষ যে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখতে অভ্যস্ত আবু বকরের ব্যক্তিত্ত তার অনেক উর্দ্ধে। এ দূরবীক্ষণ দ্বারা মানবতার সেই সু-উন্নত স্তরকে পর্যবেক্ষণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ পর্যবেক্ষক যদি ইসলামী শরিয়তের সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে তাহলে ব্যাপার আরো ঘোলাটে হয়ে যায়।
স্বীয় পুস্তক ‘আল-ফারুক-উমর’-এ ডাঃ হাইকেল পুনরায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি খালেদকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে হযরত ওমরের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। সেখানেও পুনরায় তাকে আধুনিক অধঃপতিত সভ্যতা প্রভাবিত করেছে। যে দল-নেতার সামনে আপাতঃ কল্যাণ ও আঞ্চলিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কিছুর গুরুত্ব থাকে না-ইসলামের প্রাণশক্তি যার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়- সেই নেতার চরিত্রই লেখকের মন মানসে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ৯৯ ও ১০০ পৃঃ তিনি লিখেছেনঃ
“বুঝে আসে না যে, হযরত ওমর (রাঃ) খালেদের (রাঃ) অপসারণের মত বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত কেন নিলেন। অথচ সিরিয়ায় মুসলমানদের সমগ্র সামরিক শক্তি খালেদের অধীন ছিল। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সেটা ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ মুহুর্ত। তারা রোমক সৈন্যদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধও হচিছল না- আবার দু’পক্ষের কেউ কাউকে হার মানাতে পারছিল না। ইরাক থেকে খালেদের আগমনের পূর্বে যে পরিস্থিতি ছিল তার আগমনের পরও সে পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। উভয় পক্ষ আক্রমন চালাবার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করছিল। খলিফার এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিল যে, খালেদকে পদচুত করলে মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়বে এবং পরিস্থিতি আরো অধিক বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ খালেদ যতক্ষনে না মুসলমানদের উক্ত বিপজ্জনক মুহূর্ত অতিক্রম করিয়ে না নেন ততক্ষণ খলিফার অপেক্ষা করাই উচিত ছিল এবং এরপর যা খুশী নির্দেশ তিনি জারী করতে পারতেন”।
“যুদ্ধের উত্থান-পতনে এ ব্যাপারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আবু ওবাইদা (রাঃ) খলিফার অসন্তোষ ও অমতকে অগ্রাহ্য করে এ সব ব্যাপারের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু ওমর ব্যাপারটা দেখেছেন অন্য দিক থেকে। তিনি যদি খালেদকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী রাখতেন তাহলে তার নীতি ক্ষুন্ন হতো এবং ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়তো। জানা কথা যে, যুদ্ধে মুসলমানদের হয় জয় হতো না হয় পরাজয় হতো। যদি পরাজয় হতো তাহলে খালেদকে পদচ্যুত করেও লাভ হতো না। কিন্তু যদি খালেদের নেতৃত্বে মুসলমানরা জয় লাভ করতো তাহলে হযরত ওমরের পক্ষে তাকে বিজয় ও সাফল্যের গৌরব থেকে নীচে নামিয়ে পদচ্যুত করা সম্ভব হতো না। এরূপ করা অত্যন্ত ভুল কাজ হতো।
“ওমর (রাঃ) মোটের ওপর চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, সিরিয়ায় অথবা অন্য কোথাও খালেদকে সেনাপতি পদে বহাল রাখবেন না। এ কারণেই তিনি পদচ্যুতির হুকুম জারী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন। এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তার যুক্তি এ ছিল যে খালেদ (রাঃ) হযরত আবু বকররের (রাঃ) নির্দেশাবলী যথাযতরূপে পালন করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল, তাই কেউ ওমরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারতো না। তিনি যা ভাল বুঝেছেন তা-ই করেছেন। খালেদও এমন পর্যায়ে ছিলেন যে, তাকে পদচ্যুতকারীরর ওপর কোনো অবিচারের অভিযোগ আরোপ করা যেতো না”।
এ হলো বিংশ শতাব্দীর হাইকেল ‘পাশা’র চিন্তাধারা- যা তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর ওমর ফারুকের ওপর চাপাতে চাচ্ছেন। ইতিপূর্বে তিনি হযরত আবু বকরের ব্যাপারেও এরূপ করেছেন। যার আত্মা আবু বকর (রাঃ) ও ওমরের আত্মাকে স্পর্শও করতে পারেনি, যে ইসলামের পরিবেশে কিছুদিন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও এক মুহুর্তের জন্যও বিংশ শতাব্দির মলিনতা ও কদর্যতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি- সেরূপ লোকের পক্ষেই এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করা সম্ভব। আধুনিক সভ্যতার নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বিবেক, সত্যবাদিতা ও ধর্ম- সব কিছুকে উপেক্ষাকারী সুবিধাবাদ যে লেখকের পিছু ছাড়েনি- তা অত্যন্ত স্পষ্ট। অধিকন্তু এ যুগের মিথ্যাচার ও প্রতারণা দর্শন তার চিন্তা ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
জিজ্ঞাস্য এই যে, হাইকেল সাহেব ওমর ফারুক (রাঃ) কে কি ভেবেছেন? যদি পরিস্থিতি অন্যরকম হতো এবং এরূপ সুযোগ না থাকতো তাহলে কি ওমর (রাঃ) খালেদ (রাঃ)কে ছেড়ে দিতেন? অথচ স্বয়ং হাইকেল পাশার বর্ণনা অনুসারে হযরত ওমরের বিবেক এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে, মালেক ইবনে নোয়াইরার ব্যাপারে এবং আল্লাহ ও তার দ্বীনের ব্যাপারে খালেদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল।
যে ওমর (রাঃ) পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারতেন কিন্তু নিজে নীতিচ্যুত হতেন না, যে ওমরের ঈমান ঝড়ের গতিবেগ ঘুরিয়ে দিত, কিন্তু নিজে বিচলিত হতেন না- সেই ওমর (রাঃ) কি করে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন?
এ ধরনের কাজ করতো উমাইয়া ও আব্বাসীয় বাদশাহরা। মানুষ তাদের এসব কাজকে ‘ডিপ্লোমেসী’ ও ‘চতুরতা’ বলে আখ্যায়িত করতো। কিন্তু ওমর (রাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এসব থেকে বহু উর্ধ্বে। এখন কেউ যদি তাঁদের সম্পর্কেও এই রূপ চিন্তা করা শুরু করে থাকেন তাহলে সেটা হচ্ছে বর্তমান যুগের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি ও নিম্ন মানের মূল্যবোধের প্রভাব।
আমি এই চিন্তাধারার উপস্থাপনা এবং তার ভ্রান্তি স্পষ্ট করার ব্যাপারে খানিকটা বিস্তারিত বিবরণের সাহায্য নিয়েছি। কারণ এ ছাড়া আধুনিক যুগের ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তি থেকে আক্রান্ত মন-মানসকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রাণশক্তির চরমোৎকর্ষের যুগে যে চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কেউ কেউ সেই চিন্তা পদ্ধতির ব্যাখ্যা বর্তমান জড়বাদী চিন্তা-পদ্ধতির আলোকে দিতে চান। অথচ আজকের এ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত তখনকার আত্মিক চেতনা ও জাগরণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। আমি এই বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যার অপনোদন করতে চাই। কারণ মানবীয় বিবেক এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের এ দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
অবশ্য আমি প্রথম শতকের লোকদের কোনো কৃত্রিম পোষাকে আবৃত করে পেশ করতে চাই না অথবা তাদেরকে যাবতীয় মানব-সুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত দেখাতেও ইচ্ছুক নই। আমি শুধু চাই মানুষ পুনরায় বিবেকের ওপর নির্ভর করতে শিখুক। এই উদ্দেশ্যে আমি মুসলমানদের জীবনের সঠিক পরিচয় পেশ করতে চাই। এতে করে যেসব বিবেকের মধ্যে উক্ত উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তারা সেই পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।
এখন আমি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম শতকের মুসলমানরা যেরূপ বিবেক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত পুনরায় পেশ করবো।
একদিন দেখা গেল, আমিরু মুমেনীন ওমর ইবনুল খাত্তার (রাঃ) পানির মশক ঘাড়ে করে নিয়ে আসছেন। তার পুত্র বিক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি এরূপ করছেন কেন?” তিনি জবাব দেন, “আমার মন অহংকার ও আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়েছিল, তাই ওকে আমি অপদস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি”। চেতনার তীব্রতা দেখুন! এই ব্যক্তির মনের কোনো এক কোনে ক্ষণিকের জন্য খেলাফত, রাজ্য জয় এবং অনাগত কালের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সামান্যতম আত্মম্ভরিতা মাথা তুলেছিল। তিনি এটা বরদাশত করলেন না এবং তৎক্ষণাৎ সকলের সামনে প্রবৃত্তিকে জব্দ করা শুরু করে দিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ভেবে দেখলেন না যে, তিনি কত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক, যার মধ্যে আরব উপদ্বীপ ছাড়াও রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ দেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
আর একদিন দেখা গেল, আলী ইবনে তালেব প্রচন্ড শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। তার গায়ে শীত নিবারনের উপযুক্ত পোষাক নেই। ‘বায়তুল মাল’ তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তাঁর বিবেক সচেতনতা তাঁকে একটি কপর্দকও স্পর্শ করতে দিচ্ছে না।
আবু ওবায়দা (রাঃ) ‘আমওয়াসে’ নিজ বাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেছেন। ‘আমওয়াসে’ ভয়াবহ মহামারী দেখা দিল। হযরত ওমর (রাঃ) শংকিত হলেন পাছে ‘আমিনুল উম্মতের’(আবু ওবায়দা) কোনো অনিষ্ট না হয়। তিনি তাঁকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চিঠি লিখে নিজের কাছে ডাকেন। চিঠিতে তিনি লিখেনঃ
“সালাম বাদ, একটা জরুরী কাজে তোমার আমার সামনা-সামনি কথা বলা প্রয়োজন। আমি খুব জোর দিয়ে বলছি, এই চিঠি পড়ার পর চিঠি রাখার আগেই আমার কাছে রওয়ানা হও”। আবু ওবায়দা (রাঃ) চিঠি পড়া মাত্রই আসল উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই খলিফা একটা পথ খুঁজে বের করেছেন। সংগে সংগে বলে ওঠেনঃ “আল্লাহ! আমিরুল মুমেনীনকে ক্ষমা করুন”। তিনি হযরত ওমরকে চিঠির নিম্নরূপ জবাব লিখে পাঠানঃ
“আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে দিয়ে আপনার প্রয়োজনটা কি, এ সময়ে মুসলমানদের গোটা বাহিনী আমার সাথে রয়েছে। আমি মুসলিম জোয়ানদের নিকট থেকে পৃথক হতে চাই না। আল্লাহ যতক্ষণ আমার ও তাদের ভাগ্যের লিখন পূর্ণ না করেন ততক্ষণ আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে পারি না। আমিরুল মুমেনীন, এই সব কারণে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমাকে এই নির্দেশ পালনে বাধ্য করবেন না। আমাকে আমার জোয়ানদের সাথে থাকতে দিন”।
হযরত ওমর (রাঃ) চিঠিটা পড়ে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করেন, “আবু ওবায়দা কি ইন্তেকাল করেছেন?” তিনি বাষ্পরুদ্ধ কন্ঠে জবাব দেন, “না”।
বস্তুতঃ তাকদীরের ওপর অটল বিশ্বাস এবং আল্লাহর পথের প্রতিটি সৈনিকের নিজের সমান মর্যাদা দান- এ দুটো কার্যকারণই আবু ওবায়দা (রাঃ) কে মৃত্যুর মুখে অবিচল থাকতে বাধ্য করেছিল।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুয়াজ্জিন হজরত বেলাল বিন রাবাহের ইসলামী ভাই আবু রুয়াইহা খাশ্য়ামী তার বিয়ের জন্য ইয়ামনের কতিপয় লোকের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য বেলালের কাছে আবদার ধরেন। হজরত বেলাল সেই লোকদেরকে বলেন, “আমি বেলাল বিন রাবাহ। আর এ হচ্ছে আমার ভাই আবু রুয়াইহা। এর ধর্ম ও চরিত্র দুটোই খারাপ। তোমাদের ইচ্ছা হয় তার সাথে আত্মীয়তা কর, না হয় করো না”।
একদম পরিস্কার কথা বলে দেন। নিজের ভাই এর দোষ গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেননি।
তিনি একটা বিয়ের কথা-বার্তার মাধ্যম হচ্ছেন- এ অনুভূতি তাঁকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি থেকে বিস্মৃত করে দেয়নি। ইয়ামনবাসীরা তাঁর সত্যবাদীতায় মুগ্ধ হয়ে সম্বন্ধ স্থাপনে রাজী হন। এত বড় সত্যবাদী তাদের মেয়ের জন্য বিয়ের পয়গাম এনেছে এটুকুই তাদের জন্য যথেষ্ট গৌরবের ব্যাপার ছিল।
ইমাম আবু হানিফার চরিত্র লক্ষ্যনীয়ঃ তিনি নিজের শরীক ব্যবসায়ী হাফ্স ইবনে আবদুর রহমানের কাছে কিছু কাপড় বিক্রীর জন্য পাঠান। তিনি তাঁকে বলে দেন যে, একখানা কাপড়ে কিছু খুঁত আছে তা ক্রেতাকে জানিয়ে দিতে হবে। হাফ্স সেই কাপড় বিক্রী করে দেন কিন্তু খুঁতের কথা বলতে ভুলে যান। খুঁতপূর্ণ কাপড়ের বিনিময়ে তিনি পুরো দাম আদায় করেন। এই চালানের দাম ছিল ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম। আবু হানিফা (রঃ) তাঁর শরীককে ক্রেতার সন্ধান নিতে বলেন কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর তিনি তাঁর শরীক থেকে পৃথক হন এবং গোটা চালানের দাম আল্লাহর পথে দান করে দেন। নিজের পবিত্র সম্পত্তি সাথে তিনি সেটা মিশাতেও চাননি। [আবদুল হালিম আল-জুনদীর গ্রন্থ- ‘আবু হানিফা বাতলুল হুররিয়াতি অত্-তাছামুহি ফিল ইসলাম’ থেকে গৃহীত।]
বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত ইমাম ইউনুছ বিন ওবায়েদের নিকট বিভিন্ন মূল্যের কাপড় বিক্রীর জন্য রক্ষিত ছিল। এক রকমের কাপড়ের প্রতি জোড়ার দাম ছিল চারশো দিরহাম। অপর এক ধরনের কাপড়ের প্রতি জোড়ার দাম ছিল দু’শো দিরহাম। তিনি নিজের ভ্রাতুস্পুত্রকে দোকানে রেখে নামাজ পড়তে যান। এ সময় একজন লোক আসে এবং চারশো দিরহাম মূল্যের জোড়া চায়। ছেলেটি তাকে দু’শো দিরহাম মূল্যের জোড়া দেখায়। সেটা তার পছন্দ হয় এবং সন্তুষ্ট চিত্তে খরিদ করে নিয়ে যায়। সে উক্ত কাপড় নিয়ে বাড়ী যাওয়ার সময় পথে ইউনুছের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ইউনুছ তার কাপড় চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে ওটা কত দামে খরিদ করেছে? সে জবাব দেয় যে, চারশো দিরহাম। তিনি বলেন, এটা তো দু’শো দিরহাম মূল্যের কাপড়। যাও ওটা ফেরত দিয়ে এস। সে জবাব দিল, এ কাপড় আমাদের দেশে পাঁচশো দিরহাম মূল্যে পাওয়া যায়। তাই আমি ওটা সন্তুষ্ট চিত্তেই খরিদ করেছি।ইউনুস বললেন, তোমাকে ফেরত নিতেই হবে। কারণ ইসলামের ব্যাপারে হীত কামনার চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে না। এই বলে তিনি তাকে দোকানে নিয়ে যান এবং দু’শো দিরহাম ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই বলে তিরস্কার করেনঃ “তোর লজ্জা করলো না? তোর মনে খোদার ভয়ের সৃষ্টি হলো না? শতকরা একশো ভাগ লাভ করিস্ আর মুসলমানদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিস না?” ছেলেটি শপথ করে বললো যে, ক্রেতা খুশী হয়েই কাপড় কিনেছিল। এতে তিনি বললেন, “তুই নিজের জন্য যা পছন্দ করিস- তা অপরের জন্যও পছন্দ করতে হয়, একথা ভুলে গেলি কেন?”
মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার ভৃত্য এক ব্যাক্তির নিকট পাঁচ দিরহাম দামের কাপড় দশ দিরহামে বিক্রী করে। তিনি জানতে পেরে সারাদিন উক্ত ক্রেতার সন্ধান করেন। শেষে তাকে পেয়ে বললেন, ভৃত্য ভুল করে তোমার কাছে পাচঁ দিরহামের কাপড় দশ দিরহামে বিক্রী করেছে। সে আশ্চর্য হয়ে বললো, “আমিতো খুশী হয়েই এ দাম দিয়েছি”। তিনি জবাব দিলেন, “তুমি হাজার খুশী হও। আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তা তোমার জন্যও পছন্দ করবো”। এই বলে তিনি তাকে পাঁচ দিরহাম ফিরিয়ে দেন। (আর রিসালাতুল খালেদাঃ আবদুর রহমান আজ্জাম)
এ তিনটি ঘটনার রহস্য উদঘাটনের সবচেয়ে শক্তিশালী চাবিকাঠি হচ্ছে ইউনুস ইবনে ওবায়েদের এই উক্তি যেঃ “তোর লজ্জা করলো না?” নিঃসন্দেহে নিজের বিবেকের কাছে লজ্জিত হওয়া ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়াই হচেছ এই সমস্ত ঘটনার পেছনে সক্রিয় একমাত্র শক্তি। মানুষের বিবেক, প্রকৃতি ও মন-মানস যখন ইসলামের প্রাণশক্তিকে গ্রহণ করে এবং সেই প্রাণশক্তি তার মেরু-মজ্জায় মিশে যায় তখন ইসলাম পূর্ণ শক্তি সহকারে তার মধ্যে এরূপ চরিত্রের সৃষ্টি করে।
এই কয়টি দৃষ্টান্ত ছাড়া আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু মানুষের বিবেকের পরিশুদ্ধির জন্য ইসলাম যে সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে, তার দিকে পথ-নির্দেশের জন্য এই দৃষ্টান্ত কয়টিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইসলাম মানুষের বিবেককে যাবতীয় বস্তুগত প্রয়োজন, সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং জানমাল ও পদ-মর্যাদার আকর্ষণ থেকে উর্ধ্বে তুলতে চায়। সে মানুষকে সদা সচেতন, বিবেকবান ও তীব্র অনুভূতি সহকারে জীবনের সকল দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে চায়।
সাম্যের উদাহরণ
ইসলাম মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ সাম্যের বাণী নিয়ে এসেছিল। যত মূল্যবোধ সাম্যের পথে অন্তরায় সৃ্ষ্টি করেছে তার শৃংখল থেকে সে মানুষকে মুক্ত করতে এসেছিল। এবার আমরা দেখতে চাই এই মতবাদকে বাস্তব জীবনে কিভাবে রূপায়িত করা হয়েছে।
সে সময়ে সারা দুনিয়ার দাস-শ্রেণী স্বাধীন মানব জাতি থেকে পৃথক একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বিদ্যমান ছিল। আরব উপদ্বীপেরও ছিল একই অবস্থা। এ ব্যাপারে আমরা যখন হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যাবলী বিবেচনা করি তখন দেখতে পাই যে তিনি নিজের ফুফাতো বোন এবং কোরাইশ বংশীয় হাশেমী গোত্রের মেয়ে জয়নবকে নিজের আজাদ করা গোলাম জায়েদের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ে একটা অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার, এতে উভয় পক্ষের সমতা অন্য সকল প্রশ্নের চাইতে গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।
মহানবী (সাঃ) ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো শক্তির পক্ষে এত বড় অসাধারণ কাজ করা সম্ভব ছিল না- এমন কি আজও মুসলিম জাহান ব্যতীত অন্য কোথাও সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসবৃত্তি বে-আইনী বটে কিন্তু কোনো নিগ্রোর পক্ষে কোন শ্বেতাংগিনীকে-তা সে যতই নিকৃষ্ট হোক- বিয়ে করা আইনানুগভাবে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, বরং কোনো নিগ্রোর পক্ষে বাসে বা অন্য কোন যানে-রেস্তোঁরায় থিয়েটারে অথবা অন্য কোন স্থানে কোন শ্বেতাঙ্গের পাশাপাশি উপবেশন করাও আজ পর্যন্ত নিষিদ্ধ।
হিজরতের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন তখন তার স্বাধীনকৃত গোলাম জায়েদ এবং তার চাচা হামজা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন, হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং খারেজা ইবনে জায়েদ ভাই ভাই বন্ধনে আবদ্ধ হন। খালেদ ইবনে রুয়াইছা খাশ্য়ানী এবং বিলাল ইবনে আবি রাবাহের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। এই ভ্রাতৃত্ব শুধু কথার মধ্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি- বরং রক্ত সম্পর্কের মত মজবুত ও পাকাপোক্ত সম্পর্কের রূপ ধারণ করে। জান-মাল ও জীবনের সকল ব্যাপারে তাদের মধ্যে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।
এরপরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জায়েদকে মুতা যুদ্ধে সেনাপতি বানিয়ে পাঠান। অতঃপর তার ছেলে উসামা (রাঃ)-কে রোমের যুদ্ধে এমন এক বাহিনীর সেনাপতি করেন-যার মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন মুহাজের ও আনসার। এই সেনাবাহিনীতে হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং ওমন (রাঃ)ও ছিলেন- যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকটতম সাথী ও উজীর এবং পরে পূর্ণ ঐক্যমত সহকারে খলিফা নির্বাচিত হন। উসামার নেতৃত্বে পরিচালিত এই সেনাবাহিনীতে রাসূলুল্লার (সাঃ) ঘনিষ্ট আত্মীয় সা’দ ইবনে আবি আক্কাসও ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মাতুল গোষ্ঠি-বনু জোহরা গোত্রের লোক। তাছাড়া কোরাইশদের যে সব ব্যক্তি নবুয়তের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন- তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। আল্লাহতায়ালা তাকে মাত্র সতের বছরে ইসলাম গ্রহণের তওফিক দেন। তিনি বিরাট বিত্তশালী ও মর্যাদা সম্পন্ন লোকি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ সমর-কুশলীও ছিলেন এবং সেই সাথে জেহাদী প্রেরণায়ও উদ্বুদ্ধ ছিলেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর হজরত আবু বকর (রাঃ) যখন উসামার বাহিনীকে পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিযুক্ত সেনাপতিকেও বহাল রাখেন। তিনি যখন সেনাপতিকে বিদায় দেয়ার জন্য মদিনার বাইরে আসেন- তখন উসামা সওয়ারীতে চড়ে যাচ্ছিলেন, আর খলিফাতুল মুসলেমীন চলছিলেন পায়ে হেঁটে। উসামা এতে অত্যন্ত কুন্ঠা বোধ করেন। নিজে সওয়ার হয়ে সওয়ারীতে চড়বেন, আর বৃদ্ধ খলিফা পায়ে হেঁটে চলবেন- এটা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাই উসামা বললেন, “খলিফাতুর রাসূল! আপনিও সওয়ারীতে আরোহন করুন-নইলে আমি নেমে আসবো”। খলিফা শপথ করে বলেন, “খোদার কছম! তুমি নীচে নেমনা। খোদার কছম! নীচে নেমনা। খোদার কছম! আমি সওয়ারীতে আরোহন করবো না। আমি কিছুক্ষণ আল্লাহর রাহে হেঁটে চললে আমার কোনোই ক্ষতি হবে না”। এরপর হজরত আবু বকরের (রাঃ) হঠাৎ মনে পড়ে যে, হজরত ওমরের তাঁর প্রয়োজন পড়তে পারে। অসুবিধা ছিল এই যে, ওমর (রাঃ) উসামার বাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। যেহেতু সে বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন উসামা, তাই ওমর (রাঃ) কে রাখতে হলে উসামার অনুমতি প্রয়োজন।খলিফা বলেন, “যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক ওমরকে আমার সাহায্যের জন্য রেখে যান”।
এখানে এসে বিস্ময়ে ইতিহাসের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। “যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক ওমরকে (রাঃ) আমার সাহায্যের জন্য রেখে যান”। একথা কত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে খলিফা তার মামুলী সেনাপতিকে বলতে পারেন তা বুঝিয়ে বলার উপযুক্ত ভাষা আমাদের নেই।
ইতিহাস আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়। আমরা দেখতে পাই, ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ)কে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অথচ তিনিও দাস শ্রেণী-উদ্ভুত ছিলেন। আমাদের কল্পনার চোখ আরো বিস্তারিত হয় যখনি আমরা দেখি যে, আমর ইবনে হিশামের পুত্র সোহায়েল, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং অন্যান্য কোরাইশ সর্দার দাঁড়ানো থাকতে হজরত ওমর দু’জন প্রাক্তন গোলাম সোহায়েব (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ)কে আগে ডেকে নেন। কেননা তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবী ও বদর যুদ্ধের সিপাহী। এ অগ্রাধিকারে আবু সুফিয়ান অস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে জাহেলিয়াতের উক্তি করে ফেলেনঃ “এমন কান্ড কখনো দেখিনি। আমাদেরকে দরজায় দাঁড় করিয়ে গোলামগুলোকে ভেতরে ডেকে নেয়া হলো”।
হজরত ওমর (রাঃ) একদিন মক্কা শরীফের কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখেন যে চাকর-নফররা মুনিবদের সাথে খেতে বসেনি বরং একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে মুনিবদের উদ্দেশ্যে বলেন, “ব্যাপার কি! নিজেদের ভৃত্যদের সাথে এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে কেন?” অতঃপর তিনি ওই ভৃত্যদেরকে ডেকে জোর পূর্বক মনিবদের সাথে ভোজনে বসিয়ে দেন।
হযরত ওমর (রাঃ) নাফে ইবনুল হারেসকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার সাথে উসফানে খলিফার সাক্ষাত হলে জিজ্ঞাসা করেন, “কি সংবাদ, কাকে স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ?” নাফে জবাব দেন, “ইবনে আবজাকে স্থালাভিষিক্ত করে এসেছি। তিনি আমাদের আজাদকৃত গোলামদের অন্যতম”। ওমর (রাঃ) বললেন, “সে কি! একজন আজাদকৃত গোলামকে মক্কাবাসীদের ওপর নিজের স্থলাভিষিক্ত করে এলে?” জবাব এলো, “তিনি কোরআনে অভিজ্ঞ, শরিয়তে সুপন্ডিত এবং সুবিচারক”। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, “হবেই তো! আমাদের নবী (সাঃ) বলে গেছেন যে, আল্লাহতায়ালা এই কিতাব দ্বারা অনেককে ওপরে তুলবেন, অনেককে নীচে নামাবেন”।
------------এরাবিক টেক্সট-------
বলা বাহুল্য, হযরত ওমর (রাঃ) আপত্তি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নয়- বরং ইবনে আবজার পরিচয় জানবার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন। নইলে এই ওমরই নিজের পরবর্তী খলিফা নির্বাচনকারী ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিষদকে অছিয়ত করার সময় বলতেন না যে, “হোজাইফার গোলাম সালেম জীবিত থাকলে আমি তাঁকে খলিফা নিয়োগ করে যেতাম”। এ থেকে বুঝা যায়, তিনি তাকে পরিষদের ছয়জন সদস্যের প্রত্যেকের চেয়ে উত্তম মনে করতেন। এই ছয়জন ছিলেন, ওসমান, আলী, তালহা, জোবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা’দ ইবনে আবি আক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)।
একবার জনৈক আজাদকৃত গোলাম অন্য একজন কোরাইশ বংশীয় ব্যক্তির নিকট তার বোনের পাণি গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করে এবং তার বোনকে প্রচুর অর্থ দিতে চায়। কিন্তু সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ওমর (রাঃ) যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোন কারণে তার সাথে তোমার বোন বিয়ে দিতে চাওনি? সে অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং সে তোমার বোনকে অনেক অর্থ সম্পদও দিতে চেয়েছে”। লোকটা বললো, “আমরা উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। কিন্তু সে আমার বোনের সম-পর্যায়ভুক্ত নয়”। ওমর (রাঃ) বললেন, “এই ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, দুনিয়ায় সম্ভ্রান্ত এই জন্যে যে, সে প্রচুর বিত্তবান আখেরাতে সম্ভ্রান্ত এই জন্য যে, সে খোদাভীরু ও সৎকর্মশীল। যদি মেয়ে রাজী থাকে তবে তাকে এই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও”। লোকটি তার বোনের মতামত গ্রহণ করে দেখে যে সে সম্মত। অতঃপর তার সাথে তার বোনকে বিয়ে দিয়ে দেয়।
গোলামদের যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা, উচ্চ থেকে উচ্চতর পদমর্যাদায় উন্নীত হবার অবাধ সুযোগ ছিল। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে তার গোলাম ইকরাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে তার গোলাম নাফে, আনাস ইবনে মালিকের সাথে তার গোলাম ইবনে শিরীন এবং আবু হোরাইরার সাথে তার গোলাম ইবনে হরমুজ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বসরায় হাসান বসরী এবং মক্কায় মুজাহেদ ইবনে জুবায়ের, আতা ইবনে আবি রাবাহ এবং তাউস ইবনে কাইসান খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন দাস বংশোদ্ভুত। অনুরূপভাবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সময়কার মিশরের মুফতি ইয়াজিদ ইবনে আবু যিব দিনকালার আসওয়াদ নামক ব্যক্তির গোলাম ছিলেন। (আবু হানিফাঃ আবদুল হালিম জুন্দী)।
শ্রমজীবীদের ব্যাপারেও মুসলমানদের নীতি অনুরূপ ছিল। গায়ে খেটে জীবিকা উপার্জনকারীরা মুসলমানদের সমাজ জীবনে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিল। স্বয়ং শ্রমের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। তাই শ্রমিক মাত্রই- তা সে যে পেশার সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক- সমান শ্রদ্ধা লাভ করতো। কোনো শ্রমজীবীর পেশা তাকে জ্ঞানার্জনে বাধা দিতে পারতো না- এমনকি বড় বিদ্বান ও ওস্তাদে পরিনত হবার পথেও কোনো বাধা ছিল না।
ইমাম আবু হানিফা কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন, আর তার পরবর্তী বহু বিখ্যাত মনীষি ব্যবসায়ী অথবা কারিগর ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে আমর ছিলেন জুতা প্রস্তুতকারী। তার পিতা ছিলেন ইমাম আবু হানিফার সহচর মুহাম্মদ ও হাসানের শিষ্য। ইনি একদিকে জুতা তৈরী করে জীবিকা উপার্জন করতেন, আবার অপরদিকে খলিফা মুহতাদী বিল্লাহর জন্য ‘কিতাবুল খারাজ’ বা ‘ইসলামের রাজস্ব-নীতি’ প্রণয়ন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ফেকাহ শাস্ত্রের ওপর নিজের মূল্যবান গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করতেন। কাফ্ফালের হাতে তালা বানানোর দাগ পরিদৃষ্ট হতো, ইবনে কাত্তান্দুবাগা দর্জ্জীগিরী করতেন, খ্যাতনামা ইমাম জাসসাস ছিলেন কাঁচপাত্র র্নিমাতা। এমনিভাবে ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দিতে আমাদের সামনে আসেন পিতলের পাত্র বিক্রেতা (সাফ্ফার), আতর বিক্রেতা (সায়দালানী), হালুয়া বিক্রেতার পুত্র (হালওয়ারী), আটা বিক্রেতা (দাক্কাক), সাবান বিক্রেতা (সাজুনী), জুতা প্রস্তুতকারী (নায়ালী), তরকারী বিক্রেতা (বাক্কালী) এবং হাড়ী বিক্রেতা (কুদূরী) প্রমুখ।
ইসলামী সভ্যতার প্রাতঃকালেই অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানরা যা করে দেখান, বহু শতাব্দীব্যাপী চেষ্টা করেও পাশ্চাত্য জগত তা করতে পারেনি- অর্থাৎ কিনা কোন পেশাই মূলতঃ নীচ কিংবা সম্ভ্রান্ত নয়, আসলে মানুষই উচ্চতর গুণাবলীর অধিকারী হয় অথবা তা থেকে বঞ্চিত হয়। (আবু হানিফাঃ জুন্দী)
ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা
মানবিক সাম্যের এই সু-উচ্চ মর্যাদার পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব হবে না যতক্ষন আমরা উচ্চ পদস্থ লোকদের ব্যাপারে ইসলামী সমাজের নীতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ওয়াকিফহাল না হবো। বড়রা যখন ছোটদের সাথে এক সারিতে দাঁড়াবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের একমাত্র ভিত্তি হবে- বংশ-মর্যাদা, পদ-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ নয় বরং চরিত্র- কেবলমাত্র তখনি প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কেবলমাত্র ছোটদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।
ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) তদীয় ‘কিতাবুল খারাজে’ লিখেছেনঃ ‘একবার হযরত ওমর (রাঃ) তার কর্মচারীদের হজ্জের সময় তার সাথে সাক্ষাত করার নির্দেশ পাঠান। যথাসময়ে তারা উপস্থিত হলে হযরত ওমর (রাঃ) তাদের ও সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেনঃ
“ভাইসব! সততার সাথে তোমাদের তত্ত্বাবধান ও সেবার জন্যই আমি এসব কর্মচারী নিয়োগ করেছি। তোমাদের জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য আমি এদেরকে নিযুক্ত করিনি। সুতরাং কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে তোমাদের কারো কোন অভিযোগ থাকলে তার দাঁড়িয়ে সে কথা বলা উচিত। সেদিন মাত্র এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, “আমিরুল মুমেনীন! আপনার অমুক কর্মচারী আমাকে অন্যায়ভাবে একশো কোড়া মেরেছে”।
হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমিও কি তাকে প্রহার করতে চাও? এস, প্রতিশোধ গ্রহণ কর”। তখন আমর ইবনুল আস দাঁড়িয়ে বললেন, “আমিরুল মুমেনীন! আপনি কর্মচারীদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা শুরু করলে তা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। এটা একটা স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনার পরবর্তী লোকেরাও তদনুসারে কাজ করবে”।
হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ “তাই বলে কি আমি এই ব্যক্তিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না? অথচ আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নিজের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখেছি। (লোকটিকে লক্ষ্য করে) এস, প্রতিশোধ গ্রহণ কর”। আমর ইবনুল আস বললেন, “আমাদেরকে লোকটিকে সন্তুষ্ট করার সুযোগ দিন”।
হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি দিলেন। তখন তারা লোকটিকে দু’শো দিনার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। প্রতিটি কোড়ার বিনিময়ে দুই দিনার দিতে হলো। আমর ইবনুল আস অন্য কর্মচারীর ওপর থেকে বিপদ অপসারণ করলেন সত্য, কিন্তু স্বয়ং তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে যখন জনৈক মিশরীয় ছেলেকে প্রহার করার অভিযোগ এল তখন ওমর (রাঃ) তাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে ছাড়েন এবং আমরকে কোন উচ্চ-বাচ্চ করতে দেননি। প্রতিশোধ গ্রহণ করানোর সময়ে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, “এই বড়লোকের ছেলেকে প্রহার কর”। আমর ইবনুল আসেরও শাস্তি ভোগ করা অবধারিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মিশরীয় লোকটি ক্ষমা করে দেয় এবং প্রহার থেকে বিরত থাকে।
আর একদিন হযরত ওমর (রাঃ) বসে মুসলমানদের মধ্যে কিছু অর্থ বন্টন করছিলেন। সমবেত লোকদের ভীড় প্রবল হয়ে ওঠে। সা’দ ইবনে আবি আক্কাস সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং অন্যান্য লোককে ঠেলে হযরত ওমরের নিকট পৌঁছে যান। এই সাহাবী বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের সন্তান। হযরত ওমর (রাঃ) এই বলে তাঁকে এক দোররা কষে দিলেন, “তুমি পৃথিবীর ওপরে আল্লাহর হুকুমতের প্রতাপ মান না কিন্তু আল্লাহর হুকুমাতের দৃষ্টিতে যে তোমার প্রভাব প্রতিপত্তির কানা-কড়িও মূল্য নেই তা তোমাকে দেখিয়ে দেয়া আমি প্রয়োজন বোধ করলাম”।
কেউ বলতে পারে যে, তিনিতো ছিলেন খলিফা। তার সাথে কার তুলনা? এই জন্য আমরা এবার দেখবো যে খলিফা ও বাদশাহদের সামনে তাদের প্রজারা মত প্রকাশ ও সমালোচনার ব্যাপারে কতখানি স্বাধীনচেতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। মতামত প্রকাশে এই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীকতার আসল উৎস হচ্ছে ইসলাম প্রদত্ত বিবেক ও প্রজ্ঞার স্বাধীনতা এবং কথায় ও কাজে বাস্তবায়িত পূর্ণ সাম্য।
খলিফা হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, “যদি তোমরা আমার মধ্যে কোন বক্রতা দেখ তবে আমাকে সোজা করে দিও”। সমবেত মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠেন, “তোমার মধ্যে কোন বক্রতা দেখলে আমরা তোমাকে তীক্ষ্ণধার তরবারী দিয়ে সোজা করে দেব”। একথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, “আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি ওমরের খেলাফতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও সৃষ্টি করেছেন যে তাকে তীক্ষ্ণধার তরবারী দিয়ে সোজা করতে পারে”। একবার মুসলমানরা গণিমতে কতগুলো ইয়ামেনী চাদর লাভ করেন। সকল মুসলমানের মত হযরত ওমরও একটা চাদর পান এবং তার পুত্র আব্দুল্লাহকেও একটা চাদর দেন। যেহেতু খলিফার জামার দরকার ছিল তাই আব্দুল্লাহ নিজের অংশের চাদরটা খলিফাকে দিয়ে দেন যাতে দু’টো মিলে একটা জামা হতে পারে। এ জামা গায়ে দিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) বক্তৃতা দিতে ওঠেন এবং বলেন, “তোমরা আমার কথা শোন এবং মেনে চল”।তৎক্ষনাৎ সালমান উঠে বললেন, “আপনার কথা আর শুনবোও না মানবোও না”। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন?” সালমান বললেন, “আগে আপনি জবাব দিন, এ জামা কি করে তৈরী করলেন? নিশ্চয়ই আপনিও একটা চাদরই পেয়েছেন, আর আপনি খুবই লম্বা মানুষ”। তিনি বললেন, “তাড়াহুড়া করে ফায়সালা করে ফেল না”। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডেকে বললেন, “আমি তোমাকে খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি বল, যে চাদর দিয়ে আমি জামা বানিয়েছি তা তোমার চাদর কি-না? তিনি বললেন, “হ্যাঁ”। তখন সালমান বললেন, “এবার বলুন আপনি, কি হুকুম। আমরা শুনবো এবং মানবোও”।
কেউ বলতে পারে যে, এটা তো ওমরের (রাঃ) ব্যাপার। তার সাথে কার তুলনা?
আবু জাফর মনসুরের উদাহরণ নিন। তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তার আইনের ভিত্তি শরিয়তের ওপর নয় বরং আমাদের পরিভাষা অনুসারে সামাজিক রসম-রেওয়াজ ও রীতি-প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফিয়ান সওরী তার নিকট গিয়ে বলেন, “আমিরুল মুমেনীন! আপনি আল্লাহ ও মুসলমানদের ধন-সম্পদ তাদের ইচ্ছা ও সম্মতি ছাড়াই ব্যয় করছেন। বলুন এর কি জবাব আছে আপনার কাছে?” হযরত ওমর (রাঃ) একবার সরকারী খরচে হজ্জ করেছিলেন, তাতে তার এবং তার সংগী-সাথীদের ওপর সর্বমোট ষোল দিনার ব্যয়িত হয়েছিল। তথাপি ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, আমার মনে হয় আমরা বাইতুল মালের ওপর বিরাট বোঝা চাপিয়েছি। আপনি নিশ্চই জানেন, মনসুর ইবনে আম্মার আমাদেরকে কি হাদীস শুনিয়েছিলেন। কারণ সেই মজলিসে আপনিও ছিলেন এবং সর্বপ্রথম আপনিই হাদীসটা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের সম্পদে নিজের খেয়াল খুশী মত হস্তক্ষেপ করবে তার জন্য দোজখের আগুন অবধারিত রয়েছে”। এতে বাদশাহর ঝানু চাটুকার আবু ওবায়দা নামক কেরানী বলে উঠলো, “কি! আমিরুল মুমেনীনের সাথে এ ধরনের আলাপ!” সুফিয়ান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ হতভাগা! হামান ও ফেরাউন এই ভাবেই চাটুকারীতা করে পরস্পরকে ধ্বংশ করেছিল।” এই বলেই দরকার থেকে নিস্ক্রান্ত হন।
স্বৈরাচারী শাসকদের স্বৈরাচার যতই প্রবল হোক, যার হৃদয় জোর্তিময় ছিল এবং যে বস্তুগত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর বিধানের নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করেছে- তেমন ব্যক্তির ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।
ওয়াসেকও ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। তার কাছে একবার জনৈক মুসলিম দার্শনিক আগমন করেন। তিনি ওয়াসেককে সালাম করেন কিন্তু তার জবাবে ওয়াসেক বলেন- “লা সাল্লামাল্লাহ আলায়কা” (অর্থাৎ আল্লাহ যেন তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত না করেন)”। এ কথা শোনা মাত্রই তিনি ওয়াসেককে ধমক দিয়ে বলেন, “তোমার শিক্ষকরা তোমাকে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ শিখিয়েছে”। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ
“যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম কর অথবা সেটার মতই জবাব দাও”। অথচ তুমি আমাকে উত্তম সালাম করা দূরে থাক সমান সমান জবাবও দাওনি। (আবু হানিফা-জুন্দী)।
বিচারপতি আবু ইউসুফ আদালতের অধিবেশনে বসেছেন। এক ব্যক্তি তার নিকট মোকদ্দমা নিয়ে এলো। আব্বাসী বাদশাহ হাদীর সাথে একটি বাগানের ব্যাপারে তার কোন্দল। আবু ইউসুফ মত পোষণ করেন যে, বাগান ওই লোকটিরই প্রাপ্য। কিন্তু অসুবিধা এই যে, বাদশাহের সাক্ষী ছিল। তিনি বললেন, “বাদী দাবি করছেন যে, বাদশাহর সাক্ষীরা সত্যবাদী এ মর্মে বাদশাহকে শপথ করতে হবে”। হাদী শপথ করাকে নিজের অবমাননা মনে করায় তা অস্বীকার করেন এবং বাগান তার মালিককে ফেরত দেন। অপর একটি মামলায় তিনি হারুনুর রশীদকে শপথমূলক বিবৃতি দিতে বাধ্য করেন। ফজল ইবনুর রবী হারুনুর রশীদের পক্ষে সাক্ষী হয়ে এলে তিনি তার সাক্ষ্য নাকচ করে দেন। খলিফা বিক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, “ফজলের সাক্ষ্য নাকচ হবার কারণ কি?” জবাবে আবু ইউসুফ বলেন, “আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, আমি আপনার গোলাম”। যদি তার কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় আর যদি সে মিথ্যুক হয়ে থাকে তাহলে মিথ্যুকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না”।(আবু হানিফা-জুন্দী)
ইসলাম যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রদীপ মানুষের বিবেক-মনে প্রজ্জ্বলিত করেছিল, তা ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগেও অনির্বাণ ছিল। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে বিবেকের এহেন গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতার প্রচুর উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়।
মিসরে আহমদ ইবনে তুলুন, বাক্কার ইবনে কাতিবা নামক হানাফী কাজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আহমদ তাকে আব্বাসী যুবরাজ মুয়াফ্ফাকের ওপর অভিসম্পাত করার অনুরোধ জানালে তিনি ক্ষণিক থেকে বললেনঃ
----এরাবিক টেকস্ট----
“সাবধান! অত্যাচারীদের ওপর অভিসম্পাত”। এতে এক ব্যক্তি আহমদ ইবনে তুলুনকে বলেন যে, বাক্কার আপনাকে (আহমদকে) লক্ষ্য করেই অভিসম্পাত করেছে। এর ফলে ইবনে তুলুন তাকে প্রদত্ত যাবতীয় উপঢৌকন ফেরত চান। এ জিনিসগুলো তিনি যেরূপ সিলমোহর করা অবস্থায় দিয়েছিলেন সে অবস্থায়ই ফেরত পান। অতঃপর ইবনে তুলুন বাক্কারকে একটি ভাড়াটিয়া ঘরে অন্তরীণ করেন। বহুলোক তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ইবনে তুলুনের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসতো। বাক্কার তাদের সাথে জানালার মধ্য দিয়ে আলাপ করতেন, এরপর ইবনে তুলুন এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যে, তার জীবনের কোন আশাই থাকলো না। তখন তিনি বাক্কারের মুক্তির নির্দেশ দেন। যে দূত মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিল তাকে তিনি বলেছেন, “ইবনে তুলুনকে বল, আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছি আর উনি রোগাক্রান্ত। এখন শীগগীরই আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমাদের মাঝে শুধু আল্লাহ ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন”। ইবনে তুলুন মারা গেলে বাক্কার বলতেন, “আহা! বেচারা মারা গেছে!” (আবু হানিফা-জুন্দী)
এই “বেচারা মারা গেছে!” উক্তিটির মধ্য দিয়ে তার এ অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, ইবনে তুলুন ক্ষমতাসীন ছিল সত্য, কিন্তু সে ছিল তার চেয়ে নীচ এবং অসহায়।
আইয়ুবী শাসনামলে মিশরের বাদশাহ ইসমাইল ক্রুসেড-যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করেন। ইংরেজরা তাকে সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে-এই মর্মে আশ্বাস পেয়ে সায়দাসহ কতিপয় এলাকা তিনি ইংরেজদের নিকট হস্তান্তর করেন।কিন্তু আজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুল সালাম এর কঠোর প্রতিবাদ জানালে বাদশাহ রুষ্ট হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর তিনি দূত পাঠিয়ে আজ্জুদ্দীনকে ভীতি ও লোভে প্রদর্শন করেন। দূত তাকে বলে, “আপনি বাদশাহর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করলে আপনাকে সাবেক পদে বহাল করা হবে এবং আপনার আরো পদোন্নতি হবে”। আজ্জুদ্দীন জবাব দেন, “খোদার শপথ! বাদশাহ এসে আমার হাত চুম্বন করুক-তাও আমি বরদাশত করবো না। আসলে তোমরা এক জগতের লোক আর আমি অন্য জগতের লোক”। (আবু হানিফা-আব্দুল হালিম জুন্দী)
জাহির বেবরিসের শাসনামলে শেষ মহিউদ্দিন নবভী দামেস্ক অবস্থান করতেন। তিনি জাহিরকে প্রায়ই সদুপদেশ দিতেন। তিনি কখনো চিঠি দ্বারা কখনো মৌখিক উপদেশ দিতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী তার প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘হুনসুল মহাজারা’তে বাদশাহর নিকট লিখিত তার বহু চিঠি উদ্বৃত করেছেন।এর অধিকাংশ চিঠিতে জনগনের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে কর মওকুফ করার দাবি জানানো হয়েছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “এ বছর যথোপযুক্ত বৃষ্টি হয়নি। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য দ্রব্যের তীব্র অভাব, গবাদি পশুর মড়ক প্রভৃতি কারণে সিরিয়াবাসীরা শোচনীয় অবস্থায় পতিত। এমতাবস্থায় দরিদ্র জনগনের ওপর আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শণ করা উচিত। আপনার এবং জনগনের কল্যাণের জন্যই এ কথা বলা। কেননা কল্যাণ কামনাই হচ্ছে ইসলামের মূল কথা”।
বাদশাহ এ উপদেশ শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, অধিকন্তু তার প্রতি আলেম সমাজের অসহযোগীতায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, “তাতারীরা যখন দেশের ওপর হামলা করে লুটতরাজ চালাচ্ছিল-তখন এই হুজুররা কোথায় ছিলেন?” শেখ মহিউদ্দীন তার এ টিটকারীর কঠোর জবাব দিয়েছিলেন। তিনি নিজের মতামত এবং পূর্বোক্ত উপদেশের পূনরাবৃত্তি করে বলেন, “অমুসলিম হানাদারদের ব্যাপার আর দেশের মুসলিম শাসকদের ব্যাপার সমান হতে পারে না। সেই বিদ্রোহী কাফেররা যখন আমাদের দ্বীনের ওপর বিন্দুমাত্র ঈমান রাখতো না- তখন তাদেরকে আমরা কি উপদেশ দিতে পারতাম এবং তাতে কি লাভ হতো? আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাকে সত্য কথা বলা এবং সদুপদেশ দেয়া থেকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এটা আমার এবং আমার মত অন্যান্যদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে বিপদেরই সম্মুখীন হতে হোক না কেন, সেটা আল্লাহর নিকট মহাকল্যাণের কারণ এবং মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। আমি পুরোপুরিভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি। আল্লাহ তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে সত্য কথা বলা সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখতে এবং এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদ গ্রাহ্য না করতে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা বাদশাহকে সর্বাবস্থায় ভালবাসি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার কল্যাণ কামনা করি”।
শেখ সাহেব এমনি হীত কামনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখতে থাকেন। কিন্তু জাহির তার উপদেশ কর্ণপাত না করে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির অজুহাতে কর আদায় করা অব্যাহত রাখেন। বাদশাহ নিজের মতামতের পক্ষে আলেমদের ফতোয়া জমা করে রেখেছিলেন। এই সব আলেম তার নির্দেশ অনুসারে ফতোয়া দিয়েছিল। তিনি শেখকে ডেকে অন্যান্য আলেমদের ফতোয়ায় স্বাক্ষর দিতে বলেন। শেখ এতে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, “আমি জানি, তুমি কয়েদী ক্রীতদাস ছিলে। তুমি ছিলে দেউলে। এরপর আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং তোমাকে বাদশাহর মর্যাদায় উন্নীত করেন। আমি জানি, তোমার কাছে জরিদার কাপড় পরিহিত এক হাজার ক্রীতদাস এবং আপদমস্তক স্বর্ণালংকারে মন্ডিত একশো দাসী আছে। এখন তুমি যদি ক্রীতদাসের এই জরিদার কাপড়গুলো এবং দাসীদের অলংকারগুলো খরচ করে দাও তাহলে আমি ফতোয়া দেব যে, তোমার জন্য প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করা বৈধ”।
জাহির একথা শুনে প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং তাকে তৎক্ষনাৎ দামেস্ক থেকে বহিস্কার করেন। শেখ সিরিয়ার নাভা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। পরে সমস্ত আলেমগণ ও ফকীহগণ বাদশাহকে বলেন যে, “ইনি আমাদের সর্বজনমান্য ও সবার সেরা আলেম। তাকে দামেস্কে ফিরিয়ে আনুন”। এতে বাদশাহ তাকে দামেস্কে ফিরে আসার অনুমতি দেন, কিন্তু শেখ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “যতদিন জাহির ওখানে থাকবে ততদিন আমি আসবো না”। এর একমাস পর জাহির মৃত্যুমুখে পতিত হন। (অধ্যাপক আবু জুহরা কৃত ‘ইবনে তাইমিয়া’ থেকে)।
সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসেও এ ধরনের মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমি শুধু দু’টো ঘটনার উল্লেখ করবো।
ইসমাইলের শাসনামলে একবার সুলতান আব্দুল আজীজ মিসরে আগমন করেন। ইসমাইল তার আগমনের প্রতীক্ষার দিন গুনছিলেন, কারণ তার খদেভ উপাধি লাভের ব্যাপারে তার আগমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তা ছাড়া সুলতানের সফরের ফলে মিসরের বহু রাজনৈতিক সুবিধাদি পাওয়ার বহু সম্ভাবনা ছিল। এই সময়ে সুলতান কর্তৃক আলেমদের সাক্ষাত দানে এক কর্মসূচী তৈরী
করা হয়। এই সাক্ষাত দানের অনুষ্ঠানে বহু ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ পালিত হয়। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, আগমনকারীর নতজানু হয়ে ভূমির সাথে মাথা ঠুকে তুর্কী কায়দায় কুর্ণিশ করতে হতো। রাজ প্রাসাদের ব্যবস্থাপকদের ওপর আগত আলেমদেরকে এ সব রসম-রেওয়াজের অনুশীলন দানের দায়িত্ব ছিল, পাছে তারা সুলতানের সামনে ভুল না করে বসেন।
অতঃপর সাক্ষাত অনুষ্ঠান সময় ঘনিয়ে এল, আলেমগণ একে একে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং নিছক পার্থিব স্বার্থের লোভে নিজেরই মত সৃষ্ট জীবের সামনে কুর্ণিশ করে যেতে লাগলেন। তারপর শিখানো পদ্ধতিতে সুলতানের দিকে মুখ করে পেছনের দিকে অগ্রসর হতে হতে বেরিয়ে এলেন। এই ঘৃণ্য কাজ থেকে মাত্র একজন আলেম রক্ষা পেলেন। তিনি হচ্ছেন শেখ হাসানুল আদাদী। তিনি তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেন এবং আল্লাহর হাতে সমস্ত শক্তি নিহিত এই অনুভূতি জাগ্রত রাখেন। তিনি স্বাধীন মানুষের মত মাথা উচু করে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সুলতানের সামনে এসে ইসলামী রীতি অনুসারে “আসসালামু আলাইকুম” বলে সালাম করেন। অতঃপর (শাসকের সাথে সাক্ষাত করার সময় কোন আলেমের যেমন করা উচিত) তিনি তাকে আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের সাথে সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দেন। তারপর কথা শেষ করে আবার সালাম করেন এবং নির্ভীক স্বাধীন মানুষের মত আবার মাথা উচু করে বাইরে চলে যান।
এসব দেখে দরবারের ব্যবস্থাপক এবং স্বয়ং খদেভের চেতনা বিলোপের উপক্রম হলো। তারা ভাবলেন পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে এবং সুলতানের বোধহয় ক্রোধের কোন সীমা থাকবেনা। তাদের সযত্ন অনুশীলন ব্যর্থ হওয়ায় তারা হতাশায় ভেংগে পড়লো।
কিন্তু সত্য কথার প্রভাব কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। ওটা যে শক্তি ও প্রতাপ নিয়ে মন থেকে বেরিয়ে আসে সেই শক্তি ও প্রতাপ নিয়ে অন্যান্যদের মনে উপ্ত হয়। এখানেও তাই হলো। সুলতান বে-ইখতিয়ার বলে ফেললেন যে, তোমাদের এখানে শুধু এই একজনই আলেম রয়েছে। সুলতান শুধু তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং অন্য সবাইকে বঞ্চিত রাখলেন।
দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে খদেভ তওফিক পাশা ও শেখ হাসানুওভীলের মাঝে ‘দারুল উলুমে’।
শেখ হাসানুওভীল ছিলেন দারুল উলুমের অধ্যাপক। তিনি সস্তা মূল্যের মামলী ধরণের জামা (জালবাব) পরিধান করতেন। একদিন দারুল উলুমের অধ্যক্ষ জানতে পারলেন যে, খাদেভ শীগ্গিরই মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে আসবেন। তিনি তৎক্ষনাৎ মাদ্রসা পরিস্কার করা ও সাজ শয্যা শুরু করে দিলেন। শেখ হাসানুওভীলকে পোষাক পরিবর্তন করে কাফতান ও জুব্বা (অপেক্ষাকৃত অভিজাত পোষাক) পরিধান করে আসতে বলা হলো। শেখ ইঙ্গিতে এ অনুরোধ মেনে নিলেন।
নির্ধারিত দিনে শেখ তার পুরনো পোষাক পরিধান করেই এলেন। তবে তার হাতে একটা রুমালে একটা কিছু পুটুলির মত বাধা ছিল। তাকে পুরনো পোষাকে দেখে অধ্যক্ষের মুখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। খানিকটা ক্রোধমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “শেখ! জুব্বা ও কাফতান কোথায়? তিনি রুমালের দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে দিলেন যে এখানে আছে। অধ্যক্ষ ভাবলেন যে মেহমানের আগমন আসন্ন হলেই হয়তো উনি পোষাক পরিবর্তন করে নেবে।
কিছুক্ষণ পর প্রতিক্ষিত মেহমান এলেন। সমগ্র মাদ্রাসায় একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। এর পরক্ষণেই এক অপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হলো। শেখ হাসানুওভীল হাতের পুটুলীটি নিয়ে খদেভের সামনে হাজির হলেন এবং সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে বলেলেন, “ আমাকে লোকেরা বলেছে যে আমাকে অবশ্যই জুব্বা ও কাফতান পরে আসতে হবে। যদি আপনার জুব্বা-কাফতানই চাই তাহলে এই রইলো জুব্বা-কাফতান, আর যদি আপনার হাসানুওভীলকে চাই তাহলে এই যে, হাসানুওভীল উপস্থিত”।
স্বাভাবিকভাবেই খদেভ জবাব দিলেন যে, তার হাসানুওভীলকে চাই।
এ হচ্ছে মুমিনদের প্রকৃত অবস্থা। তাদের ইসলামের সম্মান ছাড়া অন্য কোন সম্মানের আকাংখা থাকে না। তাদের মন-মানস ও বিবেক তুচ্ছ ও অসার মূল্যবোধ এবং ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে এবং তাকে পুরোপুরিভাবে জীবনে কার্যকরী করে। তারা ইসলামের দুর্জয় প্রাণশক্তি অর্জন করার পর কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন বোধ করে না। বস্তুতঃ এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম।
বিজিত দেশসমূহের সাথে ব্যবহার
বিজিত দেশসমূহের অধিবাসী এবং মুসলিম দেশসমূহের অমুসলিম জাতি সমূহের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, এবার আমরা সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করবো। কারণ সাম্য, সুবিচার ও বিবেকের স্বাধীনতার সাথে এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম প্রবর্তিত এই সাম্য ও সুবিচার ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও ইসলামের পরিধি ছাড়িয়ে সমগ্র মানবতার সাথে যুক্ত হয়েছে।
বিজিত দেশসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেশ জয়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যকারণের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই এসে পড়ে। এটা একটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আমরা এ সম্পর্কে শুধু যতটুকু অপরিহার্য এবং ইসলামের বিশ্বজনীন সামাজিক ন্যায়-নীতির সাথে সম্পৃক্ত ততটুকুই আলোচনা করবো।
ইসলামী দাওয়াত মানুষের বিবেক ও মন-মগজকে আবেদন জানায়। এতে বল প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতার অবকাশ নেই। এমনকি পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে অলৌকিক ঘটনাবলীর আকারে যে মনস্তাত্মিক বল প্রয়োগ প্রচলিত ছিল ইসলাম তাকেও প্রশ্রয় দেয়নি। ইসলামই একমাত্র বিধান, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে, তাকে অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজার মাধ্যমে সম্মোহিত করা এবং মনস্তাত্মিক উপায়ে প্রলুব্ধ করার পরিবর্তে তাকে সাদাসিদে ভাষায় সম্বোধন করে ক্ষান্ত হয়েছে। তরবারীর শক্তি দ্বারা মানতে বাধ্য করার পন্থা সে কখনো অবলম্বন করেনি।
------------এরাবিক টেক্সট------
“জীবন বিধানের ব্যাপারে বল প্রয়োগের অবকাশ নেই”।
------------এরাবিক টেক্সট------
“সদুপদেশ ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথে আহবান জানাও আর উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর”।
কিন্তু কোরাইশরা প্রথম দিন থেকেই বস্তুগত শক্তি দ্বারা এই নতুন জীবন বিধানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আল্লাহতায়ালা যাকেই ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, তার ওপর তার অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। কিছু সংখ্যক মুসলমানকে তারা তাদের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তাদেরকে পর্বতের গুহায় আটক রেখে সামাজিক ‘বয়কট’ করে অনাহারে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। মোট কথা, মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য বস্তুগত শক্তি ব্যবহারের কোনো পন্থাই তারা বাদ রাখেনি।
এমতাবস্তায় ইসলামের অনুসারীদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না-
------------এরাবিক টেক্সট------
“যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে অস্ত্র ধারনের অনুমতি দেয়া গেল। কেননা তার মজলুম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম”।
------------এরাবিক টেক্সট------
“যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অবশ্য বাড়াবাড়ি করো না। কারণ সেটা আল্লাহ পছন্দ করেন না”।
এরপর এক সময়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। দেশ জয়ের ধারাবাহিকতা আরবের বাইরে পদার্পণ করে। প্রশ্ন জাগে যে, এই দেশ জয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল?
আগেই বলেছি, ইসলাম আপনাকে একটা আন্তর্জাতিক মতাদর্শ ও বিশ্বজনীন জীবন বিধান পেশ করেছে। সে নিজেকে কোন বিশেষ উদ্দীপনার চতুর্সীমায় আবদ্ধ করতে পারে না। নিজের কল্যাণ ধারাকে সে বিশ্বের প্রতিটি কোণে এবং সমগ্র মানব জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দিতে চায়। কিন্তু পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় রোম ও পারস্যের দুই বিশাল সাম্রাজ্য। তারা তাকে ধ্বংস করার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে। এই শক্তি ইসলামী আন্দোলনের নিশানবাহীদেরকে পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে লোকদের নিকট ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। এমতাবস্থায় খোদায়ী বিধান ও সাধারণ মানুষের মাঝে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা অপসারণ করা ছাড়া ইসলামের গত্যন্তর ছিল না। এই বাধা অপসারনের পর সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা এবং মানুষের আনুগত্য ও গোলামী থেকে মুক্ত হবার সুযোগ দেয়। বাতিল ব্যবস্থার স্থলে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হবার এ হচ্ছে মর্মার্থ। এতে মানুষ অবাধ বাক-স্বাধীনতা লাভ করে। রাষ্ট্রীয় শক্তির বাধা অপসারিত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানের বিজয়ের পর আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে। এরপর যার ইচ্ছা হবে স্বেচ্ছায়-সানন্দে ও পূর্ণ অধিকার নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা হবে না- গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব নীতি নিজেরই নির্ধারণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কোরআনের নিম্নোক্ত ঘোষনায় দ্বীন বা আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার এটাই মর্মার্থ-
------------এরাবিক টেক্সট------
“এই কাফেরদের সাথে সংগ্রাম কর যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্য পুরোপুরিভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে না যায়”। এখানে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ মানুষের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধীন হবে। অতঃপর কোন বাধা বিপত্তি ও জোর-জবরদস্তি ছাড়াই নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস নিজেরাই নির্বাচন করে নেবে।
এই ব্যাখ্যার আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ইসলামের দেশ জয়মূলক ঘটনাবলী শক্তিমদমত্ত জাতি সমূহের শোষণ-নিষ্পেষণের উদ্দেশ্য বিজাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এ যুদ্ধসমূহের তাৎপর্য শুধু এই যে, এগুলো ছিল ইসলামের আনীত নতুন আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের মধ্যে ও অন্য জাতিগুলোর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রীয় শক্তি অপসারনের সংগ্রাম। এটা জাতিগুলোর জন্য ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, আর তাদের ওপর বস্তুগত শক্তির সাহায্যে খোদা হয়ে সওয়ার থাকা রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বন্তুগত ও সশস্ত্র সংগ্রাম।
ইসলাম নিজেকে গোটা মানব জাতির বিধান মনে করে এবং নিজের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে বস্তুগত শক্তি প্রয়োগ করে না। নিজের এই মূলনীতি অনুসারে সে বিশ্বের সমস্ত জাতির সামনে তিনটে পথ রেখেছে। প্রত্যেক জাতিকে তার একটা না একটা গ্রহণ করতে হবে- ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া দেয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা ও আনুগত্য প্রকাশ অথবা যুদ্ধ।
বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্য তার “ইসলাম গ্রহণের” আহ্বান নিঃসন্দেহে ন্যায় সংগত। কারণ এটাই হল একমাত্র হেদায়েতের পথ। এটা খোদা, মানুষ, জীবন ও জগত সম্পর্কে সর্বাধুনিক ও পরিপূর্ণতম মতবাদ। এটা সেই সিংহদ্বার- যেখান দিয়ে প্রবেশ করার পর একজন অমুসলিম সমস্ত মুসলিমানের ভাই হয়ে যায়, মুসলমানদের মতই তার অধিকার এবং মুসলমানদের মতই তার কর্তব্য স্থির হয়। বর্ণে, বংশে, ধনে, মানে- কোন দিক দিয়ে অন্য কোন মুসলমান এই নতুন মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না।
জিজিয়ার আহ্বানও অনুরূপ। দেশ রক্ষার জন্য মুসলমানদের জান পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা যাকাতও দেয়। একজন অমুসলিমও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক এবং অন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা উপভোগ করার ব্যাপারে সে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য সকলের সাথে সমান অংশীদার। বার্ধক্যে কিংবা অক্ষমতায় সে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুবিধাও উপভোগ করতে পারে। এমতাবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির দাবী এই যে, এ সব কাজে তারও নিজ অর্থ দ্বারা শরীক হওয়া উচিত। যাকাতে যেহেতু আর্থিক করের চেয়ে ইবাদতের বৈশিষ্ট্যই অধিকতর বিরাজমান, তাই ইসলাম তাদেরকে এই ইবাদাত পালনে বাধ্য করে না। কেননা ইসলামকে যারা গ্রহণ করেনি তাদের আবেগ অনুভূতিকেও ইসলাম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্য সে তাদের নিকট থেকে যাকাতের পরিবর্তে জিজিয়ার আকারে কর আদায় করে। জিজিয়া ধার্য করার সময় এ কথা লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন হলে সেটা শুধু মুসলমানরাই করে থাকে। এছাড়া জিজিয়া আনুগত্য ও আত্মসমর্পনেরও নিদর্শন। এ থেকে বোঝা যায় যে, জিজিয়া দানকারীরা শক্তির মাধ্যমে ইসলামের পথে বাধার সৃষ্টি করবে না এবং জনগণের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেয়ার পথে কেউ অন্তরায় হবে না। এটাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য।
সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ। ইসলাম এবং জিজিয়া- এ দুটোই প্রত্যাখ্যান করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে (অর্থাৎ অমুসলিম) ইসলাম ও সাধারণ মানুষের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে প্রদর্শিত এ স্পর্ধাকে মুক্তি দিয়েই খতম করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা এ ছাড়া এর আর কোন ওষুধ নেই।
ইসলাম বিজিত দেশগুলোতে নিজের মানবিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচীকে যথাযথরূপে বাস্তবায়িত করেছে। ইসলাম গ্রহণ করলে সে সেই অধিবাসীদেরকে সকল ব্যাপারে মুসলমানদের সমান অধিকার দিয়েছে। জিজিয়া দিলেও তাদেরকে সব উচ্চতর মানবাধিকারে সমৃদ্ধ করেছে। এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও সে তাদের সাথে ব্যবহারে ইনসাফ ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
কোন বিজিত দেশের শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম যথারীতি তাদেরকে সেখানকার শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রেখেছে। পারস্য বংশোদ্ভূত ‘বাজান’ কে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখেন। এমনিভাবে সানার শাসনকর্তা পারসিক ফিরোজকে তার পদে নিয়োজিত রাখেন। আরব বংশোদ্ভূত কায়েস ইবনে আবদে ইয়াগুস যখন ফিরোজকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে তখন আবু বকর (রাঃ) আরবী মুসলমানের বিরুদ্ধে পারসিক মুসলমানের সাহায্য করেন এবং তাকে পুনরায় সেখানে এনে পূর্বপদে বহাল করেন। এমনিভাবে মুসলমানরা অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে এবং আমীরের নিম্নপদস্থ অমুসলিম কর্মকর্তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখেন।
যারা ইসলামও গ্রহণ করে না- এবং জিজিয়াও দিতে স্বীকৃত হয় না বরং যুদ্ধের পথ বেছে নেয়- সেই সব বিদ্রোহীর যাবতীয় ধনসম্পদ বিজেতা কর্তৃক করায়ত্ব করা ইসলামী আইন অনুসারে সম্পূর্ণ বৈধ। এ সত্ত্বেও হযরত ওমরের (রাঃ) যুগে যখন পারস্য বিজিত হয়, তখন তিনি ইসলামের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের দাবিতে অন্য এক নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ভূমির ওপর যথারীতি ভূমি মালিকদের স্বত্বাধিকার স্বীকার করেন, তবে তার ওপর খাজনা ধার্য করেন। তিনি একাধারে দুটো স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। একটি হলো স্বয়ং বিজিত দেশগুলোর স্বার্থ, যদিও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল; তথাপি তিনি তাদের জীবিকার উপায় হরণ করতে চাননি। দ্বিতীয় স্বার্থ ছিল মুসলমানদের পরবর্তী বংশধরদের। সমস্ত ভূমি বর্তমান বিজেতাদেরকে দিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ বংশধররা তার ফল থেকে বঞ্চিত হতো।তাই তিনি মনে করলেন ভুমি থেকে খাজনা গ্রহণ করার পন্থাই উত্তম। এতে করে লব্ধ অর্থ সব সময় জনকল্যাণে ব্যয় করা যাবে এবং ভবিষ্যতের বংশধররাও তা থেকে যুক্তিসঙ্গত অংশ পেতে থাকবে।
এটা একটা সর্ববাদী সম্মত সত্য কথা যে, বিজিত দেশগুলোর সাথে ইসলাম সর্বদা অতি উন্নতমানের মানবিক আচরণ করেছে। মানুষকে সে তার সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকর গুণাবলী দ্বারা উপকৃত হওয়ার অবাধ ও শর্তহীন সুযোগ দিয়েছে। অধিকন্তু এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য সে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বানও জানিয়েছে। প্রত্যেককে সমাজ কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার সুযোগ দিয়েছে। ইসলামের একটা বিশেষ বিভাগে অর্থাৎ আইন ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিজিত দেশের অধিবাসীরা ও দাস শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল। গণজীবনের কোন একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগেও আরবদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল না। এমনকি আমীর ও শাসনকর্তার পদেও এমন সব লোক নিযুক্ত করা হতো, যারা সংশ্লিষ্ট দেশের অতিরিক্ত রাজস্ব প্রথমে সে দেশের কল্যাণ খাতে ব্যয় করতো এবং এর শুধু অবশিষ্টাংশই কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা করতো। বিজিত দেশগুলো উপনিবেশের পর্যায়ভুক্ত ছিল না এবং বিজেতাদের জন্য দেশবাসীর জানমাল নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যাবহার করার অবকাশও ছিল না। ঠিক অনুরূপ ভাবে ইসলাম বিজিত দেশগুলোর অধিবাসীদেরকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের অতুলনীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। তাদের ইবাদতখানা, খানকা, গির্জা এবং আলেমদের ও ধর্মযাজকদের সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলাম স্ব-হস্তে গ্রহণ করেছে। সে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিগুলো এমন সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে যার কোন নজির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ইতিহাসে মেলা দুষ্কর। আজও এ ব্যাপারে ইসলামের প্রবর্তিত রীতিই বহাল রয়েছে।
আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা হতভাগ্য উপনিবেশগুলোর সাথে যে ব্যাবহার করে, তার সাথে যখন আমরা ইসলামের তুলনা করি, তখন ইসলামকে তার ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে পবিত্র আদর্শ হিসেবে উজ্জ্বল ও ভাস্বর দেখতে পাই। আজ আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ বৈশিষ্ট্য থেকে ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যাতে যত দীর্ঘদিন সম্ভব তাদেরকে দুধের গাভীর মত দোহন করা যেতে পারে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে মানবীয় মান-সম্মান ও ভদ্র রীতি-নীতিকে জলাঞ্জলি দেয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে নৈতিক নৈরাজ্য বিস্তার করা, গোষ্ঠীগত ও দলগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ও তা সম্প্রসারিত করা এবং অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন চালানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
পাশ্চাত্যবাসীরা আজ ধর্মীয় স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়ান বটে কিন্তু তাদের পূর্বতন ইতিহাস স্পেনের তথাকথিত আদালতগুলোর পাশবিক শাস্তি এবং প্রাচ্যে ক্রুসেড যুদ্ধের নৃশংসতা দ্বারা কলংকিত। আজও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিছক একটি প্রদর্শনী মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ সুদানে খ্রিস্টান মিশনারীদের সকল সুযোগ সুবিধা থাকলেও মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গত মহাযুদ্ধে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি এ্যালেন বী (Allen by) বায়তুল মুক্ককাদাসে প্রবেশ করার সময়ে ইউরোপের প্রতিটি মানুষের মানসিকতার রূপ এই বলে তুলে ধরেন যে “প্রকৃতপক্ষে ‘ক্রুসেড যুদ্ধ’ আজ শেষ হল।” ফরাসি জেনারেল কাট্টো ১৯৪০ শালে দামেস্কে বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর সেখানে দাঁড়িয়ে বলেন, “আমরা ক্রুসেড যোদ্ধাদের বংশধর। আমাদের সরকার যাদের পছন্দ না হয়, তারা এখান থেকে চলে যেতে পারে।” ঠিক এই ধরনেরই কথা তার এক সম-মতাবলম্বী ১৯৪৫ সালে আলজিরিয়াতে বলেছিলেন।
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবস্থা আরও সাংঘাতিক। সেখানে মুসলমানদেরকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চলছে। মাত্র সিকি শতাব্দীতে রাশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা চার কোটি দু’লাখ থেকে কমে দু’কোটি ছ’লাখে এসে দাঁড়িয়েছে। যে রেশন কার্ড ছাড়া সেখানে জীবনযাপনের উপায় উপকরণ মেলা সম্ভব নয় তা থেকেও আজকাল মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের বলা হয়, “তোমাদের যখন খুশি নামাজ পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সরকার তোমাদেরকে খাদ্য দিতে পারবে না। তোমরা তোমাদের খোদার কাছে খাদ্য চাও।” এমনি ব্যবহার তাদের সাথে যুগোস্লাভিয়া এবং অন্যান্য দেশেও করা হয়।
ইসলাম চিরদিনই সর্বাত্মক ও সার্বজনীন সামাজিক সুবিচারের এমন উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে- যার ধারে কাছেও ইউরোপীয় সভ্যতা যেতে পারেনি। আর কোনদিন পারবেও না, কেননা ওটা হচ্ছে নিছক জড়বাদী ও বস্তুবাদী সভ্যতা। নরহত্যা, লুটতারাজ, রক্তপাত, হিংস্রতা ও নৃশংসতার ওপরই ওর ভিত্তি প্রথিষ্ঠিত। [এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থকারের “আসসালামুল আলমী আল-ইসলাম (বিশ্বশান্তি ও ইসলাম) এবং “দিরাসাতুন ইসলামিয়া’র ‘ইসলামের দেশ জয়ের প্রকৃতি ও তাৎপর্য’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]
পারষ্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
সবল ও দুর্বল, ধনী ও নির্ধন, ব্যক্তি ও সমাজ, শাসক ও শাসিত এবং এমনিভাবে সকল মানব মণ্ডলীর মধ্যে দয়া, সহানুভূতি, হীতকামনা ও পারষ্পরিক সহযোগিতার যে গুণাবলী ইসলামের কাম্য সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকে কতিপয় বাস্তব উদাহরন পেশ করবো। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ মালায় পরিপূর্ণ।
ইসলাম গ্রহণের সময় আবু বকর (রাঃ) এর নিকট ব্যবসায়ের মুনাফালব্ধ চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ব্যাবসা করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু যেদিন তার মহান বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ সাঃ এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন সেদিন তার এত পুঁজির মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। নিজের অবশিষ্ট সমস্ত পুঁজি তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলিম গোলামদের স্বাধীন করার জন্য ব্যয় করেন, এ সম্পদ থেকে তিনি দরিদ্র সর্বহারাদেরকে সাহায্য করতেন।
হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। খয়বরে তিনি এক টুকরো ভূমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট এসে বলেন, “আমি খয়বরে খানিকটা জমি পেয়েছি। এত মূল্যবান সম্পত্তি আমি কোন দিন পাইনি। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন “যদি তোমার মনে চায় তবে আসল জমি নিজের অধিকারে রেখে তার লভ্যাংশ দান করে দিও।”
হযরত ওমর (রাঃ) সেটা গরিব-দুঃখী, অভাবী আত্নীয়-স্বজনের জন্য, গোলামদেরকে স্বাধীন করার জন্য এবং দুর্বল-অক্ষম লোকদের সাহায্যে ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এভাবে তিনি নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে দান করে কোরআনের এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করেনঃ
------------এরাবিক টেক্সট------
“তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হবে না।”
খেলাফতের পূর্বে হযরত ওসমানের নিকট সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য বহর আসে। এই বহরে গম,জয়তুনের তেল ও মোনাক্কাবাহী এক হাজার উট ছিল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষের দরুন মুসলমানগণ শোচনীয় দুর্দশায় পতিত ছিলেন। বহু ব্যবসায়ী তার কাছে এসে বলে, “দেশে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা কত তীব্র তাতো আপনি ভাল করেই জানেন। এই দ্রব্য সম্ভার আমাদের নিকট বিক্রি করে দিন।” হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, “স্বাচ্ছন্দে বিক্রি করতে পারি কিন্তু আমাকে কত মুনাফা দেবে তাই বল।” ব্যাবসায়ীরা বললো, “দ্বিগুণ মূল্য দেব।” হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, “আমাকে তো এর চেয়ে অনেক বেশী মুনাফা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।” তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার বাণিজ্য বহর এইমাত্র এলো, আর ওটা পৌঁছানো মাত্রই আমরা মদিনার সমস্ত ব্যাবসায়ী হাজির হয়েছি। অন্য কেউ তো আপনার সাথে আমাদের পূর্বে সাক্ষাত করেনি। তা হলে কোন ব্যক্তি আপনাকে এত মুনাফা দিতে চেয়েছে?” হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, “আল্লাহ তায়ালা আমাকে দশগুণ মুনাফা দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তোমরা কি আমাকে এর চেয়ে বেশী দিতে পার?” তারা বললো, “না”। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) আল্লাহকে সাক্ষী করে ঘোষণা করলেন যে, “এই বাণিজ্যে বহরের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্য দরিদ্র ও মিসকিনদের জন্য সদ্কা করে দিলাম।”
হযরত আলীর (রাঃ) পরিবারে একদিন মাত্র তিনটে জবের রুটি ছিল। এই রুটি কয়টি তিনি একজন ইয়াতিম, একজন মিসকিন, ও একজন কয়েদীকে দান করে দিলেন। তিনি তাদেরকে তৃপ্তির সাথে খাইয়ে নিজে সপরিবারে অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রা গেলেন।
হরত হোসাইনের ওপর ঋণের ছাপ বেড়ে গেছে। আবি নাইজারের নির্ঝরিণী তার মালিকাধিন, ইচ্ছা করলে সেটা বিক্রি করে তিনি ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু গরীব মুসলমানরা তা থেকে সেচ কার্য সম্পন্ন করে, সে জন্য তিনি তা বিক্রী করলেন না। অথচ বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠ পরিবারের সন্তান হয়ে ঋণের বোঝা বয়ে বেরাতে লাগলেন।
মদিনায় আনসাররা মুহাজেরদেরকে নিজ নিজ সম্পত্তি, ঘরবাড়ী সকল জিনিসেরই অংশীদার করেন। তাদেরকে নিজেদের ভাই বলে গ্রহণ করেন। তাদের পক্ষ থেকে দিয়াত(অনিচ্ছাকৃত হত্যা বা জখমের আর্থিক ক্ষতিপূরণ) দিয়ে দেন, তাদের কয়েদিদেরকে ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করেন। এক কথায় তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আপন করে নেন। কোরআনের ভাষায়ঃ
------------এরাবিক টেক্সট------
“তারা যা কিছু মুহাজেরদেরকে দেয় সে সম্পর্কে মনে কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ করে না। তারা নিজ স্বার্থের ওপর অপরের স্বার্থকে অগ্রগণ্য মনে করে, এমনকি যদি তাদেরকে অভুক্তও থাকতে হয়।”
বস্তুতঃ যতদিন মুসলিম দেশগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবমুক্ত থাকে ততদিন তাদের সমাজ জীবনে এই প্রাণশক্তি সক্রিয় থাকে। জনাব আবদুর রহমান আযযাম তার গ্রন্থ “আর রিসালাতুল খালিদা”য় লিখেছেনঃ
“আমি উত্তর আফ্রিকার তাওয়ারেক গোত্রকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে দেখেছি। তাদের গোত্রে কোন ব্যক্তিই শুধু নিজের জন্য নয় বরং গোটা সমাজের জন্য জীবন ধারণ করে। তারা যে কাজ সমাজের জন্য করে তাতেই তারা সবচেয়ে বেশী গর্ব অনুভব করে। একটা অপূর্ব ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জনৈক শহরবাসী ফরাসিদের এলাকা থেকে হিজরত করে তাওয়ারেকদের নিকট ‘ফাজানে’ বসবাস এবং তাদের কৃপাদৃষ্টির ওপর জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। অতঃপর সে জীবিকার সন্ধানে বের হয়। সে তাদের দানের প্রতিদান দিতেও সংকল্পবদ্ধ ছিল। সে তার পরিবার পরিজনকে ঐ মুসলিম গোত্রের তত্তাবাধানে রেখে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কোন চাকরির সন্ধান পেলো না। সে আমাদের নিকট ‘মিসরাতা’ নামক স্থানে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এলো। আমরা তাকে, যাতে সে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারে সেই পরিমাণ সাহায্য করলাম। কিন্তু সে প্রায় এক বছর পর আবার আমাদের নিকট ফিরে এলো। আমরা মনে করলাম যে, সে তার পরিবারবর্গের নিকট থেকে ফিরে আসছে। কিন্তু সে আমাদের ধারণা খণ্ডন করে বলে যে, সে এখন নিজ পরিবারবর্গের নিকট যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, “কিভাবে?” সে বললো, “গত সাক্ষাতের সময় আমি যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে ব্যাবসা করেছি। এখন আমার নিকট যে টাকা সঞ্চিত হয়েছে তা নিয়ে আমি তাওয়ারেকদের নিকট যেতে পারবো।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি নিজের পরিবারের নিকট যাবে- না তাওয়ারাকদের নিকট?” সে বললো, “আমি প্রথমে তাওয়ারাকেদের নিকট যাব, কেননা তারা আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করেছে। এখন আমি গিয়ে তাদের মধ্যে যারা নিজ পরিবার থেকে অনুপস্থিত রয়েছে তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চালাবো এবং নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের এবং প্রতিবেশীদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বণ্টন করে দেব।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমাদের সমাজে কি প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি এরূপই?” সে বলল, “হাঁ, আমারা সকলে সুখে-দুঃখে পরস্পরের অংশীদার হই। আমারা বিদেশ থেকে খালি হাতে বাড়ি যেতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করি। কারণ আমাদের প্রতিবেশীরাও ঠিক আমাদের পরিবারবর্গের মতই আমাদের পথ চেয়ে থাকে।
এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঘটনার অত্যন্ত নির্ভুল ব্যাখ্যা দেনঃ
“সমাজ জীবনের এ বিচিত্র পদ্ধতি শুধু তাওয়ারেক গোত্র কিংবা বেদুঈন যাযাবরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা তাদের গোত্রবাদেরও ফল নয়। এটাই হচ্ছে আসল ইসলামী পদ্ধতি। আধুনিক জড়বাদী ও বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে যারা বহু দূরে অবস্থিত- সে সমস্ত গোত্রের মধ্যেই এ সমাজ ব্যবস্থার অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। আমি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু শহর বন্দরকে ইসলামী ভাবাপন্ন দেখেছি এবং শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ও আরব-অনারব নির্বিশেষে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ সমাজ পদ্ধতির প্রচলন দেখেছি। আমি বহু জায়গায় আজও মুসলমানদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সুখী জীবন-যাপন করতে দেখেছি। তারা নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য জড়বাদীর সভ্যতার পূজারী কোটি কোটি মানুষের তুলনায় অধিক সুখী ও সমৃদ্ধশালী। তারা আজও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কায়েম করা সমাজ ব্যবস্থার খুবই নিকটবর্তী। পাশ্চাত্য পূজারী মানুষ সমাজের বিরাট ক্ষতি ও বিপর্যয়ের বিনিময়েও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী। নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রয়োজন হলে তারা নিজ পরিবারেরও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, প্রতিবেশীর স্বার্থে সদ্বব্যবহারের তো প্রশ্নই ওঠে না।”
প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পারস্পারিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ইসলামের প্রাণশক্তিরই সৃষ্টি। কিন্তু এটাকে শুধু ব্যক্তির ও সমাজের বিবেকের বা দয়া-মায়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। সরকারও এটা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতো। হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক ‘বাইতুল মাল’ থেকে মাতৃদুগ্ধত্যাগী শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করা এর প্রকৃষ্ট উদাহরন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যয়ের খাতগুলো যাকাতের সুপরিচিত ব্যয়ের খাত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। স্বীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ খাতকে ‘সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা’ (Social security) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় চুরির শাস্তি রহিত করেছিলেন। কেননা হয়তোবা তীব্র ক্ষুধা কাউকে চুরি করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। ইসলামে সন্দেহের ভিত্তিতে দণ্ডবিধি মওকুফ করা হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত ঘটনা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং এ থেকে ব্যক্তি মালিকানার প্রকৃত সরূপ ও সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
বর্ণিত আছে যে, আব্দুর রহমান ইবনে হাতেব বালতায়ার কতিপয় গোলাম মোজাইনা গোত্রের একটি উট চুরি করে। তাদেরকে ধরে হযরত ওমরের (রাঃ) দরবারে নেয়া হলে তারা চুরির কথা স্বীকার করে। হযরত ওমর (রাঃ) কাছির ইবনুচ্চালতকে নির্দেশ দেন তাদের হাত কেটে দিতে। সে যখন হুকুম তামিল করতে এগিয়ে গেল, ওমর (রাঃ) তাকে থামলেন এবং বললেন, “শোন আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা ঐ গোলামদের থেকে প্রচুর পরিশ্রম নিয়ে থাক অথচ তাদেরকে অভুক্ত রাখ? এমনকি তাদের ক্ষুধা এতো তীব্র হয় যে তারা হারাম জিনিস খেলেও তা বৈধ হয়। আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, এটা জানতে না পারলে আমি ওদের হাত কেটে দিতাম।” অতঃপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেব ইবনে আবি বালতায়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন “আমি ওদের হাত কাটলাম না সত্য, তবে আমি তোমার ওপর এমন জরিমানা ধার্য করবো যে তুমি মজা টের পাবে।” তিনি মোজাইনা গোত্রীয় লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার উটের দাম কত?” সে বললো, “চারশো দিরহাম”। ওমর (রাঃ) ইবনে হাতেবকে বললেন, “যাও ওকে আটশো দিরহাম দিয়ে যাও।” তিনি গোলামদের চুরির শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন। কেননা তাদের মনিব তাদেরকে অভুক্ত রেখে চুরি করতে বাধ্য করেছিল।
ইসলামের ইতিহাসে সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মর্যাদা অন্য এক দিক দিয়েও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। সে দিকটি হচ্ছে তার সার্বজনীনতা। কেননা ইসলামের গণ্ডি পেরিয়েও এ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকে।
একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক অন্ধ বৃদ্ধকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখেন। জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন যে, সে ইহুদি। তিনি তার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি ভিক্ষা করছ কেন?” সে বলল, “জিজিয়া, অভাব ও বার্ধক্য- এই তিনে মিলে আমাকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করেছে।” হযরত ওমর (রাঃ) তাকে হাত ধরে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ দিলেন। অতঃপর বায়তুল মালের তত্তাবাধায়ককে বলে পাঠালেন, এই ব্যক্তি এবং এর মত অন্যান্য লোকদের খোঁজ নাও। খোদার শপথ, এটা আদৌ ইনসাফের কথা নয় যে, যৌবনে আমরা তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবো আর বার্ধক্যে তাকে অবজ্ঞাভরে তাড়িয়ে দেব। যাকাত দরিদ্র ও সর্বহারাদের প্রাপ্য। আর এ লোকটি আহলে কিতাবের একজন সর্বহারা। তিনি তার এবং তার মত অন্যান্য লোকদের জিজিয়া মওকুফ করে দেন।
দামেষ্ক সফরের সময়ে তিনি একটি গ্রামের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তিনি জানতে পারেন যে, সেখানে কতিপয় খ্রিষ্টান কুষ্ঠরোগী বাস করে। তিনি তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে সাহায্য দান এবং তাদের জন্য রেশনে খাদ্য সরবারাহ করার নির্দেশ দেন।
তেরশো বছরেরও বেশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাণশক্তি ওমরকে মানবতার সেই সুমহান স্তরে অধিষ্ঠিত করেছিল, যেখান থেকে তিনি সামাজিক নিরাপত্তাকে একটি সার্বজনীন মানবাধিকারের মর্যাদা দান করেন। এই অধিকার অর্জনের জন্য কোন বিশেষ ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের শর্ত ছিল না- কোন শরিয়ত এবং কি আকিদার অনুসারী তাও দেখার প্রয়োজন ছিলা না।
এটা হচ্ছে সেই সু-উচ্চ স্তর যেখানে পোঁছাতে মানবতার পদদ্বয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং সে এখনো তা থেকে বহু দূরে রয়েছে।
রাজনৈতিক ব্যবস্থা
ইতিহাস সাক্ষী যে, একটি সু-সংহত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে ইসলামের একটি দুর্লভ ও আদর্শ যুগ অতিবাহিত হয়েছে। নিদারুন পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলামের এ যুগ বেশী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। আগামীতে আমরা এর প্রকৃত কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করবো। কোন কোন ব্যক্তির ধারণা এই যে, এই কারণ স্বয়ং ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কারণ তার অভ্যন্তরেই নিহিত না বাইরে- তা আমরা পরে আলোচনা করবো। প্রথমে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো। কেননা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবসময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন এবং তার প্রকৃতির অনুসারী হয়ে থাকে।
নবী করিম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামাজের ইমামতী করার নির্দেশ দিলেন। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই যুক্তি দেখিয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করেন যে, আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয় অত্যন্ত কোমল। তাই নামাজের ইমামতি করলে লোকেরা তার আওয়াজ শুনতে পাবে না, তাঁকে তার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেন। এতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রেগে যান এবং আবু বকর (রাঃ)-কে ইমামতী করার জন্য ডেকে আনার ওপর জোর দেন।
প্রশ্ন এই যে, এর অর্থ কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খলিফা নিযুক্ত করে গেছেন? মুসলমানরা কি এ দ্বারা স্পষ্টতঃ তাই বুঝেছিলেন?
আমাদের মতে এ দু’টোই নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যদি খলিফা নিযুক্ত করে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করতেন এবং ইসলামে যদি খলিফা মনোনীত করার বিধানই থাকতো তাহলে তিনি যেমন ইসলামের অন্যান্য বিধি ও নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, এটাও সেরূপ করতেন। আর মুসলমানরাও যদি স্পষ্ট বুঝে থাকতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু বকরকে খলিফা নিযুক্ত করে গেছেন- তাহলে সাকিফা নামক স্থানে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে খলিফা নিয়ে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তার প্রশ্নই উঠতো না। কারন আনাসাররা কখনো রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সিদ্ধান্তে আপত্তি করার মত লোক ছিলেন না।
প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের গোটা ব্যাপারটাকেই মুসলামানদের পারস্পরিক পরামর্শের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়ছে। লোকেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্মতির সাথে খেলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন করবে- এটাই ছিল উদ্দেশ্য। সাকিফায় অনুষ্ঠিত আলোচনার পর যদি এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যে, খলিফা মুহাজেরদের মধ্যে থেকে হবে- তাহলে সেটা ইসলামের কোন নির্দিষ্ট বিধান ছিল না বরং মুসলমানদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটা সিদ্ধান্ত। আনসাররা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তাতে কেউ আপত্তি করতে পারতো না। কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছিল তাহলো এই যে, আনসাররা হযরত আবু বকরের খেলাফতে সম্মত হয়ে যান। কেননা তিনি অন্য সকলের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য মদিনায় আওস ও খাযরাজ গোত্র আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ উস্কিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা ঘোলাটে করতে চেয়েছিল কিন্তু আনসাররা সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন।
এ ক্ষেত্রে খলিফা মোহাজেরদের মধ্য থেকে হবে, এ সিদ্ধান্তের অর্থ এই নয় যে খলিফা কোরেশ বংশের মধ্য থেকেই হতে হবে, যদি তাই হতো তাহলে হযরত ওমর রাঃ পরামর্শ পরিষদ নিযুক্ত করার সময় বলতেন না যে, “হোজায়ফার গোলাম সালেম জীবিত থাকলে আমি তাকে খলিফা নিযুক্ত করতাম।” জানা কথা যে, সালেম (রাঃ) কোরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তাছাড়া ইসলামের মূলনীতি অনুসারেও কোন কোরেশীকে শুধু ‘কোরেশী’ এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ-
-------এরাবিক টেক্সট------
“যার কার্যকালাপ তাঁকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ-মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না।”
হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কে খলিফা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি মুসলমানদেরকে বাধ্য করে গিয়েছিলেন। তার এই নিয়োগকে রদ করার পূর্ণ অধিকার তাদের ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) আবুবকরের নিয়োগের ফলে নয় বরং লোকদের নির্বাচনের ফলেই খলিফা হয়েছিলেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদকে নিজেদের মধ্য হতে একজনকে খলিফা নির্বাচনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু মুসলমানদের ওপর সেই ছয়জনের একজনকে খলিফা মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না। তার সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে নির্বাচিত করেন। কারন প্রকৃতপক্ষে তখনকার মুসলিম উম্মতের মধ্যে ঐ ছয় জনই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাক্তি ছিলেন।
হযরত আলীর রাঃ নির্বাচনের সময় মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদের দরুন প্রথম বারের মত মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এর পরিণামেই একে একে এমন সব হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয় যে, ইসলামের প্রাণশক্তি, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূলনীতি এবং জীবনের অন্যান্য বিভাগে তার প্রবর্তিত চিন্তাধারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের আসল মতাদর্শ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেটা হচ্ছে এই যে,কেবলমাত্র মুসলমানদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতেই কোন ব্যাক্তি শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচাত ভাই, তার জামাতা, তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। এসব জেনে বুঝেও মুসলমানরা তাঁকে অনেক বিলম্বে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হয়তো বা হযরত আলীকে এরূপ বিলম্বিত করা বিশেষতঃ হযরত ওমরের পর-তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করারই নামান্তর। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই বিলম্ব দ্বারাই ইসলামের শাসন পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা নিখুঁত মূল্যায়ণ সম্ভব হয়েছে। এতে করে এই বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়েছে যে উত্তারাধিকারের ধারণা খেলাফতের আসনের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। কারণ এ ধারণা ইসলামের প্রাণসত্তা ও তার মূলনীতিসমূহ থেকে সবচেয়ে দূরত্বে অবস্থিত। হযরত আলীর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে একটু অবিচার হলেও এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ন যে তার চেয়েও গুরুতর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
এরপরে এল বনু উমাইয়ার যুগ। তারা ইসলামী খেলাফতকে বনু উমাইয়ার বংশের মধ্যে সীমিতই শুধু করলো না বরং এক স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় রূপান্তরিত করলো। এটা ইসলামের শিক্ষার ফল ছিল না বরং এটা ছিল “জাহেলিয়াতের” প্রভাব। জাহেলিয়াতের এই প্রভাব ইসলামের প্রাণশক্তিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।
এখানে ইয়াজিদের নিয়োগ ও বাইয়াত কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল সে সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত পেশ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
সিরিয়ায় ইয়াজিদের পক্ষে ‘বাইয়াত’ (প্রস্তাবিত অথবা মনোনীত খলিফার প্রতি জনগণের আনুগত্য বা সমর্থন ও সম্মতিকে বাইয়াত বলা হয়) গ্রহণের পর মুয়াবিয়া সাইদ ইবনুল আসকে যে প্রকারেই হোক হেজাজবাসীদের সমর্থন আদায় করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু সাইদ ব্যর্থ হন। অতঃপর মুয়াবিয়া স্বয়ং বিপুল সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে মক্কায় যান এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলমানদেরকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ
“দেখ, তোমাদের সাথে আমি যেরূপ ব্যবহার করেছি এবং তোমাদের আত্নীয়তা ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের যেরূপ মর্যাদা রক্ষা করেছি তা তোমরা ভালভাবেই অবগত আছো। ইয়াজিদ তোমাদেরই ভাই-তোমাদের চাচার ছেলে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা ইয়াজিদকে নামে মাত্র খলিফা মেনে নাও। যাবতীয় নিয়োগ-বদলি, রাজস্ব আদায় ও বণ্টন প্রভৃতি কাজ তোমরাই করবে।”
আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) জবাব দিলেন, আপনার জন্য দু’টো পন্থার একটা অনুসরণ করা উচিত, হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন নিজের বংশ বহির্ভূত এক ব্যাক্তির পক্ষে অছিয়ত করেছিলেন তাই করুন, নচেৎ হযরত ওমর (রাঃ) যেমন কোন নিকট আত্নীয় নয় এমন ছয় ব্যাক্তির সমন্বয়ে যে পরিষদ গঠন করেন সেরূপ একটি নিরপেক্ষ পরিষদ গঠন করুন।”
মুয়াবিয়া (রাঃ) ক্রোধে যেন জ্বলে উঠলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কাছে তৃতীয় কোন পন্থা নেই?” ইবনে জোবায়ের বললেন, “না।” মুয়াবিয়া অন্যান্য লোকদের দিকে ফিরে বললেন, “তোমাদের মতামত কি?” সকলে একযোগে বললেন, “ইবনে জোবায়ের যা বলেছেন আমাদের বক্তব্যও তাই।” তখন মুয়াবিয়া (রাঃ) তাদেরকে হুমকি দিয়ে বললেন, “কোন চরম পন্থা অবলম্বন করার আগে হুশিয়ারী সংকেত দিলে পরে আর আপত্তির অবকাশ থাকে না। আমি তোমাদের সামনে ভাষণ দিলাম সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের একজন দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমার কথার প্রতিবাদ করলো। আমি এটা বরদাশ্ত করলাম এবং ক্ষমা করে দিলাম।
কিন্তু এখন আমি একটি চূড়ান্ত কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমি হুশিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের কেউ যদি এর জবাবে একটি কোথাও বলে, তবে দ্বিতীয় কোন কথা কর্ণগোচর হবার আগেই তরবারী তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলবে। এখন প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করার চিন্তা করা উচিত।
এরপর মোয়াবিয়ার দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ইয়াজিদের মননোয়নের বিরোধী হেজাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগনের মস্তকোপরি উলঙ্গ তরবারীধারী দুজন করে লোক নিযুক্ত করে মুয়াবিয়া অধিনায়ককে নির্দেশ দেন যে ওদের কেউ যদি আমার ঘোষণার সমর্থনে অথবা প্রতিবাদে একটি বাক্যও উচ্চারণ করে তবে উভয় যেন একযোগে তরবারি দিয়ে আঘাত করে।
এই ব্যবস্থা করার পর মুয়াবিয়া মিম্বারে আরোহণপূর্বক বললেন, “এই ব্যক্তিগণ হচ্ছেন মুসলমানদের নেতা এবং তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, এদের মতামত ছাড়া কোন কিছু করা উচিত নয়। এরা ইয়াজিদের খেলাফতে সম্মত হয়ে ‘বাইয়াত’ করেছেন তোমরাও আল্লাহর নাম নিয়ে বাইয়াত কর। সংগে সংগে লোকেরা ‘বাইয়াত’ করলো। [ইবনুল আমীর, হাওয়াদেস হিঃ ৫৬। আমরা এই বর্ণনাতে সত্য বলে গ্রহণ করার ব্যাপারে বেশী জোর দেয়া পছন্দ করি না। কিন্তু ইসলামের মূলনীতিকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটুকু নিশ্চয়ই বলবো যে, এই রেওয়ায়েত যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ ধরণের কাজ ইসলামের মূল প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। কোন যুক্তি কিংবা ওজর আপত্তি এ কাজকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারে না। - গ্রন্থকার]
এই হচ্ছে ইয়াজিদ সরকারের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে ইসলাম কখনো মেনে নিতে পারে না। আর স্বয়ং ইয়াজিদ কি ধরনের লোক ছিল? তার সম্পর্কে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালার (রাঃ) বিবরণ লক্ষ্যণীয়।
“খোদার শপথ! আমরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে তখন আন্দোলন শুরু করি যখন আমাদের আশংকা হয় যে আমাদের ওপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি হবে। এই ব্যক্তি মা ও কন্যা এবং একাধিক বোনকে এক সাথে বিয়ে করে, মদ পান করে, নামাজ পরিত্যাগ করে। খোদার শপথ! অন্য কোন লোক আমার সাথী না হলেও আমি একাই আল্লাহর পথে কোরবানী দিতাম।”
হয়তো বা এটা ইয়াজিদের একজন দুশমনের অতিরঞ্জিত কথা। কিন্তু পরে ইয়াজিদ যে সব জঘন্য কাজ করেছিল যথাঃ হযরত হোসাইন (রাঃ) কে এমন নিকৃষ্ট পন্থায় হত্যা করা, কাবা শরীফ ঘেরাও এবং তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে ইয়াজিদের দুশমনেরা আদৌ অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেয়নি। প্রকৃত অবস্থা যাই থাক না কেন মুসলমানদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেইনদের উপস্থিতি সত্ত্বেও ইয়াজিদই খেলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল- এ কথা দাবি করার ধৃষ্ঠতা কেউ দেখাতে পারে না। মূলতঃ এ সবের লক্ষ্য ছিল সরকারকে শুধু উমাইয়া বংশের মধ্যে সীমিত করা এবং তাকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। এ প্রবণতা ইসলাম ও ইসলামী বিধানের বুকে ছুরিকাঘাতের সমতুল্য ছিল।
এ তথ্যগুলো আমাদের পরিবেশন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তির নিন্দা করা নয়, বরং ইসলামে যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন শরিয়ত সম্মত সনদ ছাড়াই শুরু করা হয়, তার সাথে ইসলামের প্রাণশক্তি ও মূলনীতির যে কোনই সম্পর্ক নেই, তা স্পষ্ট করে দেখানো। ইসলামকে ও ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত ও আসল স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য আমাদের এ আলোচনার অবতারণা।
শাসন পদ্ধতির কতিপয় নমুনা
এই সত্যের সঠিক উপলব্ধির ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য আমরা খেলাফতে রাশেদার বিভিন্ন যুগ যথাঃ হযরত আবু বকর ও ওমরের যুগ, হযরত ওসমান ও মারওয়ানের যুগ, অতঃপর হযরত আলীর যুগ এবং এমনিভাবে আব্বাসী ও উমাইয়া যুগ থেকে শাসন পদ্ধতির কতপয় বাস্তব নমুনা পেশ করার চেষ্টা করবো।
যখন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খেলাফতের আসনে অভিষিক্ত করেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতে মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়তকে বাস্তবায়িত করা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। এ ধরনের কোন চিন্তা তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি যে, ইতিপূর্বে সাধারণ নাগরিক হিসেবে তার ওপর যে সব কাজ হারাম ছিল এখন তা এ পদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। অথবা আগে যে সব অধিকার ছিল না, তেমন কোন নতুন অধিকার তিনি পাচ্ছেন কিংবা তার ওপর যে সব দায়েত্ব ও কর্তব্য এতদিন ছিল, এখন তা থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।
সাকিফায় যখন তার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তখন তিনি নিম্নরূপ ভঅষণ দেন, “আমি যদি আমার দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালন করি তাহলে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আর যদি আমি বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করি তাহলে তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে। সত্যবাদিতা হচ্ছে বিশ্বস্ততা আর মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে দুর্বল, সে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সবল– যাবত আমি তাকে তার অধিকার না দিয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, সে আমার নিকট সবচেয়ে দুর্বল– যাবত আমি তার নিকট থেকে রাষ্ট্রের অধিকার আদায় করি। মনে রেখো, কোন জাতি যখনি জেহাদ থেকে পিছপা হয়, তখনই আল্লাহ তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন। যখনি কোন জাতি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই আল্লাহ তায়ালা সকলের ওপর পাইকারীভাবে আজাব নাজিল করেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করতে থাকবো, ততক্ষণ তোমরা আমার আদেশ মান্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হই, তখন তোমাদের ওপর আমার আদেশ পালনের দায়িত্ব থাকবে না।”
হযরত আবু বকরের বাড়ী মদিনার পার্শ্ববর্তী “সানহে” অবস্থিত ছিল। একটা ক্ষুদ্র মামুলী ধরণের বাড়ী। খলিফা হবার পরও তিনি সে বাড়ী মেরামতও করাননি। সেই বাড়ী থেকে মদিনা পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে পদব্রজে আসা-যাওয়া করতেন। কখনো কখনো একটা ঘোড়া ব্যবহার করতেন কিন্তু সেটা বাইতুল মালের ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত। পরে কাজের চাপ বেড়ে গেলে তিনি মদিনায় চলে আসেন।
তিনি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলিফা নির্বাচিত হবার পরের দিন যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন, তখন মুসলমানরা তাকে থামিয়ে বললেন, “খেলাফতের দায়িত্ব ব্যাবসা-বানিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পালন করা যাবে না।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি যখন জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন পন্থা জানি না তখন আমার চলবে কি করে?” সবাই তার বিষয় বিবেচনা করলেন এবং তার ব্যবসায় করতে না পারা ও খেলাফতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে ‘বাইতুল মাল’ থেকে তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান বেতন নির্ধারণ করেন।
এ সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুকালে অছিয়ত করেন যে তিনি ‘বাইতুল মাল’ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা যেন হিসাব করে তার জমি-জমা ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে গ্রহণ করে বাইতুল মালে জমা দেয়া হয়।
ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিবেক ও মন-মগজে যে চেতনা ও দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলে তারই প্রভাবাধীনে উজ্জীবিত হয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিটি প্রজার অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী মনে করতেন। তিনি সানহে অবস্থানকালে তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল ও অসহায় প্রতিবেশীদের ছাগলের দুধ প্রতিদিন দুইয়ে দিতেন। যখন তিনি খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর প্রতিবেশীর একটি শিশু মেয়ে তাকে বলে, “এখনতো আপনি আর আমাদের ছাগল দুইয়ে দেবেন না, তাই না?” আবু বকর (রাঃ) বলেন, “কেন দেব না? নিশ্চয় দুইয়ে দেব।” তিনি যথার্থই তাদের দুধ দুইয়ে দেয়া অব্যহত রাখলেন। কখনো কখনো ছাগলের মালিক বালিকাকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, ‘খালি দুধ দুইয়ে দেব, না মাখনও বের করবো?” কখনো সে বলতো, “মাখন বের করে দাও।” আবার কখনো বলতো, “খালি দুধ রেখে দাও।” মোট কথা সে যা বলতো, তিনি তাই করতেন।
হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে হযরত ওমর (রাঃ) মদিনায় একটি অন্ধ মহিলার তত্বাবধান করতেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখেন, তিনি যাওয়ার আগেই কে এসে মহিলাটির কাজ করে দিয়ে যায়। এরূপ প্রতিদিন হতে লাগলো। একদিন গোপনে লুকিয়ে বসে থাকেন। দেখেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে মহিলাটির সব কাজ করে দিয়ে যান। খেলাফত এবং তার গুরুদায়িত্ব তাকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। তাকে দেখামাত্র হযরত ওমর (রাঃ) চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ “নিশ্চয়ই আপনি। খোদার শপথ আপনিই (প্রতিদিন এই কাজ করে থাকেন)।”
এটা হল হযরত আবু বকরের শাসন নীতির কয়েকটা সাধারণ নমুনা! তার স্থলে যখন হযরত ওমর এলেন তখনও এই নীতি অক্ষুন্ন ছিল। ওমর (রাঃ) কখনো খেলাফতকে নিজের একটা বাড়তি অধিকার হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে বাড়তি দায়িত্ব অবশ্যই মনে করেছেন। বলা বাহুল্য সে দায়িত্ব আল্লাহর আইন জারী করা ছাড়া আর কিছু নয়।
‘বাইয়াত’ অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে বলেন, “ভাই সব! আমি তোমাদেরই একজন। তার চেয়ে বেশী কিছু নই। যদি খলিফাতুর রসূলের (হযরত আবু বকর) অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সংগত হতো তাহলে আমি কিছুতেই তোমাদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না।”
অপর এক ভাষণে তিনি বলেন, “আমার ওপর তোমাদের সম্পর্কে কতিপয় দায়িত্ব অর্পিত আছে সেগুলো আমি উল্লেখ করছি। ওগুলো সম্পর্কে তোমরা সব সময় আমার কাছে হিসাব চাইবে। তোমাদের খাজনা ও কর আদায় করা আমার দায়িত্ব। আমি তোমাদের মধ্যে সততার সাথে ধন বন্টন করবো, তোমাদেরকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করবো না, বেশীদিন সীমন্ত রাখবো না এবং যুদ্ধের জন্যে বিদেশে থাকাকালে তোমাদের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করবো।”
তিনি বলতেন, “আমি আল্লাহর মালকে নিজের পক্ষে ইয়াতিমের মালের সমতুল্য মনে করি। প্রয়োজন না হলে স্পর্শ করবো না আর প্রয়োজন হলে সততার সাথে গ্রহণ করবো।”
একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, “আল্লাহর মাল থেকে আপনি কতটুকু গ্রহণ করা নিজের পক্ষে বৈধ মনে করেন?” তিনি উত্তরে বলেন, “শীত ও গ্রীষ্মের জন্য দু’খানা কাপড়, হজ্জ-ওমরার জন্যে সওয়ারীর জন্তু এবং কোরেশের কোন মাঝারী পরিবারের সমমানের খাদ্য আমার পরিবারবর্গের জন্য। এর পরে আমি সাধারণ মুসলমানের মতই একজন মুসলমান। তারা যা পাবে আমিও তাই পাব।”
সাধারণত তিনি এভাবেই জীবন যাপন করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি নিজের জন্য যা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তার ব্যাপারেও অসাধারণ কঠোরতা প্রয়োগ করতেন। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য মধু ব্যবহার করতে বলা হল।
বাইতুল মালে প্রচুর মধু ছিল। তিনি মিম্বরে আরোহন করে বললেন : “তোমরা অনুমতি দিলে মধু ব্যবহার করতে পারি নইলে এটা আমার জন্য হারাম।” তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সবাই অনুমতি দিয়ে দিল।
মুসলমানরা হযরত ওমরের এই কঠোরতা দেখে তাঁর কন্যা উম্মুল মোমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট গিয়ে বললেন, “ওমর (রাঃ) নিজের ব্যাপারে কৃচ্ছতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। বর্তমান সময়ে আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছলতা দান করেছেন। যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে তাঁর ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত গ্রহণ করা উচিত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের এরূপ করার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে।” হযরত হাফসা (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ) কে এ কথা বললেন তখন তিনি জবাব দিলেন, “হাফসা, তুমি তোমার জাতির পক্ষপাতিত্ব করেছ আর নিজের পিতার সাথে অহিতাকাঙ্খী সুলভ আচরণ করেছ। আমার পরিবারভুক্ত লোকদের আমার জান ও মালে অধিকার রয়েছে, কিন্তু আমার ধর্ম ও আমানতদারীতে কোন অধিকার নেই।”
তিনি নিজের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে সাম্যের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। যখন বিখ্যাত আমুর রামাদা’র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তখন হযরত ওমর (রাঃ) শপথ করেন যে যতদিন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন তিনি ঘি ও গোশত স্পর্শ করবেন না। তিনি এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ফলে তেল খেতে খেতে তার শরীরের চামড়া শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর বাজার দুটো পাত্রে দুধ ও ঘি বিক্রি হতে দেখা গেল। হযরত ওমরের জনৈক ভৃত্য চল্লিশ দিরহাম দ্বারা তা কিনে নিয়ে এল। সে এসে তাকে বললো, এখন আল্লাহ আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দিয়েছেন। বাজারে দুধ ও ঘি বিক্রির জন্য এসেছে, আমি তা কিনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যখন তিনি তার দাম জানতে পারলেন তখন বললেন, “খুব চড়া দামে কিনেছ দু’টোই সদকা করে দাও। আমি অপব্যয় করে খাওয়া পছন্দ করি না।” মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতপঃর বললেন, “জনগণের যে দুরবস্থা হয় তা যদি আমারও না হয় তাহলে তাদের সমস্যার গুরুত্ব আমি কি করে বুঝবো।”
ওমর (রাঃ) এর মত ছিল যে জিনিস থেকে প্রজারা বঞ্চিত তা থেকে তার নিজেরও বঞ্চিত হওয়া উচিত। যেমন তিনি নিজেই বলেছিলেন, তার মনের কোন কোণেও এরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল না যে, খেলাফতের পদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি কোনরূপ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে এ ব্যাপারে তিনি যদি সাম্য ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হন তাহলে জনগণের আনুগত্য লাভের কোন অধিকারই তার থাকবে না। এ থেকে ইসলামের রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা যায়। তা হচ্ছে এই যে, কোন শাসক আল্লাহর আইন কার্যকর করা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজের বিচার ফায়সালায় ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি রক্ষা না করলে আনুগত্য লাভের যোগ্য হতে পারে না। হযরত ওমর (রাঃ) এর মনে ইসলামের এই মূলনীতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল এবং এ সম্পর্কে অনুভুতি সবসময় জাগরূক থাকত।
একবার তিনি এক ব্যক্তির সাথে একটি ঘোড়ার দরদস্তুর করেন। এরপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সেটায় সওয়ার হয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন। ইত্যবসরে ঘোড়া ঠোকর খেয়ে পড়ে যায় এবং আহত হয়। তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মালিক ঘোড়া ফেরত নিতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে মোকদ্দমা নিয়ে বিচারপতি শোরাইহের আদালতে গিয়ে হাজির হলেন। শোরাইহ উভয় পক্ষের বিবৃতি শ্রবণের পর বললেন, “আমিরুল মোমিনীন! আপনি যে জিনিস কিনেছেন তা নিয়ে নিন। নচেৎ ওটা যে অবস্থায় নিয়েছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিন।” ওমর বে-ইখতিয়ার বলে ওঠলেন, “একেই বলে ন্যায় বিচার।” অতঃপর তিনি শোরাইহকে তার ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে কুফার বিচারপতি নিযুক্ত করেন।
যখন হযরত ওমরের নীতি নিজের ব্যাপারে এতটাই কঠিন ছিল তখন খলিফার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য নাগরিকের বেলায় কোন বৈষম্যমূলক আচরণের তো প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণ স্বরূপ, যখন তার পুত্র আব্দুর রহমান মদ পান করেন তখন তার ওপর ইসলামী দন্ড কার্যকর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে তার ঘটনা সর্বজন বিদিত। এমনিভাবে আমর ইবনুল আসের পুত্র জনৈক মিশরীয় বালকের ওপর অত্যাচার করলে তাকে শরীয়তের দন্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়।
কর্মচারীদের ব্যাপারে তার নীতি ছিল, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের নিকট যে অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যেত, সে সম্পর্কে তাদের জবাবদিহী করতে হতো। মুসলমানদের ক্ষতি করে কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঐ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে পুংখানুপুংখরূপে তদন্ত করা হতো। “সম্পদ কিভাবে অর্জিত হলো?” – এটা ছিল একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং এ অনুসারে তিনি যখনই কোন কর্মচারীর মধ্যে দুর্নীতির সন্দেহ বোধ করেছেন তখনই কৈফিয়ত তলব করেছেন। মিশরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আসের অর্ধেক সম্পত্তি এই অনুসারেই বাজেয়াপ্ত করে বাইতুল মালে জমা করা হয়। কুফাস্থ প্রতিনিধি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথেও তিনি এ নীতি অবলম্বন করেন। এমনিভাবে বাহরাইনের শাসনকর্তা হযরত আবু হোরাইরার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।
হযরত ওমরের রাজনীতির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, প্রজার ইসলামের চতুর্সীমার মধ্যে থেকে সরকারের আনুগত্য ও হিত কামনা করবে, আর সরকার করবে ন্যায় বিচার ও সর্বাঙ্গীন জনকল্যাণ। এ জন্যই তিনি তার একজন সাধারণ প্রজার এ উক্তি স্বীকার করেন যে, “যদি তোমার মধ্যে আমরা গোমরাহী দেখি তবে আমরা তরবারী দ্বারা সোজা করে দেব।” অর্থাৎ তিনি মেনে নিলেন যে প্রজাদের শাসকের সমালোচনা ও সংশোধনের অধিকার রয়েছে। একদিন তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “তোমাদের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের ওপর অযথা হস্তক্ষেপের জন্যে আমি কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করিনি। তাদেরকে নিয়োগ করেছি তোমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব শিক্ষাদানের জন্য। যদি কোন কর্মচারী কারও ওপর জুলুম অত্যাচার করে তবে আমি তা কিছুতেই বরদাশ্ত করবো না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তার সম্পর্কে আমার নিকট অভিযোগ আনা উচিত।” এ ভাবে তিনি কর্মচারীদের জন্য তাদের ক্ষমতার সীমারেখা নির্দেশ করেন এবং তা লংঘন করতে নিষেধ করে দেন।
শাসকের এহেন গুরুদায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি খাত্তাবের বংশধরদের মধ্য থেকে দ্বিতীয় কোন খলিফা নির্বাচিত হওয়া পছন্দ করেননি। তিনি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে যান যে আব্দুল্লাহকে যেন খলিফা নির্বাচিত করা না হয়। অবশ্য তিনি তাকে পরামর্শ পরিষদে শামিল করেন। এ সময় তিনি যে উক্তি করেন, তা খেলাফত সম্পর্কে তার ধারণার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি বলেন,
“আমরা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করার আদৌ কোন অভিলাষ পোষণ করি না। আমি নিজেও এটা করে সুখী হইনি। তাই আমার বংশধরের মধ্যে আর কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক তাও আমি চাই না। এটা যদি সত্যই ভালভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা সকলে তার নায্য অংশ পেয়েছি। অন্যথায় সমগ্র বংশের মধ্যে একলা ওমরের জবাবদিহী করাই যথেষ্ট।”
হযরত ওসমানের শাসন পদ্ধতি
সন্দেহ নেই, শাসন পদ্ধতি সম্পর্কিত এ ধারণা হযরত ওসমানের (রাঃ) আমলে খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ পরিবর্তন সত্ত্বেও সেটা সামগ্রিকভাবে ইসলামের আওতাভূক্ত থাকে।
হযরত ওসমান (রাঃ) যখন অশীতিপর বৃদ্ধ তখন তার ওপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। মারওয়ান তার বার্ধক্যের সুযোগ গ্রহণ করে বহু বিষয়ে ইসলামের পরিপন্থী নীতি অবলম্বন করে। ওদিকে হযরত ওসমানের কোমলচিত্ততা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার অস্বাভাবিক প্রীতি ও স্নেহ এই দু’টোর কারণে এমন কতিপয় পদক্ষেপ গৃহীত হয় যা সাহাবাদের নিকট বিশেষ আপত্তিজনক বলে মনে হয়। এই পদক্ষেপগুলোর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে ভয়াবহ গোলযোগ ও বিশৃংখলা দেখা দেয় তা ইসলামকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
হযরত ওসমান (রাঃ) এর স্বীয় জামাতা হারেস ইবনে হাকামকে তার বিয়ের দিন বাইতুল মাল থেকে দু’লাখ দিরহাম দান করেন। পরদিন প্রাতে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বিষন্ন বদনে অশ্রুসজল নয়নে খলিফার নিকট এসে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিতে অনুরোধ করেন। তিনি তার নিকট কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে মুসলমানদের ধনাগার থেকে তার জামাতাকে দান করার কারণেই তিনি ইস্তফা দিতে চান। হযরত ওসমান (রাঃ) বিস্ময়ের সাথে বললেন, “ইবনে আরকাম। আমি আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করেছি এজন্য তুমি কাঁদছো? ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে সুতীব্র অনুভূতির অধিকারী সেই ব্যক্তি এ প্রশ্নের উত্তরে যে জবাব দিলেন তা হলো, “না, আমীরুল মুমিনীন! কথা সেটা নয়, আমি এ চিন্তা করে কাঁদছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশায় মুসলমানদের জন্য যে বিপুল অর্থ দান করতেন তারই প্রতিদান হিসেবে এ অর্থ গ্রহণ করলেন না তো? খোদার শপথ করে বলছি, আপনি তাকে একশো দিরহাম দিলেও তা বেশী হতো। খলিফার আত্মীয়-স্বজনের জন্য একশো দিরহাম ব্যয় করাকেও যার বিবেক সংগত মনে করতো না- সেই ব্যক্তির ওপর হযরত ওসমান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং বলেন, “ইবনে আরকাম! তুমি চাবি রেখে যাও। আমি অন্য লোক অবশ্যই পাব।”
এই ধরনের দৃষ্টান্ত হযরত ওসমানের মধ্যে বহু দেখা যায়। একবার তিনি জুবায়েরকে ছ’লাখ, তালহাকে দু’লাখ এবং মারওয়ান ইবনে হাকামকে আফ্রিকার এক পঞ্চমাংশ প্রদান করেন। এতে হযরত আলীর নেতৃত্বাধীন সাহাবাদের একটি দল প্রবল আপত্তি তুললে খলিফা জবাব দেন, “আমার অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে এবং তাদের সাথে আমার সহৃদয় ব্যবহার করা উচিত।” লোকেরা এই জবাবকে আরো আপত্তিকর আখ্যায়িত করে প্রশ্ন করলেন “হযরত আবু বকর ও ওমরের কি আত্মীয়-স্বজন ছিল না?” হযরত ওসমান (রাঃ) জবাব দিলেন, “আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চিত করে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করতেন আর আমি তাদেরকে দান করে পূণ্য অর্জন করতে চাই।” এতে তারা রাগান্বিত হয়ে উঠে চলে এলেন এবং বললেন, “খোদার শপথ! যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেই দু’জনের নীতিই আমাদের নিকট আপনার নীতির চেয়ে অধিক প্রিয়।”
ধন-সম্পদ ছাড়া পদ ও চাকুরীর অবস্থা ছিল এই যে, ওসমানের (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনের ওপর তা বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়েছিল। এদেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া। ওসমান (রাঃ) মুয়াবিয়ার রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে ফিলিস্তিন ও হেমসকেও তার অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাকে সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বানিয়ে দেন এবং তিনি যাতে সমগ্র আর্থিক ও সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে হযরত আলীর মোকাবিলায় খেলাফতের দাবীদার হয়ে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য তার পথ খোলাসা করে দেন। চাকুরীর সুবিধা লাভকারী এই সব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রত্যাখ্যাত হাকাম ইবনে আস, তার পুত্র মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং তার দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবিচ্ছারাহ অন্যতম ছিলেন। মারওয়ানকে তিনি নিজের প্রধান উজীরের পদে অধিষ্ঠিত করেন।
সাহাবারা এই সব কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিনতির কথা চিন্তা করে বারবার মদিনায় ছুটে আসতেন এবং ইসলামী রীতি-নীতিকে বিকৃতির হাত থেকে এবং খলিফাতুল মুসলেমীনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু খলিফার অবস্থা এই যে, বার্ধক্য ও দুর্বলতার দরুন মারওয়ানের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ কথা ঠিক যে হযরত ওসমান (রাঃ) এর মধ্যে ইসলামী ভাবধারার অবস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ অথবা কোন অভিযোগ আরোপ করার অবকাশ নেই। কিন্তু সংগে সংগে তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলাও কঠিন। ভুল-ভ্রান্তির কারণ আমাদের মতে মারওয়ানের ওজারত এবং হযরত ওসমানের বার্ধক্যজনিত মানসিক অস্বাভাবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।
একবার জনগণ সমবেত হয়ে হযরত আলীকে হযরত ওসমানের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে বলেনঃ
“আমি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। তারা আমার নিকট আপনার সম্পর্কে নানা কথা বলেছে। কিন্তু আমি আপনাকে কি বলব তা বুঝতেই পারছি না। আমি যা জানি তা আপনার অজানা নয়। আপনাকে কোন কথা বুঝানোরও সাধ্য আমার নেই। কেননা আপনি নিজেই সব কিছু বুঝতে পারেন। আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমাদের কারও নেই। ইসলাম সম্পর্কে আপনার আগে আমরা কোন জ্ঞান অর্জন করিনি। এমন কোন তথ্য নেই যা শুধু আমরা জানি এবং আপনার নিকট তা এখন পৌঁছানোর প্রয়োজন হতে পারে। কোন কথাই আপনার কাছ থেকে গোপন করে আমাদেরকে শিখানো হয়নি। আপনি রাসূল (সাঃ) কে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তার সাহচর্যে অবস্থান করেছেন এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আপনার চাইতে বেশী কল্যাণের নিকটবর্তীয় ছিল না। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়েও যেমন, আবার শ্বশুর জামাতা সম্পর্কেও তেমন- আপনি তাদের উভয়ের চাইতে রাসূলুল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। তাদের কেউ এ ব্যাপারে আপনার চাইতে অগ্রগামী ছিল না। সুতরাং নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনা কিংবা অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে আনার কোনই প্রয়োজন নেই। সঠিক পথ সম্পূর্ণ উজ্জল ও স্পষ্ট। ইসলামের নিদর্শন সমূহ এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওসমান! জেনে রাখুন! যে ন্যায়পরায়ণ শাসক নিজেও সুপথে থাকে, অপরকেও পরিচালিত করে, সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত এবং বেদা’তকে বিলুপ্ত করে- সেই হলো আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি। খোদার শপথ! সব কিছুই স্পষ্ট। আল্লাহর নীতি এখনো প্রতিষ্ঠিত এবং তার পতাকা এখনো উড্ডীন। আল্লাহর নিকট সবচাইতে অধম ব্যক্তি হচ্ছে সেই, যে সুন্নাতকে বিলুপ্ত এবং বেদা’তকে প্রচলিত করে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন জালেম শাসককে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় হাজির করা হবে। তার ওজর-আপত্তি শ্রবণ করা হবে না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” (তাবারী)
হযরত ওসমান (রাঃ) জবাব দিলেন, “আমি জানি, তুমি যা বলেছ লোকেরাও তাই বলে থাকে। শোন! খোদার শপথ করে বলছি, যদি তোমার স্থলে আমি হতাম তাহলে আমি তোমার নিন্দা বা সমালোচনা করতাম না এবং তোমাকে সমালোচনার মুখে অসহায় ছেড়ে দিতাম না। আমি এ আপত্তি তুলতাম না যে, তুমি আত্নীয়-স্বজনের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করলে কেন? গরীব-দুঃখীর সাহায্য করলে কেন? ওমর (রাঃ) যাদেরকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করতেন- তাদেরকে নিয়োগ করলে কেন? আলী! আমি খোদার শপথ দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না- মুগিরা ইবনে শো’বা সেই পদে নিযুক্ত আছে।”
তিনি বললেনঃ “হ্যাঁ জানি।”
ওসমানঃ “জান, তাঁকে হযরত ওমর (রাঃ) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন?”
আলিঃ “হ্যাঁ।”
ওসমানঃ তাহলে আমি যদি আত্মীয়তার জন্য ইবনে আমেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে থাকি তাহলে তোমরা সে জন্য আমাকে সমালোচনা কর কেন?
আলীঃ “আমি আপনাকে আসল ব্যপার বলছি। ওমর (রাঃ) যাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন, ওমরের জুতা তার মস্তকোপরি থাকতো। তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি শুনলেও তৎক্ষণাৎ তাকে হাজির হতে বলতেন এবং তার শেষ মীমাংসা করে তবে ক্ষান্ত হতেন। এই কাজটাই আপনি করেন না। আপনি নিজে দুর্বল হয়ে পরেছেন এবং আত্নীয়-স্বজনের সাথে নম্র ব্যবহার শুরু করেছেন।
ওসমানঃ “আর তোমার আত্মীয়দের সাথেও তো করি।”
আলীঃ “সন্দেহ নেই, তাঁদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ আত্নীয়তা রয়েছে কিন্তু অন্য লোক তাঁদের চেয়ে উত্তম।”
ওসমানঃ “তুমি নিশ্চয় জান, ওমর (রাঃ) তার খেলাফতের গোটা যুগ ধরেই মুয়াবিয়াকে শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। আমিও তো তাকে শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রেখেছি।”
আলীঃ “আমি আপনাকে খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন না যে, ওমরকে গোলাম ‘ইয়ারফা’ যত ভয় করতো, মুয়াবিয়া তার চাইতেও বেশি ভয় করতেন?”
ওসমানঃ “হ্যাঁ”
আলীঃ “কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, মুয়াবিয়া আপনার মতামত না নিয়েই সিদ্ধান্ত করতে থাকেন অথচ আপনি তার খবরও রাখেন না। তিনি নিজের হুকুম কে লোকদের মধ্যে ওসমানের হুকুম বলে চালিয়ে দেন। এ সব ব্যাপার আপনার নিকট পৌঁছায়, কিন্তু আপনি মুয়াবিয়ার উক্তির প্রতিবাদ করেন না”।
শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে এক ভায়াবহ অভ্যুত্থান শুরু হলো- এর মধ্যে সত্য ও অসত্য, ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কার্যকারণ মিশ্রিত ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, এই অভ্যুত্থান মোটামুটিভাবে ইসলামী ভাবধারার একটি গণবিস্ফোরণ ছিল। অবশ্য এই মত প্রকাশ করার সময় আমরা এ সত্য অগ্রাহ্য করছি না যে, এই বিস্ফোরণের পিছনে অভিশপ্ত ইহুদী সন্ত্রাসবাদী নেতা ইবনে সাবারও গোপন হাত সক্রিয় ছিল।
হযরত ওসমানের ওজর হিসেবে আমরা এ কথা পেশ করতে চাই যে, খেলাফতের দায়িত্ব তার ওপর তার শেষ বয়সে এসে অর্পিত হয়। তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ আর উমাইয়া গোত্রের লোকেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছেল। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আলী রা. সবচেয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি যদি ঘরে বসে থাকি তবে তিনি (ওসমান) বলবেন যে, তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ- আমার অধিকার ও সম্পর্ক অগ্রাহ্য করেছো। আর যদি তার সাথে আলাপ-আলোচনা করি, তাহলেও তিনি নিজের খেয়াল-খুশি অনুসারেই কাজ করেন। মারওয়ান তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করায়। রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহচর্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও বার্ধক্যের কারণে তিনি পুরোপুরিভাবে তাদের খপ্পরে পড়ে গেছেন। তারা তাকে যেদিকে ইচ্ছা করে- সেদিকে চালিত করে।’’
বস্তুতঃ তৃতীয় খলিফার বার্ধক্যের সময় এই গতিশীল জীবন ব্যবস্থাটি উমাইয়া চক্রের মুষ্ঠির মধ্যে চলে যাওয়ায় তার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা এর বাস্তব রীতি-পদ্ধতিকে এর আদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার সময় আর দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়নি।
তাঁর দীর্ঘ খেলাফত যুগে উমাইয়া চক্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও মজবুত হয়। তারা সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে ক্ষমতা সু-সংহত করার সুযোগ লাভ করে। তা ছাড়া হযরত ওসমানের অনুসৃত নীতির স্বাভাবিক ফল হিসেবে সম্পদের কেন্দ্রায়ন অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। ফলে তার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান মুসলিম উম্মাতের ভিত্তিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই দুর্বল করে দেয়।
এ যুগের ইতিহাস একদিকে সত্য দ্বীনের কতিপয় দুর্লভ গুণাগুণের স্বাক্ষর বহন করে। অপরদিকে তার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার সম্পর্কে এক প্রবল চিন্তাগত বিপ্লবেরও নিদর্শন বহন করে। অবশ্য যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার বিপজ্জনক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবও কম গুরুতর নয়।
হজরত ওসমানের পর
হজরত ওসমারন রা. যখন ইন্তেকাল করেন তখন কার্যতঃ উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। খলিফা নিজেই তাদেরকে এ সুযোগ সরবরাহ করেন। সারাদেশে বিশেষতঃ সিরিয়ায় তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং অন্যান্য যাবতীয় সম্পদকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে। তারা সৌভ্রাতৃত্ব, অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি কাজকে উপেক্ষা করতে থাকে। আর এ সবই হজরত ওসমানের খেলাফতের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হতে থাকে। এর কারণে মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের প্রণশক্তি ও ভাবধারা অত্যন্ত দুর্বল ও ম্লান হয়ে পড়ে।
খলিফার কতিপয় পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ জনগণের মনে কখনো স্বাভাবিকভাবে আর কখনো অযৌক্তিকভাবে এক তীব্র ও তিক্ত ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা অভিযোগ মুখর হয়ে ওঠে যে, খলিফা নিজের আত্মীয়-স্বজনের সংগে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন এবং তাদের লাখ লাখ দিরহাম উপঢৌকন দেন। তিনি রাসূলুল্লাহর সা. দুশমনদেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করার জন্য তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে অপসারিত করেন এবং আবু জরের রা. মত উন্নত চরিত্রের সাহাবীর ওপর শুধু এ জন্য নির্যাতন চালান যে, তিনি সম্পদের কেন্দ্রায়ন ও উঁচু তলার লোকদের বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের বাড়াবাড়ির বিরোধিতা করেছিলেন। আবু জর রা. দানশীলতা ও সৎপথে ব্যয়ের প্রচলন এবং শালীনতা ও পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছিলেন।
এ সব কার্যকলাপ মুসলমানদেরকে মর্মাহত ও বিচলিত করে তোলে। এ ধরণের প্রবণতা যখন ব্যাপকভঅবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কিছু লোকের মধ্যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আবার কিছু লোকের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। যাদের মনে ইসলামী আদর্শ বদ্ধমূল ছিল তাঁরা এ সব কার্যকলাপ দেখে নীরবতা অবলম্বন করাকে পাপ মনে করতে থাকেন। তাঁদের মনে সৃষ্ট এ ভাবধারা তাঁদেরকে বিদ্রোহ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর যারা ইসলামকে শুধু লেবেল হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের পার্থিব লোভ লালসা তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে, যারা সব সময় বাতাসের দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেন, তাদের চরিত্র উচ্ছৃংখল এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। এহেন পরিস্থিতিই হজরত ওসমানের খেলাফতের অবসান ঘটায়।
হজরত আলী রা. যখন খেলাফতের মসনদে আসীন হলেন, তখন পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা সহজসাধ্য ছিল না। ওসমানের রা. যুগে যারা অবৈধ মুনাফাখোরীতের লিপ্ত ছিল বিশেষতঃ বনু উমাইয়া ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে হজরত আলী রা. তাদের ব্যাপারে নীরব থাকবেন না। এ সব চিন্তা করে তারা নিজ নিজ কল্যাণের খাতিরে মুয়াবিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।
হজরত আলী রা. এই লক্ষ্য নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন যে তিনি জনগণ ও সরকারকে পুনরায় ইসলামের আসল রাজনৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তাঁর স্ত্রী স্ব-হস্তে গম পিষতেন এবং তা-ই তিনি আহার করতেন। একবার তিনি নিজের এক বস্তা গমের ওপর বায়তুল মালে জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী সিল মোহর অংকিত করছিলেন। বললেন, ‘‘আমি নিজের পেটে শুধু তাই প্রবেশ করাতে চাই যার হালাল হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।’’ কখনো কখনো এমন অবস্থা হয়েছে যে, তাঁকে খাদ্য বস্ত্র খরিদ করার জন্য নিজের তরবারী পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। কুফায় তিনি শ্বেত–প্রসাদে অবস্থান করতেন, তিনি কি ধরণের জীবন যাপন করতেন সে সম্পর্কে নজরে ইবনে মানসুরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ
‘‘আমি হজরত আলীর নিকট গিয়ে দেখি, তাঁর সামনে দুর্গন্ধযুক্ত টক দুধ এবং শুকনো রুটি রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনি কি এসব জিনিস খান?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সা. এর চেয়ে শুকনো রুটি এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। আমি যদি তাঁর নীতি অনুসরণ করে না চলি তাহলে আমার আশংকা হয় যে, হয়তো রাসূলুল্লাহর সা. সংগী হতে পারবো না।’’
এমনিভাবে হারুন ইবনে আনতারা বর্ণনা করেছেন যে, আমি খাওরানাক নামক স্থানে হজরত আলীর সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তখন ছিল শীতকাল। হজরত আলীর রা. গায়ে একটা ছিন্ন পুরনো চাদর ছিল এবং তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। আমি বললাম, ‘‘আমিরুল মি’মিনীন! আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের জন্য এই সম্পদে আল্লাহ কিছু অধিকার নির্ধারিত করেছের। তা সত্ত্বেও আপনি নিজের প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করছেন।’’ আলী রা. বললেন, ‘‘খোদার শপথ! আমি তোমাদের হক নষ্ট করব না। এটা আমার সেই চাদর যা আমি মদিনা থেকে এনেছিলাম।’’
অবশ্য হজরত আলী রা. নিজের ও নিজের পরিবার বর্গের ব্যাপারে এরূপ নীতি অবলম্বন করার সময় এ কথা নিশ্চয়ই জানতেন যে, ইসলাম তাকে এর চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণের অনুমতি দেয়। ইসলাম কাউকে সর্ব রকমের আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে নিতান্ত সংসার বিরাগীর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করে না। তিনি জানতেন যে, তখনো একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাইতুল মালের ধন-সম্পদে তার যা প্রাপ্য ছিল তার চাইতে তিনি অনেক কম গ্রহণ করছিলেন। তা ছাড়া জনগণের কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত শাসক হিসেবে তার প্রাপ্য আরো বেশী ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে অন্ততঃ হজরত ওমর রা. বিভিন্ন দেশের শাসন কর্তাদের যেরূপ বেতন নির্ধারণ করতেন সেই পরিমাণ বেতন গ্রহণ করতে পারতেন। হজরত ওমর রা. কুফার শাসনকর্তা আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং তার সহকারীদের জন্য মাসিক ছ’শ দিরহাম বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। আর সাধারণ লোকদের মত যে সব দানের অংশ পেতেন সেটা এ থেকে স্বতন্ত্র। তাছাড়া তিনি দৈনিক একটি ছাগলের অর্ধাংশ ও আধা বস্তা আটা পেতেন। এমনিভাবে কুফার জনগণকে ইসলামের শিক্ষাদানের এবং বাইতুল মালের দেখাশুনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে নিয়োগ করেন এবং তাঁর জন্য মাসিক একশো দিরহাম এবং দৈনিক একটি ছাগলের এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন। ওসমান ইবনে হানিফের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার দিরহাম বৃত্তি, দৈনিক একটি ছাগলের এক চতুর্থাংশ ও মাসিক দেড়শো দিরহাম বেতন নির্ধারণ করেন।
হজরত আলী রা. নিজের জন্য যে কঠিন পথ অবলম্বন করেন, তা এ সব ব্যাপার না জেনে করেননি। তিনি যে দৃষ্টিভংগী অনুসারে এ নীতি অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, শাসক সব সময়ই জনসাধারণের জন্য আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকে এবং তার ওপর সন্দেহের প্রচুর অবকাশ থাকে। যেহেতু সরকারী কোষাগার তার অধীন থাকে, তাই আত্মসাতের সন্দেহও সৃষ্টি হতে পারে। সেটা জনসাধারণ ও নিজের অধীনস্থ রাজ-কর্মচারীদের জন্য সততা ও সংযমের আদর্শ হয়ে থাকে। এ কারণে তিনি নিজেকে হজরত আবু বকর ও ওমরের রা. সংযমের নীতির অনুসারী করে তোলেন। যে সব ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাদের জন্য এই উন্নত মাপকাঠিই সর্বাপেক্ষা সংগত ছিল।
হজরত আলী রা. গোটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নবী সা. ও তার পরবর্তী খলিফাদ্বয়ের আদর্শের অনুসারী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান।
একবার তিনি স্বীয় বর্ম জনৈক খৃস্টানের নিকটে পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে বিচারপতি শোরাইহের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন এবং একজন সাধারণ নাগরিকের মত তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তিনি দাবী করেন যে, ওই বর্ম তার। শোরাইহ খৃস্টানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমিরুল মু’মিনীনের দাবী সম্পর্কে তার বক্তব্য কী? খৃস্টান বললো, ‘বর্ম নিশ্চয়ই আমার, তবে আমিরুল মু’মিনীনকেও আমি মিথ্যুক বলতে চাই না।’’ শোরাইহ বললেন, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে কী?’’ হজরত আলী রা. হেসে বললেন, ‘‘আমার কাছে প্রমাণ নেই।’’ শোরাইহ রায় দিলেন যে, বর্ম খ্রীস্টানকে দিতে হবে। সে বর্ম নিয়ে রওয়ানা দিল আর আমিরুল মু’মিনীন অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকলেন। কয়েক পা গিয়ে সে ফিরে এল এবং বলতে লাগলো ‘‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে ধর্মের খলিফা স্বয়ং আমাকে বিচারকের নিকট পেশ করে এবং বিচারক তার বিরুদ্ধে রায় দেন; নিঃসন্দেহে তা সত্য ধর্ম।’’ এ বলেই সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো। অতঃপর সে বললো, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! খোদার শপথ করে বলছি, এ বর্ম আপনার। আপনি যখন সিফ্ফিন অভিমুখে যাত্রা করেন তখন আমি সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে চলছিলাম। এ বর্ম আপনার বাদামী রং-এর উটের ওপর থেকে পড়ে গেছে।’’ হজরত আলী রা. বললেন, ‘‘তুমি যখন ঈমান এনেছ তখন এটা তোমাকেই উপহার দিলাম।’’ (আবকারিয়া ইমাম- উস্তাদ আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ)
তিনি যে শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার রূপরেখা তিনি তার অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণেই নির্দেশ করেনঃ
‘‘ভাইসব! আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমাদের যা অধিকার আমারও তাই। তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা আমার ওপরও অর্পিত হয়। আমি তোমাদের নবীর নীতি অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবো এবং তারই আইন চালু করবে। শোনো! ওসমান রা. যাকে যত জায়গা-জমি এবং আল্লাহর ধন থেকে যাকে যা কিছু দিয়েছেন তা বাইতুল মালে ফেরত নেয়া হবে। কেননা, বাস্তবকে কোন জিনিস পরিবর্তিত করতে পারে না। এমনকি যদি আমি দেখি যে, এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিয়ে কিংবা বাঁদী খরিদ করার কাজে ব্যয়িত হয়েছে অথবা তা বিদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তবুও আমি তা ফেরত আনবো। কারণ, ন্যায়-নীতি যার পক্ষে দুঃসহ হবে, জুলুম ও অত্যাচার তার পক্ষে আরো বেশী দুঃসহ হবে।’’
‘‘ভাইসব! হুশিয়ার হয়ে যাও! কিছুদিন আগে যাদের ওপর দুনিয়ার স্বার্থ প্রবল হয়ে পড়েছিল এবং তারা বড় বড় দালান-কোঠা, উট-ঘোড়া, দাস-দাসী ও চাকর-নফরের মালিক হয়েছিল- তাদেরকে যখন আমি এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত করবো এবং তাদের আসল অধিকারের আওতায় ফিরিয়ে আনবো- তখন যেন তারা বলতে আরম্ভ না করে থাকে যে, আবু তালেবের বেটা আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহর সাহাবী, মুহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে কেউ যদি এরূপ মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের দরুণ অন্যান্যদের ওপর তার অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তাহলে তার জানা উচিত যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি শুধু আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে এবং সেখানেই এর উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়া যাবে। জেনে রাখ! যে ব্যক্তি খোদা ও রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দেবে, আমাদের জাতীয়তাকে গ্রহণ করবে, আমাদের সত্য দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং আমাদের কেবলামুখী হবে, সে ইসলামের দেয়া যাবতীয় অধিকার লাভ করবে এবং তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য হবে। তোমরা সকলে আল্লাহর দাস এবং এ সম্পদ আল্লাহর সম্পদ। এটা তোমাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। এ ব্যাপারে কাউকে কারো ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে না। খোদাভীরু লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে।’’
মুনাফাখোর, বৈষম্যপ্রিয়, স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী মহল হযরত আলীর সমবণ্টন নীতিতে খুশী হতে পারেনি এবং তা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই এই মেহল শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী উমাইয়া শিবিরে গিয়ে মিলিত হয়। এই শিবিরে গিয়ে তারা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থের শেষ রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠে।
যাদের দৃষ্টিতে মুয়াবিয়ার মধ্যে হযরত আলীর চাইতে বেশী চাতুর্য, বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও দ্ক্ষতা ধরা পড়ে এবং যারা এই কারণে শেষ পর্যন্ত মুয়াবিয়া বিজয়ী হয়েছেন বলে মনে করেন, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ভুল করেন এবং হযরত আলীর প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ ও তার আসল কর্তব্য পালন সম্পর্কে সঠিক মতামত স্থাপনে ব্যর্থ হন। হযরত আলীর সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ কর্তব্য ছিল ইসলামী ঐতিহ্যকে তার প্রকৃত শক্তিতে পুনর্বহাল করা এবং সত্য দ্বীনের নির্জীব-প্রায় দেহে পুনরায় জীবনীশক্তির সঞ্চার করা। হযরত ওসমানের রা. দুর্বলতা ও বার্ধক্যের সুযোগে উমাইয়া বংশীয় কু-চক্রীদের যে মলীনতা ও কদর্যতা ইসলামের প্রাণশক্তিকে কলুষিত করে তোলে তা থেকে তাকে মুক্ত করাই ছিল হযরত আলীর অন্যতম মিশন।
এই মিশন সফল করার সংগ্রামে তিনি যদি মুয়াবিয়ার রা. মত কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর মিশনই ব্যর্থ হয়ে যেত। এর অর্থ এই দাঁড়াতো যে, তিনি খেলাফত অর্জনের সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করেছেন। এরূপ হলে তাঁর সংগ্রামের কোন মূল্যই থাকতো না। আলী ‘আলী’ হয়েই থাকতে হবে, নচেৎ ‘খেলাফত এবং সেই সাথে তার প্রাণও যদি তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে তার আপত্তি নেই’- এই ছিল হযরত আলী রা. এর সংকল্প। এ সংকল্প তার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্য স্থলিত হতো না। এক বর্ণনা অনুসারে (অবশ্য যদি এটা সত্য হয়) হযরত আলী রা. বলতেন, ‘‘খোদার শপথ, মুয়াবিয়া আমার চাইতে ধূর্ত নয়, কিন্তু সে ধোকাবাজ। সে প্রকাশ্যে নাফরমানি করে। আমি যদি ধোঁকা ও প্রতারণা পছন্দ করতাম তাহলে আমি সবচাইতে ধূর্ত হতাম।’’
হযরত আলীর ইন্তেকালের পর বনু উমাইয়ার যুগ আসে। উমাইয়াদের সামনে হযরত ওসমানের রা. ঈমান, তার খোদাভীরুতা এবং তার হৃদয়ের কোমলতা একটা প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল। কিন্ত সেটা তো আগেই অপসারিত হয়েছিল। এবার হযরত আলীর ইন্তিকালে সর্বশেষ বাধাও দূর হয়ে গেল এবং উচ্ছৃংখলতার পথ উন্মুক্ত হলো।
এরপরও ইসলাম পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু ইসলামের প্রাণশক্তি যে মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল সে ব্যাপারে কো দ্বি-মতের অবকাশ নেই। যদি স্বয়ং ইসলামের প্রকৃতিতে একটি প্রবল শক্তি লুকানো না থাকতো এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তিতে গতিশীলতার যোগ্যতা না থাকতো তাহলে উমাইয়া যুগই তাকে তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার প্রাণশক্তি অবিরাম সংগ্রাম করতে এবং শক্তি অর্জন করতে থাকে। আজও তার মধ্যে সংগ্রামের ও বিজয়ের গোপন শক্তি নিহিত রয়েছে।
উমাইয়া যুগ থেকে মুসলমানদের কোষাগার অতিমাত্রায় উদার হয়ে পড়ে এবং তা বদাশাহ, তাদের চাটুকার ও তল্পিবাহীদের লুটের মালে পরিণত হয়। ইসলামী সুবিচার-ন্যায়নীতির ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। শাসকরা বিশেষ সুবিধাভোগী আর তাদের চাটুকাররা উপঢৌকন-ভোগীতে পরিণত হয়। মোটকথা খেলাফত রূপান্তরিত হয় রাজতন্ত্রে, আর তাও নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে। এই স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সা. ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। এর পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, আমাদের গায়ক কবি ও চাটুকারদেরকে পুরস্কার দেয়ার বহু কাহিনী শ্রবণ করতে হলো। মাবাদ নামক কবিকে জনৈক উমাইয়া বাদশাহ ১২ হাজার দিনার পুরস্কার দেন এবং আব্বাসী বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইসমাইল ইবনে জামে নামক গায়ককে শুধুমাত্র একটি গানের জন্য চার হাজার দিনার দান করেন, সেই সাথে একটা সুন্দর কারুকার্য খচিত মনোরম বাড়ীও দেন। কালের স্রোতধারা এভাবেই চলতে থাকে। কখনো অল্প সময়ের জন্যে এতে বিরতি দেখা দেয়, অতঃপর আবার পূর্ণ গতিবেগে ছুটে চলে।
ওমর ইবনে আবদুল আজিজ
এবারে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের যুগের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ যুগটা ছিল খেলাফতে রাশেদারই পরিশিষ্ট। এটা ছিল একটা তীব্র আলোকচ্ছটা যা গোটা পথকে আলোকিত করে তুলেছিল। অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত শাসন ক্ষমতাকে তার আসল মালিক মুসলিম জাতির নিকট ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তিনি তার খেলাফত যুগের উদ্বোধন করেন। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার গঠনের একমাত্র বৈধ পন্থা হচ্ছে এই যে, মুসলিম জাতি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় শাসক নির্বাচিত করবে, সামরিক শক্তি দ্বারা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেনঃ
‘‘ভাই সব! আমাকে আমার নিজের এবং জাতির মতামত ছাড়াই এ কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমার আনুগত্যের যে বোঝা তোমাদের ওপর চেপে রয়েছে তা আমি নিজেই দূরে নিক্ষেপ করছি। তোমরা নিজেরাই কাউকে নির্বাচন কর।’’
জনতা চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আমরা আপনাকেই নির্বাচন করছি। আপনার নেতৃত্বের ওপর আমরা পূর্ণ আস্থাশীল।’’
এভাবে তিনি শাসক নির্বাচনের আসল পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কেননা জাতির সম্মতি ও পরামর্শ ব্যতিত কেউ শাসক নিযুক্ত হতে পারে না।
অতঃপর তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন,
‘‘বন্ধুগণ! আমার আগে কিছু সংখ্যক শাসক অতিবাহিত হয়ে গেছে। তারা ছিল জালেম। তোমরা কেবল তাদের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছ। মনে রেখ! স্রষ্টার না-ফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না। যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তার আনুগত্য স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে আল্লাহ্র না-ফরমানী করে তার আনুগত্য স্বীকার করা উচিত নয়। যতক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করবো ততক্ষণ তোমরাও আমার নির্দেশ মেনে চলবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহর না-ফরমানী করি তাহলে আমার নির্দেশ পালন করা তোমাদের জন্য জরুরী নয়।’’
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ প্রত্যর্পণ করা শুরু করেন। এ কাজ তিনি নিজের সম্পদ থেকেই শুরু করেন। তিনি নিজের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির উপার্জন সূত্র অনুসন্ধান করে দেখতে পান যে, তার সবই অবৈধভাবে অর্জিত। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই সব সস্পদ ফিরিয়ে দেন। এমনকি তার হাতে একটা অংগুরী ছিল। সেটার দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘এটা আমাকে পশ্চিমাঞ্চল থেকে আদায়কৃত অর্থ সম্ভার থেকে ওলিদ অন্যায়ভাবে দিয়েছিল।’’ তিনি সেটা তৎক্ষণাৎ বায়তুল মালে জমা দেন। তার নিকট যত জায়গীর ছিল তা তিনি ফিরিয়ে দেন। এমামার কতিপয় জায়গীর, ইয়ামনে মুকাইদিস, জাবালুল অরস ও ফিদিক তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল- এর সব ক’টি তিনি পরিত্যাগ করেন এবং মুসলমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন, শুধুমাত্র সুয়াইদা নামক স্থানে একটি নির্ঝরিনী তিনি নিজের অধিকারে রাখেন। এটি তিনি নিজের অর্থে খোদাই করেছিলেন। এর মুনাফা প্রতি বছর তার হাতে আসতো এবং তা প্রায় দেড়শো দিনার হতো।
যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যা কিছু তার অধিকারভুক্ত রয়েছে, তার সবই তিনি মুসলমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করবেন তখন অন্যায়ভাবে অধিকারভুক্ত মুসলমানদের সকল অধিকার প্রত্যর্পণ করতে হবে এই বলে জনগণকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দিলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেনঃ
‘‘নাগরিকবৃন্দ আমাদেরকে বহু জিনিস দিয়েছিলেন, সেগুলো আমাদের গ্রহণ করাও উচিত ছিল না, কাউকে দান করাও উচিত ছিল না। এর সব সম্পদ আমার হস্তগত হয়েছিল। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার নিকট হিসাব চাইতে পারতো না। তোমরা শুনে নাও, আমি এ ধরণের সমস্ত ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করেছি। তবে এ কাজ আমি আমার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ থেকেই শুরু করছি।
মুহাজেম! তুমি পড়তে আরম্ভ কর।’’
এর আগে একটি থলিতে করে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র আনা হয়েছিল। মুহাজেম এক একটি করে দলিল পড়তে আরম্ভ করলেন। এক একটি পড়া শেষ হলে ওমর সেটি নিয়ে নিতেন, তার হাতে ছিল এক কাঁচি, তা দিয়ে তিনি দলিলগুলো কেটে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত কোন একটি দলিল তার কাট-ছাটের হাত থেকে রক্ষা পেলো না। এর পর তিনি স্বীয়-মহিষী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেকের মামলা হাতে নিলেন। তিনি তাকে বললেন, ‘‘তুমি তোমার গহনা বাইতুল মালে দাখিল করে দাও নতুবা আমাকে তোমার থেকে পৃথক হবার অনুমতি দাও। দু’টোর একটা গ্রহণ কর। আমার পক্ষে ওগুলোর সাথে ঘরে বসবাস করা সম্ভব নয়।’’ ফাতিমা বললেন, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আমি আপনাকেই গ্রহণ করবো। একটি হীরকের কিইবা মূল্য। ওর চাইতে হাজার গুণ মূল্যবান জিনিস হলেও আমি তার মোকাবেলায় আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম।’’ এরপর তার নির্দেশে ওটা বাইতুলমালে জমা করা হলো। যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইন্তেকাল করেন এবং ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তিনি তাঁর বোন ফাতিমাকে বলেন যে, তুমি যদি চাও তবে তোমার হীরক তোমাকে ফেরত দেয়া যেতে পারে।’’ তিনি জবাবে বলেন, ‘‘আমি ওটা ওমরের জীবদ্দশায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিয়েছিলাম, আজ তার ইন্তেকালের পর আমি তা কিছুতেই গ্রহণ করবো না।’’
ওমর ইবনে আবদুল আজিজ শুধু অবৈধ সম্পদ ফেরত দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিজের জন্য ‘বাইতুল মাল’ থেকেও কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। অথচ হজরত ওমর ফারুক রা. ‘ফায়’ লব্ধ সম্পদ থেকে নিজের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দূল আজীজকে হযরত ওমর ফারুকের সমান গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তার জবাবে বলেন, ‘‘ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট ব্যক্তিগত সম্পত্তি মোটেই ছিল না- এদিকে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা আছে তাদের আমার বেশ চলে যায়।’’
তিনি মারওয়ান বংশধরকে অর্ধেক সম্পত্তি আসল মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণে উদ্বুদ্ধ করেন। বর্ণিত আছে যে, হেমসের একজন অমুসলিম এসে বলেছিল, ‘‘আমিরুল মুমিনীন! আমার অনুরোধ আল্লাহর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করে দিন।’’ তিনি বললেন, ‘‘কি ব্যাপারে?’’ সে বললো, ‘‘আব্বাস ইবনে ওলিদ ইবনে আব্দুল মালেক আমার ভূমি কেড়ে নিয়েছে।’’ আব্বাস সেখানেই বসা ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আব্বাস, কি বলতে চাও?’’ আব্বাস বললো, ‘‘ওটা আমাকে (পিতা) ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে লিখিত দলিলও দিয়েছেন।’’ তিনি আগন্তুককে বললেন, ‘‘এখন তোমার বক্তব্য কি?’’ সে বললো, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দিন।’’ ওমর বললেন, ‘‘হ্যা, ওলিদ ইবনে আব্দুল মালেকের দলিলের চাইতে আল্লাহর ফরমানই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তুমি এর জমি ফিরিয়ে দাও।’’ তৎক্ষণাৎ সে তার জমি ফিরিয়ে দিল।
রওহ নামে ওলিদের এক ছেলে ছিল। সে আশৈশব গ্রামে লালিত পালিত হওয়ার দরুন দেখতে সম্পূর্ণ গ্রাম্য বলে মনে হতো। কতিপয় ব্যক্তি ওমরের নিকট হেমসে অবস্থিত কয়েকটি দোকান সম্পর্কে মোকদ্দমা রুজু করে। আসলে এই দোকানগুলো ছিল অভিযোগকারীদের, কিন্তু ওলিদ তা রওহের নামে লিখিয়ে দেন। ওমর রওহকে ডেকে তাদের দোকান প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেন। রওহ জবাব দেয় যে, দোকান ওলিদের লিখিত দলিল অনুসারে তার মালিকানাভুক্ত। তিনি জবাব দেন, ওলিদের দলিল দিয়ে তোমার কোন কাজ হবে না। দোকান ওদের এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। তুমি ফিরিয়ে দাও।’’ তখন রওহ এবং হেমসের এক ব্যক্তি উঠে দরবার থেকে ফিরে আসতে লাগলো। পথে রওহ হেমসবাসীকে হুমকি দিল। হেমসবাসী ফিরে গিয়ে ওমরের কাছে উপস্থিত হয়ে রওহের হুমকির কথা জানালো। ওমর তার দেহরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি কাব ইবনে হামেদকে নির্দেশ দিলেন, ‘‘রওহের নিকট গিয়ে বল যে, সে যেন দোকান তার মালিকদের ফিরিয়ে দেয়। যদি ফিরিয়ে দেয় উত্তম, নচেৎ তার মস্তক ছেদন করে আমার কাছে হাজির কর।’’ একথা শুনে রওহের এক শুভাকাংখী দরবার থেকে বেরিয়ে এল এবং আমিরুল মু’মিনীনের নির্দেশের কথা ব্যক্ত করলো। শুনে রওহের চৈতন্য বিলুপ্ত হবার উপক্রম হলো। কাব তার নিকট অর্ধোন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে উপনীত হলো। কাব বলা মাত্রই সে গিয়ে দোকান খালি করে দিল।
জনগণ অবিশ্রান্তভাবে জুলুম, বল প্রয়োগ ও হয়রানির নালিশ নিয়ে তার দরবারে হাজির হতে থাকে। অবৈধভাবে ছিনিয়ে নেয়া সব সম্পত্তির মামলাই তার নিকট পেশ করা হয় এবং তিনি তার সব গুলোই প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করেন, তা তার অধিকারভুক্ত থাকুক বা অন্য কারো। তিনি বনু মারওয়ানের নিকট থেকেও বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নেয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন এবং তার আসল মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। তিনি অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াও এ ধরণের জুলুমের প্রতিকার করতেন, এ ব্যাপারে তিনি সামান্য প্রমাণকেও যথেষ্ট মনে করতেন, যখনই তার নিকট কোন সম্পত্তির ব্যাপারে জুলুম করা হয়েছে বলে অনুমিত হতো অমনি তিনি সে সম্পত্তির মালিকানা প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, পূর্বতন শাসকরা জনগণের সাথে অবিচার করতো। বর্ণিত আছে যে, জুলুমের মাধ্যমে গৃহীত ধন-দৌলত ফেরত দিতে দিতে তিনি ইরাকের ‘বাইতুল মাল’ শূণ্য করে দেন। ফলে সিরিয়া থেকে সেখানে সম্পদ স্থানান্তরিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক উমাইয়া বংশোদ্ভূত আম্বাসা ইবনে সাইদ ইবনুল আসকে ২০ হাজার দিনার উপহার দেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ঘুরে নির্দেশনাটি মোহরের দপ্তরে এসে উপনীত হয় এবং কেবল টাকা গ্রহণ করা বাকী থাকতেই সুলাইমানের মৃত্যু হয়। আম্বাসা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের বন্ধু ছিলেন। ভোর হতেই তিনি ওমরের নিকট উক্ত উপহারটির ব্যাপারে আলাপ করার জন্য রওনা হন। এসে দেখেন, তার দুয়ারে বনু উমাইয়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে। তারাও নিজ নিজ ব্যাপারে কথা বলার জন্য সাক্ষাতপ্রার্থী। আম্বাসাকে দেখে তারা ভাবলেন যে, আমরা নিজেরা আলাপ-আলোচনা করার পূর্বে এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয় তা-ই দেখে নেয়া যাক। আম্বাসা তার নিকট গিয়ে বললেন, ‘আামিরুল ম’মিনীন! সুলাইমান আমাকে ২০ হাজার দিনার দেয়ার নির্দেশ জারী করেছিলেন। এই নির্দেশ মোহরের দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং কেবল ওটা গ্রহণ করা বাকী ছিল। এমন সময় তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস আপনি এই মহানুভবতার কাজটি সম্পূর্ণ করে দেবেন। কেননা সুলাইমানের চেয়ওে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।’’ ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘কত টাকা?’’ তিনি বললেন, ‘’২০ হাজার দিনার।’’ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বললেন, ‘’২০ হাজার দিনার তো মুসলমানদের চার হাজার পরিবারের জন্য যথেষ্ট। এতটা অর্থ আমি কি করে এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে পারি? আমি তা কিছুতেই পারবো না।’’ আম্বাসা বলেন, এ কথা শুনে আমি সেই দলিলটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেই- যাতে অর্থের কথা লিখিত ছিল। ওমর বললেন, ‘‘দলিল তুমি নিজের কাছেও রাখতে পার। কারণ আমার পরে এমন লোকও ক্ষমতাসীন হতে পারে, যে এই সরকারী অর্থের ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী দুঃসাহসী হবে এবং এই দলিলে লিখিত টাকা তোমাকে হয়তো দিয়ে দেবে।’’ এ কথা শুনে আমি দলিলটি তুলে নিলাম এবং বাইরে এসে বনু উমাইয়ার লোকদেরকে আমার সাথে খলিফার আচরণের কথা খুলে বললাম। তারা বলে উঠলো, ‘‘এর পরে আর আমাদের কোনো আশা নেই। তুমি গিয়ে খলিফার নিকট আবেদন কর যেন আমাদেরকে অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার অনুমতি দেন।’’ আমি তার নিকট পুনরায় গিয়ে বললাম, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আপনার বংশের লোকেরা আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আগে তাদেরকে যে সব বৃত্তি দেয়া হতো তা এখনও জারী রাখার আবেদন জানাচ্ছে।’’ ওমর জবাব দিলেন, ‘‘খোদার শপথ! এ অর্থ আমার নয় আর আমি এ ধরণের দান করার অবকাশও দেখি না।’’ আমি বললাম, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! তাহলে তারা অন্য অঞ্চলে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুমতি চাচ্ছে।’’ তিনি বললেন, ‘‘তারা যা করতে চায়, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে।’’ আমিও বললাম, ‘‘আমিও যেতে চাই।’’ তিনি বললেন, ‘‘হা, তোমাকেও অনুমতি দিচ্ছি। তবে আমার মতে তোমার এখানে থাকাই উত্তম। তোমার কাছে যথেষ্ট পুঁজি রয়েছে। এদিকে আমি সুলাইমানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রি করবো। দেখা যেতে পারে, তুমি সেখান থেকে এমন কিছু কিনতে পার কিনা-যার লভ্যাংশ দ্বারা তোমার এই ক্ষতিপূরণ হতে পারে। আম্বাসা বলেন, ‘‘আমি সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং সুলাইমানের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক লাখ দিনারের জিনিসপত্র কিনে তা ইরাকে নিয়ে দু’লাখ দিনারে বিক্রি করলাম। আমি সেই দলিলও সংরক্ষণ করেছিলাম। ওমরের ইন্তেকালের পর ইয়াজীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট উক্ত দলিল নিয়ে উপনীত হই এবং তিনি সেই ২০ হাজার দিনার আমাকে দিয়ে দেন।’’
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ মারওয়ানের বংশধরকে ডেকে বলেন যে, ‘‘তোমাদেরকে আল্লাহ বিপুযল ধন-ঐশ্বর্য দান করেছেন। আমার ধারণা মতে উম্মতের সামগ্রিক সম্পদের অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ তোমাদের কুক্ষিগত রয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের যা কিছু প্রাপ্য তোমাদের নিকট রয়েছে তা তাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করো না।’’ কিন্তু কেউ এ কথার জবাব দিল না। তিনি বললেন যে, ‘তোমরা আমার কথার জবাব দাও।’’ তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ‘‘আমরা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমরা এভাবে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নিঃস্ব বানিয়ে দিতে এবং পিতৃপুরুষদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারবো না, তা আমাদের মস্তক ছেদন করাই হোক না কেন।’’ ওমর বললেন, ‘‘খোদার শপথ! যদি আমি আশংকা না করতাম যে, যে জনগণের অধিকারের জন্য আমি এই চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত রয়েছি, তাদেরকেই তোমরা দলে ভিড়িয়ে ফেলবে- তাহলে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাদেরকে জব্দ করে ছাড়তাম। কিন্তু আমার গোলযোগের আশংকা রয়েছে। যাদি আল্লাহ আমাকে আরো কিছু দিন জীবিত রাখেন, তাহলে আমি প্রত্যেক নাগরিককে তার ন্যায্য অীধকার দিয়ে তবে ক্ষান্ত হব।’’ (ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ, আহম্মদ, জাকি, সফওয়াত)।
কিন্তু তিনি নিজ বাসনা অনুসারে এতটা আয়ু লাভ করতে পারেননি যাতে সকলের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া যায়। তার পরবর্তী শাসকরা তার প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে উমাইয়াদের পথে চলতে থাকে। এরপর আব্বাসীয়রাও এল বাদশাহ হয়ে। তারা যখন এল, তখন দেশে বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, দেশবাসী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। কেননা উমাইয়া শাসকরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামী জীবনপদ্ধতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বস্তুতঃ আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসনের চাইতে উত্তম ছিল না। সেটাও ছিল একই ধরণের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন।
রাজতন্ত্র
আমরা যেহেতু এখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন পদ্ধতি নয়- বরং শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে ইসলামী প্রাণশক্তির ইতিহাস আলোচনা করতে চাচ্ছি- তাই আমরা সেই প্রাণশক্তির বিকৃতি করণ ও তাতে মলিনতার স্পর্শের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করার জন্য রাজততান্ত্রিক শাসনামলের তিনটি ভাষণ পেশ করেই ক্ষান্ত হব। খেলাফতে রাশেদার যুগে যে তিনটি ভাষণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এ তিনটির তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
সন্ধির পর মুয়াবিয়া কুফায় জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘কুফাবাসীগণ! তোমরা কি মনে করেছ যে আমি নামাজ, জাকা, ও হজ্জ্বের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি? আমিতো ভাল করেই জানি যে, তোমরা নামাজ, জাকাত ও হজ্জ্ব যথারীতি পালন করে থাক। আসলে আমি যুদ্ধ করেছি তোমাদের গর্দানের ওপর আমার শাসন চালাবার জন্য। তোমাদের অসম্মতি সত্ত্বেও আল্লাহ আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। জেনে রেখ, এই হাংগামায় যত জান-মালেরই ক্ষতি হয়ে থাক না কেন তার কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। আর আমি যত প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে না কেন তা সব এই যে আমার পায়ের তলে পিষ্ট করে দিলাম।’’ এমনিভাবে তিনি মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ
‘‘খোদার শপথ! আমার যতদূর জানা আছে, আমি তোমাদের প্রীতি-ভালবাসার পরিণতিতে ক্ষমতা লাভ করিনি। তোমরা এতে খুশী হওনি- তাও আমি জানি। আমি এই তরবারীর সাহায্যে সংগ্রাম করেছি। তোমাদের ব্যাপারে আমি আবু বকর ও ওমরের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনকে সম্মত করতে পারলাম না। সুতরাং আমি নিজেকে এমন এক পথে চালিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে আমার ও তোমাদের- উভয় পক্ষেরই কল্যাণ সাধিত হবে। সকলকে সুচারুরূপে মিলেমিশে পানাহার করতে হবে। তোমরা যদি আমাকে শাসক হিসেবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে মনে না কর, তথাপি আমি তোমাদের জন্য উত্তম শাসক।’’
মনসুর আব্বাসী উমাইয়া শাসন ধারাকে চরম বিকৃতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান এবং রাজত্ব ও বাদশাহীকে একটি ঐশী ও খোদার পক্ষ থেকে সঠিক ও সত্য ব্যাপার বলে গণ-মানসে ধারণার সৃষ্টি করে দেন। অথচ ইসলামের নিকট এ ধারণা সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরূপ অপকীর্তি সাধনের পর মনসুর নিম্নরূপ ভাষণ দেনঃ
‘‘দেশবাসী! আমি আল্লাহর জমীনে তার স্থলাভিষিক্ত। তারই সাহায্য সহায়তায় তোমাদের ওপর শাসন চালাবো। আমি তার ধন-সম্পদের ওপর তার পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রহরী। তার ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে আমি তা ব্যয় করি অথবা কাউকে দান করি। আল্লাহ আমাকে জাতীয় কোষাগারের তালা স্বরূপ বানিয়েছেন। তিনি যদি আমাকে খুলতে চান তাহলে তোমাদের মধ্যে খাদ্য বণ্টন অথবা দান করার জন্য খোলেন আর যদি বন্ধ করতে চান তাহলে বন্ধ করে দেন।’’
এরপর শাসন ব্যবস্থা ইসলাম ও তার মূলনীতির আওতা থেকে একেবারেই বাইরে নিক্ষিপ্ত হলো।
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
স্বর্ণযুগে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন ছিল। শাসকবৃন্দ শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার সম্পর্কে যে ধরণের চিন্তা করতেন, তাদের অর্থনীতিও সেই ধরণের ছিল। হযরত মুহাম্মাদ সা., হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা. এবং হযরত আলী রা. এর যুগে ইসলামী আদর্শ সক্রিয় ছিল অর্থাৎ এই নীতি প্রচলিত ছিল যে, সরকারী অর্থ-সম্পদ সবই জাতির এবং জনতার সম্পদ। শাসক তা থেকে কেবলমাত্র নিজের অথবা নিজের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রমাণ করেই কিছু গ্রহণ করতে পারে। এমনিভাবে শাসক প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেবলমাত্র তার সত্যিকার প্রাপ্য যতটুকু ততটুকুই দিতে বাধ্য। কেননা এ ব্যাপারে শাসক ও অন্যান্যরা সমান। হযরত ওসমান রা.-এর যুগে এ নীতিতে সামান্য বিকৃতি দেখা দিয়েছিল, তখনও জনগণ নিজেদের পূর্ণ অধিকার অর্জন করতো। তবে সম্ভবতঃ সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ লোকদের নির্ধারিত বৃত্তি ইত্যাদি দেয়ার পরেও বিপুল অর্থ বেঁচে থাকতো। খলিফার ধারণা ছিল এই যে, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও তার ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য লোকদের দান করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরপর যখন শাসন ক্ষমতা চলে গেল স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে, তখন সমস্ত বিধি-নিষেধ অপসারিত হলো এবং শাসকরা জনগণকে দান কিংবা বঞ্চনার হিড়িক চলতে থাকলো। মুসলমানদের সম্পদে শাসকদের, তাদের সন্তান-সন্ততির, তাদের তল্পিবাহী ও চাটুকারদের জন্য অবাধ ভোগের দ্বার উন্মুক্ত হলো। তারা এ ব্যাপারে ইসলামের সমস্ত সীমরেখা অতিক্রম করে চলতে থাকলো।
এ হলো পরিস্থিতির একটা মোটামুটি বিবরণ। এবারে আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করবো।
রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগ থেকে বাইতুল মালের আয়ের যে সব পন্থা চলে আসছিল তা হচ্ছেঃ
প্রথমতঃ যাকাত- এটা মুসলমানদের বিভিন্ন রকমের সম্পদের ওপর ধার্য করা হয়। যেমনঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, কৃষি উৎপাদন, ফলমূল, গবাদিপশু, বাণিজ্য পণ্য, খনিজ ও প্রোথিত ধন প্রভৃতি। সাধারণভাবে যাকাতের গড় হার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এটা ৮টি প্রসিদ্ধ খাতে ব্যয় করা হয়।
দ্বিতীয়তঃ জিজিয়া- এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের বসবাসের জন্য রাষ্ট্রকে প্রদত্ত কর বিশেষ। এটা মুসলমানদের যাকাত এবং কায়িক ত্যাগ কুরবানীর সমপর্যায়ভুক্ত।
তৃতীয়তঃ ‘ফায়’- এটা হচ্ছে সেই অর্থ-সম্পদ যা মোশরেকদের নিকট থেকে যুদ্ধ ছাড়াই আদৌ পরিশ্রম না করেই পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান অনুসারে এই অর্থ সম্পদের সমগ্রটাই আল্লাহ, তাঁর রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও প্রবাসীদের প্রাপ্য।
চতুর্থতঃ গণিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ- এর চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের আর বাকীটুকু ‘ফায়’-এর অনুরূপ এবং ঐ সব খাতেই ব্যয়িত হবে।
অথবা, গণিমতের স্থলে ‘খারাজ’- মোশরেকদের যে সব জমি যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের হস্তগত হয়; যেমন হযরত ওমর রা. পারস্যের জমির ব্যাপারে করেছিলেন- সেই সব জমির ওপর ধার্যকৃত কর বিশেষ।
রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে বাইতুল মালের আয় পর্যাপ্ত ছিল না। মুহাজেররা নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে মদিনায় এসেছিলেন এবং আনসারগণ তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের ধন সম্পত্তিতে অংশীদার করে ভাই বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। যুদ্ধের আগে মুসলমানদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল ইচ্ছাকৃত দান।
যখন যুদ্ধাভিযানের ধারাবাহিকতা শুরু হলো এবং হিজরতের দ্বিতীয় বছর যাকাত ফরজ হলো তখন আসল আয়ের উৎস অর্থাৎ যাকাতের সাথে আরেকটা উৎস গণিমতের মাল যুক্ত হলো। এর এক পঞ্চমাংশ দেয়া হতো যোদ্ধাদেরকে। রাসূলুল্লাহ সা. পদাতিককে একাংশ এবং অশ্বারোহীকে দুই অংশ অন্য এক রেওয়ায়েত তিন অংশ দিতেন। এভাবে তিনি এই নীতি নির্ধারিত করে দিলেন যে, ‘‘প্রত্যেকের অংশ তার ত্যাগ ও কুরবানী অনুপাতে।’’ তিনি অবিবাহিতকে একাংশ এবং বিবাহিতকে দুই অংশ দিতেন। এমনিভাবে তিনি দ্বিতীয় নীতি এই নির্ধারণ করেন যে, ‘‘প্রত্যেকের অংশ তার প্রয়োজন অনুপাতে।’’ গণিমতের অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ ব্যায়ের খাত ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
অতঃপর একটা নতুন ব্যাপার ঘটলো। বনু নজীর অভিযানে প্রথম বারের মত ‘ফায়’ অর্জিত হলো। এটিকে রাসূলুল্লাহ সা. মুহাজেরদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। আনসারদের মধ্য থেকে মাত্র দু’জন দরিদ্র ব্যক্তিকে এ থেকে অংশ দেয়া হয়। এরপর কোরআনের এক আয়াতে এই মূলনীতি ঘোষণা করা হয় যে,
‘তোমাদের ধনিকদের মধ্যে যেন সম্পদের আবর্তন সীমিত হয়ে না থাকে।’
অপ্রতিহত গতিতে দেশ জয় ও ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাইতুল মালের আয় বর্ধিত হতে থাকে। সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে মুসলমানগণ ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে। কারণ ইসলামের নির্ধারিত অংশ অনুসারে তারা সকলেই বাইতুল মালের অর্থের সমান অংশীদার।
যখন রাসূলুল্লাহ সা. ইন্তেকাল করেন এবং কিছু লোক ইসলাম-ত্যাগী হয়ে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তখন আবু বকর রা. যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা ইতিহাসের অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ
‘‘খোদার শপথ! (যাকাতের) উট ও অন্যান্য গবাদি পশু বাঁধার এক গাছি রশিও যদি তারা দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।’’ এ ব্যাপারে তিনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের অভিমতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে হযরত ওমরও হযরত আবু বকরের অভিমত সমর্থন করেন ও নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথমদিকে তার মত ছিল এই যে, তারা ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) স্বীকার করে বলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। তার মতভেদ এতটা তীব্র ছিল যে, তিনি খানিকটা চড়া স্বরে বলে ওঠেন, ‘‘আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করে অস্ত্র ধারণ করি’’ যখন রাসূলুল্লাহ সা. বলে গেছেনঃ
‘‘মানুষ যতক্ষণ না বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ‘ইলাহ’ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ রাসূল, ততক্ষণ আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এটা বলবে, তার ধন ও প্রাণ আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। অবশ্য ইসলামী বিধান অনুসারে তাতে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হলে সে কথা স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আয়ত্তাধীন।’’ এতে হযরত আবু বকর রা. পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন যে, ‘‘খোদার শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতে প্রভেদ করবে আমি তার সাথে যদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হলো ধন-সম্পদের ওপর ধার্য অধিকার বিশেষ।’’ সংগে সংগে হযরত ওমর রা. বলে উঠলেন, ‘‘খোদার শপথ! আমি অনুভব করতে পেরেছি যে, আল্লাহ আবু বকরের বক্ষকে যুদ্ধের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এখন আমিও বুঝতে পেরেছি যে, এটাই সঠিক পন্থা।
এই মহান যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ইতিহাসে ইসলামের একটি মূলনীতিকে কার্যকরী করে দেখিয়ে দিলেন। তিনি সপ্রমাণ করলেন যে, আল্লাহ ধন-সম্পদে সমাজের জন্য যে হারে ও যে নিয়মে অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা আদায় করার জন্য যুদ্ধ করাও ন্যায়সংগত।
হযরত আবু বকর রা. যাকাত, গণিমত ও ‘ফায়’ প্রভৃতির তহবিল নির্ধারিত খাতে ব্যায় করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. এর পদানুসরণ করতে থাকেন। তিনি নিজেদের জন্য মুসলমান জনসাধারণের নির্ধারিত মামুলী বৃত্তি গ্রহণ করতেন আর সেটা ছিল দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম। এর পর তিনি জনগণকে নির্ধারিত বৃত্তি প্রদান করতেন। অতঃপর অবশিষ্ট অর্থ তিনি সামরিক খাতে ব্যয় করতেন।
হযরত আবু বকরের যুগে অপর একটি ব্যাপারেও হযরত ওমরের সাথে তাঁর মতভেদ ঘটে। হযরত আবু বকরের অভিমত ছিল, ধন বণ্টনের ব্যাপারে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং পরবর্তী যুগে ইসলাম গ্রহণকারী, স্বাধীন ও গোলাম, নারী ও পুরুষ সকলকে সমান অংশ দেওয়া উচিত। কিন্তু হযরত ওমর রা. ও সাহাবাদের একটি দল ইসলামের প্রতি প্রথম অগ্রসর ব্যক্তিদের পর্যায়ক্রমে অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। হযরত আবু বকর রা. তাদের লক্ষ্য করে বলেন, ‘‘তোমরা যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের কথা বলছ, সে সম্পর্কে আমি উত্তম রূপে ওয়াকিবহাল। কিন্তু আসলে ওটা এমন একটা ব্যাপার, যার সওয়াব আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে প্রদান করবেন। পক্ষান্তরে এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যাপার। এখানে অগ্রাধিকারের চাইতে সমাধিকারের নীতিই উত্তম।’’
বস্তুতঃ এই সমাধিকারের নীতি অনুসরণই অব্যাহত থাকে এবং আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ যতই বাড়তে থাকে ততই সমান হারে মুসলমানদেরকে স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে থাকে। অবশেষে ওমর ইবনে খাত্তাবের রা. যুগ এলো। তিনি তখনো একই অভিমত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, ‘‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সা. বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাকে আমি রাসূলুল্লাহর সা. পক্ষে যুদ্ধকারীর সম-মর্যাদা দিতে পারি না।’’
একদিন বাহরাইনের শাসনকর্তা আবু হোরাইরা রা. বহু অর্থ-সম্পদ নিয়ে খলিফার দরবারে উপনীত হন। তাঁর ভাষায়, ‘‘পাঁচ লাখ দিরহাম নিয়ে আমি সন্ধ্যা বেলায় ওমরের সাথে সাক্ষাত করি। আমি বললাম, ‘আমিরুল মু’মিনীন! এই নিন টাকা।’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কত টাকা?’ আমি বললাম, ‘পাঁচ লাখ দিরহাম।’ তিনি বললেন, ‘জান, পাঁচ লাখে কত হয়।’ আমি বললাম, ‘জি হাঁ, পাঁচশো হাজার।’ কিন্ত তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন, ‘মনে হচ্ছে তোমার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। যাও রাত্রে আরাম কর গিয়ে। সকালে এস।’ আমি সারারাত বিশ্রাম করে ভোরে আবার এসে বললাম, ‘আমিরুল মু’মিনীন! টাকা নিন।’ তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ টাকা ন্যায়সঙ্গত পন্থায় অর্জিত হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘যতদূর আমার জানা আছে, ন্যায়সঙ্গত পন্থায়ই অর্জিত হয়েছে।’ তখন হজরত ওমর রা. উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘ভাই সব! আমাদের কাছে বহু অর্থ এসেছে। তোমরা মেপে-গুণে অথবা ওজন করে যেভাবে ইচ্ছা বন্টন করে নিতে পার।’ এক ব্যক্তি উঠে বললোঃ ‘আমিরুল মু’মিনীন। আপনি যথারীতি হিসাবের খাতা তৈরী করে নিন এবং সেই হিসাবের বিবরণ অনুসারে লোকদের মধ্যে বণ্টন করুন। হযরত ওমর রা. এ প্রস্তাব পছন্দ করেন। তিনি মুহাজেরদের জন্য মাথা প্রতি ৫ হাজার, আনসারদের জন্য মাথা প্রতি ৩ হাজার এবং নবীর সা. মহিষীদের জন্য মাথা প্রতি ১২ হাজার দিরহাম ধার্য করেন।
এখানে আমরা এ রেওয়ায়েত এই জন্য উদ্ধৃত করেছি যাতে অগ্রাধিকার দান সম্পর্কে হযরত ওমরের রা. নীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এ দ্বারা সেই সময়কার প্রাচুর্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। অর্ধ মিলিয়ন দিরহাম তখন এমন একটা স্বপ্ন বলে মনে হতো যেন এ কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারে না। অবশ্য পরবর্তী যুগে বড় বড় বিজয়ের ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তার কিতাবুল খারাজে লিখেন, ‘‘হযরত ওমর রা. বলেছেন, ‘খোদার শপথ! এই ধন-সম্পদে (বাইতুল মালের ধনসম্পদে) প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে। এতে কারো অধিকার অপরের চেয়ে বেশী নয়। এ ধরণের ব্যাপারে আমিও তোমাদেরই মত একজন। তবে আমাদের মর্যাদার তারতম্য আল্লাহর কিতাবের আলোকে এবং রাসূলুল্লাহর সা. সাহচার্য অনুপাতে নির্ধারিত হবে। ইসলামের জন্য কে কি পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং কে কত আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা বিবেচনা করতে হবে, মুসলমান অবস্থায় স্বচ্ছলতা অথবা দারিদ্রের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হবে। খোদার শপথ! আমি যদি বেঁচে থাকি তবে সানার পাহাড়ে মেষচারণকারী রাখালও বিনা পরিশ্রমে নিজের জায়গায় বসেই ধন-সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য অংশ লাভ করতে পারবে।’’
‘‘তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক ৫ হাজার দিরহাম, ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং হাবশায় হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক ৪ হাজার দিরহাম এবং বদর-যোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের মাথা প্রতি ২ হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করেন। হযরত হাসান রা. ও হযরত হোসেনের রা. জন্য বার্ষিক ৫ হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারিত করেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য তিনি বার্ষিক ৩ হাজার দিরহাম এবং মক্কা বিজয়ের পর ঈমান আনয়নকারীদের জন্য মাথা প্রতি ২ হাজার দিরহাম এবং আনসার ও মোহাজেরদের তরুণ পুত্রদের জন্যও অনুরূপ বৃত্তি নির্ধারণ করেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণে তিনি তাদের সামাজিক মর্যাদা, কোরআনের জ্ঞান এবং ইসলামের পথে জেহাদকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সবাইকে তিনি এক সারিতে রাখেন। যে কোন মুসলমান মদিনায় এসে অবস্থান করলে তার জন্য ২৫ দিনার বৃত্তি ধার্য করা হতো। সিরিয়া ও ইরাকের মতই ইয়ামেনবাসীদের জন্যেও দুই হাজার, এক হাজার, নয়শো, পাচশো’ এবং তিনশ’ দিরহাম করে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। তিনশ’র চেয়ে কম কারো ছিল না। তিনি বলতেন যে, সম্পদ যদি আরো বর্ধিত হয় তাহলে আমি প্রত্যেকের জন্য চার হাজার দিরহাম ধার্য করবো- এক হাজার তার সফরের জন্য, এক হাজার অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য, এক হাজার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়ার জন্য এবং এক হাজার তার ঘোড়া ও খচ্চরের জন্য।’’ (আল-ফারুক ওমর, দ্বিতীয় খণ্ড; ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হাইকেল)
বৃত্তি ধার্য করার ব্যাপারে হযরত ওমর রা. যে নীতি নির্ধারণ করেন কোন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে তা অনুসরণ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। এই সব ব্যক্তিকে তিনি তারই সমপর্যায়ের অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক বৃত্তি দেন।
ওমর ইবনে আবি ছালমার জন্য তিনি ৪ হাজার দিরহাম ধার্য করেন। ইনি হলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমার পুত্র। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস এতে আপত্তি জ্ঞাপন করে আমিরুল মুমিনীনকে বলেন, ‘‘আপনি ওমরকে কিসের ভিত্তিতে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন? তার পিতার মত আমাদের পিতারাওতো হিযরত এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।’’ আমিরুল মুমিনীন তাকে জবাব দেন, ‘‘আমি তাকে, রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট তার মর্যাদা ছিল ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার নিকট আপত্তি করছে সে উম্মে সালমার মত মা নিয়ে আসুক, আমি তার কথা মেনে নেব।’’ তিনি উসামা ইবনে জায়েদের জন্য চার হাজার দিরহাম ধার্য করেন। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, ‘‘আপনি আমার জন্য তিন হাজার ধার্য করলেন। আর উসামার জন্য চার হাজার ধার্য করলেন। অথচ আমি এমন বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি যাতে উসামা অংশগ্রহণ করেননি।?’’ হযরত ওমর রা. তাকে জবাব দিলেনঃ ‘‘আমি তাকে এ জন্য বেশি দিয়েছি যে, সে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। তার পিতাও রাসূলুল্লাহর সা. নিকট তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন।’’ তিনি হযরত আবু বকরের রা. স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের জন্য এক হাজার দিরহাম, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার জন্য এক হাজার দিরহাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মায়ের জন্য এক হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। এই সব মহিলাকে তিনি তাদেরই সমপর্যায়ের অন্যান্য মহিলার চেয়ে বেশি দেন, কেননা তারা যে সব পুরুষের স্ত্রী কিংবা মা ছিলেন, তাদের অন্যান্য পুরুষের ওপর অগ্রাধিকার ছিল।’’ (আল-ফারুক ওমর, দ্বিতীয় খণ্ড, হাইকেল)
এখানে ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে আবু বকর ও ওমরের দুটো পৃথক অভিমত দেখা যাচ্ছে। ওমরের অভিমতের ভিত্তি ছিল, ‘‘যারা রাসূলুল্লাহর সা. বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তাদেরকে আমি তাঁর পক্ষে যোদ্ধাদের সমপর্যায়ে গণ্য করতে পারবো না।’’ এছাড়া ইসলামের পথে দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরদাশত করাকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করার জন্যও ইসলামে ভিত্তি রয়েছে। সেই ভিত্তি হচ্ছে শ্রম ও শ্রমের মজুরীর মধ্যে সমতার নীতি। এমনিভাবে আবু বকরের রা. অভিমতেরও ভিত্তি রয়েছে, ‘‘লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং তার প্রতিদানও তার হাতে নিবদ্ধ। তিনি কেয়ামতের দিন এর পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। দুনিয়ায় কারো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের চেয়ে বেশী অধিকার নেই।’’
কিন্তু আমরা কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ ছাড়াই হযরত আবু বকরের মতকে অগ্রাধিকার দেব। কারণ এটা মুসলমানদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। আর জানা কথা এই যে, সাম্য হচ্ছে ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ নীতি সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারেও অধিক সহায়ক- যা এই বৈষম্য নীতি গ্রহণ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। এক শ্রেণীর লোকের সম্পদ বর্ধিত হয়ে গিয়েছিল এবং বছরের পর বছর মুনাফার দ্বারা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল। ধন-বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, মুনাফার মাধ্যমে সম্পদ যত বাড়ে, তা মূলধনের বৃদ্ধি অনুপাতে অনেক বেশী। স্বীয় অনুসৃত নীতির এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে হযরত ওমর রা. তার জীবনের শেষ ভাগে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পরবর্তী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকলে সকলের বৃত্তি সমান করে দেবেন। এই সময়ে তার এ উক্তি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেঃ
‘‘যে সব সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছি তা পুনরায় করার সুযোগ পেলে ধনিকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতাম।’’
কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। বৈষম্যমূলক বণ্টন নীতির যে সব কুফল দেখা দেয় তা গোটা ইসলামী সমাজের ভারসাম্য ব্যাহত করে। এরপর যখন মারওয়ানের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপ শুরু হয় এবং হযরত ওসমান রা. তা বরদাশত করতে থাকেন তখন সমাজ মারাত্মক বিপর্যয়ের কবলে পতিত হয়।
মর্যাদার পার্থক্য অনুসারে ধন-বণ্টনের কুফল দেখে হযরত ওমর রা. নিজের মত পরিত্যাগ এবং হযরত আবু বকরের রা. মত গ্রহণ করেন। হযরত আলীর রা. মতও ছিল প্রথম খলিফার ন্যায়।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা হযরত আলীর খেলাফতকে প্রথম দুই খলিফার খেলাফতেরই স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বলে মনে করি। আর হযরত ওসমানের যুগকে মনে করি একটি শূণ্যতা, যা আলী ও পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের মাঝে বিভেদের দেয়াল টেনে দিয়েছিল। কারণ এ সময়ে মারওয়ানই ছিল আসল শাসন পরিচালক। এ জন্য এখন আমরা হযরত আলী রা. সম্পর্কে আলোচনা করবো, এর পর আলোচনা করবো হযরত ওসমানের রা. যুগ সম্পর্কে।
হযরত আলী বৃত্তি বণ্টনের ব্যাপারে সাম্যের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম ভাষণেই স্পষ্ট করে বলেনঃ
‘‘শোনো! রাসূলুল্লাহর সা. সাহাবীদের মধ্যে আনসার কিংবা মোহাজের-যেই মনে করে যে, রাসূলুল্লাহর সা. সাহচর্যের কারণে অন্যান্যদের ওপর তার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার রয়েছে, তার জানা উচিত যে, এই অগ্রাধিকার সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট লাভ করবে এবং তার প্রতিদানও সেখানে পাবে। ভালো করে বুঝে নাও! যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়, আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেয়, আমাদের জীবন-বিধান গ্রহণ করে এবং আমাদের কেবলা অভিমুখী হয়- ইসলামের যাবতীয় অধিকার ও কর্তব্য তার ওপর অর্পিত হয়। তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা, আর এ সমস্ত সম্পদ আল্লাহর। এটা সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। এ ব্যাপারে কেউ অপর কারো ওপর অগ্রাধিকার পাবে না। অবশ্য খোদাভীরু লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’’
এটাই প্রকৃত ইসলামী বিধান, ইসলামের সাম্যের আদর্শের সাথে এর পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। এটা ইসলামী সমাজে ভারসাম্য রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় এবং এতে কেবল কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনা দ্বারাই সম্পদ বাড়ানো যায়। এই নীতি কাউকে লাভজনক কাজের জন্য অপরের চেয়ে বেশী অর্থ সরবরাহ করে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেয়ার অবকাশ রাখে না।
হযরত ওমর রা. জীবনের শেষ ভাগে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সময় পাননি। আকস্মিক শাহাদাতের ফলে তিনি তাঁর দু’টো ইচ্ছা সফল করতে পারেননি। একটা হলো তিনি চেয়েছিলেন যে, ধনিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবেন। কেননা এই অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল শুধুমাত্র সরকারী অর্থের অসম বণ্টনের ফলে। দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল তিনি ধনবন্টনের ব্যাপারে সম-অধিকার নীতি প্রবর্তন করবেন।
হযরত ওসমান রা. যখন খলিফা হলেন তখন তিনি এই দু’টো সিদ্ধান্তের একটিও কার্যকরী করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি বাড়তি অর্থ তার মালিকের হাতেই ছেড়ে দেন এবং বৃত্তি বন্টনেও বৈষম্য বহাল রাখেন। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে মুক্ত হাতে আরো উপঢৌকনাদি দিতে থাকেন। এর ফল দাঁড়াল এই যে, ধনীরা আরো বেশি ধনী এবং গরীবরা আরো গরীব হয়ে পড়ে। অবশ্য গরীবরাও কখনো কখনো স্বচ্ছলতা বোধ করতো। যাদের ধন-দৌলতের কোন অভাব ছিল না তিনি তাদেরকেও বড় বড় অংকের অর্থ সাহায্য করেন। কোরেশদেরকে তিনি সারা দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অবাধ সুযোগ দেন। তিনি বড় বড় ধনীদেরকে সাওয়াদ অঞ্চলে অথবা বিদেশে দালান কোঠা ও জায়গা-জমি খরিদ করারও সুযোগ দেন। এর পরিণতি স্বরূপ তাঁর খেলাফতের শেষের দিকে সমগ্র মুসলিম সমাজে ধন-বণ্টনে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাঁর ওপর অনুগ্রহ করুন।
হযরত আবু বকর রা. ও তার পর হযরত ওমর রা. এই নীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে কার্যকরী করতেন যে, কোরাইশ প্রধানদের একটি উল্লেখযোগ্য দলকে মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য করতেন। তাই আবু বকর রা. ও ওমর রা. তাদেরকে বিজিত দেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দিতেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা, ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং জেহাদে তাদের অগ্রসরতার দরুণ জনগণ বিশেষভাবে তাদের ভক্ত ও অনুরক্ত হতে পারে এবং তখন এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধন-সম্পদ, দক্ষতা ও পদের লিপ্সা জন্মাতে পারে। এটাকে অবশ্য ইসলামের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ বলা যেতে পারে না। কেননা ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের শর্তের সাথে জড়িত। যখন হযরত ওসমানের যুগ এলো, কখন তিনি তাদেরকে সর্বত্র অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা দান করলেন। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে বিজিত দেশ সমূহে ঘর-বাড়ী ও জায়গা-জমি ক্রয় করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করলেন। আর এটা করলেন তখনি- যখন তিনি তাদেরকে লাখ লাখ দিরহাম দিয়ে ফেলেছেন।
নিঃসন্দেহে মুসলমানদের এবং বিশেষতঃ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে উদার ও সদয় ব্যবহার হিসেবেই এ সব করা হয়েছিল। কিন্তু এই নীতির অত্যন্ত মারাত্মক কুফল দেখা দেয়। সে কুফল আবু বকর রা. ও ওমরের রা. দৃষ্টি থেকে গোপন ছিল না। এর ফলে মুসলমানদের সমাজে বিপুল আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজে একটি অলস ও নিষ্ক্রীয় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। চরম নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও তাদের ধন সম্পদের অন্ত ছিল না। বিনা চেষ্টায় বসে বসে তারা পরম তৃপ্তিকর জীবন যাপন করতো।
এভাবে বিলাসিতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। অথচ এই বিলাসিতার বিরুদ্ধে ইসলাম তার আইন-কানুন ও নীতিমালা উভয়ের মাধ্যমেই অবিরাম যুদ্ধ ঘোষণা করে আসছিল। হযরত ওসমানের পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং এটা যাতে কোনক্রমেই মাথা তুলতে না পারে তার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয় তখন কতিপয় লোকের মধ্যে ইসলামী প্রাণশক্তির বিষ্ফোরণ ঘটে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত আবু জর। তিনি ছিলেন সবচেয়ে স্পষ্টবাদী ও বিপ্লবী।
দুঃখের বিষয়, হযরত আবু জরের নীতিকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে মিশরের দারুল ইফতা সম্প্রতি এক ফতোয়া দিয়ে আবু জরের চেয়ে বেশি ইসলাম বুঝার দাবী ফলাতে চেষ্টা করেছেন। খোদার দ্বীন তাদের নিকট যেন ব্যবসা-পণ্যে পরিণত হয়েছে।
আবু জর রা. মুসলিম সমাজের উঁচু তলার লোকদের বিলাসিতাকে পূর্ণোদ্যমে চ্যালেঞ্জ করেন। কেননা ওটা ছিল ইসলামের একেবারেই পরিপন্থী। এই বিলাসিতার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বনু উমাইয়া ও হযরত মুয়াবিয়ার সমালোচনা করেন। কেননা তার এ নীতির দরুন ধনিকদের ধন এবং বিলাসীদের বিলাসিতাই কেবল বেড়ে চলছিল।
আবু জর রা. জানতে পারলেন যে, হযরত ওসমান রা. মারওয়ানকে আফ্রিকার রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ, হারেসকে দুই লাখ দিরহাম এবং জায়েদ ইবনে ছাবেতকে এক লাখ দিরহাম দান করেছেন। এটা তার বিবেকের পক্ষে অসহনীয় ছিল। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করে এক জনসভায় নিম্নরূপ বক্তৃতা দেনঃ
‘‘আজকাল এমন সব কাজ করা হচ্ছে যা আমার বুদ্ধির অগম্য। খোদার শপথ! এ সব কাজের পেছনে আল্লাহর কোরআনে কিংবা রসূলের হাদীসে কোথাও কোনো ভিত্তি নেই। খোদার শপথ! আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সত্য পদদলিত হচ্ছে, বাতিলকে পুনরায় জীবন্ত করে তোলা হচ্ছে, সত্যবাদী লোকদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করা হচ্ছে এবং ‘তাকওয়া’ ও খোদাভীতি ছাড়াই লোকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। হে ধনিক সমাজ! তোমরা গরীবদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার কর। যারা টাকা-পয়সা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে জানিয়ে দাও যে তাদের কপালে, পিঠে ও পার্শ্বে আগুন দিয়ে দাগানো হবে। হে পুঁজিপতিরা! জেনে রাখ, ধন-সম্পদে তিনজন অংশীদার রয়েছেঃ প্রথমতঃ অদৃষ্ট। এটা যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে তোমাদের বিনা-অনুমতিতে তোমাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকারী। সে সব সময় অপেক্ষা করছে, কখন তোমার চোখ মুদিত হবে এবং সে তোমার ধন-সম্পদ কুক্খিগত করবে। তৃতীয়তঃ তোমার অধিকার। যদি তুমি এই তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশীদার না হতে চাও তবে সে জন্য অবশ্যই চেষ্টা কর। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
‘‘তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয়তম সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে না।’’ বন্ধুগণ! তোমরা এখন রেশমী পর্দা এবং মখমলের বালিশ ব্যবহার করা শুরু করেছে। আজকাল আজার বাইজানের গদিতে শয়ন করা তোমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. শুধু চাটাই-এর ওপর শয়ন করতেন। তোমরা আজ রকমারী খাদ্য খাও অথচ রাসূলুল্লাহ সা. পেট ভরে জবের রুটিও পেতেন না।’’
মালেক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বর্ণনা করেন যে, একবার আবু জর রা. হযরত ওসমানের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকলে আবু জর রা. একখানা লাঠি হাতে করে দরবারে উপস্থিত হন। এই সময়ে হযরত ওসমান রা. কা’ব নামক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ‘‘কা’ব, আবদুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বহু টাকা রেখে গেছেন। সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?’’ কা’ব বললেন, ‘‘তিনি যদি তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করে থাকেন তাহলে আর তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করা যায় না।’’ এ কথা শোনামাত্র আবু জর রা. তার লাঠি উত্তোলন করলেন এবং কা’বকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যেঃ
‘‘যদি আমার কাছে এই পর্বতের সমান সোনা থাকতো এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম ও তা আল্লাহ গ্রহণ করতে থাকতেন তবে আমি তা থেকে ছয় উকিয়া পরিমাণ স্বর্ণও রেখে যাওয়া পছন্দ করতাম না।’’ এই হাদীস বর্ণনা করে তিনি হযরত ওসমানকে তিনবার খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আপনি কি এ হাদীস শুনেছেন?’’ তিনি বললেন, ‘‘হাঁ!’’ (৪৫৩ নম্বর হাদীস- মুসনাদে আহমদ)
এ ধরণের আহ্বান বরদাশত করা মারওয়ান ও মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা অবিরাম হযরত ওসমানকে তার বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবু জরকে উপযুক্ত শরিয়ত সম্মত অপরাধ ছাড়াই দেশান্তরিত হয়ে ‘রবজা’য় চলে যেতে হয়।
দেশে সম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও অর্থলিপ্সা যাকে পর্যদস্ত করতে পারেনি সেই জাগ্রত বিবেকের পক্ষ থেকেই এই উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছিল। তখন সম্পদের কেন্দ্রায়ণ এমন প্রকট হয় যে, ইসলামী সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ইসলামের প্রধান প্রধান মূলনীতিগুলো অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। আমরা এই সময়কার আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে মাসউদী বর্ণিত কতিপয় নমুনা পেশ করছি। তিনি বর্ণনা করেনঃ
‘‘ওসমানের রা. আমলে সাহাবারা বিপুল ধন-সম্পদ উপার্জন করেন। যেদিন ওসমান রা. শাহাদাত বরণ করেন, সেদিন তার কোষাধ্যক্ষের নিকট তার দেড় লাখ দিনার ও দশ লাখ দিরহাম নগদ জমা ছিল। ওয়াদিল কুরা ও হোনাইন প্রভৃতি স্থানে তাঁর যে ভূ-সম্পত্তি ছিল তার দাম ছিল এক লাখ দিনার। এ ছাড়াও তিনি বহু সংখ্যক ঘোড়া ও উট রেখে যান। জোবায়ের রা. এর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত একটি ভূ-সম্পত্তির মূল্যই ছিল ৫০ হাজার দিনার। তা ছাড়া তিনি এক হাজার ঘোড়া ও এক হাজার বাঁদী রেখে যান। তালহার রা. ইরাক থেকে দৈনিক এক হাজার দিনার এবং সারাত থেকে এর চেয়েও বেশী আয় হতো। আবদুর রহমান ইবনে আওফের আস্তাবলে এক হাজার ঘোড়া ছিল, তার এক হাজার উট এবং দশ হাজার ছাগল-ভেড়াও ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের মূল্য দাঁড়ায় ৮৪ হাজার দিরহাম। জায়েদ ইবনে ছাবেত এত বেশী সোনা রূপা রেখে যান যে, তা কুড়াল দিয়ে কাটতো হতো। যে সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তিনি রেখে যান তা এ থেকে পৃথক। জোবায়ের বসরায়, মিশরে, কুফায় ও আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি করে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এমনভিাবে তালহা রা. কুফায় একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মদিনায়ও তিনি সেগুনের কাঠ ও চুন-সুরকী দিয়ে একটি বিরাট কোঠা নির্মাণ করেন। সা’দ ইবনে আবি আক্কাস আকিকে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গন গম্বুজসহ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মিকদাদ মদিনার ভিতরে ও বাইরে কারুকার্যখচিত এক মনোরম প্রাসাদ তৈরী করেন। ইয়ালা ইবনে মুম্বা ৫০ হাজার দিনার নগদ এবং তিন লাখ দিরহাম মূল্যের ভূ-সম্পত্তি রেখে যান।’’ (ওসমান- উস্তাদ ছাদেক উরজুন)
ওমরের রা. আমলে ধন বণ্টনে মর্যাদার তারতম্য করার অনিবার্য ফল হিসাবে সম্পদের এই ভারসাম্যহীন প্রাচুর্যের উৎপত্তি হয়। হযরত ওমর রা. এ নীতি ও এর ফলাফলের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এটার অবসান করেই ছাড়তেন যদি তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ না হতো। তার শাহাদাতের পর এ প্রাচুর্য ক্রমশঃ বেড়েই যেতে থাকে। হযরত ওসমান রা. সে নীতি অব্যাহত রাখেন এবং তার ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। হযরত ওসমান রা. অসম বণ্টন ছাড়াও যে সব উপহার-উপঢৌকনাদি এবং জায়গীর ইত্যাদি প্রদান করেন সেগুলোও মুসলিম সমাজে ধনবাদী প্রবণতা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে সহায়তা করে। এরপর এমন কতগুলো কার্যকারণ আত্মপ্রকাশ করে যার দরুণ ধন-সম্পদের ভারসাম্যহীন প্রাচুর্য অস্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করে। বিশেষতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একত্রিকরণ এবং লাভজনক কারবারের উপায়-উপকরণ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজে পুঁজিবাদী প্রবণতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। আবু জরের মন থেকে যে গভীর ও আন্তরিকতা পূর্ণ আবেদন বহির্গত হয়েছিল তার বিরোধিতা ও উপেক্ষার কারণেও পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। যদি তার আবেদন সফলকাম হতো এবং রাষ্ট্র প্রধানকে তিনি স্ব-মতে দীক্ষিত করতে পারতেন তাহলে তার মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার যোগ্যতা ছিল। এতে করে ধনিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা সম্পর্কিত হযরত ওমরের শেষ সংকল্প পূর্ণ হতো। জাতিকে পুজিবাদী অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের এরূপ করা সম্পূর্ণ বৈধই শুধু ছিল না বরং বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের খাতিরে অবশ্য কর্তব্যও ছিল।
একদিকে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবারের সদস্যদের জীবনে প্রাচুর্যের বান ডেকেছিল। অপরদিকে ঠিক তেমনি তীব্রতা ও প্রাবল্য নিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র ও হাহাকার আঘাত হানছিল সাধারণ মানুষের জীবনে। এতে স্বভাবতই বিদ্বেষ ও ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। এই সমস্ত কার্যকারণ অব্যাহত গতিতে পুঞ্জিভূত হতে থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত এক বিভীষিকাময় সহিংস অভ্যুত্থানের সূচনা করে ছাড়ে। এই অভ্যুত্থানে ইসলামের শত্রুদেরই উপকার সাধিত হয় এবং তা হযরত ওসমানের প্রাণ সংহার করে। সেই সাথে মুসলিম উম্মতের শান্তি ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয় এবং তাকে বিশৃংখলা ও উত্তেজনার গভীরতম আবর্তে নিক্ষেপ করে। যতক্ষণ স্বয়ং ইসলামের প্রাণশক্তি এই বিশৃংখলার আগুনে ধূমায়িত না হয় এবং উম্মত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের হিংস্র থাবায় আক্রান্ত না হয় ততক্ষণ এ বিশৃংখলার আগুন নির্বাপিত হয়নি।
ওসমানের রা. পর আলী রা. সাম্য ও ন্যায় বিচারের যে নীতি গ্রহণ করেন, তাতে পুঁজিবাদী মহল এবং যারা সম্পদের অসম-বণ্টন দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হয়েছিল তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; এটা আদৌ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল না। তারা হযরত আলীকে এ নীতি পরিহার করার পরামর্শ দেয় এবং আশংকা প্রকাশ করে যে, এতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। তাঁর জাগ্রত বিবেকে ইসলামের যে দীপশিক্ষা প্রজ্জ্বলিত ছিল তদনুসারে তার এই জবাব দেয়াই স্বাভাবিক ছিল যে, ‘‘তোমরা কি আমাকে আমার দেশবাসীর ওপর জুলুম করে অন্য কারো সাহায্যে গ্রহণের পরামর্শ দিতে চাচ্ছ? এ ধন-সম্পদ যদি আমার হতো তথাপি আমি এর বণ্টনে সাম্য অবলম্বন করতাম। আর এটা যখন আল্লাহর সম্পদ, তখন আমি কি করে বে-ইনসাফী করতে পারি? জেনে রাখ, সম্পদ অন্যায়ভাবে কাউকে দেয়া অপব্যায়ের আওতায় পড়ে। সন্দেহ নেই যে, এতে করে দানকারী দুনিয়ায় খানিকটা মর্যাদাশীল হতে পারে, কিন্তু আখেরাতে এরূপ নীতি তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।’’
বনু উমাইয়া অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপারে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। অবশেষে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগ এলে তিনি অন্যায়ভাবে অর্জিত ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণ এবং অপব্যয় রোধ করার কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। এই সময়ে বনু উমাইয়ার লোকেরা বাইতুল মালের অর্থ সম্পদের ব্যাপারে অন্যান্য প্রজাদের সমানাধিকার পায়। তখন আর চাটুকার, স্তুতিবাদী কবি ও গায়কদের কোনো অংশ তাতে ছিল না। তিনি কবিদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বাইতুল মাল থেকে তাদের পুরস্কার দেয়ার নীতি রহিত করেন।
একবার কবি জারির তার প্রশংসা করে এক কবিতা পাঠ করেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাকে বলেন, ‘‘জারির! তুমি কি মোহাজেরদের সন্তান, যে তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তা তোমাকেও দেব? তুমি কি আনসারদের সন্তান, যে তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তা তোমাকেও দেব? না তুমি কোন গরীব লোক, যে তোমাকে তোমার জাতির ছদকা ও জাকাতের তহবিল থেকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দেব?’’
সে জবাব দিল, ‘‘আমিরুল মু’মিনীন! আমি এর কোনোটি নই। বরং আমি সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। আমাকে সাবেক শাসকরা এর পুরস্কার হিসাবে চার হাজার দিরহাম ও তার সাথে মূল্যবান কাপড়-চোপড় ও সওয়ারীর জন্তু দিতেন। ওগুলো গ্রহণ করার আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাই আপনার কাছে আমি সেই পুরস্কার চাই।’’
ওমর জবাব দিলেন, ‘‘প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের প্রতিফল আল্লাহর কাছে পাবে। তবে আমার যতদূর জানা আছে, আল্লাহর সম্পদে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) তোমার কোন প্রাপ্য নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত ভাতা লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি হিসাব করে দেখবো যে, আমার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য সারা বছরে কত লাগে। যত লাগে ততটা আমি রেখে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তোমাকে দিয়ে দেব।’’ জারির বললো, ‘‘না আমার দরকার নেই। আল্লাহ আমিরুল মু’মিনীনকে আরো বেশী দান করুক এবং তার আরো বেশী প্রশংসা করা হোক এই কামনা করি। আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট মনে বিদায় হচ্ছি।’’ তিনি বললেন, ‘‘এটাই আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা।’’ জারির সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে ওমর ভাবলেন, ও আবার নিন্দাবাদও করতে পারে। এর একটা প্রতি-বিধান করা উচিত। এই ভেবে তিনি তাকে পুনরায় ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। জারির এলে তিনি বললেন, ‘‘আমার কাছে চল্লিশটি দিনার ও দুই জোড়া কাপড় আছে। এর এক জোড়া ধুয়ে অপর জোড়া পরি। আমি এই জিনিসগুলোর অর্ধেক তোমাকে দিতে পারি। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী আছেন যে, তোমার চাইতে ওমরের এই জিনিসগুলোর বেশী প্রয়োজন।’’ জারির বললো, ‘‘আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে আরো বেশী দিন। খোদার শপথ! আমি সন্তুষ্টচিত্তেই যাচ্ছি। এগুলোর আমার কোনো দরকার নেই।’’ তিনি বেললেন, ‘‘বেশ! তাহলে তুমি যখন শপথ করে বললে, তখন আমি তোমাকে বলতে চাই যে, তুমি এই প্রার্থনা ও পুরস্কার গ্রহণ না করে আমাদেরকে যে অনটন থেকে অব্যাহতি দান করলে সেটা আমাকে তোমার কবিতা ও স্তুতিবাদের চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। এখন তুমি আমার বন্ধু হয়ে যাও।’’
মুসলমানদের সম্পদকে যখন এভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং তাকে তার আসল পাওনাদারদের নিকট পৌঁছানো হয়েছে তখন আর বর্ণনাকারীদের এ বর্ণনায় বিস্ময়ের কিছু থাকে না যে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগে লোকেরা এত স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিল যে, যাকাত নেয়ার লোক পাওয়া যেত না, কেননা তারা তাদের অন্যায্য ন্যায্য পাওনা পেয়ে যাকাতের দিক থেকে অভাব শূণ্য হয়ে গিয়েছিল।
ইয়াহিয়া ইবনে সা’দ বর্ণনা করেন, ‘‘আমাকে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ যাকাত ও ছদ্কা সংগ্রহের জন্য আফ্রিকায় পাঠান। আমি সেখানকার যাকাত ও ছদ্কা সংগ্রহ করে তা বিতরণ করার জন্য গরীব লোকদের সন্ধান করি। কিন্তু কোনো গরীব লোক আমি সেখানে পাইনি। কোনো ব্যক্তিই সেখানে অর্থ গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। কারণ ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাদের সকলকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে আমি সেই অর্থ দ্বারা গোলাম ক্রয় করে স্বাধীন করে দেই।’’
আসল ব্যাপার হলো, দারিদ্র ও অভাব শুধুমাত্র সম্পদের কেন্দ্রীকরণেরই সৃষ্টি। প্রত্যেক যুগে গরীব লোকেরা বৃহৎ পুঁজিপতিদের জুলুম-উৎপীড়ন ও শোষণের শিকার হয়ে থাকে, আর এই বৃহৎ পুঁজিপতিরা আত্মপ্রকাশ করে বড় বড় দান, উপঢৌকন, পুরস্কার, জায়গীর, শোষণ, জুলুম ও মুনাফাখুরীর বলে।
উমাইয়া ও তার পরবর্তী আব্বাসীয় শাসনামলে সরকারী কোষাগার বাদশাহদের জন্য নিজের সম্পদের মতই ‘‘হালাল’’ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে দু’টো পৃথক পৃথক কোষাগার স্থাপন করা হয়। একটি সাধারণ কোষাগার- অপরটি বিশেষ কোষাগার। শোষোক্তটি সম্পর্কে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ওটার আয় ও ব্যয় বাদশাহর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এরূপ বহু দেখা যেত যে, কোনো সাধারণ খাতের অর্থ বিশেষ কোষাগারে দাখিল করা হয় আবার কোনো বিশেষ ব্যয় সাধারণ কোষাগার থেকে সম্পন্ন করা হয়।
অধ্যাপক আদম মেজ (Adam Mez) স্বীয় পুস্তক ‘ইসলামী সভ্যতা চতুর্থ শতাব্দী’-তে বলেনঃ
ভাতা ও রাজধানী সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের জন্য সাধারণ কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণ করা হতো। আমাদের কাছে চতুর্থ শতকের প্রথম দিকের একটি ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে যাতে বিশেষ কোষাগারের উপার্জন খাত সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ
১. সন্তান-সন্ততির জন্য পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদঃ কথিত আছে যে, সবচেয়ে বেশী সম্পদ রেখে যান হারুনুর রশীদ অর্থাৎ ৪ কোটি ৮ লাখ দিনার। মুতাজিদ (হিঃ ২৭৯-২৮৯) নিজ শাসনামলে প্রতি বছর সকল ব্যয়-বরাদ্দের পর বিশেষ উপার্জন খাত থেকে দশ লাখ দিনার সঞ্চয় করতেন। এভাবে তার কাছে ৯০ লাখ দিনার সঞ্চিত হয়। তিনি আশা পোষণ করতেন যে এক কোটি দিনার হলে তা গলিয়ে বড় একটা পিন্ড তৈরী করবেন এবং তাঁর কাছে এক কোটি দিরহাম আছে তাই তার আর কোনো অর্থের লোভ নেই এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি সেই পিন্ড প্রকাশ্য দরবারে ঝুলিয়ে রাখবেন বলেও স্থির করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, এক কোটি দিরহাম সঞ্চিত হলে তিনি এক বছরের জন্য জনগণের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা মওকুফ করে দেবেন। কিন্তু এ বাসনা পূর্ণ হবার আগেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।
মুতাজিদের পর মুকতাফির (২৮৯-২৯৫) যুগ আসে। তিনি কোষাগারের উপার্জন এক কোটি চল্লিশ লাখে উন্নীত করেন।
২. পারস্য ও কিরমান থেকে বার্ষিক গড়ে (ব্যয়ের খাত কেটে রাখার পর) হিঃ ২৯৯-৩২০ পর্যন্ত ২ কোটি ৩০ লাখ দিনার কর ও সরকারী সম্পত্তি লব্ধ অর্থ। এ থেকে চল্লিশ লাখ সাধারণ কোষাগারে ও অবশিষ্ট এক কোটি ৯০ লাখ বিশেষ কোষাগারে দাখিল করা হতো। অবশ্য এ থেকে সেই সব দেশের জরুরী প্রয়োজনের খাত সমূহে ব্যয়িত অর্থ বাদ দেয়া আবশ্যক মনে করা হতো। যেমন হিঃ ৩০৩ সালে (৯১৫ খৃঃ) এই দেশগুলো জয় করতে তিনি ৭০ লাখের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করেন।
৩. মিসর ও সিরিয়া থেকে অর্জিত অর্থঃ যেমন অমুসলিমদের ‘জিজিয়া’ সংগ্রহ করে জনসাধারণের কোষাগারে দাখিল করার পরিবর্তে খলিফার কোষাগারে জমা করা হতো। কেননা আমিরুল মুমিনীন হবার কারণে নীতিগত ভাবে ওটা তার ন্যায্য অধিকার ছিল।
৪. পদচ্যুত উজীর, সচিব ও সরকারী কর্মচারীদের উপার্জিত অর্থ, তাদের বাজেয়াফ্ত করা সম্পত্তিঃ তাছাড়া খলিফা নিজের নিঃসন্তান ভৃত্যদের এবং রাজ পরিবারের নিঃসন্তান গোলামদের উপার্জিত অর্থের মালিক হতেন। যেহেতু তারা সাধারণতঃ উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী ছিল, তাই এ উপায়ে খলিফার কোষাগারে বিপুল অর্থের সমাগম হতো।
৫. সাওয়াদ, আওয়াজ এবং অন্যান্য পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত ও সরকারী সম্পত্তি লব্ধ অর্থঃ এটাও বিশেষ কোষাগারে দাখিল করা হতো।
৬. খলিফারা যে অর্থ সঞ্চয় করতেনঃ যেমন হিঃ তৃতীয় শতকের দু’জন শেষ খলিফা মুতাজিদ ও মুকাতাফী বার্ষিক ১০ লাখ দিনার সঞ্চয় করতেন। মুকতাদিরও অনুরূপ সঞ্চয় করতেন। এভাবে পনেরো বছরে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াতো এক কোটি পঞ্চাশ লাখ অর্থাৎ প্রায় খলিফা হারুনুর রশীদের অর্থের অর্ধেক।
এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ‘খলিফা’ নামধারী এই বাদশাহরা মুসলিম জনগণের ধন-সম্পদের ওপর কিভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামো ইসলামী মূলনীতি থেকে কতখানি ভিন্ন ধরণের হয়ে পড়েছিল।
একদিকে ধনের প্রাচুর্য, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা চরমে উঠেছিল অপরদিকে তারই পাশাপাশি বঞ্চনা, ক্ষুধা ও দারিদ্রের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। ইসলামী সমাজ ইসলামী রীতি-নীতি থেকে দূরীভূত ও ইসলামী মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ফলে অবনতির সর্বনিম্নস্তর উপনীত হয়েছিল।
কতিপয় মূলনীতি
কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ইসলামের বাস্তব কর্মধারা অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপারে অনেকগুলো মূলনীতি নির্ধারিত করে দিয়েছে। মানবতার একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, উমাইয়া শাসকদের কারণে ইসলামকে তার প্রথম যুগেই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তথাপি ইসলামী ইতিহাস ইসলামের অনেকগুলো মতাদর্শকে বাস্তব রূপদান করে দেখিয়ে দিয়েছে।
বাস্তব ইতিহাস এ কথা চূড়ান্তরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেঃ
১. ইসলামে অগ্রসর ব্যক্তিদের চেয়ে দরিদ্র লোকেরা বাইতুল মালের অর্থের অধিক হকদার। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘‘আদি ইবনে হাতেম বর্ণনা করেছেন, আমি স্বীয় গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট গমন করি। তিনি তাই গোত্রের কয়েক ব্যক্তির জন্য দু’হাজার করে ভাতা নির্ধারণ করছিলেন। আদি বলেন, আমি পুনরায় তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তথাপি তিনি আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমি পুনরায় তার সামনে এসে দাঁড়ালাম এখনো তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, ‘‘আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন?’’ হযরত ওমর রা. খিল খিল করে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, খোদার শপথ! আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি। সকলে যখন কুফরির ওপর অবিচল ছিল তুমি তখন ঈমান এনেছিলে। অন্যের যখন পশ্চাদপসরণ করছিল তুমি তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলে। অনেকেই যখন প্রতারণা করছিল তুমি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলে। আমার ভালভাবেই মনে পড়ে যাকাতের যে প্রথম অর্থ দেখে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবা রা. দের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সেটা ছিল তাই গোত্রের যাকাতের টাকা। আমিই সে টাকা রাসূলুল্লাহ সা. এর দরবারে আনয়ন করেছিলাম।’’ অতপর হযরত ওমর রা. এই বলে ওজর পেশ করতে আরম্ভ করেন যে, আমি এই অর্থ থেকে শুধুমাত্র সেই সব লোকের ভাতা নির্ধারণ করেছি যারা নিজ নিজ পোষ্যদের খাদ্য না দিতে পেরে অনাহারে কষ্ট ভোগ করছে। কেননা তারা হচ্ছে গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।’’
যে ওমর রা. ইসলামের ব্যাপারে অগ্রসর লোকদের অগ্রাধিকার দানের পক্ষপাতি ছিলেন, সেই ওমরের রা. পক্ষ থেকে এ উক্তি অত্যন্ত অর্থবহ এবং এ থেকে অনেক কিছু প্রমাণিত হয়। আসলে ইসলামী সমাজে ‘প্রয়োজন’ হচ্ছে অধিকারের সর্বপ্রথম ভিত্তি। এই মূলনীতি থেকেই বুঝা যায় যে ইসলাম দারিদ্র ও অভাবের কত বড় দুশমন এবং এগুলো মোচনের চেষ্টাকে সে অন্য সকল চেষ্টার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়।
২. সমাজের এক শ্রেণী সীমাহীন প্রাচুর্যের উদ্দাম স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে আর অপর শ্রেণী থাকবে বঞ্চিত-নিঃস্ব-সর্বহারা, ইসলাম কিছুতেই এটা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। এ ধরণের অবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসলাম সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে। এটা এমন একটা মূলনীতি যা ঐতিহাসিক ভাবে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে প্রমাণিত। তিনি বনু নজীর থেকে সংগ্রহীত ‘ফায়’ এর সমগ্র অর্থই শুধুমাত্র দরিদ্র মোহাজেরদের মধ্যে বিতরণ করেন- যাতে প্রথম সুযোগেই ইসলামী সমাজে খানিকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র দু’জন দরিদ্র আনসারকে তিনি তাদের সাথে শামিল করেন। অতঃপর কোরআন এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসেঃ
‘‘যাতে করে ধন-সম্পদ শুধুমাত্র তোমাদের ধার্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবর্তনশীল না থাকে।’’
এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এর আলোকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী শাসনকারী মুসলমান শাসন মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাইতুল মাল থেকে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য করার সর্বদাই ক্ষমতা রাখে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের মধ্যে যাতে সাধারণ ভারসাম্য ব্যাহতকারী বৈষম্য বিরাজিত না থাকে এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।
৩. ক্ষমতা ও অক্ষমতা অনুপাতে করের হারে তারতম্য করা অপরিহার্য। অমুসলিমদের ওপর জিজিয়া ধার্য করার সময়ে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের ওপর নিম্নলিখিত হারে কর ধার্য করা হয়ঃ
ক. বিত্তশালী শ্রেণী- মাথা প্রতি বার্ষিক ৪৮ দিরহাম।
খ. মধ্যম শ্রেণী- মাথা প্রতি বার্ষিক ২৪ দিরহাম।
গ. দরিদ্র শ্রমজীবি- মাথা প্রতি বার্ষিক ১২ দিরহাম।
সম্পূর্ণ নিঃস্ব, দেউলে, শ্রমে অক্ষয় এবং শারীরিক অথবা মানসিক দিক থেকে পঙ্গু ব্যক্তিদের জিজিয়া মওকুফ। কেবলমাত্র স্বাধীন সুস্থমনা পুরুষদের জিজিয়া দিতে হতো। মহিলা কিংবা শিশুদের জিজিয়া দিতে হতো না।
দুর্ভিক্ষের বছর হযরত ওমর রা. জাকাত সংগ্রহ করার জন্য কর্মচারী পাঠাননি- বরং দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া পর্যন্ত জাকাত আদায় স্থগিত রেখেছিলেন। দুর্ভিক্ষ শেষে তিনি আদায়কারী পাঠান এবং সক্ষম লোকদের নিকট দ্বিগুণ জাকাত দাবি করেন। একটি দুর্ভিক্ষের বছরের দ্বিতীয়টি চলতি বছরের। অক্ষম লোকদের তিনি ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দেন যে আদায়কারী যেন তার সংগৃহীত দ্বিগুণ অর্থের এক ভাগ উক্ত অক্ষম লোকদেরকে দিয়ে আসে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ রাজধানীতে নিয়ে আসে।
৪. বল প্রয়োগ করা অথবা জীবনের প্রয়োজনীয় অর্থ থেকে কাউকে বঞ্চিত করে কর আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল। হযরত আলী রা. তার জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ দেন ‘‘তুমি যখন তাদের নিকট যাবে তখন কর আদায় করার জন্যে তাদের গ্রীষ্ম কিংবা শীতের বস্ত্র-খাদ্য-দ্রব্য ও সওয়ারীর জন্তু বিক্রি করবে না, কাউকে একটা বেত্রাঘাতও করবে না, কাউকে এক পায়েও দাঁড় করাবে না যতই খাজনা বা কর বাকী থাকুক না কেন। কেননা আমাদেরকে শুধু জন-সাধারণের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
৫. ‘‘প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ত্যাগের অনুপাতে’’ এই নীতির পাশাপাশি ‘‘প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুপাতে’’ নীতিও কার্যকরী করা অপরিহার্য। নবী করীম সা. গণিমত লব্ধ অর্থ থেকে অবিবাহিতদের জন্য এক অংশ এবং বিবাহিতদের জন্য দুই অংশ নির্ধারিত করেন। এ থেকে এ কথাই প্রামণিত হয় যে ভাতা নির্ধারণে পরিশ্রমের সাথে সাথে প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নইলে এটা জানা কথা যে, জেহাদে বিবাহিত এবং অবিবাহিতকে সমান পরিশ্রম করতে হয়। কেবল বিবাহিতের প্রয়োজন দ্বিগুণ বলে তাকে দ্বিগুণ ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে শুধুমাত্র ‘প্রয়োজন’ ও ইসলামে মালিকানা অর্জনের একটা পৃথক মাধ্যম হতে পারে। ‘সামাজিক নিরাপত্তা’র ব্যাপারে এ মূলনীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৬. প্রত্যেক অক্ষম ও অভাবী ব্যক্তির জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিধান। হযরত ওমর রা. প্রত্যেক নবজাতকদের জন্য একশো দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। শিশু একটু বড় হলে দু’শো দিরহাম এবং সাবালক হবার পর তাকে আরো বেশী দেয়া হতো। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর জন্য একশো দিরহাম এবং তাকে লালন-পালনকারীর জন্য অতিরিক্ত ভাতা দেয়া হতো, শিশুর দুধ পান করানো ও অন্যান্য ব্যয়ভার ‘বাইতুল মাল’ থেকে বহন করা হতো, আর সে বড় হলে অন্যান্য বালকদের সমান ভাতা পেত।
হযরত ওমরের এই উদারতা আসলে ইসলামের উদারতারই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ, কেননা পথে পড়া শিশু নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। সে তার অপরাধী মা-বাপের পাপের জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নয়। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত ওমর রা. অন্ধ ইহুদী ও খৃষ্টান কুষ্ঠ রোগীদের জন্য ‘বাইতুল মাল’ থেকে সাহায্য বরাদ্দ করেছিলেন। ওমরের রা. প্রকৃতিতেও উদারতা সকল মানুষের জন্য ছিল, শুধু মাসলমানদের জন্য নয়। এটা হচ্ছে অভাব, অক্ষমতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।
৭. ‘‘সম্পদ কোত্থেকে অর্জিত হয়েছে?’’ এ মৌলিক প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাসকের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা আসলে জাতির সম্পদ না তার নিজস্ব এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার মুসলিম সমাজের রয়েছে, এ ব্যাপারে জনগণের হিসাব গ্রহণের হাত থেকে তার অব্যাহতি লাভের কোনো উপায় নেই। এ হিসাব গ্রহণের নীতি নির্ধারিত হওয়ার ফলে জাতীয় কোষাগার প্রশাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। এ ধরণের কোনো কিছু করার পূর্বে শাসককে একাধিকবার চিন্তা করতে হয়। হযরত ওমর রা. তার সকল শাসনকর্তাদের সাথে এরূপ করেছেন। হযরত আলীও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ নীতি অবলম্বন করেছেন।
৮. যাকাত ব্যবস্থা ইতিহাসের সেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগেও স্থগিত হয়নিঃ যদিও সে যুগ ইসলামের প্রাণশক্তি থেকে বহু দুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। হযরত আবু বকর রা. এর যুগের প্রারম্ভে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ যাবত কোনো এক ব্যক্তিও মৌখিক অথবা কার্যতঃ যাকাত অস্বীকার করেনি। কেবল আমাদের যুগে এসে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ীর আসনের অধিষ্ঠিত হলো। তখন তারই পরিণামে ইসলামী মূলনীতি সমূহের সর্বশেষটি যাকাতও মুসলমান সমাজের বাস্তব জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।
৯. সাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক জনপদের লোকদেরকে সেখানে অনাহারে মৃত্যুবরণকারী যে কোনো ব্যক্তির জন্যে দায়ী করা হয়। ফৌজদারী বিধি অনুসারে তাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়। এই ভাবে মৃত্যুবরণকারী লোকের জন্য সংশ্লিষ্ট জনপদের সবাইকে পাইকারীভাবে জরিমানা তথা ‘দিয়াত’ দিতে হয়। কারণ সমাজের সকলে সেই ব্যক্তির হত্যাকারী সাব্যস্ত হয় যে তাদেরই মধ্যে থেকে অনাহারে ধুকে ধুকে মরেছে।
এই বিধান শরিয়াতের অপর একটি বিধান দ্বারাও সমর্থিত হয়। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন ক্ষুধা-পিপাসা জর্জরিত ব্যক্তি ক্ষুধা-পিপাসায় মৃত্যু বরণ করার আশংকা বোধ করলে তাকে খাদ্য অথবা পানীয়ধারী ব্যক্তির সাথে সবশেষ পন্থা হিসাবে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তিকে সে হত্যা করলে তার দুনিয়ায়ও কোনো শাস্তি জরিমানা হবে না এবং আখেরাতেও আযাব ভোগ করতে হবে না।
১০. সুদ বিলোপ এবং দারিদ্রাবস্থায় ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির নীতিঃ আধুনিক সভ্যতা সুদকে হালাল ঘোষণা করার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম সমাজে সুদ যথারীতি নিষিদ্ধই ছিল। ফরাসী আইন এই অভিশাপ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং একে আমাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনের একটা অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করে। অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটা শুধু এই জন্যে প্রচলিত হয় যে আমাদের বাস্তব জীবন থেকে নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব মুছে গিয়েছিল এবং মানুষের মন থেকে সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ ইসলাম এই মনোভাবকে সমাজে ও পারস্পরিক লেন-দেনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।
এ বিষয়গুলি ছাড়াও পারস্পরিক সহানুভূতি ও সামাজিক নিরাপত্তা জনিত বহুনীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে যা আইনের শক্তি দ্বারা কার্যকরী করার বস্তু নয়। স্বয়ং আমাদের নিকট অতীত ও মুসলিম সমাজের ওপর ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। এ যুগ আমাদের দাদারা নয় বরং পিতারাই স্বচক্ষে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে অবলোকন করেছেন। মুসলিম জাহানের ওপর পাশ্চাত্যে বস্তুবাদী সভ্যতার সর্বাত্মক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও আজও এই প্রভাব অনেকটা অম্লান রয়েছে। সেখানে এই মূল্যবোধ কার্যকরী করার ব্যাপারে আইন ও বল প্রয়োগের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আজ কালকার সরকার সমূহের মধ্যে যে সব ওয়াক্ফ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়- যাকে আজ তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যাকে বিভিন্ন শোষক শ্রেণী নানা নামে ও নানা দলে কুক্ষিগত করে রেখেছে এ সব প্রকৃতপক্ষে দূর ও নিকট অতীতের মুসলমানদের হৃদয়ে অবস্থিত দয়া, সহানুভূতি, সৎকর্মশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পবিত্র মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে। পাশ্চাত্যের নৃশংসতা, মৃত চেতনা ও স্থবির জড়বাদী সভ্যতা তাদের অন্তরাত্মাকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়নি।
আমাদের স্বর্ণযুগে দুর্বলের প্রতি সামাজিক নিরাপত্তা দানের মনোভাব এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, শুধু মানুষই নয় জন্তু-জানোয়ারও তা থেকে উপকৃত হয়েছে, বহু স্থানে দুর্বল পশুদের আশ্রয় স্থল তৈরী করার জন্য কোনো কোনো স্থান ওয়াক্ফ করা হয়েছে যাতে তারা সেখানে এসে ক্ষুধা ও দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।
প্রাথমিক স্তরে শাসন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক কার্যধারায় কিছুটা বিকৃতি দেখা দেয়ায় সে সুদূর প্রসারী ক্ষতি হয়েছে তা সত্ত্বেও এটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম।
ইতিহাসের বাস্তব মঞ্চে এই হচ্ছে ইসলামের ভূমিকা যা বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর সাধারণ মূলনীতিগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা চলে যে, নবতর পরিস্থিতির দাবি পূরণ এবং নতুন সমস্যাবলীর সমাধান করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা তার রয়েছে, ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে। আগামী দিনে যে সমাজ ইসলামের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যেখানে ইসলামী শরিয়তকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দান করা হবে সেখানে ইসলাম, সেই সমাজের যাবতীয় দাবী ও প্রয়োজন অত্যন্ত ব্যাপকতা ও ভারসাম্য সহকারে পূরণ করতে সক্ষম হবে। আজকের মানব সমাজ যেভাবে মতবাদ সমূহ ও মানবীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরন্তর এক চরম সীমা থেকে অপর চরম সীমায় গিয়ে আঘাত খাচ্ছে, আর এই ঘাত-প্রতিঘাতে মানব জাতি যেরূপ তার বহু মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দিচ্ছে- ইসলাম তাকে এই অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি থেকে চিরতরে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করবে। [গ্রন্থকারের ‘‘আল ইসলাম ওয়া মুসকিলাতুল হাজারা’’ (ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার সংকট) গ্রন্থের ‘‘উজতেরাব ওয়া ইনতেমার’’ (উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি) অধ্যায় দ্রষ্টব্য]
........ সমাপ্ত ........
সুচীপত্রঃ
প্রকাশকের কথা
ইসলামের মূল প্রাণশক্তি
বিবেকের সচেতনতার দৃষ্টান্ত
সাম্যের উদাহরণ
ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা
বিজিত দেশসমূহের সাথে ব্যবহার
পারষ্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
রাজনৈতিক ব্যবস্থা
শাসন পদ্ধতির কতিপয় নমুনা
হযরত ওসমানের শাসন পদ্ধতি
হজরত ওসমানের পর
ওমর ইবনে আবদুল আজিজ
রাজতন্ত্র
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
কতিপয় মূলনীতি
প্রকাশকের কথা
ইসলামের মূল প্রাণশক্তি
বিবেকের সচেতনতার দৃষ্টান্ত
সাম্যের উদাহরণ
ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা
বিজিত দেশসমূহের সাথে ব্যবহার
পারষ্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
রাজনৈতিক ব্যবস্থা
শাসন পদ্ধতির কতিপয় নমুনা
হযরত ওসমানের শাসন পদ্ধতি
হজরত ওসমানের পর
ওমর ইবনে আবদুল আজিজ
রাজতন্ত্র
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
কতিপয় মূলনীতি

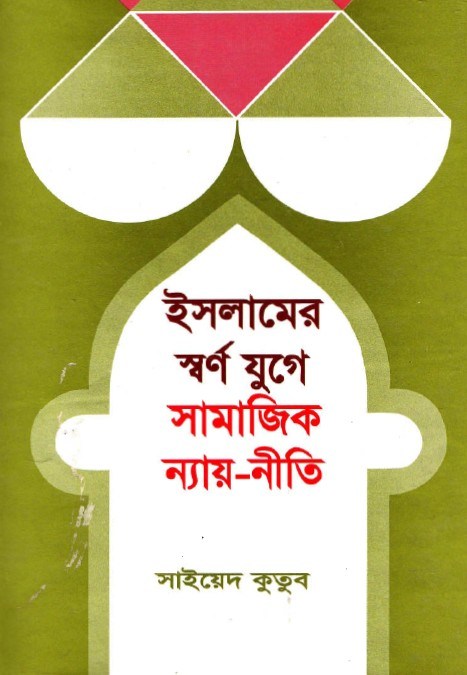 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড